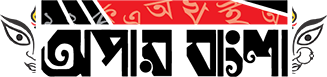ছন্দা বিশ্বাস
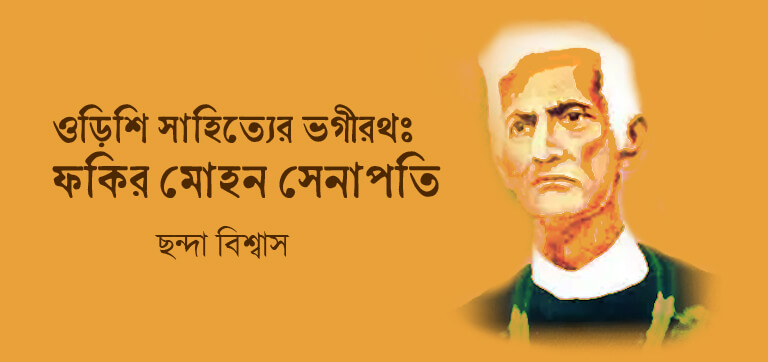
অসমিয়া সাহিত্যের পথ প্রদর্শক লক্ষ্মীকান্ত বেজুবরুয়া তখন শিলং-এ। অসমিয়া ভাষায় তিনি একের পর এক রচনা করে চলেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, প্রহসন ইত্যাদি। সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ পদসঞ্চার। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল। সেদিন কথার ভিতরে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেন, “তোমরাই তো আসামকে বাংলা থেকে বার করে করে নিয়ে বাংলা ভাষার পরিসর কমিয়ে দিলে।”
সেদিন লক্ষ্মীকান্ত মুখ বুজে রবীন্দ্রনাথের সেই কথা সহ্য করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন তখন ঠাকুর বাড়ির জামাতা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলতে পারেন সেটা ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে।
ঠিক এই রকমভাবে ওড়িশা ভাষায় সাহিত্য রচনা নিয়েও কম বিপাকে পড়তে হয়নি সাহিত্যিক শ্রী ফকির মোহন সেনাপতি মহাশয়কে।
তাঁকে বলা হয় ওড়িশা সাহিত্যের ভগীরথ। ওড়িশা সাহিত্যের নবযুগের সূচনা ঘটেছিল তাঁরই হাতে।
যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে ওড়িশার অবস্থান ছিল, বাংলা, মাদ্রাজ এবং সেন্ট্রাল- এই তিন প্রেসিডেন্সীর ভিতরে। গঞ্জাম ছিল মাদ্রাজের ভিতরে, সম্বলপুর ছিল সেন্ট্রালের অধীনে এবং পূর্ব দিকের উপকূল অঞ্চলের ভিতরে পুরী, বালেশ্বর আর মেদিনীপুর ছিল বাংলার ভিতরে। এই সব অঞ্চলে তখন হিন্দী, তেলেগু এবং বাংলাভাষী আমলাদেরই প্রবল দাপট।
এরাই যেন সেই সময়ে এই সমস্ত অঞ্চলে উপনিবেশবাদ গড়ে তুলেছিলেন। বাংলার মানুষজন সেই সময়ে ওড়িয়াভাষী মানুষদেরকে খুব একটা সুনজরে দেখতেন না।
কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। বাঙ্গালিদের প্রবল দাপট গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। ওড়িশাও তখন এই বাংলাভাষীদের দাপটের ভিতরে কুন্ঠিত হয়ে থাকত। বাঙ্গালিরা স্বাভাবিক কারণে ওড়িয়া ভাষাকে কিছুতেই স্বীকৃতি দিতে চাইল না। কিছু করতে গেলেই রে রে করে উঠতেন। এমনই দাপট ছিল বাংলা ভাষা তথা বাঙ্গালিদের।
ইতিহাসের পরিভাষায় একেবারে মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতি। ভাষার এমন সংকটজনক পরিস্থিতি অনেকের মতো ফকিরমোহনকেও ব্যথিত করল। বাংলা ভাষা তখন দাপটের সঙ্গে দাবিয়ে রাখতে চাইছে ওড়িয়া আর অসমিয়া ভাষাকে। সেই সময়ে ভাষার এই মাৎসন্যায়ের দলে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। সরাসরি ওড়িশা ভাষার স্বাতন্ত্র্য অগ্রাহ্য করতে শুরু করলেন। এই দলে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত।
সেই সময়ে ওড়িশা ভাষার কয়েকজন অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। ওড়িয়া ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যে করেই হোক এই ভাষার অধিকার আদায় করতে হবে। এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্যেই ওড়িশায় শুরু হল ভাষা অন্দোলন। ফকিরমোহন সেই সময়ে এগিয়ে এলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওড়িশার মানুষদেরকে বাংলা শিখে তারপরে বাঙ্গালিদের সঙ্গে চাকরির প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়াটা মোটেও সহজ কথা নয়। তাই স্বভাষীদের ক্ষমতা আদায়ের লক্ষ্যে তিনিও যোগ দিলেন এই অন্দোলনে।
প্রথমেই তিনি ওড়িশার স্কুলগুলোতে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করলেন। বাংলা চালু থাকলে এতে এখানকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া শেখাটা কঠিন হবে। চাকরি বাকরি পাওয়াটাও কঠিন হবে। বাঙ্গালিরাই তখন প্রশাসনিক কাজে তাদের আধিপত্য বজায় রাখবে।
এদিকে বাংলার লেখক সাহিত্যিকদের একাংশ চাইছিলেন ওড়িয়া ভাষায় যাতে সাহিত্য রচনা না হতে পারে। এতে তাদের আয়ের উৎস কমে যাবে।
স্বয়ং রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬৯ সালে কটকের এক বক্তৃতা সভায় স্পষ্ট করে বললেন, ওড়িয়া ভাষা ওঠাতে না পারলে এ দেশে(ওড়িশা)র উন্নতি সম্ভব নয়।
কারণটা কারো অজানা ছিল না। তাঁর রচিত বই সে সময়ে স্কুলের পাঠ্যবই হিসাবে পঠিত হচ্ছে। চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে কথাগুলো বলে চরম হীনমন্যতার পরিচয় দিলেন। ওড়িয়া ভাষী মানুষ সেদিন তাঁর এই কথাগুলোয় কষ্ট পাওয়ার থেকে ক্ষুব্ধ হলেন বেশী।
উপায়ান্তর না দেখে এই সময়ে ফকিরমোহন নিজেই কলম ধরলেন। ওড়িশার ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে নিজেই বই লিখতে শুরু করেন। তিনিই প্রথম ওড়িয়া ভাষায় লিখলেন, ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’।
এই বই প্রকাশের পরে ওড়িয়া লেখক এবং ওড়িয়া শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের ভিতরে আলোড়ন উঠল। এই বই ভাষা আন্দোলনকে আরো কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেল।
তবে এই অন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যে বহু মানুষ নানা ভাবে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সমালোচনা, নানা গালমন্দ কু-কথার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ফকিরমোহনকে।
তবু তিনি আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। বরঞ্চ আরও বেশী করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই মাৎস্যন্যায়ের বিরুদ্ধে।
বালেশ্বর গভর্ণমেন্ট স্কুলের ওড়িয়া পন্ডিত শ্রী কান্তিমোহন ভট্টাচার্য একদিন বলেই ফেললেন, ওড়িয়া পড়ার আর দরকার নেই। এটা হল বাংলারই এক বিকৃত সংস্করণ।
তিনি এই কথাটাই সকলের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।
কিছুদিনের মধ্যেই এর স্বপক্ষে তিনি একটা পুস্তক রচনা করে ফেলেন, “ওড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে”।
১৮৭০ সালে এটি প্রকাশিত হলে ফকির মোহনের অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।
বইটিতে তিনি ফকিরমোহনকে রীতিমতো ফাঁসিয়ে দিলেন।
ইতিমধ্যে ফকিরমোহন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে অনুবাদ করে ফেলেছেন ‘বিদ্যাসাগর জীবন চরিত’। ১৮৬৬ সালে সেটি প্রকাশিত হলে এবারে সেই বই থেকে উদ্ধৃতি তুলে তুলে কান্তিমোহন ভট্টাচার্য দেখালেন, স্বয়ং ফকির মোহন পর্যন্ত বলেছেন, বাংলার সঙ্গে ওড়িয়ার কত সাদৃশ্য। কেবল ক্রিয়ামাত্র পাল্টে দিলেই বাংলা ওড়িয়া হয়ে যায়।”
অবশ্য এ কথা ঠিক যে ফকিরমোহনের লেখাতে বাংলা ভাষার যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি তো বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছেন। দীনবন্ধু মিত্রের রচনা পড়েছেন। সঞ্জীব চট্টপাধ্যায়, রমেশ্চন্দ্র দত্তের লেখা পড়েছেন। তাই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘ছ মণ আথা গুঁথা’ উপন্যাসে অনেক জায়গায় বঙ্কিমী প্রভাব উপন্যাস ‘বিষবৃক্ষে’র কিছু কিছু জায়গার সঙ্গে মিল আছে।
এরপরে ফকিরমোহন ভ্রমণ কাহিনি লিখলেন। ‘উৎকল ভ্রমণে’ও দীনবন্ধু মিত্রের ‘সুরধুনী কাব্যে’র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
আসলে তিনি তো বাংলা ভাষাকে রীতিমতো ভালবেসেই করায়ত্ত করেছিলেন। কখনো উপনিবেশের ভাষা বলে মনে করেননি। তাই তাঁর রচনাতে বাংলার প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক।
সেই সময়ে মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষেরা ওড়িয়া ভাষায় কথা বললেও তাদের শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলাই। ফকিরমোহন এবং তাঁর দলের কয়েকজন ঠিক করলেন এটা চলতে পারে না। তাঁরা ওড়িয়া পন্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। পন্ডিতেরা বুঝতে পারলেন এভাবে চলতে থাকলে ওড়িয়া ভাষা একদিন কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। এবারে ওড়িয়া পন্ডিতেরা তাঁদের সঙ্গে অংশ নিলেন।
এরপরে ভাষা আন্দোলন শুরু হলে ওড়িয়া পন্ডিতেরা দাঁতন, পটাশপুর, কোলাঘাট, তমলুক, মহিষাদল ইত্যাদি অঞ্চলে যেতেন কেবলমাত্র ওড়িয়া ভাষা শিক্ষাদানের জন্যে।
বালেশ্বর সেই সময়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৪৩ সালের ১৩ই জানুয়ারী মল্লিকাশপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ফকিরমোহন সেনাপতি। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হলেও খুব শৈশবে তিনি পিতৃহারা হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র দেড় বছর। এর পরের বছরে মা মারা গেলেন। বাবা লক্ষ্মণচরণ সেনাপতি এবং মা তুলসীদেবীর মৃত্যুর পরে শিশুর দায়িত্বভার এসে পড়ল পিতামহীর উপরে। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্যে তিনি পড়াশুনাতে বেশ পিছিয়ে ছিলেন। শৈশবে পিতামাতার মৃত্যুতে তাঁর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। ওই শিশু বয়েসেই তাঁর আপন ছোট কাকা তাকে হিংসা করতে লাগলেন। নানা কাজের দায়িত্ব পড়ল তাঁর উপরে। সঙ্গে মারধোর তো উপরি পাওনা হিসাবে ছিলই। অল্প বয়েসে তিনি শিশু শ্রমিক হিসাবে নিজের ব্যয় ভার বহন করতে শুরু করেন।
কখনো কখনো স্কুলের ফি দিতে না পারার জন্যে শিক্ষকদের বাড়িতে পর্যন্ত কাজ করেছেন। নানা ফাইফরমায়েশ খেটেছেন। নীরবে নানা আদেশ পালন করেছেন। তাঁর সামনে তখন একটাই লক্ষ্য, যে করেই হোক পড়াশুনা শিখে বড় হতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষা ছাড়া তাঁর জীবনের এই আঁধার কিছুতেই ঘুচবে না।
এরপরে নানান ঘটনাক্রমের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হতে লাগল।
প্রথমে বালেশ্বরের স্কুলে ভর্তি হলেন। কিছুদিন পড়ার পরে অর্থের কারণে তাঁকে পড়াশুনা ছাড়তে হল। এরপরে আবার সংগ্রামী জীবন শুরু হল। নানান প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে তিনি আবার স্কুলে ভর্তি হলেন। পড়াশুনার প্রতি অদম্য নিষ্ঠা তাঁকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারল না।
নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি ডিঙ্গিয়ে অবশেষে তিনি বারবাটিতে আড়াই টাকা বেতনের শিক্ষকতা জীবন শুরু করলেন। এরপরে কিছুদিন এখানকার কালেকটরেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন।
এখানেও কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর। এরপরে ১৮৭১ সালে তিনি মিশন স্কুলে চাকরি নিলেন। পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিখতে লাগলেন।
ফকিরমোহন সেনাপতি বাংলা, ইংরাজী আর সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন নিজের চেষ্টায়। ইংরাজী অভিধানের সাহায্য নিয়ে তিনি ইংরাজী শিখেছিলেন। জীবনে নানা ধরণের কাজ করেছেন। কখনো কখনো বন্দর শ্রমিক হিসাবে কখনো বা কাঠের ব্যবসা আর কখনো কাগজের ব্যবসায় নেমেছিলেন।
বোঝাই যাচ্ছে ফকিরমোহন যে সময়ে জন্মান সেটা হল ওড়িশি সাহিত্যের এক অন্ধকারময় যুগ।
এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে দেখা দিয়েছিল ‘নানকা’ দুর্ভিক্ষ।
যার ফলে এই অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। এই সময়ের মর্মন্তুদ বর্ণনা তাঁর অনেক গল্প উপন্যাসে বিধৃত আছে। এসময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল একজন সাহেব কালেক্টর জন বীমসের সঙ্গে। জন সাহেব ফকিরমোহনকে ধরে বসলেন তাঁকে ওড়িয়া ভাষা সেখাতে হবে।
এই জন সাহেব পরে ফকিরমোহনকে নীলগিরির দেওয়ান পদের জন্যে সুপারিশ করেন। এরপরে ফকিরমোহন ওড়িশার নানান জায়গায় চাকরিসূত্রে কাটান। দামাপাড়া, ঢেঙ্কানল, দাস পাল্লা, পাল্লাদা ইত্যাদি নানান জায়গার দিওয়ান হন। কাজের ভিতরেও চলল সাহিত্য সাধনা।
এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দীর্ঘ একটি কবিতা লিখে ফেললেন। নাম দিলেন, ‘উৎকল ভ্রমণম।’
কবিতাটি ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
তিনি চারটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এগুলি হল, ‘ছয় মনা আথা গুন্থা’, ‘প্রায়শ্চিতা’, মামু, লাছমা।
প্রথম তিনটি উপন্যাসে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছাপ রাখা আছে।
‘লাচমি’ উপন্যাসের পটভূমিকা হল মারাঠা কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের ভয়ংকর বর্ণনা।
এই উপন্যাস চারটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ থকে ১৯১৫ সালের ভিতরে।
ফকিরমোহন বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন। তাঁর গল্পগুলি সামাজিক দলিল হসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গল্পের ভিতরে সাড়া জাগানো গল্প হল, ‘রেবতী’।
প্রথম ওড়িয়া গল্প হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। ছত্রিশটি ভারতীয় ভাষায় এবং বিদেশী ভাষাতে অনুদিত হয়েছিল। এই গল্পকে বলা হয়, ‘বিশ্বের মহামারী সাহিত্যের গল্প’।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রেবতী নামে একটি মেয়ের জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যার পড়াশুনাতে ছিল অদম্য বাসনা। কিন্তু নিষ্ঠুর মারণ রোগ কলেরায় সে আক্রান্ত হল। তার মৃত্যু কাহিনীর এক মর্মান্তিক পরিণতি। এক রক্ষণশীল পরিবারের কথা ধরা আছে এই গল্পের ভিতরে। এ ছাড়া আরো উল্লেখযোগ্য গল্প হল, ‘পেটেন্ট মেডিসিন’, ‘অধর্ম বিত্ত,’ ‘ধুলিয়া বাবা’, ‘ডাক মুন্সী’ ইত্যাদি।
বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে ‘রান্দিপুয়া অনন্ত’ গল্পটি।
এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্ত গ্রামের একজন কুখ্যাত চরিত্রের যুবক। কিন্তু সেই যুবকই শেষ পর্যন্ত কীভাবে মানুষের উপকারে নেমে গেল সেটাই গল্পের মূল বিষয়। নদী বাঁধে ফাঁটলের ফলে গ্রামে হু হু করে করে জল ঢুকছে দেখে অনন্ত তার ঘরের দরজা সেই গর্তের উপরে পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়লেই দরজাশুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এবারে সেই গ্রামের মানুষদেরকে বলে এর উপরে মাটি ফেলতে। মাটি ফেলতে ফেলতে এমন পরিস্থিতি হয় সে তার নিচেয় চাপা পড়ে যায়। নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে গেল গ্রামবাসীকে। তার মৃত্যুবরণ গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্যে। অনন্ত ওড়িয়া ছোটগল্পের এক বিরল চরিত্র ।
‘ছয় মনা আথা গুন্থা’ উপন্যাসটি পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। পার্বতী ঘোষের প্রযোজনায় এটি নির্মিত হয় ১৯৮৬ সালে। আঞ্চলিক ছায়াছবি হিসাবে এটি নির্মিত হয়েছিল। বিজয় মোহন এবং পার্বতী ঘোষ রূপদান করেন যথাক্রমে সরিয়া এবং বাঘিয়া চরিত্রে। সরাত পূজারী ছিলেন খলনায়কের চরিত্রে।
রামচন্দ্র মঙ্গরাজ এর চরিত্রে তিনি রূপদান করেন। একজন ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের উপরে সামন্ত প্রভুদের অকথ্য অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে। যদিও এটি রুশ বিপ্লব কিম্বা ভারতের মার্কসবাদী উত্থানের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল।
মাত্র তের বছর বয়সে ফকিরমোহন লীলাবতীকে বিয়ে করেন। পরে লীলাবতী দেবী মারা গেলে তিনি কৃষ্ণকুমারী দেবীকে বিয়ে করলেন। ফকিরমোহন এরপরে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন, সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করছেন। সাহিত্যের নানা ধারায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। ‘আধুনিক ওড়িয়া গদ্যের জনক’ হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর রচিত চারটি উপন্যাস অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ছাপ রেখে গেছে। ‘মামু’, ছয় মন আথা গুন্থা’, ‘প্রয়াশ্চিতা’ উপন্যাসে ধরা পড়েছে সামাজিক বাস্তবতা।
‘লাচমা’ উপন্যাসের পটভূমিকা হল মারাঠা আক্রমনে উড়িষ্যার যে ভয়ংকর রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল তারই বর্ণনা।
গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ ইত্যাদি হরেক ফুল ফুটিয়েছেন সাহিত্যের আঙ্গিনায়। এরপরে তিনি লিখলেন ‘আত্মজীবনী।’ তিনি ছিলেন ওড়িয়া ভাষার প্রথম আত্মজীবনীকার।
তাঁর আত্মজীবনীর নাম হল, ‘আত্মাজীবন চরিতা’।
সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি চলল ওড়িয়া ভাষা নিয়ে নিরন্তর আন্দোলন।
ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল স্কুলগুলো থেকে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করা।
সেই সময়ে সরকারী অফিস-কাছারিগুলোই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কর্মক্ষেত্র এবং আয়ের একমাত্র উৎস। তাঁর মাথায় এসেছিল যতদিন বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকবে ততদিন ওড়িয়াভাষীদের পক্ষে উচ্চশিক্ষায় লেখাপড়া শেখাটা শক্ত হবে। ফলে আশানুরূপ চাকরিও জুটবে না। এর ফলে সব জায়গাতেই বাঙ্গালিদের আধিপত্য বেড়েই চলবে। ওড়িয়াভাষীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ক্রমাগত।
রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেদিন সভায় বললেন, বাংলা ভাষা না তুলে দিলে এ দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।
‘দেশ’ বলতে তিনি উড়িষ্যাকেই বুঝিয়েছেন।
রাজেন্দ্রলালের এই বক্তৃতার পরে বেশ উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। ‘উৎকল দীপিকার’ সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য মহাশয় পর্যন্ত জোর করে বাংলা ভাষা চাপানোর বিরোধিতা করেছিলেন।
সেই সময়ে অনেকেরই ধারণা ছিল, ওড়িয়া কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নয়। ওড়িয়া কোনো স্বাধীন ভাষাও নয়।
সাহিত্যের একই আঙ্গিনায় বসে যুযুধান দুই পক্ষ।
কিন্তু ফকিরমোহন এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন যতদিন ওড়িষ্যার মানুষ ওড়িয়া ভাষায় নিজেদের শিক্ষিত করতে পারবে ততদিন সরকারী চাকরি তাদের কাছে দুরাশা মাত্র। কারণ বাংলা ভাষীরাই এই সব চাকরিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। ওড়িশাভাষীরা পদে পদে বাঙ্গালীদের কাছে হেনস্থা হচ্ছে।
আনন্দীলাল মিত্র ছিলেন এই বিরোধীদের ভিতরে একজন।
ফকিরমোহন তাদের এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিলেন। তাই নিয়ে তাঁকে কম লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি।
অনেকেই তাঁকে সামনাসামনি বলতেন, আপনার লেখায় তো বাংলার প্রভাব রয়েছে। এখন বাংলার বিরুদ্ধাচারণ করছেন কেন?
এটা ঠিকই যে ‘ছয় মনা আথা গুন্থা’ উপন্যাসে ফকিরমোহন অনেক জায়গাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের কিছু কিছু অংশ তুলে নিয়েছেন। যেমন, ‘যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা’র জায়গায় লিখেছেন, ‘যা দেবী বৃক্ষমূলেষু শিলারূপেণ সংস্থিতা।’
ঠিক তেমনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ‘উৎকল ভ্রমণে’ও দীনবন্ধু মিত্রের রচনার বেশ কিছু জায়গার মিল আছে। ‘সুরধুনি কাব্যে’র প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কিছু কিছু জায়গায়।
বিতর্ক উঠলে অনেকেই আবার ফকিরমোহনের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। বলেছেন, এগুলোকে ঠিক অনুকরণ বলা চলে না। শিশিরকুমার দাসের মতে, ‘It created a new world of fiction which was further expanded and enriched later in the century by Premchand and Tarashanker Bandyopadhyay.’
আসলে ফকিরমোহন বুঝতে পেরেছিলেন বিভিন্ন প্রকাশনার দরকার। প্রকাশকরাও তাঁর বই ছাপাতে চাইছেন না। তিনি পদেপদে ঠোক্কর খাচ্ছেন। অথচ তাঁর ভিতরে সৃষ্টির রসদ পূর্ণ। তাই তিনি নিজে থেকে একটা ওড়িয়া প্রিন্টিং প্রেস চালু করলেন। এরজন্যে অনেকের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন।
যাই হোক পরে অবশ্য সকলের ধার শোধ করে দেন।
নিজের মনের বাসনা পূরণ করলেন এই ‘পি এম সেনাপতি এন্ড কোং উৎকল প্রেস’ স্থাপন করার পরে। বালেশ্বরে এই প্রেস দেখার জন্যে দলে দলে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসতে লাগলেন।
এরপরে সেই প্রেস থেকেই নিজের লেখা ওড়িয়া ভাষায় বই প্রকাশ করতে লাগলেন।
এরপরে তিনি ওড়িয়াতে লিখে ফেললেন ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’।
অনুবাদ করলেন বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত। অবশ্যই পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে।
এ ব্যাপারে মধুসূদন দাস ও গৌরীশংকর রায়কে তিনি পাশে পেয়েছিলেন। এঁদেরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।
অবশেষে সুদিন এলো। ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার গ্রাস থেকে মুক্ত হল।
সাহিত্যের ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা হল।
ওড়িয়া ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ায় নানা সময়ে নানা ভাবে ফকিরমোহনকে মানুষ হেনস্থা করেছিল। নানা অপবাদ, দুর্নাম রটাতেও দ্বিধা করেনি।
কিন্তু ফকিরমোহন এক জায়গায় স্থির-অবিচল ছিলেন। হাজার দুর্বনাম, প্রতিরোধেও তিনি মাথা নোয়ান নি। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন ওড়িয়া ভাষাকে যে করেই হোক সরকারী সিলমোহর লাগাতে হবে।
ফকিরমোহন তাঁর জীবন চরিতের এক জায়গায় লিখেছিলেন, মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশের কিছু জায়গার মানুষ কথাবার্তা বলেন ওড়িয়াতে কিন্তু তাদের পঠন পাঠন চলে বাংলায়। আবার কাঁথি থেকে প্রকাশিত ‘নীহার’ পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে জগন্নাথ দাসের ‘শ্রীমদভাগবত’ বইটি উৎকল ভাষায় বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত।
ওড়িয়া শিক্ষকেরাই ভাষা শেখাতে আসতেন দাঁতন, মহিষাদল, পটাশপুর ইত্যাদি অঞ্চলে। এদিকে কাঁথি, দাঁতন, বেলদা অঞ্চলে চলত ওড়িয়া যাত্রাপালা। গিরিশ ঘোষের ‘বিল্বমঙ্গল’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘মেবার পতন’, নিমাই সন্ন্যাস’ খুবই জনপ্রিয় ছিল। মোট কথা বাংলা আর ওড়িয়া ভাষার মানুষরা দুটি ভাষাকেই খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। মাঝে পড়ে কিছু মানুষ নিজেদেরকে খারাপ ভাবে জড়িয়ে ফেললেন।
সেই সময়ে একটা খারাপ সংবাদ শুনলেন ফকিরমোহন। জানতে পারলেন বালেশ্বরের একজন প্রভাবশালী জমিদারের কাছারি বাড়িতে বাঙ্গালী বাবুদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে কীভাবে সরকারী অফিসগুলিতে ওড়িয়া তুলে দিয়ে বাংলা ভাষার প্রচলন করা যায়।
এদিকে ফকিরমোহনের মনে হচ্ছে, কবে উৎকল ভাষায় ‘সোমপ্রকাশ’, এডুকেশান গেজেট’, ‘বিবিধার্থ
সংগ্রহে’র মতো বই প্রকাশিত হবে।
নিজের প্রেস থেকে একের পর এক বই বের করছেন তিনি। ফকিরমোহনকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না দেখে বিরোধীরা নতুন একটা ফন্দি আঁটলেন।
কেওনঝাড়ে থাকাকালীন বিদ্রোহীরা তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখলেন।
ফকিরমোহন বন্দীদশা থেকে বেরনোর উপায় খুঁজতে লাগলেন।
বাইরে পাহারাদার রাখা হল। এতেও তাঁকে ধরে রাখা গেল না। এই সময়ে ফকিরমোহনের একজন বন্ধু দেখা করতে এলে তিনি খুব গোপনে তার হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, “প্রিয় বন্ধু ভোলানাথ, অতি শীঘ্র আপনি একশত সুপারী আর একশত বাদাম পাঠান। উত্তর দিক থেকে পানি দিয়ে আখ ক্ষেতে সেচ দিন। অন্যথায় আপনি পুরো ক্ষেত হারাবেন।”
আপাত দৃষ্টিতে এটা ছিল খুবই সাদামাটা একটা চিঠি। কিন্তু বন্ধুটি হাতে পাওয়া মাত্র বুঝতে পারলেন সুপারি হল বন্দুকের কোড আর বাদাম হল বুলেট।
এরপরে বন্ধুটি খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্রসহ তাঁকে উদ্ধার করলেন।
ফকিরমোহন কেবলমাত্র একজন কবি, গদ্যকার, ঔপন্যাসিক ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যে তিনি নানা কাজ করেছিলেন। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির জন্যে তাদের বাবামায়েরদের বোঝাতেন। কেউ কেউ তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন ‘উৎকলের ব্যাস’ নামে। কেউ বলেন ‘ওড়িয়া ভাষা সাহিত্যের জনক’।
মোটকথা ফকিরমোহন ওড়িয়া ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ওড়িশা সাহিত্যে ভগীরথ। তাঁর জীবন ওড়িয়া সাহিত্যের পুনরুত্থানের গল্প বলে।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন