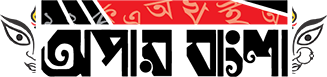দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন পলাশকান্দি
হরিশংকর জলদাস
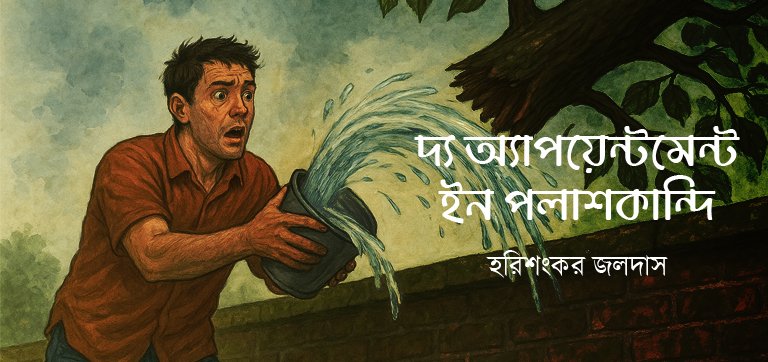
গল্পটির প্রথম অংশ ধার করা। উইলিয়াম সমারসেট মম থেকে। ১৯৩৩ সালে লেখেন তিনি। বাগদাদের জনজীবনকে কেন্দ্র করে গল্পের নাম ‘দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন সামারা’। বাগদাদের মতন সামারাও সেই সময়ের একটা শহর। গল্পের আরম্ভ বাগদাদে, শেষ হয় সামারায়। গল্পে তিনটি চরিত্র ব্যবসায়ী তার চাকর এবং মৃত্যু। হ্যাঁ, মৃত্যু একটা চরিত্র এই গল্পে। তবে আরও একটা চরিত্র আছে। একটি ঘোড়া। তাকে আপনারা চরিত্র ভাবলেই তবে সে চরিত্র, না হলে পশু।
ব্যবসায়ী এবং চাকরটির নাম দেননি গল্পকার। বলার সুবিধার জন্য আমি ওই দুজনের নাম দিচ্ছি। আব্দুল্লাহ এবং কাদের আর মৃত্যুর নাম তো মৃত্যুই। হিন্দু মিথলজিতে মৃত্যু একজন পুরুষ। মম তার গল্পে মৃত্যুকে নারী রূপে রূপায়িত করেছেন।
ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহ একদিন তার চাকর কাদেরকে কিছু সদাই কিনতে বাজারে পাঠালেন কিন্তু বাজারে যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই চাকরি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো।
ব্যবসায়ী জিজ্ঞেস করলেন, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? আর তুমি এইরকম করে কাঁপছই-বা কেন?
কাদের বলল, হুজুর, আমি বাজারে যাওয়ার পর এক বিশাল কদাকার মহিলা আমার গায়ে জোর ধাক্কা দেয়। আমি একটু কঠোর চোখে তাকিয়ে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এরকম করে ধাক্কা দিলে কেন? মহিলাটি অদ্ভুত গলায় বলল, তুমি আমাকে চিনবে না আমার নাম মৃত্যু। মৃত্যু কোন নারীর নাম হয় নাকি, হুজুর?
আব্দুল্লাহ চাকরের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলেন না। শুধু জানতে চাইলেন, মহিলাটি কি তোমাকে চোখ রাঙিয়ে ছিল? তখন তার চোখ মুখ কেমন ছিল?
সেটাইতো ভাবনার বিষয়, হুজুর। বিস্মিত চোখে মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল আমাকে। তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে ভয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।
কাদেরের কথা শুনে ব্যবসায়ীটির মনে বেশ কৌতূহল হলো। সেই মৃত্যু নাম্নী নারীটিকে দেখতে খুব ইচ্ছা জাগলো ব্যবসায়ীর মনে।
তখন ব্যবসায়ী তার চাকরের কাতর কণ্ঠ শুনতে পেলেন, আমি জানি এই শহরে থাকলে আমার নিশ্চিত মৃত্যু হবে। এখান থেকে পালাতে চাই আমি। আমাকে আপনার ঘোড়াটা ধার দিন, হুজুর। আমি সামারা শহরে চলে যাব। সেখানে মৃত্যু আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
বলাই বাহুল্য, গল্পের থিমটা সমারসেট মমের। বর্ণনা – সংলাপ এসব এই অধম লেখকের। যাক সে কথা। গল্পকথায় আসি।
ব্যবসায়ী আব্দুল্লাহ বড় দয়াবান মানুষ। এতদিন ধরে কাদের তার বাড়িতে চাকরি করেছে। সে বিশ্বাসই করে ফেলেছে যে বাজারে মৃত্যুর সঙ্গেই দেখা হয়েছে তার। এই শহরে মৃত্যু তার জান কবচ করবে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই শহর থেকে পালাতে চাইছে সে। যদি পালিয়ে বাঁচতে পারে মন্দ কী! একটি মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ঘোড়াটি দিয়ে দিলে এমন কি ক্ষতি! কাদেরকে ঘোড়াটি দিয়ে দিলেন তিনি। কাদের ঘোড়ায় চড়ে সামারার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।
ব্যবসায়ীটি কৌতূহলে বাজারে গেলেন যদি ওই নারীটির দেখা পান। বাজারের ভিড়ের মধ্যে তিনি তার চাকর বর্ণিত নারীটিকে দেখতে পেলেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার চাকরটিকে ধমকেছো কেন? মৃত্যুরূপী নারীটি শান্ত কন্ঠে উত্তর দিল, আমি আপনার চাকরকে ধমকও দিইনি, চোখও রাঙাইনি।
তাহলে কী করেছ, কী বলেছ তাকে?
নারী বলল, তাকে বাগদাদে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেছিলাম আমি।
কেন! সে তো বাগদাদেরই বাসিন্দা। এই শহরেই তো থাকে সে। ব্যবসায়ীর অবাক হবার পালা।
মৃত্যু নামের নারীটি বলল, আজ রাতে তার সঙ্গে আমার সামারায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাকে বাগদাদের বাজারে দেখে ভাবলাম এখানে সে কী করছে, তার তো আজ সামারায় থাকার কথা।
মম এখানেই গল্পটি শেষ করেছেন। বিচক্ষণ পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, সামারাতেই কাদেরের মৃত্যু হবে এবং এটাই তার ললাট লিখন। নিয়তিই তাকে বাগদাদ থেকে সামারায় নিয়ে গেছে।
এবার গল্পের দ্বিতীয় অংশ। এই অংশটি বানানো বা ধার করা নয়। একেবারে সত্যি কাহিনি, আমারই এক আত্মীয় পরিবারের বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্ত শোনবার আগে আপনাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি কে? ধার করা গল্পই বা বলতে গেলাম কেন? আবার সত্যি ঘটনা বলে মমের গল্পের ঘটনার সঙ্গে আজগুবি কোন কাহিনি জুড়ে দিতে যাচ্ছি না তো? আপনাদের সন্দেহ আর কৌতূহল দূর করা দরকার এই জন্য আমার পরিচয়টা সংক্ষেপে লিখছি।
আমার নাম অনিরুদ্ধ লাহিড়ী। একটা হাইস্কুলে পড়াই। সিনিয়র শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স – এম.এ করেছি। স্কুলটা মীরপুরের দিকে। আপনারা অনেকে চিনবেন বলে স্কুলের নামটা উহ্য রাখলাম। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে ওই হাই স্কুলে বাংলা টিচার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলাম। ওই সময় নিয়োগের ক্ষেত্রে অত ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। ছিল না বলেই সংস্কৃতে এম.এ হয়ে বাংলার টিচার হিসাবে নিযুক্তি পেয়েছিলাম।
সততা – নিষ্ঠা এসবের কারণে খুব নাম হয়ে গেছিল আমার ওই স্কুলে। একদিন আমি ওই স্কুলের হেডমাস্টার হলাম। কিন্তু হেডমাস্টার হিসাবে বেশি দিন টিকে থাকতে পারলাম না। ষড়যন্ত্রের শিকার হলাম আমি। অবনমিত হয়ে আগের পোস্টে ফিরে এলাম। কাজী রহমত উল্লাহ খান হেডমাস্টার হলেন। নিজের সম্পর্কে বড্ড বেশি বলা শুরু করেছি। আর একটু সময় দিন আমায়। আর দুই একটি কথা বলে গল্পে ফিরে যাব।
তুরাগ নদীর পারেই আমার বাসাবাড়িটি। দুই কন্যা আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। স্ত্রী আমার গৃহিণী। চাকরি-বাকরি করেন না। আমি যে খুব হিসেবী মানুষ এমন নয়। যেখানে পাঁচশো টাকা খরচ করলে হয়। সেখানে পাঁচ হাজার খরচ করি। আর যেখানে তিনশো টাকাই লাগবে, সেখানে দুইশো টাকা পকেট থেকে বের করতে গড়িমসি করি। আমার জীবন ও জগৎ নিয়ে আমি বেশ আনন্দেই আছি। ও আরেকটি কথা, সংস্কৃত পড়েছি বলে আমি কিন্তু রক্ষণশীল নই। সমাজের কূপ-মন্ডুক রীতিনীতি আমি মোটেই পছন্দ করি না। জীবনের ঘটনা সমূহকে আমি যুক্তি দিয়ে বিচার করি। এর মধ্যে গোটা তিনেক অভিধান রচনা করেছি। সবগুলি পুরাণ বিষয়ক। আরেকটি কথা বলে আমার কথা শেষ করছি — আমি কোনভাবেই অলৌকিকতাকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু উত্তমের ঘটনায় আমার সেই আস্থা টলে গেল একদিন। আধি-ভৌতিক ব্যাপারটিকে কেন জানি অবহেলা দেখাতে ইচ্ছে করলো না সেদিন।
ঘটনাটা খুলে বললে বুঝতে পারবেন আপনারা। আমার বাড়ি মাদারিপুর জেলার গণেশপুর গ্রামে। ছয় ভাই তিন বোন আমরা। আমি সবার বড়। বাবা মারা যাবার আগে তিন পুত্রকে বিয়ে করিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বোনেদের বিয়ে আগেই হয়ে গেছিল। অন্য তিন ভাইয়ের বিয়ে আমাকেই করাতে হয়েছিল। খুব বেশি ‘আমি’ ‘আমি’ হয়ে যাচ্ছে এই গল্প। কিন্তু উপায় কি বলুন! যাকে নিয়ে এই ঘটনা সেই উত্তম পর্যন্ত পৌঁছাতে গেলে থোড়বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ের কথা যে একটু শুনতেই হবে আপনাদের।
তো আমার পঞ্চম ভাই সুধীরকে বিয়ে করিয়েছিলাম আমাদের গ্রাম থেকে দুই গ্রাম দক্ষিণের গ্রাম পলাশকান্দিতে। সুধীরের শ্বশুর ছাপোষা মানুষ। আবার একেবারে ছাপোষা মানুষ বললে ভুল হবে গোপাল বাবুকে। ছাপোষা ভাবের সঙ্গে ধুরন্ধরতারও মিশেল আছে তাঁর স্বভাবে। ভেজা বিড়ালের মতন থাকেন। সুযোগ পেলে কাউকে পথে বসিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। যাক, এই বৃত্তান্ত তাকে ঘিরে নয়। তাঁর বড় ছেলে উত্তম দাশকে নিয়ে। আমার ভাই দেখতে শুনতে তত ভালো নয়। লেখাপড়াও করেনি তেমন। পাল্টি ঘরে কনে না পেয়ে তাই ওই দাশবাবুর বাড়ি থেকেই মেয়ে আনতে হয়েছিল আমাদের।
গোপাল দাসের দুই ছেলে তিন মেয়ে। দুই মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছেন। বিবাহযোগ্যা হয়েও তৃতীয় মেয়েটি ঘরে পড়ে আছে। আগের দুই মেয়ের বিয়েতে যা কান্ড করেছেন তা পাড়া-পড়শী আর আশেপাশের গা গেরামের মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকেনি। বিয়েতে বরপক্ষকে যা দেবার কথা ছিল, দেননি। বিয়েতে যা যা আইটেম দিয়ে খাওয়ানোর কথা ছিল, খাওয়াননি। এই নিয়ে তার বদনাম ছড়িয়েছে এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে। গোপাল বাবুর যে খুব জমিজমা আছে তেমন নয়। বাস্তু ভিটেটাই সম্বল। বাজারে একটা মুদির দোকান আছে। ওই দিয়ে সংসার চলে কোনরকমে। ছেলে দুটোকে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বড় ছেলে উত্তম এসএসসির বেড়া ডিঙিয়ে থেমে গিয়েছিল। ছোট ছেলে প্রশান্ত এইটে গিয়ে যে হোঁচট খেলো আর এগোতে পারল না। তবে প্রশান্তর মধ্যে এক অদ্ভুত গুণের দেখা মিলল। সে তবলা – মৃদঙ্গ – বাঁশি – ঢোল এইসব বাজাতে শিখলো আর গাইতে শিখলো বেশ। রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদ গান, দলীয় কীর্তন তার গলায় খুব শ্রুতিমধুর শোনালো। কালক্রমে উত্তমরা বড় হলো। উত্তম মাদারীপুর শহরের একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি নিল। পিওনের চাকরি। নামে পিওনের চাকরি। কাজ জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। অফিসের যত কাজ সবই উত্তমকে করতে হয়। তাতে উত্তমের কোন কষ্ট হয় না। বেতন যাই দিক মাসের শেষে তা উত্তমের হাতে তুলে দেয় ফার্মটি। বেতনের টাকাটা বাপের হাতে দেয় উত্তম। প্রশান্ত কীর্তনীয়া দলে গিয়ে ভেড়ে, প্রহর অনুসারে টাকা। অষ্টপ্রহরের কীর্তন হলে একরকম টাকা। চতুর্দশ প্রহর, অষ্টাদশ প্রহর হলে বেশি টাকা। এক সফরে অনেকগুলো আসরে কীর্তন গান পরিবেশন করে দলটি। সফর শেষে দলের সদস্যদের মধ্যে টাকা ভাগ হয়। ভাগে প্রশান্ত যা পায় তার কিয়দংশ বাবার হাতে দেয়। অধিকাংশ নিজে রেখে দেয়। মুদি দোকানের সামান্য লাভ, উত্তমের বেতন এবং প্রশান্তর আয়ের কিয়দংশ দিয়ে গোপাল বাবুর খুঁড়িয়ে চলা সংসারটা ঠিক ঠিক পদক্ষেপে চলতে শুরু করল। গোপাল বাবু ঘরের চালের জীর্ণ টিন বদলালেন, কাত হয়ে পড়া টয়লেট মেরামত করলেন এবং ভিটের চারিদিকে বুক সমান সীমানা দেয়াল তুললেন।
এক রাতে গোপালবাবু মনে মনে আচমকা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, উত্তমকে বিয়ে করাবেন। পাশে শোয়া ঘুমন্ত স্ত্রীকে জাগিয়ে কথাটি বললেন। ছেলের বিয়েতে কোন্ মা না রাজি হন! সুবালাও রাজি হয়ে গেলেন। পরদিন কথাটা ছেলে-মেয়ের কাছে গোপন রাখলেন না গোপাল-দম্পতি। চাকরিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল উত্তম। মায়ের মুখে কথাটা শুনে মুচকি একটু হাসলো। তরুণ বয়সে বিয়ের কথা শুনে কে না পুলকিত হয়! সবচেয়ে বেশি খুশি হল প্রশান্ত। যাক দাদার পরে তারই তো পালা। অখুশি হল অরক্ষণীয়া ছোট বোনটি। ভেবেছিল তাকে বিয়ে দিয়েই বাবা দাদার বিয়ের কথা ভাববে। সেদিন থেকেই কনে খোঁজা শুরু করলেন গোপাল বাবু। এ গ্রাম, ও গ্রাম, সেই গ্রাম। মনের মতন কনে জোটে না। মেয়ে পছন্দের হলে কনেপক্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা পছন্দের হয় না। আবার কনেপক্ষের ঘরদোর অবস্থা পছন্দের হলে কনের চেহারাখানা পছন্দের হয় না। শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েকে পছন্দ হয় গোপাল দাশের। মেয়ের বাবাকে ওজন করে নিলেন। পণের দাবি মেটাতে পারবেন বলে মনে হলো তাঁর।
শেফালিকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন গোপাল বাবু। শেফালি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে হলে কি হবে গোপাল বাবুর মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশ খাপ খাইয়ে নেয়। শেফালি সবচেয়ে বেশি খুশি হয় উত্তমকে পেয়ে। উত্তম দেখতে খুবই সুন্দর তা নয়, কিন্তু চেহারাখানা ফেলনা নয়। গায়ের রং তেলকাজলা। চোখ দুটো গভীর। মাঝারি উচ্চতা। উত্তমের যেটি শেফালির বেশি পছন্দের তা হলো তার শরীরের গঠন-গড়ন। পেটা শরীর। পুষ্ট ঠোঁট। ঠোঁটের উপর চিকন গোঁফ। ওই গোঁফটা উত্তমকে লোভনীয় করে তুলেছে। আগে ছুটি হলে উত্তম ধীরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিত। বাড়ি থেকেই অফিসে নিত্যদিন আসা যাওয়া করে উত্তম। আগে বাস ধরতে না পারলে পরের বাসের জন্য অলস ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতো। এখন বাস ফেল করলে মনটা বড় আনচান করে উত্তমের। এক ঘন্টা বেশি শেফালি সাহচর্য উত্তমের কাছে যে ভীষণ কাঙ্খিত! দিন যায় রাত পোহায়, দিন কাটে বিরহে, রাত কাটে সংসর্গে শিহরণে। উত্তম শেফালির দেহের খাঁজে ভাঁজে আনন্দ খোঁজে। শেফালি চক্ষু মুদে সেই আনন্দের স্বাদ নেয়। কালক্রমে শেখালির গর্ভে সন্তান আসে। নাম দেয় নদী। মেয়েটির নাম নদী রাখার পেছনেও একটা কারণ আছে। গোপাল বাবুর বাড়িটি খাল পারে। গ্রামেগঞ্জে এমন কিছু স্রোতস্বিনী আছে। যাদের খাল বললে অপমান করা হয়। নদী বললে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। গোপাল বাবুর বাড়ির পাশের খালটি সেরকম। প্রস্থে নদীর বিরাটত্ব। পাশের খালটির প্রশস্ততা অবহেলা করার মতন না। ভালো সাঁতারুর সাঁতরে পার হতে দম ফুরিয়ে যাবে। পলাশকান্দির মানুষেরা খালটিকে নদীর মান দেয়। এটির আলাদা কোনো নাম নেই। সবাই একে নদী নামেই ডাকে। জন্মের পর থেকে বাড়ির পাশে নদীটিকে দেখে আসছে উত্তম। এই নদীটিতে লাফিয়েছে ঝাঁপিয়েছে। নিজের অজান্তে এই নদীকে ভালোবেসে ফেলেছে। তাই যখন প্রিয়তম কন্যাটির নাম রাখার সময় এলো, নদী রাখল। কন্যা জন্মানোর পর ঘরের প্রতি টান বাড়লো উত্তমের। আগে শেফালির জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতো, এখন নদীর জন্য ছুটে আসে।
একদিন ঢাকায় চাকরি পেয়ে গেল উত্তম। বেতন বর্তমান চাকরির দেড়া। চাকরিটাও ছোটাছুটির নয়। গুলিস্তানের এক ব্যবসায়ী অফিসে ফাইলপত্র এই টেবিল থেকে ও টেবিলে পৌঁছে দেওয়া। শুধু কষ্ট যা, দূরে যেতে হবে। আগে প্রতিদিন বউ – বাচ্চা, মা – বাপের মুখ দেখতে পেত, এখন পাবে না। গুলিস্তান যে অনেক দূর। তারপরও চাকরিটা নিল উত্তম। কন্যা হয়েছে পরিবারের খরচ বেড়েছে। এর মধ্যে মুদি দোকানটাতেও লালবাতি জ্বলেছে। মাত্রাতিরিক্ত বাকি দিয়ে ফেলেছেন গোপালবাবু, পরিচিত কাস্টমারদের বাকি দেওয়া টাকা তুলতে না পারায় দোকানের ঝাঁপটা চিরতরে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। গোপালের স্ত্রী সুবালা উত্তমের বেতনে সংসারটা চালিয়ে নিচ্ছেন। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়িতে আসতে পারে না উত্তম। অফিস থেকে সেরকম ছুটি মেলে না। তাছাড়া তার কাছে অত টাকা কোথায় যে ঘন ঘন ঢাকা থেকে মাদারিপুর আসে। মনের কষ্টে চূর্ণ হতে থাকে উত্তম। রাজারবাগের এক মেসে থাকে। ছুটির দিন ছাড়া সপ্তাহের অন্য দিনগুলো কর্মব্যস্ততায় কাটে, ঘরবাড়ির কথা তেমন মনে পড়ে না। কষ্ট বাড়ে ছুটির দিনে অলস মুহূর্তগুলোতে বারবার নদী আর শেফালির কথা মনে পড়ে। মাসে একবার যায় বাড়িতে। প্রথম সপ্তাহে বেতন নিয়ে ছুটির দুটো রাত চোখের পলকে কেটে যায়। বন্ধের দিন ভোর সকালে মন ভালো থাকলে হাঁটতে বের হয়ে উত্তম। রমনা পার্কে যায়। সেখানে হাঁটতে দৌড়াতে সুবিধা। রুমমেট আনিসকে সঙ্গে নিতে চায়। আনিস সহজে রাজি হয় না। তার শরীর একটু মোটা ধরনের। সে খেতে আর শুয়ে থাকতে পছন্দ করে। উত্তম টেনেটুনে তাকে ঘরের বার করে। পার্কে উত্তম দৌড়ায়, আনিস হাটে মৃদু পায়ে। তাতেই দম ফুরিয়ে আসে আনিসের। কোন একটা বেঞ্চি দেখে বসে পড়ে। মর্নিংওয়াক শেষ করে উত্তম পাশে এসে বসে। আনিস জিজ্ঞেস করে, ছুটির দিনে বাড়িতে যাও না কেন, ভাই? তুমি বাড়িতে গেলে আমি একটু শান্তি পাই, সকালটা আরামে ঘুমাতে পারি, মৃদু হাসে উত্তম। তোমার ওজন কমাতে হবে আনিস, হাঁটা ওজন কমানোর মহৌষধ। তারপরে হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যায় উত্তম। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। যেতে বড় মন চায় রে, আনিস। নদী শেফাল… অর্ধেক পথে থেমে যায় আনিস। বলে, চলো মন খারাপ করতে নেই। আগামী মাসে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের সঙ্গে একদিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি যেও। নদীকে দেখে এসো। দাঁড়াতে যাবে ওমনি পাশের গাছের একটা মরা ডাল উত্তমের মাথা ঘেঁষে মাটিতে পড়ল।
আনিস ধাক্কা মেরে সরিয়ে না দিলে উত্তমের মাথাতেই পড়তো ডালটি। গতরাতে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আষাঢ় মাস শুরু হয়ে গেছে। গ্রীষ্মে শুকিয়ে যাওয়া শাখাগুলো জলে ভিজে ফসফসে হয়ে গেছে।
বড় বাঁচা বেঁচে গেলে রে, ভাই। ডালটা মাথায় পড়লে কি হতো কে জানে! ত্রস্ত গলায় বলল আনিস।
ভয়ে উত্তমের গলা শুকিয়ে গেছে। কোনরকমে বলল, চল, ঘরে যাই আনিস।
মাসখানেক পরের ঘটনা। উত্তম বাড়িতে এসেছে। শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি কখনো অবিরাম, কখনো থেমে থেমে। আকাশে ঘনঘোর। মেঘ বৃষ্টির সঙ্গী হাওয়াও। পাশের নদী ভরপুর। গত দুদিন বৃষ্টি হচ্ছে না তেমন। উত্তমদের বাড়ির তিন দিকে নানা গাছ বড় ছোট। পূব দিকে উঠান। বাড়ির পিছনে আম কাঁঠাল আর শিরিষ গাছ। আম গাছ বহুদিন ফল দিয়ে দিয়ে বুড়ো হয়ে গেছে। গেল বৃষ্টিতে হঠাৎ মরে গেল গাছটি। মৃত আম গাছটি এখন শুকিয়ে কাঠ। কয়েকটি ডালপালা নিয়ে বাড়ির পশ্চিমের বাউন্ডারি দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে। সেই সন্ধেটি সেই রাতটি বেশ আনন্দে কাটলো উত্তমের। নদী তার সন্ধেটি মনোরম করল। শেফালি রাত্রি উচ্ছল করল। মা বাবা বোনকে নিয়ে জীবনটা বড় সুখকর বলে মনে হলো উত্তমের। পরদিন সকালে নাস্তা খেল বাবার সঙ্গে। সংসারের টুকটাক দু একটি কথাও হল। নদী উত্তমের কোলে বসে ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে হাসলো। সুবালা এসে স্বামী পুত্রকে এক পলক দেখে গেল। উত্তম বলল, প্রশান্তের জন্যই মাংসটা আনলাম। এখন সে বাড়িতে নেই। ঢাকা থেকে আসবার সময় দু’ কেজি খাসির মাংস এনেছে উত্তম। গোপালবাবু বললেন, এতদিন বাড়িতে ছিল গত পরশুই বরিশাল গেল। ষোল প্রহর কীর্তন গাইবে সে। উত্তম বলে, নদীকে একটু কোলে নাও, বাবা। আমি একটু বাড়ির পেছন দিকটায় যাচ্ছি।
এত সকালে ওদিকে যাওয়ার দরকার কী!
রোদ দিয়েছে, বাবা। ঢাকার চাকরি করাতে বাড়িটার দিকে নজর দিতে পারি না! যাই একটু ওদিকে বাড়িটার পিছনটা দেখা হবে, নদীটাও দেখা হবে। গোপালবাবু আর কিছু বললেন না। উত্তম উঠে যায়। গিয়ে নদীপাড়ে দাঁড়ায়। চোখ মেলে নদীর দিকে দেখে। জল দেখে। তার শৈশবকেও দেখে। একসময় পিছন ফিরে তাকায়। বাউন্ডারি দেয়ালে চোখ আটকে যায়। একি! বাউন্ডারি দেয়ালে এত শ্যাওলা দেওয়ালের আস্তরটাই তো বুঝে গেছে। একটু কি যেন ভাবল উত্তম। নাহ্, দেয়ালটাকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। অনেকটা দিন ঘরের কোন কাজ করছে না সে। শুধু বাড়ি আর ঢাকা, ঢাকা আর বাড়ি। প্রশান্তটাও এমন, বাড়িতে থাকে যখন একটু আধটু বাড়ির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিলে কী হয়! বাপটা বুড়ো হয়ে গেছে, প্রশান্ত তো যুবক। ভাবতে ভাবতে একবার নদীর দিকে তাকালে উত্তম। পাড়ছোঁয়া জল নদীর। বালতি বালতি পানি এনে দেয়ালটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে অসুবিধা হবে না। ঘরে গিয়ে শেফালিকে বলল, আমাকে বালতি আর একটা জগ দাও তো, শেফালি।
শেফালি অবাক চোখে বলে, বালতি জগ দিয়ে কি করবে?
বাড়ির পেছনের বাউন্ডারি দেয়ালটা পরিষ্কার করবো।
তোমাকে দেয়াল পরিষ্কার করতে হবে না। এসেছো কাল। দু চারটি কথা বলব তারও ফুরসত মিলছে না তোমার। আহ! শেফালী আছি তো আমি আজ তো আর চলে যাচ্ছি না। দাও তো বালতিটা!
অসুখী মুখে জগ বালতি এগিয়ে দেয় শেফালি। বলে, বৃষ্টি পড়ে পড়ে চারদিক স্যাঁতসেঁতে। সাবধানে করো।
আচ্ছা, বলে, জগ বালতি নিয়ে পেছন ফেরে উত্তম।
তারপর নদী থেকে বালতি বালতি জল এনে দেয়ালের শ্যাওলাগুলো ভিজিয়ে দেয় উত্তম। ঝামা দিয়ে দেয়ালটা ঘষতে শুরু করে। একটুক্ষণ পরেই মড়মড় মড়াৎ করে মরা আম গাছটির বড় একটা ডাল আছড়ে পড়ল। প্রথমে ঘরের চালে পড়ল ডালটি। ভেঙে টুকরো হল। টুকরোর একটা অংশের এক প্রান্ত তীরের ফলার আকার ধারণ করল। চাল থেকে ফলাওয়ালা শাখাটি উত্তমের মাথায় এসে গেঁথে গেল। মাটিতে গড়িয়ে পড়ল উত্তম। ঘিলুতে রক্ততে জায়গাটি তখন ভেসে যাচ্ছে। নদী বা শেফালি, মা বা বাবা অথবা ঈশ্বরকে ডাকার সময় পেল না উত্তম।
যে ডালটি রমনা-পার্কে উত্তমের প্রাণ হরণ করতে চেয়েছিল, ঢাকা থেকে বহু দূরের এই পলাশকান্দিতে এসে সেই শাখাটি কি উত্তমের প্রাণ হরণ করল? আমের মরা ডালটি কি বাগদাদের সেই নারীরূপী মৃত্যু? পলাশকান্দি কি সামারা শহর?