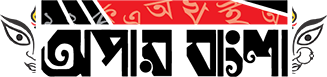ফিচার
নবকুমার বসু

প্রবাসী জীবন ও যাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে যেমন কিছু সীমাবদ্ধতা ও টানাপোড়েন আছে, তেমনই কিছু সীমাহীনতা ও ভাবনার স্বাধীনতাও আছে। আর সেই বিষয়টাই নির্ভর করে, প্রবাসী জীবনযাপনে মানুষ কতটা গুরুত্ব দিয়ে এই বিশেষ ও ব্যতিক্রমী যাপনকে নিয়ে ভাবতে চায়। তার ওপর এমনিতেই যত দিন যাচ্ছে, একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে যে, ভাবনা নিয়ে মানুষ আর এত ভাবিত না। তার ভাবনার ইচ্ছে বা দায় ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, একথা বললে খুব অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু সেই বিষয়টা খুব বেশি বিস্তারিত করব না, কেন না তাহলে প্রবাসী বিষয়টা পাশে সরে যাবে।
আগে প্রবাসী ব্যাপারটা নিয়ে দু চার কথা বলি। তারপর সেই নিরিখে ভাষা-ধর্ম-রাজনীতি-বাঙালিজাতি… ইত্যাদি প্রসঙ্গে আসব।
একেবারে আদিযুগে মানুষ যখন তার জন্মস্থানের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতো না, তার কাছে স্বাভাবিকভাবেই প্রবাসজীবন বলে কিছুই ছিল না। তখন সবাই একই গোষ্ঠীভুক্ত, একই লোকালয়বাসী। তারা একই ভাষায় কথা বলত, একই রকমের রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে ছিল। তারা বিজাতীয় কী, তা জানতো না, বুঝতো না। সুতরাং আলাদা কোনও জাতীয়তাবোধ তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল না। প্রবাস ও প্রবাসী বলেও কিছু ছিল না।
কিন্তু একটা সময়ে নানান কারণে মানুষের এই একক গোষ্ঠীতন্ত্র ভাঙতে শুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাসের দরুণ, মতানৈক্য কিংবা নেহাত দুঃসাহসিক অভিমানের অভিঘাতেই হোক, মানুষ তার নিজের চেনাজানা গণ্ডী এলাকা বা দেশের সীমানা অতিক্রম করেছে এবং অন্য দেশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আর ভিন্ন রীতিনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, অভ্যস্ত হয়েছে। অজানা অচেনা মানুষরা একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে। এবং যত সহজে কথাটা লিখে ফেললাম তত সহজে, নির্বিবাদে তা হয়নি। মারামারি কাটাকাটি হয়েছে। তারপর রেষারেষি কমে মিলমিশ হয়েছে। ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে এবং অন্য ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। বলা যায় দুই ভাষা মিশে কোথাও একটা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। বলা যেতে পারে ভাষার স্বভাব খুব মিশুকে। উদাহরণস্বরূপ উর্দু ভাষাটির সৃষ্টি হয়েছে হিন্দি আর ফরাসির মিশ্রণে। বাংলার মধ্যে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি ভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর তাইতো ভাষা আরও বেশি ক্ষমতাশালী হয়েছে।
সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাপারেও স্বদেশী-প্রবাসীরা বোঝাপড়া করে নিয়েছিল অনেকখানি। পুরনোরা কিছুটা নতুনকে গ্রহণ করেছে। আর নতুনরা তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। দেখা গেছে মিলনে মিশ্রণে সবসময়ই শক্তি বৃদ্ধি হয়। তবে মনে রাখতে হবে এইসব কথাই কিন্তু বহু অতীতের। এখনকার প্রবাসী জীবন সম্পর্কে নয়। তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বা উৎস সম্পর্কে।
এখানেই ধর্মের কথা একটুখানি বলে রাখা দরকার।
ধর্ম কিন্তু ভাষার মতো উদারতা দেখাতে পারে না। এমনকি ওই ঐতিহ্য-অনুগত সনাতন সমাজ আর তার ব্যবস্থায় ইত্যাদি, সেও ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, অনেক নতুন আচার-আচরণ, নতুন মানুষদের অভ্যাসকে মেনে নেয়। অথচ ধর্মই একমাত্র ধর্মকথায় কান দেয় না, অর্থাৎ এক ধর্ম কিছুতেই অন্য ধর্মের কথা শুনতে এবং মানতে চায় না। সে নিজের কথা অন্যদের শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। কিন্তু অন্যের কথা নিজে কিছুতেই শুনবে না। অতএব বলা যায় ধর্মই সর্বাপেক্ষা ধর্মান্ধ।
তো এইরকম একটা সোশিও-রিলিজিয়ান-লিঙ্গুয়িস্টিক কালচারাল ব্যাপারের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে প্রবাসী— তাদের মন, জীবন। একটা সচেতন প্রশ্ন উঠতে পারে যাদের আমরা প্রবাসী বলছি তাদের মধ্যে জাতীয় সংহতি ব্যাপারটার অস্তিত্ব কি থাকে! আসলে জাতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বদেশী প্রবাসী সকলেই প্রায় একই রকম মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। যে কোন জাতিই যখন পরাধীন থাকে তখন তারা স্বদেশ অন্ত প্রাণ হয়ে থাকে। ভারতের কথাই যদি ধরি, স্বাধীনতার আগে তারা সকলেই ভারতমাতা সন্তান এই আবেগে ডুবেছিল। আর যেই দেশ স্বাধীন হয়ে গেল তারা বলতে শুরু করলে আমাদের দাবি মানতে হবে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, মানুষ পরাধীনতাকে যতখানি গুরুত্ব দিয়েছে স্বাধীনতাকে ততখানি দেয়নি। তারপর এই মনুষ্যসমাজই ভাগ হয়েছে নানান শ্রেণিতে। তার মধ্যে প্রবাসী হয়ে গেছে একটা শ্রেণি। যে দেশে তারা গেছে সেখানেই নাগরিকত্ব পেয়ে গেলেও, মানসিকতা দিক থেকে, স্বাধীনতার দাম নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। বরং হালকা ভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু তার জন্য কোনোদিক থেকেই স্বদেশী প্রবাসীর মধ্যে কোন বিভাজন আছে এমন নয়। সুবিধা অসুবিধা সব দিক দিয়েই তারা একই রকম রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং নিয়ম শৃঙ্খলার আওতায় পড়ে। জাতীয় সংহতির বিষয়ে কেউই আলাদাভাবে মাথায় রাখে না।
কিন্তু ভাবনার ক্ষেত্রে? এই বিষয়টারই গতিপ্রকৃতির এত বিভিন্ন শাখায় পল্লবিত যে তার হিসেব করা এবং হিসেব রাখার কোনো উপায় নেই। আমরা শুধু গড়পড়তা প্রবাসী… এবং তার মধ্যেও ভারতীয় বঙ্গ সন্তান প্রবাসী যারা, তাদের মন, ভাবনা, ভাবনার বিষয়, ভাষা, দেখা ও অভিজ্ঞতা … ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলব। একটা কথা এখানেই বলে রাখি, বর্তমান লেখক স্বয়ং কয়েক দশকে প্রবাসী বলে দূর থেকে দেশকে দেখার যে প্রতিক্রিয়া, সীমাহীনতা, ভাবনা স্তরে যে স্বাধীনতা ও টানাপোড়েন সেই সব কথাই এই রচনার উপজীব্য হয়ে উঠবে।
প্রথমে খোলা মনে একটা কথা বলি, কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে, কোথাও একটা বাঙালি চরিত্রে ভাঙ্গন ধরেছে, এই ভাঙ্গনের ফলে, পশ্চিমবঙ্গের গায়ে যেখানে সেখানে নানান ফাটল ধরেছে, একটু আগে ‘সংহতি’ শব্দের উল্লেখ করেছি যদিও তা অন্য উদ্দেশ্যে এখন আর একবার তা স্মরণ করছি। পশ্চিমবঙ্গ দেশের একটা রাজ্য হলেও ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন তা আমরা সবাই জানি। একথাও জানি পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধর্মাবলম্বী সবাই মিলেমিশে থাকার দরকার। এবং তার জন্য সংহতিবোধ, আত্মীয়তাবোধের প্রয়োজন খুব বেশি এবং একদিন তা ছিলও। কিন্তু সাম্প্রতিককালের তা লোপ পেতে চলেছে। লোপ পাওয়ার কারণ যে রাজনৈতিক এবং অতঃপর ক্ষমতাদখল, প্রতিদিন আমরা তা দূর থেকে পাখির চোখে ঠিক দেখতে পাচ্ছি। কয়েক বছর আগেও আমরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, বন্ধুভাবাপন্ন ছিলাম ছোটখাটো গন্ডগোল মতবিরোধ হলেও তা মাথা চাড়া দিত না। কিছুদিন ধরেই দেখছি কোথায় যেন স্বার্থের সংঘাতকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। একই রাজ্যের মধ্যে আমরা আর একজনের সমব্যথী সম দুঃখী বলে মনে করছি না। প্রচ্ছন্নভাবে আমরা ওরা বিভাজন ভাবনা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনো কোনো উৎস থেকে যার যার নিজস্ব স্বার্থের বিষয়টাকে খুঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে খুব চতুর উপায়ে সজাগ ও সচেতন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একটা হট্টগোল বাঁধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সফল হতে চলেছে। যার মূল বিষয় হচ্ছে ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাষাও। নেতা বা নেত্রী, বাংলায় বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎ হিন্দি বলতে শুরু করে দেন (গুণমানের কথা ছেড়ে দিন)। এটা কি শুধু আবেগে? আদৌ তা নয়। আসলে খুব সুচতুর ভাবনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে, রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রেণিকে তুষ্ট করার জন্য ওই ভাষাবদল।
আমাদের প্রবাসী কান দূরদেশ থেকে এসব শোনে। শুনে নিজের ফিরে আসা দেশটা সম্পর্কে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। বলা যায় না, হঠাৎ এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, নিজের দেশটাকে ফেলে এলেন কেন? এলেনই যদি, তাহলে আবার এই উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনার মায়াকান্নাই বা কেন! প্রথমটার জবাব দেওয়ার জায়গা এটা নয়। সে আলোচনার কারণ বিশ্লেষণও অন্য বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয়টির উত্তর খুব কঠিন নয়। কেবল তা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রবাসী হলেই সে স্বদেশ বিষয়ে উদাসীন, তা হয় না। বাস্তব দূরত্ব থাকলেও, অনুভবে, যোগাযোগে, যাতায়াতে, কাজেকর্মে দূরত্ব থাকে না, তা সবাই জানে এবং বোঝে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনেও যে প্রবাসীদের ভূমিকা আছে, তা অন্যদের সঙ্গে রাজনীতির লোকেরাও করেন।
সুতরাং দূর দেশে বাস করলেই, বসবাসকারীরা ব্রাত্য হয়ে গেলেন তা নয়। দেশের আস্থা তাঁদের প্রভাবিত করে। দেশের মধ্যে বিভাজন, স্বার্থের সংঘাত বাঁধিয়ে দিলে, প্রবাসীরাও নানান ভাবে উদ্বেগাক্রান্ত হন, হবেন সেটাই স্বাভাবিক।
আসলে মন ছোট হয়ে গেলে, দেশ ছোট হয়ে যায়। প্রবাসী থাকলেও তাঁরা টের পান, নিজের দেশটা কত বড়। বোধ হয় দেশবাসীর থেকে একটু বেশি পান, কেননা কিছুটা দূর থেকেই যে কোন বস্তুকে, তা স্বদেশ হলেও, তাকে কিছুটা বেশি দেখা ও চেনা যায়। দূরের গৃহ কোণে বসেও, বিশাল ভারতের চিত্র চোখে সামনে দেখা সম্ভব। রামায়ণ, মহাভারতের কবি কিংবা কালিদাসের কাজেও প্রচুর ভারতের বর্ণনা ও বন্দনা আছে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বা শান্তিনিকেতনে বসেই বিশাল ভারতবর্ষকে সমদৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে যানবাহনের অপ্রতুলতা এবং যাতায়াতে সীমাবদ্ধতার জন্য ওই সব দেশও তো প্রবাস-ই ছিল। কিন্তু মনের প্রসারতা থাকার দরুণ দেশের চিন্তাবিদ, কবি, মনীষী এবং রাজনৈতিক নেতারাও ‘আমরা ওরা’ ভাগ করে দেশকে দেখেননি। অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস, এখন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বাঙালিরা মারামারি, কাটাকাটি করছে। আর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় ক্ষমতায় থাকা ছোট মনের মানুষগুলো সাধারণ মানুষদের তাইতে মদত দিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে থেকেই রাজ্যের প্রশাসন ক্ষমতাকে ব্যবহার করেই রাজ্যকে ভাঙার ব্যবস্থা করার আয়োজন দেখা যাচ্ছে। তাহলে প্রতিটি ব্যাপারে কেন্দ্রকে দায়ী করে লাভ কী!
দেশের ভিতরে থেকেই তা বঙ্গদেশ যেন একটা প্রবাস হয়ে উঠছে সাম্প্রতিককালে। ভারতের মধ্যে থেকেও ভারতীয় বঙ্গসন্তানেরা যেন প্রবাসী। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা… সবাই যদি ভিন্ন রাজ্যে থেকেও ভারতবাসী বলেই পরিচিত হন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারীরা কেন শুধু বাঙালি পরিচয় নিয়ে থাকবে! আগে বলুন আমরা ভারতীয়।
খুব আশ্চর্যভাবেই দেখা যায়, একটা খুব বড় দেশের মধ্যে অনেকগুলো রাজ্য থাকার যে সুবিধা ভৌগোলিক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা না, যে প্রশাসনিক সুবিধা কিংবা সম্পত্তি বন্টনের সুবিধা, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেন বরাবর সেটাই সবথেকে অসুবিধার কারণ হয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ চিরকাল বলে আসছে ‘কেন্দ্রের বঞ্চনা’। এই শব্দ বন্ধ এমন জায়গায় থেকে এসে পৌঁছেছে যে, বাল্যকাল থেকেই বাঙালি জানে, কেন্দ্র এমন একটা বড় জায়গা, যা শুধু আমাদের বঞ্চনা করার জন্যই দিল্লিতে রাজধানী হয়ে বসে আছে। এ কথা বাঙালি বলতে এবং ভাবতে শিখছে না, ওই কেন্দ্র এবং দিল্লিটাও আমাদেরই, ওটা আমাদেরও রাজধানী। আমার দেশ আগে ভারতবর্ষ, তারপর আমি বাঙালি। মনে আছে, একেবারে ছেলেবেলাতেই শুনেছি, যারা বাংলা বলে না, তারা হিন্দুস্থানী। আমরা কি তাহলে ভারতের বাইরের মানুষ! হিন্দুস্তান আমার দেশ না! বাঙালি তাহলে নিজভূমে পরবাসী! কে এই অবস্থা করে ছাড়ল? বিগত অর্ধশতাব্দি ধরে দেখা যাচ্ছে, যারা এখন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেছে। তারাই কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করে, গালাগালি করে, সম্পর্ক নষ্ট করে, নিজেদের আরও বিচ্ছিন্ন করেছে মূল ভারতীয় স্রোত থেকে। আর বাঙালি সব স্বজনপোষণ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে দিতে গরীব থেকে গরীবতর হয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে, এবার বাঙালি বাংলা ছেড়ে অন্যান্য রাজ্যে যাবার উপায় খুঁজছে অর্থাৎ ভারতীয় পরিচয় পেতে চাইছে। কিন্তু সময় অনেকটা বয়ে গেছে এরমধ্যে। হায়।
একটু ভাষার কথা বলা যাক এবার।
খেয়াল করে দেখুন, ভাষার মধ্যে দিয়ে একটা আত্মীয়তার অনুভব আমাদের উপভোগ্যতায় পর্যবসিত হয়। যদি বাংলা ভাষার কথা ধরি, কিন্তু তাহলে যে কোন দেশে গিয়ে যদি হঠাৎ কানে আসে, আর একজন কেউ বাংলা কথা বলছেন, আমরা খুশিতে চমকে উঠি। এগিয়ে যাই নিজের থেকে। মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, আপনি বাঙালি? নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞতা বহু মানুষেরই দেশের বাইরে গেলেই এইরকম অভিজ্ঞতা হয়।
দেখছি, ভাষার সেই আত্মীয়তা বোধটা কমে যাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয়েরই ভাষা বাংলা। অথচ ভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্র। ভাষা এক কিন্তু ধর্ম আলাদা। এই ধর্মের অজুহাতেই কিন্তু এর এক জাতি দুই ভাগ হয়েছিল। তাতে কি প্রমাণ হয়? ভাষার চাইতে ধর্মের জোর বেশি। আমরা আবেগে, আহ্লাদে, ভালবাসায়, বিবিধ সাংস্কৃতিক আচরণ, এই ভাষার জন্যই আত্মীয়তাকে অবলম্বন করে সম্পর্ক রচনা করেছি বিপদে বিপর্যয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এই ভাষাগত আত্মীয়তা, সম্প্রীতি টিকে থাকেনি।
সম্পর্ক, সম্প্রীতিকে অধিকার করে নিয়েছে ক্ষমতাবান ধর্ম। আমাদের মুসলিম ভ্রাতারা নিজ ধর্মালম্বীদের জাতভাই বলে, কিন্তু এক ভাষাভাষীদের জাতভাই বলে না। অর্থাৎ স্বজাত এবং ভ্রাতৃত্ব, এই দুয়েরই পরিচয় ধর্মে। পাশের বাড়ির মানুষ হলেও আমি আপনজন হবো না। কিন্তু সুদূর আরব দেশের মানুষ তার ভাই, ধর্মভাই। সেই কারণে জাতভাই।
কিন্তু ধর্ম কি রাষ্ট্র গড়তে পারে? পারে না। রাষ্ট্রকে রক্ষা করতেও পারেনা। যদি পারতো, তাহলে পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। মজার কথা হচ্ছে, মূল কলহটা কিন্তু বেঁধেছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে। বাঙালি মুসলমানরা বলেছিলেন, প্রাণ গেলেও ভাষা ছাড়ব না। তারপর পূর্ববঙ্গ কিভাবে পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়েছিল, তা আমরা জানি। তাহলে কি প্রমাণিত হল না, ধর্মের চাইতে ভাষার জোর বেশি! কিন্তু সত্যিই কি তাই? না, তা নয়। ভাষার আবেগ ধর্মের কাছে আবারও পরাজিত হয়েছে বারেবারে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছে।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অর্ধশতাব্দীর বেশি দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কলহ তেমন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠলেও, এবার তো একেবারে উলঙ্গ হয়ে পড়ল ধর্মের ক্ষমতা। বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর বাংলাদেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়ে দিল, ভাষা-টাসার কথা ভুলে যাও। ধর্মভাই, জাতভাই-ই আসল। ধর্মই ক্ষমতার উৎস। যে পাকিস্থানের হাত থেকে হিন্দুস্থানের সাহায্যে একদিন তাঁরা স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, সেই পাকিস্তানের সঙ্গেই আবার করমর্দন শুরু করল জাতভাই হিসাবে। তাহলে কোথায় গেল ভাষার জোর!
আর প্রবাসী হিসেবে আমরা দূরদেশ থেকেও দেখলাম, এখনও দেখছি, আমাদের সম-ভাষাভাষী বাংলাদেশি বন্ধুরা, প্রতিবেশীরা, খুবই সম্প্রীতির কথা, বন্ধুত্ব, ভালবাসার কথা বলছেন। এমন কি প্রবাসের বড় বড় শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছেন – রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-লালন-হুমায়ুন-বিদ্যাসাগরের নামও করছেন। গান গাইছেন। কিন্তু ভুল করেও কাউকে দেখছি না, তাঁদের জাতভাইদের অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে, প্রতিবাদ জানাতে। কেন? কেননা ভাষার থেকে ক্ষমতাবান হচ্ছে ধর্ম। আবার আলোচনার খাতিরে এখানে ঐতিহ্যের কথাটাও আসা উচিত। ঐতিহ্য অর্থাৎ ট্র্যাডিশন।
একটি কমন ট্র্যাডিশনের অভাবে কিন্তু ভাষা ও ধর্ম এক হওয়া সত্ত্বেও দুটি জাতি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতিতে পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজ এবং আমেরিকানদের কথা বলা যেতে পারে। একদিন ইংল্যান্ডের লোকেরাই সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় পৌঁছে ঘর বেঁধেছিল। তাদের কথা এক, ধর্মও এক। কিন্তু ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় ছিল না। সুতরাং উভয় স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে গেল। ইংরেজদের এ্যাংলো স্যাকসন ঐতিহ্য ক্রমশ আমেরিকাবাসীদের থেকে মুছে যেতে লাগল। বহু আগে ফেলে আসা জীবনের, ভাবনার, ট্র্যাডিশনের টান ক্রমশ ফুরিয়ে যেতে শুরু করল। মাঝখানে তিন হাজার মাইল জলরাশি দূরত্বও দুজনকে পৃথক হতে সাহায্য করল। ভাষা রইল (যদিও উচ্চারণ বদলে গেল), ধর্মও একই রইল। কিন্তু জাতি বদলে গেল। রাষ্ট্র আলাদা হল।
আরব ইহুদিদের কথা আর তুলছি না। তাহলে অপার বাংলার শারদীয় রচনা শেষ করতে পারব না। শুধু এটুকু উল্লেখ করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করব। সুদূর অতীতে আরব ইহুদির আদি পুরুষদ্বয় একই পরিবারের দুই ভাই ছিলেন। আর আজ তারা একে অপরের পরম শত্রু। ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে এই দশা ঘটবেই।
সুতরাং আমাদের দুই বঙ্গের সম্পর্ক যেখানে এসে দাঁড়াল সময়ের ব্যবধানে তা কি জাতি-শত্রুতা নয়!
এবার এসব ছেড়ে একটু আমাদের নিজেদের ঘরের কথায় আসা যাক। অবশ্য ঘরের কথা ভাবতে বলতে বা লিখতে গেলেও এখন নিজের প্রবাসী পরিচয়ের কথা আরো একবার মনে আসে। তার পেছনে কারণ আছে। আমরা যারা কয়েক দশক ধরে বিদেশের মাটিতে জীবিকা নির্বাহ এবং জীবন যাপন করে আসছি, কেউ নাগরিকত্ব নিয়ে অথবা কেউ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে, তারা কি সত্যিই নিজেদের প্রকৃত জাতীয় পরিচয় (যেমন আমরা ভারতবাসী) ভুলে গেছি, নাকি, যাওয়া সম্ভব! অন্য দেশে থাকলেও, আমাদের ভাষা-রুচি-সংস্কৃতি-খাদ্যাভাস… এসব কি মুছে গেছে, নাকি তা যাওয়া সম্ভব!
একটু ভাবলেই দেখা যায়, আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে কতখানি দেশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি। এবং ওপর ওপর না, বেশ গভীরভাবেই। বিচার করলে দেখা যাবে, দেশের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংস্কৃতিক ব্যাপারেও পরোক্ষভাবে এন আর আইরা কতটা গভীর এবং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নিত্য নিয়মিত আসা যাওয়া চলে। এবং চলছে। আমাদের প্রজন্মের প্রবাসীরা খুব নিবিড়ভাবে কোথাও একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্য রচনা এবং রক্ষা করে চলেছেন।
অথচ এই প্রবাসীরাই যখন দেশের (এখানে মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) কোন ব্যাপারে মুখ খোলেন, বিশেষত তা যদি দেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় হয়, তাহলেই দেশের এক শ্রেণীর মানুষ খ্যাঁক করে ওঠেন। আরও বিশেষ করে যদি কোন সমালোচনার সুর ফুটে ওঠে কথার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে তার মুণ্ডপাত করা হবে এই বলে, যে উনি এই ব্যাপারে মন্তব্য করার কে? উনি তো অন্য দেশের লোক।… উনি কী জানেন এদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে!
সব মানুষ বা দেশবাসীর কথা বলছি না। কিন্তু বিদেশে থাকতে থাকতে একটা ব্যাপার বুঝি যেখানে এবং যখনই প্রবাসীরা দেশের দুরবস্থা কোরাপশন, সামাজিক ভেদাভেদ ইত্যাদি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেছেন তখনই দেশের একটা বড় অংশের মানুষ তাঁদের ওপর খড়গহস্ত হয়েছেন। আর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করলে তো কথাই নেই। সেই মতামতের মধ্যে যদি একটুও নেতিবাচক সমালোচনা থাকে তাহলে ক্ষমতাসীন দেশের আস্ফালন তুঙ্গে ওঠে তো বটেই, শাসানি এমন জায়গায় পৌঁছায়, যার মধ্যে প্রাণ নিয়ে টানাটানির হুমকিও থাকে। আর মজা হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দশ যে পন্থীই হোক, সোশ্যালিজম্ বা কম্যুনিজম্, তারা পুরো ধর্মীয় ফ্যানাটিকদের মতোই আচরণ করে। কেউ কখনো তলিয়ে ভাবতে চাইবে না, কে বা কারা কিংবা কেন ওইরকম মন্তব্য বা সমালোচনা করছেন!
আসলে ধর্মের মতোই কট্টর রাজনৈতিক বোধও এক ধরনের ফ্যানাটিজম্। উভয়ই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এক্ষেত্রে অবশ্যই একথা অনেক রাখতে হবে, ব্যক্তিস্বার্থে বারংবার যারা রাজনৈতিক দল বদল করে, যাদের মতাদর্শ বলে কোন ব্যাপারই নেই, তাদের কথা বলছি না। কেননা তাদের একমাত্র পরিচয় স্বার্থপর ধান্দাবাজ… সে তারা যতই বলুক – ওই দলের থেকে আমি কাজ করতে পারছিলাম না। কাজ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। তাই দল পালটে এই দলে ঢুকছি। এসব মিথ্যে কথা।
কিন্তু একটা শ্রেণীর সাধারণ মানুষকে কম্যুনিজম্-ক্যাপিটালিজম্-সোশ্যালিজম্… সকলেই আচ্ছন্ন করে রাখে। আর যারা সেই দলগুলো চালায় তারা সব সময় চাইবে— মানুষ কম বুঝুক, কম প্রশ্ন করুক। তারা আমাদের ওপর নির্ভর করুক। আমাদের অনুগত থাকুক। সকলেরই, অর্থাৎ সব দলেরই রীতি পদ্ধতি একরকম। দেশের সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ, গ্রামের মানুষজন যত কম সচেতন হবে, যত কম জানবে, ক্ষমতাবাসীনরা তত স্বচ্ছন্দে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের নিছক স্বার্থ রক্ষার দিকটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।
অথচ কোন রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য কিন্তু ধর্মের মতো ইজম্-নির্ভর হওয়ার কথা নয়। কম্যুনিজম্ বা ক্যাপিটালিজম্ দুই-ই একটা ফিলজফি অফ লাইফ… একটি জীবন দর্শন- যা মানবসমাজকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে কাজে লাগবে। কিন্তু লাগে কি? লাগলেও কতটা? শেষপর্যন্ত দেখা যায়, সকলেই ব্যক্তিগত মতাদর্শ আর শক্তি সাধনায় মত্ত। আপনি সমালোচনা করতে যান, ভুল ধরিয়ে দিন… আর রক্ষে নেই। আপনি শত্রু। প্রবাসী হলে তো কথাই নেই।
প্রায় সব পলিটিক্যাল ইজম্-ই আজ স্বধর্মচ্যুত। একদা জাতি-ধর্ম-ভৌগোলিক সীমানা কোনো কিছুকে গুরুত্ব না দিয়ে তারা ছিল আদর্শবাদী। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল মানব কল্যাণ সাধন। অথচ সেই কল্যাণ সাধনের মূল উদ্দেশ্য হয়েছে ক্ষমতার দখল। ঠিক সেই কারণে অধিকাংশ দেশ আজ খাদ্য উৎপাদনের চাইতে গোলা বারুদ অস্ত্র উৎপাদনে বেশি তৎপর। অস্ত্র বিক্রি করে ব্যবসা হয়, ব্যবহার করে ক্ষমতা পাওয়া যায়। মাঝেমাঝেই মনে হয়, একদিন সুন্দর উচ্ছল মহিমান্বিত এক মানব সমাজের যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তাঁরা অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমরা নেতাহীন, আদর্শহীন, এসব এক পৃথিবীতে বসবাস করি যেখানে নিকৃষ্ট উদ্ধত ক্ষমতালোভী মানুষের আস্ফালন সেই ধরণীকে নরকে পর্যবসিত করতে চলেছে।
যাই হোক… শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বকে মানুষ নানা ভাবে জানে, নানানভাবে দেখে, তা সে স্বদেশী, প্রবাসী, ভিনদেশী, অভিবাসী… যে-নামেই যাকে সম্বোধন করা হোক না কেন একটা কথা মানতে হবে, মানুষের জন্যই এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। বলা যায় না, এই কথা মনে করাও হয়তো একটা মোহ। তবুও বিশ্বময় শক্তিপুঞ্জের ভিতরে যে চেতনার উদ্ভব হয়েছিল, তাকি কম বিস্ময়ের! বলা যায়, চেতনার তরঙ্গের সঙ্গে কোথাও বিশ্বের তরঙ্গের মিল আছে। আর তা উপলব্ধির নাম হচ্ছে আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষ করে এই আনন্দের উল্লেখ আছে বারবার। হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে হয়তো দেখবো পৃথিবীর যাবতীয় হানাহানি, মারামারি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সভ্যতা-সংস্কৃতি-সামাজিকতা নিয়ে যত টানাপোড়েন, সবকিছুকেই হয়তো আমরা কিছুটা হলেও অতিক্রম করতে পারব, সহনশীল করে নিতে পারব, যদি কিছুটা আনন্দের সন্ধান করতে পারি।
আমরা সবাই সংসারী মানুষ। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে সংসারে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক দুরকম দৃষ্টির সহাবস্থানেই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা রচিত হয়। মাঝেমাঝে এই দুইয়ের মধ্যেই কলহ বা ভুল বোঝাবুঝি হয়। কিন্তু তা বলে কোনোটাই ত্যাজ্য নয়। কেননা শুধু সংসারিকতা দিয়ে সংসার রক্ষা পায় না। সেটা তাহলে কেবলই শুধু একটা আয়-ব্যয় আর হিসেব–নিকেশের দোকান হয়ে যেত। আর আমরা সংসারী মানুষরা কেবলই ওইসব ভাষা, ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি দেশ বিদেশ যুদ্ধ… ইত্যাদি নিয়ে একটা থিয়োরিটিক্যাল জগৎ সংসারের বাসিন্দা হয়ে থাকতাম। ভালোবাসা প্রীতি আনন্দ ক্ষমা এসবের সন্ধান পেতাম না।
আধ্যাত্মিকতার নিঃশব্দবোধ থেকে মানুষ টের পায়, কোথাও একটা অকারণ আনন্দের ব্যাপার আছে। আর সেটা না থাকলে এই জগত সংসার থেকে উত্থিত ক্ষোভ আর হিংসার সঞ্চিত বিষে সবকিছু ছারখার হয়ে যেত। আমাদের সহ্য আনন্দ শুভেচ্ছার মধ্যে দিয়েই জীবন ও সংসারের নিত্য আরোহণ-অবরোহণ চলেছে। সেই ধারাবাহিকতাই বিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ধরিত্রী সন্তানদের প্রাণদান করে চলেছে।