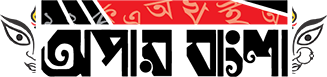ফিচার
সুরবেক বিশ্বাস
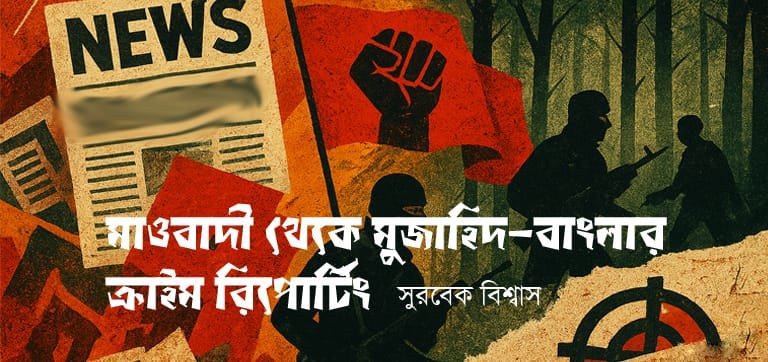
পাকাপাকি ভাবে বিচ্ছেদ আমার তখনও হয়নি ধূমপানের সঙ্গে। রোজ কম-বেশি দশটা সিগারেটের একটা প্যাকেট শেষ হয়। সিগারেট ধরিয়ে দু’টো সুখটান দিয়েছি, এমন সময়ে আমার সাংবাদিক-বন্ধু প্রণব, তখন ‘দ্য টেলিগ্রাফ’-এর সিনিয়র জার্নালিস্ট প্রণব মণ্ডল কথাটা বলল।
প্রণবের আর আমার সিগারেটের ব্র্যান্ড এক। কেউ এক জন অন্য জনের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়েছি। লম্বা একটা টান দিয়ে অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে গলায় একরাশ উৎসাহ নিয়ে প্রণব বলল, ‘যদি এমন হতো, মনে করো, আচমকা জঙ্গলের মধ্যে থেকে অনেকটা যেন মাটি ফুঁড়ে জলপাই পোশাক পরা মাওবাদীরা কালাশনিকভ রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের মুখোমুখি হয়ে প্রেস কনফারেন্স করল! ওফ্ফ্ফ্। তা হলে কেমন হতো বলো তো? তোমাকে এ কথাটা বলতে বলতেই, দ্যাখো, আমার গায়ের রোম কেমন খাড়া হয়ে উঠছে।’ বললাম, ‘তুমি যা বলছ, সে রকম হলে তো কথাই নেই। কিন্তু তেমন কিছু যে হবে না, তা তুমি জানো। আমরা পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক, এ সব দেখার সুযোগ আমাদের হবে না। বাদ দাও। যারা প্রেস মিট করবে বলে জানিয়েছে, অন্তত তারা বিকেলের মধ্যে আমাদের মুখোমুখি হয়ে যা বলার, তা বলুক। না-হলে ফিরতে দেরি হবে, কপি পাঠাতেও দেরি হয়ে যাবে।’ প্রণব তখন একটু বেজার মুখে বলল, ‘ঠিক কথা। তবে স্বপ্ন দেখতে তো আর ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না। এখানকার পরিবেশটাই আলাদা। তার জন্যই এ সব কল্পনা করেও কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছে।’
এখানকার মানে কাঁটাপাহাড়ির। কাঁটাপাহাড়ি। ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় এলাকার কাঁটাপাহাড়ি গ্রাম। যখনকার কথা, তখন কাঁটাপাহাড়ি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরে। ২০০৮-এর ১৭ নভেম্বর। ওই তল্লাটে শীতের বার্তাবাহক বাতাস তখন শিরশিরানি ধরাচ্ছে, সেই বাতাসে আবার বারুদেরও গন্ধ। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে টানা তিন বছর ধরে চলা, গোটা রাজ্যকে কাঁপিয়ে দেওয়া লালগড় আন্দোলন ঠিক তার ১১ দিন আগে শুরু হয়েছে প্রাথমিক ভাবে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যাচার, তাদের হাতে এমনকী মহিলাদেরও শারীরিক নিগ্রহের প্রতিবাদে। সেই সময়ে আমি ‘হিন্দুস্তান টাইমস’-এর সাংবাদিক। কলকাতাতেই। রাস্তা কেটে, গাছ কেটে উপড়ে রাস্তায় ফেলে, গাড়ি-বাস ভাঙচুর করে যে গণ আন্দোলনের সূত্রপাত সে বছর ৬ নভেম্বর সকালে, সেই সময়ে ঘটনাচক্রে, নেহাতই ঘটনাচক্রে একমাত্র সাংবাদিক হিসেবে আমি গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে। প্রথম দিকে আন্দোলনের রাশ সাধারণ মানুষের হাতে অনেকটা থাকলেও ধীরে ধীরে তার লাগাম চলে যায় মাওবাদীদের কাছে। আন্দোলন শুরু হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায়, ১৩ নভেম্বর অতি বাম বিপ্লবীরা তৈরি করে ফেলেন ‘পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি’। বাংলার জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের প্রথম ব্যাপক গণ সংগঠন। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়, মাওবাদীরা সামনে আসবেন না— তাঁদের তৈরি এবং তাঁদের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ওই গণ সংগঠনই আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকবে। ভ্যানগার্ড। আর ১৭ নভেম্বর সেই পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটির প্রথম সাংবাদিক বৈঠক কাঁটাপাহাড়ির স্কুলমাঠে। যে কারণে প্রণব, আমার এবং আরও বহু সাংবাদিক-চিত্র সাংবাদিকের সে দিন সকাল থেকে কাঁটাপাহাড়িতে পড়ে থাকা। শেষমেশ সে দিন বিকেলে সূর্য ডোবার মুখে খোলা মাঠে, খোলা আকাশের নীচে সাংবাদিক বৈঠক করলেন ওই কমিটির পদাধিকারীরা। তাঁরা নিরস্ত্র, অধিকাংশই স্থানীয় এবং আমাদের প্রশ্নের সব উত্তর যে ঠিকঠাক গুছিয়ে দিতে পারলেন, তেমনটাও নয়। আমার বন্ধু-সাংবাদিক প্রণবের সেই স্বপ্ন সে দিন যথারীতি সত্যি হলো না।
তবে প্রণবের সেই স্বপ্ন অনেকটাই সত্যি হলো তার সাত মাস পরে।
২০০৯-এর ১৬ জুন। লালগড়ের ধরমপুর তল্লাটে কালাশনিকভ রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মাওবাদী নেতা বিকাশ ওরফে সিংরাইল টুডু। যাঁর আসল নাম মনসারাম হেমব্রম। বিকাশের ডান কাঁধে ঝোলানো একে-ফর্টি সেভেন রাইফেলের নল মাটির দিকে কোনাকুনি মুখ করা। তার পিছনে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা ধরে আছেন সংবাদপত্রের ফোটো জার্নালিস্ট ও নিউজ় চ্যানেলের ক্যামেরাম্যানরা। কারণ, বিকাশের মুখের ছবি ওঠা চলবে না কিছুতেই। আর ক্যামেরা ছাড়া রিপোর্টাররা বিকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছেন। অস্ত্র প্রদর্শন করে কোনও বিপ্লবী বা নিষিদ্ধ সংগঠনের কারও প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনের সে-ই প্রথম বার সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ। তার আগের মাস দুয়েক যাবৎ মাওবাদীদের তদানীন্তন শীর্ষনেতা কিষেনজি ওরফে কোটেশ্বর রাও একাধিক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের আলাদা আলাদা ভাবে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, পিছন থেকে তোলা অটোম্যাটিক রাইফেল হাতে বা কাঁধে কিষেণজির ছবি সংবাদপত্রে ছেপে বেরিয়েছে কিংবা নিউজ় চ্যানেলে দেখানোও হয়েছে। তবে সেগুলোর কোনওটা সাংবাদিক বৈঠক ছিল না। লালগড়ের ধরমপুরে বিকাশের সাংবাদিক সম্মেলন সে দিক থেকে মাইলফলক। এবং আমরা, সাংবাদিকরা ওই ঘটনায় এক ধাক্কায় অনেকটাই যেন পরিণত হয়ে গেলাম।
আর একটা ব্যাপার। সেই ২০০৮-এর ১৭ নভেম্বর পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটির সাংবাদিক বৈঠকের আগে কাঁটাপাহাড়ির স্কুলমাঠের পিছনে একটা জঙ্গলে কমিটির সদস্যরা এক জন কারও সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। আবার সাংবাদিক বৈঠকের সময়ে আমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর তাঁরা উঠে গিয়ে নিয়ে আসছিলেন সেই জঙ্গলের ভিতরে কোনও এক জনের কাছ থেকে। তার বেশ কয়েক বছর পরে জেনেছি, তিনি বিকাশ।
ওই ঘটনার ৯ বছর আগে রিপোর্টিংয়ে আমার হাতেখড়ি। ২০০০ সালের মে। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় সাংবাদিকের চাকরি পাই তার আগের বছর জুলাইয়ে। প্রথম চাকরি। তবে চাকরির প্রথম ১০ মাস কাজ করেছি ডেস্কে। কোনও খবর লেখা ও সম্পাদনা করা, অন্য কোনও সহকর্মীর খবর নতুন ভাবে লেখা অর্থাৎ রিরাইট করা, বানান সম্পর্কে ধারণা এবং পেজ মেকআপ— এ সব কিছুর ঠিকঠাক তালিমের জন্য ডেস্ক-ই আসল জায়গা। চাকরি পাওয়ার তিন বছর আগে থেকেই, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেওয়ার পর পরই ফ্রি-ল্যান্স লেখালিখি শুরু করি আনন্দবাজার পত্রিকা এবং দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোক ম্যাগাজ়িনে। কিন্তু সেই সব লেখালিখি, এমনকী অ্যাসাইনমেন্ট ভিত্তিক লেখালিখির সঙ্গে সাংবাদিকতার চাকরির ফারাক আসমান-জমিনের চেয়েও বেশি। কেউ আগে যতই লেখালিখি করে থাকুন, সেগুলো সত্যিকার বিচারে অভিজ্ঞতা হিসেবে সাংবাদিকতার চাকরিতে গণ্য হয় না। সাংবাদিকতার চাকরি করার সময়ে সব কিছুই কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়। ডেস্কে কাজ করার সময়েই রিপোর্টিংয়ে আমার আগ্রহ দেখে আনন্দবাজার পত্রিকার তখনকার রেওয়াজ এক রকম ভেঙে চাকরির কনফারমেশনের আগেই আমাকে পাঠানো হলো রিপোর্টিং বিভাগে। এবং প্রথম দিনের অ্যাসাইনমেন্টই লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর।
তারিখটা ২০০০ সালের ৩ মে। প্রথম দিন আমার সঙ্গী হলেন রিপোর্টিংয়ে আমার দুই সিনিয়র সুব্রত বসু ও পার্থসারথি সেনগুপ্ত । তাঁরাই আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন লালবাজারের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার, ডেপুটি কমিশনার হেড কোয়ার্টার্স এবং ডিসি ডিডি ওয়ান অর্থাৎ শহরের গোয়েন্দা প্রধানের সঙ্গে (গত প্রায় দেড় দশক যাবৎ ডিসি ডিডি ওয়ান আর কলকাতার গোয়েন্দা প্রধান নন, গোয়েন্দা প্রধান এখন জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ-ক্রাইম)। তা ছাড়া, আমার ওই দুই অফিসতুতো দাদা আমাকে নিয়ে গেলেন গোয়েন্দা বিভাগের ডাকাতি দমন, হোমিসাইডের মতো কয়েকটি শাখায়। পরিচয় হলো সে সব শাখার ওসি-দের সঙ্গেও। তবে লালবাজারে সব শেষে সে দিন যেটা হলো, ভুল বললাম, আসলে কিছুই হলো না— কোনও খবর পাওয়া গেল না। আমার অফিসের দুই দাদাদের এক জন, সুব্রতদা বললেন, ‘নাঃ, আজ কোথাও কিছু নেই। না-আছে ল অ্যান্ড অর্ডার সংক্রান্ত কোনও খবর, না-আছে ক্রাইমের কিছু খবর। পুরো ফাঁকা বাজার।’ এ সব কথা হচ্ছে লালবাজারের চাতালে, ডিডি (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) বিল্ডিংয়ের সামনে। সেখানে আছেন অন্য খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরাও (২৪ ঘণ্টার নিউজ় চ্যানেল তখনও কিছু নেই)। যাঁরা লালবাজারে এসেছেন ব্রিফিং নিতে। তাঁদেরই এক জন, ‘দ্য টাইম্স অফ ইন্ডিয়া’-র কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুব্রতদাকে কৃষ্ণেন্দু বলল, ‘বুঝলে দাদা, মুম্বইয়ে আমার এক কলিগের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল। ও বলল, ‘তোদের কলকাতায় বা স্টেটে ক্রাইম বিটের (বিট অর্থাৎ কোনও একটা বিষয় বা জায়গা, যেখান থেকে নিয়মিত খবর পান বা খবর করেন রিপোর্টাররা) তো তেমন খবরই হয় না। তোদের চাকরি থাকে কী করে বল তো?’ এ কথা কৃষ্ণেন্দু বলল হাসিমুখে এবং অন্যরাও সবাই হেসে উঠল।
আমার কিন্তু হাসি পেল না। ভাবলাম, এ আমি রিপোর্টিংয়ের কোন বিটে এসে পড়লাম, যেখানে শুনছি তেমন কোনও খবরই হয় না!
সেই সময়ে আনন্দবাজার এবং ‘দ্য স্টেটসম্যান’, কলকাতার মূলত এই দুটো দৈনিক সংবাদপত্রে জুনিয়র রিপোর্টারদের তালিম দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম অনুসরণ করা হতো। বিভাগে যে সব চেয়ে নতুন, তার প্রথম বিট হবে লালবাজার কিংবা কলকাতা পুরসভা। বছর খানেক বা বছর দুয়েক পরে সেই রিপোর্টার যখন কিছুটা পরিণত হবে, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, তখন তাঁকে দেওয়া হবে পলিটিক্যাল, রাইটার্স (সেই সময়ে রাজ্যের প্রধান সচিবালয় নবান্নে স্থানান্তরিত হয়নি, ছিল রাইটার্স বিল্ডিংস বা মহাকরণেই), নিউ সেক্রেটারিয়েট কিংবা পাওয়ার (ইলেকট্রিসিটি)-এর মতো বিট। অর্থাৎ, সার্বিক ভাবে লালবাজার বা পুরসভা তখন এক জন রিপোর্টারের লঞ্চিং প্যাডের বাইরে অন্য কিছু নয়।
লালবাজার বা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে ওই সব বিট পাওয়া মানে, সেই সময়ে ধরা হতো, রিপোর্টারের উত্তরণ হলো, মর্যাদা বাড়ল। কারণ, ওই সব জায়গা থেকে একদিকে যেমন নিয়মিত খবর হয়, অন্য দিকে তেমনই নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যায় এবং আখেরে ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয় কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে। এর মধ্যে পলিটিক্যাল রিপোর্টিং ছিল, ছিল কেন এখনও আছে, সব চেয়ে বেশি গ্ল্যামারের। তার তুলনায় পুলিশ রিপোর্টিং তখন ছিল নেহাতই ফেলনা। খুব পুরোনোদের কথা বলতে পারব না। তবে আমরা যাঁদের পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে ‘বর্তমান’-এর জীবানন্দ বসু ও জয়ন্ত মজুমদার, ‘আজকাল’-এর অমিত মুখোপাধ্যায়, টেলিগ্রাফ-এর অভিজিৎ নন্দী মজুমদার এবং ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর গৌতম বসুকে বাদ দিয়ে এক জন রিপোর্টার টানা বহু বছর লালবাজার বিট করে গিয়েছেন, এমন নজির সম্ভবত তেমন নেই। পুলিশ রিপোর্টিং শব্দবন্ধ ব্যবহার না-করে ক্রাইম রিপোর্টিং বলাই মনে হয় সঙ্গত, কারণ তদানীন্তন সময়ের বিচারে ক্রাইম রিপোর্টিং বলাটা বাড়াবাড়ি। তখন সাড়া ফেলার মতো অপরাধের খবরই হতো খুব কম। তার বাইরে টুকটাক যা খবর হতো, সেগুলো লিখতে হতো কেবল পুলিশ অফিসারদের কথা শুনেই। বেশির ভাগই চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানির মতো খবর। একটু অন্য রকম বলতে টুকটাক ক্রিকেট বেটিংয়ের খবর।
প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার মাস্টারমশাই, অধ্যাপক রবীন বসুর সঙ্গে একবার দেখা হতে তিনি কিছুটা বিরক্ত মুখে বলেছিলেন, ‘তুমি তো খুনখারাপি নিয়ে লেখো-টেখো।’ স্যরের হয়তো আশা ছিল, পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্সের এই ছাত্র সাংবাদিকতার চাকরি পেয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করবে, কলাম-টলাম লিখবে। সেই জায়গায় কেবল খুন-খারাপি তো নয়, লিখতে হতো মধুচক্রের খবরও। আমার নিজেরই তখন মাঝেমধ্যেই মনে হতো, কবে আমি এই পুলিশ বিট থেকে মুক্তি পাব, কবে আমার উত্তরণ হবে পলিটিক্যালের মতো বিটে।
তবে মুক্তি তো দূর, এই পুলিশ বিট-ই কালেদিনে আমার এক রকম নেশা ধরিয়ে দিল। এবং কলকাতা তথা বাংলার রিপোর্টিংয়ে যা ছিল যুগ যুগ ধরে পুলিশ বিট, তার প্রকৃত অর্থে উত্তরণ হলো ক্রাইম বিট বা ক্রাইম রিপোর্টিংয়ে।
আসলে খেলাটা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল ২০০১-এর ২৫ জুলাই থেকে। মুক্তিপণের জন্য যে দিন কলকাতার তিলজলা এলাকা থেকে অপহরণ করা হলো খাদিম জুতো কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার পার্থ রায় বর্মনকে। তার দেড় মাসের মধ্যেই নাইন ইলেভেন এবং ছ’মাসের মধ্যে, ২০০২-এর ২২ জানুয়ারি কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের সামনে জঙ্গি হামলা। এই তিনটে ঘটনাই বাঁধা পড়ে গেল একটা সুতোয়। যে সুতোর নাম আফতাব আনসারি। খাদিমকর্তা অপহরণ ও আমেরিকান সেন্টারের সামনে পুলিশকর্মীদের উপর জঙ্গি হামলার অন্যতম প্রধান চক্রী ও দোষী সাব্যস্ত, দুবাইয়ে থেকে কাজ করা আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন আফতাব আনসারিই খাদিমকর্তার মুক্তিপণের টাকার একটা অংশ পাঠায় ব্রিটিশ-পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে অপহরণ ও খুন করা ওমর শেখকে এবং সেই টাকা ওমর শেখের মাধ্যমে পৌঁছয় নাইন ইলেভেন-এর অন্যতম হামলাকারী মহম্মদ আটার হাতে। ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে কাঠমান্ডু থেকে দিল্লি আসার পথে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের উড়ান আইসি-এইট ওয়ান ফোর-কে হাইজ্যাক করে কান্দাহারে নিয়ে গিয়ে পণবন্দি যাত্রীদের মুক্তির বিনিময়ে যে সন্ত্রাসবাদীদের ছাড়িয়ে নিয়েছিল বিমান অপরহণকারীরা, ওমর শেখ সেই সন্ত্রাসবাদীদের এক জন। এবং এ ভাবেই প্রমাণিত হলো, সন্ত্রাসবাদের কোনও ভৌগোলিক সীমা নেই আর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গও সেই সীমার বাইরে কোনও দ্বীপের মতো অবস্থান করছে না।
খাদিমকর্তা পার্থ রায়বর্মনকে যারা অপহরণ করেছিল, তাদের পান্ডাদের এক জন আসিফ রেজ়া খানের বাড়ি কলকাতার পার্ক সার্কাসের কাছে মফিদুল ইসলাম লেনে। এই আসিফ পরে গুজরাটে প্রাণ হারায় পুলিশের গুলিতে। আসিফের ভাই আমির রেজ়া খান দাদার মৃত্যুর বদলা নিতে আফতাব ও আরও কয়েক জনের সঙ্গে মিলে গড়ে তোলে ‘আসিফ রেজ়া কম্যান্ডো ফোর্স’। যারা জঙ্গি হামলা চালায় কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের সামনে ডিউটিতে থাকা পুলিশকর্মীদের উপর। একে-ফর্টি সেভেন রাইফেল থেকে ব্রাশ ফায়ারে পাঁচ জন সিপাহিকে (আর্মড পুলিশ বা সশস্ত্র বাহিনীর কনস্টেবলদের বলা হয় সিপাহি) হত্যা করার কিছুক্ষণ পরে প্রধান চক্রী আফতাব দুবাই থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা-সহ কয়েকটি সংবাদপত্রের অফিসে ফোন করে পরিষ্কার বলেছিল, ‘আমরা আসিফ রেজ়া কম্যান্ডো ফোর্স। এটা আমাদের কাজ। আসিফের ফল্স এনকাউন্টার করা হয়েছিল। আমরা তার বদলা নিলাম।’ দুবাই থেকে আফতাব সে দিন ফোন করেছিল ভবানী ভবনের সিআইডি-র সদর দপ্তরে এক আইপিএস অফিসারকেও। রাজীব কুমার। তখন সিআইডি-র এস এস (স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট) রাজীব কুমার এখন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সর্বময় কর্তা— ডিরেক্টর জেনারেল বা ডিজি। ওই দুঁদে গোয়েন্দা অফিসারকে আফতাব ফোন করে বলেছিল, ‘টিভি দেখছেন স্যর? কী করেছি শুধু দেখুন। আমার নাম আফতাব আনসারি।’ রাজীব বলেছিলেন, ‘দুবাইয়ে কী করছিস আফতাব? তুই চলে আয় কলকাতায়। তোর সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া বাকি।’ ঘটনাচক্রে, তার পর দিনই, ২০০২-এর ২৩ জানুয়ারি দুবাইয়ে আটক করা হয় আফতাবকে। পরে তাকে কলকাতায় আনা হয় এবং এখন সে সাজা খাটছে কলকাতার জেলে। কলকাতার ছেলে আমির রেজ়া খানকে কিন্তু পুলিশ ধরতে পারেনি। ভারতের যে দেশজ জঙ্গি সংগঠন (ভারতীয়দের নিয়ে তৈরি, ভারতের মধ্যে কার্যকলাপ, ভারতে বসেই নাশকতার ব্লু প্রিন্ট— কোনও পড়শি দেশে নয়) মোটামুটি ভাবে ২০০৭ থেকে দেশের একটার পর একটা শহরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নাশকতা করেছে, সেই ‘ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন’ (আইএম)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমির-ই। বছর পাঁচেক আগে সিরিয়ায় আমির প্রাণ হারিয়েছে বলে ভারতীয় গোয়েন্দাদের একটা বড় অংশ মোটামুটি নিশ্চিত।
আইসি-এইট ওয়ান ফোর হাইজ্যাক বা কান্দাহার হাইজ্যাকের অন্যতম চক্রীকে ২০০০ সালের গোড়ার দিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে। তবে সেই সময়েও মোটের উপর একটা ধারণা ছিল যে, কলকাতা কিংবা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং কলকাতায় বহু ভাষাভাষী মানুষের বসবাসের কারণে জঙ্গি সংগঠনগুলো কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গকে নিছকই শেল্টার বা সেফ প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহার করে— এখানে তাদের কার্যকলাপ তেমন নেই। কিন্তু খাদিমকর্তা অপহরণ-নাইন ইলেভেন-কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের সামনে জঙ্গি হামলার ত্রিযোগ সেই পুরোনো ধারণা ও ধারায় আমূল পরিবর্তন আনল বড়সড়। তার সঙ্গেই তাল রেখে মৌলিক পরিবর্তিত হলো বাংলার ক্রাইম রিপোর্টিং।
ভয়ঙ্কর, হাড় হিম হয়ে যাওয়া ঘটনাবলি প্রাপ্তবয়স্ক করে তুলল বাংলার ক্রাইম রিপোর্টিংকে। কোনও খবরকে দেখার দৃষ্টিকোণ আমাদের, ক্রাইম রিপোর্টারদের যেমন পাল্টে গেল, তেমনই ক্রাইম বিটের মধ্যে থেকেই উত্তরণ ঘটল রিপোর্টারদের। অন্য বিটে যেতে হলো না। বরং, অন্য বিটের রিপোর্টারদের কাছে কিছুটা হলেও সম্ভ্রম বাড়ল। রোমাঞ্চকর সব ঘটনার সাক্ষী হতে হচ্ছে যে! ক্রাইম বিটের রিপোর্টারদের দিয়ে ফিচার পেজে লেখানো হতে লাগল কভার স্টোরি। বছর বছর ধরে কম গুরুত্ব পাওয়া একটা বিটে কাজ করার ফলে যেটা তাঁরা এতদিন করতে পারেননি, এ বার সেটাও তাঁরা করতে পারলেন। হাত খুলে লিখতে শুরু করলেন। পরিচয় দিতে পারলেন নিজের কলমের…ভুল বললাম, কি প্যাডের মুন্সিয়ানার। উল্টো দিকে, কেবল তথ্য দেওয়া নয়, ক্রাইম বিটের রিপোর্টারদের কাছ থেকে সংবাদপত্রের সিনিয়র এডিটর, চিফ রিপোর্টাররা প্রত্যাশা করলেন ভালো লেখা পাওয়ার। ঘটনার তখন এতটাই ঘনঘটা, এক-একটা ঘটনার মধ্যেই কত রকম যে বৈচিত্র।
তার পরে মাওবাদীদের পরিচালিত লালগড় আন্দোলন আরও এক ধাপ নয়, বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল বাংলার অপরাধমূলক সংবাদ সংগ্রহ ও তার পরিবেশনকে। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের তাবড় সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কাছে গুরুত্ব ও ইজ্জত বাড়ল পশ্চিমবঙ্গের ক্রাইম বিটের সাংবাদিকদের। লালগড় আন্দোলনের আগে প্রণব মণ্ডল-সহ জনা কয়েক জন সাংবাদিককে আলাদা আলাদা ভাবে মাওবাদী নেতারা মাঝেমধ্যে ডেকে নিতেন পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামের কোনও গোপন ডেরায়। সেই সব মাওবাদী নেতা সেই সময়ে অস্ত্র প্রদর্শন তেমন একটা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু লালগড়-পর্বে মাওবাদী শীর্ষনেতা কিষেনজি অটোম্যাটিক রাইফেল নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন বার কয়েক। ২০০৯-এর ২০ অক্টোবর ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থানা আক্রমণ করে দু’জন পুলিশকর্মীকে গুলি করে খুন করল মাওবাদীদের একটা বড় স্কোয়াড, লুট করল থানা লাগোয়া একটি ব্যাঙ্কের কয়েক লক্ষ টাকা এবং সব শেষে থানার ঠিক উল্টো দিকের কোয়ার্টার থেকে অপহরণ করা হলো ওসি-কে। এক সাংবাদিককে ফোন করে কিষেনজি জানালেন, এটা তাঁদের ‘অপারেশন গুডউইল’। মাওবাদীদের ও প্রশাসনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নামতে হলো কলকাতারই আর এক সাংবাদিককে। কিষেনজির সঙ্গে অপহৃত ওসি-র বাড়ির লোকজনের টেলিফোন-কথোপকথনের লাইভ সম্প্রচার করা হলো নিউজ় চ্যানেলে। অপহরণের দু’দিন পরে এক রাতে মাওবাদীদের খাস তালুক লালগড়ের এক প্রত্যন্ত গ্রামে সাংবাদিকদের ডেকে তাঁদের হাতে কিষেনজি ও তাঁর সংগঠনের অন্যেরা তুলে দিলেন ওসি-কে অক্ষত অবস্থায়। ওসি-র গলায় ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে লেখা ‘প্রিজ়নার অফ ওয়ার’। আবার ২০১০-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রামের শিলদায় ইএফআর (ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার্স রাইফেল্স) ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে ২৪ জন জওয়ানকে খুন করার পরে কিষেনজি সাংবাদিকদের ফোন করে বললেন, ‘এটা হলো আমাদের অপারেশন পিস হান্ট (তখন মাওবাদী দমনে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি রাজ্যে ‘অপারেশন গ্রিন হান্ট’ চালাচ্ছে)।’ শিলদার ইএফআর ক্যাম্পে ওই হামলা পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী হিংসার ঘটনাগুলোর মধ্যে ভয়ঙ্করতম।
সভ্য সমাজে হিংসা সব সময়েই বর্জনীয়, যদি হয়, তা হলে সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। পাশাপাশি, এটাও অস্বীকার করা যাবে না, মাওবাদীদের ওই সব কার্যকলাপ এবং আমাদের সঙ্গে তাঁদের ঘন ঘন যোগাযোগের ফলে একটা রোমান্টিসিজ়মও তৈরি হলো— অভিপ্রেত ও আকাঙ্ক্ষিত নয়, তবুও। যেটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পুলিশ বিটে একতরফা পুলিশ অফিসারদের মুখে ঝাল খেয়ে সেটাই লিখতে হতো, অন্য পক্ষের বক্তব্য শোনার সুযোগ থাকত না। সেই অভাব মিটে গেল লালগড় আন্দোলন-পর্বে, কিষেনজির সৌজন্যে।
পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদী আন্দোলনের সেই উত্তাল অধ্যায়ের অবসান হয় ২০১১-র নভেম্বরে কিষেণজি নিহত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তা বলে বাংলার ক্রাইম রিপোর্টাররাও তার পর থেকে গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন, তা কিন্তু নয়। আরও অনেক কিছু দেখা, জানার বাকি ছিল আমাদের— এখনও আছে।
২০১৪-র ২ অক্টোবর, গান্ধী জন্মজয়ন্তী ও সে বছর দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন দুপুরে বর্ধমান শহরের অদূরে খাগড়াগড় শহরে একটি বাড়ির দোতলায় আচমকা বিস্ফোরণে নিহত হলো দু’জন। পরে জানা গেল, তখন মূলত বাংলাদেশে কাজ করা ও সে দেশে নিষিদ্ধ হওয়া জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) বর্ধমানের খাগড়াগড়ের ওই জায়গায় বেশ কিছু কাল যাবৎ ওয়ার্কশপ তৈরি করেছে। বোমা, গ্রেনেড বানানোর ছোটখাটো কারখানা। পড়শি দেশে নাশকতা ঘটাতে বানানো হচ্ছিল সে সব। সেই ২ অক্টোবর বোমা বানানোর সময়ে তাড়াহুড়োয় এ দিক-ও দিক হওয়ায় কোনও ভাবে বিস্ফোরণ ঘটে কারখানায়। দুর্ঘটনামূলক বিস্ফোরণ। যা না-ঘটলে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে জেএমবি-র অস্তিত্ব আরও কত কাল আড়ালে থেকে যেত, তা কে জানে! কোনও প্রতিবেশী দেশে নাশকতা ঘটানোর জন্য ভারতের মাটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে— এমন ঘটনা সেই প্রথম বার জানা গেল খাগড়াগড়ের সূত্রে। আরও জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, ঝাড়খণ্ড, অসম, কেরালা, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যেও জেএমবি তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। এমনকী, খাগড়াগড় মামলার তদন্তের সূত্রে ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) যখন জেএমবি-র একের পর এক সদস্যকে জালে তুলছে, সেই সময়ে ২০১৮-র জানুয়ারিতে বিহারের বুদ্ধগয়াতেও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ওই জঙ্গি সংগঠন। খাগড়াগড়ের ঘটনা, জেএমবি, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জঙ্গি নেটওয়ার্ক, গোটা বিষয়টার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব মিলেমিশে কেবল জাতীয় স্তরে নয়, ভারতের বাইরেও গুরুত্ব বাড়াল বাংলার ক্রাইম রিপোর্টারদের।
তবে খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের প্রায় দু’মাস পরে একটি সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলায় গিয়ে জানতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে জেএমবি ঘাঁটি গেড়েছিল খাগড়াগড়ের ঘটনার এক দশকেরও বেশি আগে। তখন কিছু গ্রেপ্তারি হয়েছিল, মামলাও হয়েছিল। কিন্তু কোনও কারণে রাজ্য প্রশাসনের বেশ উঁচু স্তর থেকে সব কিছু ধামাচাপা দেওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়। সেই মতো শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হয় তখনকার মতো। বেশ কয়েক বছরের জন্য। তবে দেরিতে হলেও শেষমেশ সেই মাছের গন্ধ চারপাশে যে ছড়িয়ে পড়ল, তার জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে বাংলার ক্রাইম রিপোর্টিংকেই।