রাজা ভট্টাচার্য
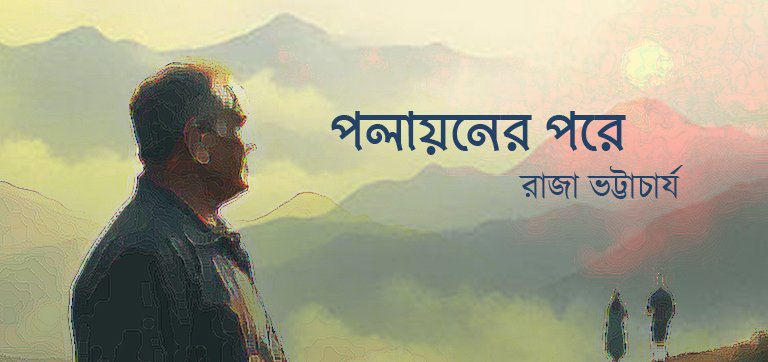
১
সেই লোকটা আজ আবার এসেছে। হাতে একটা ক্ষুদে ব্যাগ। তার মধ্যে খান চারেক ছোট ছোট তেলাপিয়া মাছ খাবি খাচ্ছে। ব্যাগের নড়াচড়ায় সেটা ধরা পড়ছে। ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকটা বের করে প্রায় বুক-সমান উচ্চতায় সিমেন্টের স্ল্যাবের উপরে বসে থাকা মালতীর দিকে সেটা ছুঁড়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “বিড়ালের মাছগুলো কেটে রেখো, মালতী। আমি বাজার সেরে আসি।”
মালতী এই বাজারে মাছ কাটছে কুড়ি বছর হয়ে গেল। কালোকোলো গোলগাল চেহারা। ছাই-মাখা বাঁহাতে প্লাস্টিকটা নিজের একটু কাছে টেনে নিয়ে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে নিজের কাজ করে চলল। শুধু লোকটা চলে যাওয়ার পর একবার আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে আপন মনে গম্ভীরভাবে বলল, “কবে যে ইনি নিজের জন্য কেনা মাছটা আমাকে কাটতে দেবেন, কে জানে?”
লোকটার পরিচয় জানা নেই গোপীনাথ সেনের। তবে প্রত্যেক রবিবার ঘটে চলা এই দৃশ্যটা তাঁরও বহু বছরের পরিচিত। চারটে বাটামাছ বা তিন ইঞ্চি লম্বা তেলাপিয়া নিয়ে আসে লোকটা, আর ওই বাধা বুলি আউড়ে চলে, “বিড়ালের মাছটা কেটে রেখো।” হাড়-কঞ্জুস যাকে বলে। কিন্তু সেটা স্বীকার করবে না। তাই ওই বেড়ালের মাছের ঢং।
অন্যদিন লোকটা চলে গেলেই খিকখিক করে হাসতে আরম্ভ করেন গোপীনাথবাবু নিজেও। মালতীও একবার কটমট করে তাকিয়ে ফের নিজের কাজে মন দেয়।
কিন্তু আজ হাসি পেল না গোপীনাথবাবুর। আগের মতোই ভুরু কুঁচকে তিনি দেখতে লাগলেন মালতীর অভ্যস্ত হাতের কাজ। ঝড়ের বেগে মাছ কেটে চলেছে সে। ন্যাদোশ মাছ। সেই কোন ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে স্বপনকুমারের বই কিনতে বাজারে আসতেন গোপীনাথবাবু। সেই সময় এই মাছ শেষবার খেয়েছিলেন তিনি। আজ হঠাৎই কমলের কাছে চকচকে মাছগুলোকে দেখে মুহূর্তের জন্য ধৈর্য হারিয়েছিলেন। আর তারই ফলে…
আজ দেবযানী একেবারে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি করেছে।
দেবযানী, অর্থাৎ গোপীনাথবাবুর মধ্যবয়স্কা গৃহিণী সম্প্রতি পঞ্চাশ পার করেছেন। গোলগাল চেহারা, মুখে এখনও কিছু লাবণ্য লেগে রয়েছে। তবে কী— সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই, তাঁর ধাত কিঞ্চিত কড়া। কথায় কথায় স্বামীকে সাংঘাতিক বকাবকি করা তাঁর অভ্যাস। প্রায় বিশ বছরের দাম্পত্যে সেই ধমক খাওয়াটাও গোপীনাথবাবুর অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তার উপর দেবযানী বকাবকি করার কারণের জন্য সব সময় গোপীনাথের কোনও ভুলের জন্য অপেক্ষাও করেন না। গাইঘাটায় যেবার তুমুল ঝড় হয়ে মেলাই গাছপালা পড়ে গেল, বাড়িঘরদোর ভেঙে গেল, সেবারও তিনি গোপীনাথকে ভয়ংকর ধমকাধমকি করেছিলেন। জাপানের সুনামির জন্য কম বকা খাননি গোপীনাথ। কাজেই ওসব ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে যাওয়া তাঁর অভ্যেস আছে।
কিন্তু আজ একেবারে সর্বসমক্ষে ভরা বাজারের মধ্যে বেলা ন’টার সময় দেবযানী যা করলেন, সেটা সহ্য করা এমনকি নিরীহ স্বভাবের গোপীনাথ সেনের পক্ষেও রীতিমত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।
দোষের মধ্যে ওই ন্যাদোশ মাছ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন গোপীনাথ।
আজ রবিবার। এই দিনটায় সারা সপ্তাহের মাছ-মাংস কেনার জন্য তিনি সস্ত্রীক বাজারে আসেন; কারণ মাছ-মাংস কেনার ব্যাপারে তাঁর উপরে মোটেই ভরসা রাখেন না দেবযানী। গোপীনাথবাবু যে চোখ থাকতেও কানা এবং মাছের কানকো তুলে দেখে নিতে নিতান্তই অপারগ, সে কথা তিনি প্রতি রোববার সকালেই একবার স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। গোপীনাথবাবুও সে কথা বহুকাল আগেই মেনে নিয়েছেন। কাজেই তাঁকে থমকে দাঁড়াতে দেখে দেবযানী তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, “কোনও ভদ্রলোক এই মাছ খায় না। তুমি এগুলো কিনবে না। স্পষ্ট বলে দিলাম।”
ঝোঁকের মাথায় আজ বহুদিন পর স্ত্রীর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বসলেন গোপীনাথবাবু। কথাটা না শোনার ভান করে কমলের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বললেন, “ও কমল, আড়াইশো গ্রাম ন্যাদোশ দিয়ে দে তো বাবা!”
কথাটা আলগোছে মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘাড়ের উপর একটা গরম নিঃশ্বাস অনুভব করলেন। একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়েও গোপীনাথবাবু বুঝতে পারছিলেন, দেবযানীর গোল গোল চোখ দুটো এই মুহূর্তে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। আজ কেবল বাড়ি ফেরার অপেক্ষা।
দুঃখের বিষয়, গোপীনাথবাবু একবারও পিছনে ফিরে না তাকানোয় দেবযানীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বাজারু লোকেদের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি সপ্তমে গলা তুলে চিৎকার করতে শুরু করলেন, “আমি বারণ করার পরেও তুমি ওই পচা মাছগুলোই কিনলে? বললাম— এসব ছোটলোকেরা খায়। হবে না কেন? ভদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে করলেই তো কেউ জাতে উঠে যায় না! আসলে তো সেই ক্যাম্পে থাকা বাঙাল! এসব ছোটলোকি মাছ বাদ দিয়ে তোমাদের চলবে কেন? ইলিশ, ভেটকি, চিতল— এসব তো তোমাদের পোষাবে না! বাবা বাজার করত যদুবাবুর বাজার থেকে। আস্ত ইলিশ দড়িতে ঝুলিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসত, মাছের ন্যাজে রাস্তার ধুলো লেগে যেত— এত বড় সেই মাছ। আর আজ কিনা এই মাছ খেতে হবে, যার নাম ন্যাদোশ! হে ঈশ্বর! কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম!!”
“আহা…কী বলো তো? বাবা একবার খাইয়েছিল। সে বহুকাল আগের কথা। খাসা টেস্ট।” চাপের মুখে বলে ফেললেন গোপীনাথ।
এরপর থেকেই ক্রমাগত ধমকে চলেছেন দেবযানী। আর প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ একই কথা বলে শেষ হচ্ছে। “আজ বাড়ি চলো, তোমার হচ্ছে।”
মুশকিল হল, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পক্ষে আজ বড্ড বেলা হয়ে গেছে। তাছাড়া এই মাছ ক’টা না খেয়ে গৃহত্যাগী হওয়ার কোনও মানেই হয় না। সৌভাগ্যবশত রান্নাবান্নার দায়িত্ব দেবযানীর উপরে নয়। সোমা নামের যে মেয়েটি রান্নাঘরের দায়িত্বে আছে, তার রান্নার হাতটি চমৎকার। কাজেই মাছগুলো কোনক্রমে তার হাতে তুলে দিতে পারলে আজ দুপুরে ছেলেবেলার সেই অতুলনীয় স্বাদ আরেকবার উপভোগ করা যেতেই পারে। আশায় বুক বেঁধে দাঁতে দাঁত চেপে মালতীর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন গোপীনাথ। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নাকে আঁচল দিয়ে এখনও দুর্দান্ত প্রতাপে ধমকে চলেছেন দেবযানী।
এমন সময় পাশ থেকে শোনা গেল একটা হাসি হাসি গলা, “বৌমা আজ বড্ড ক্ষেপে গিয়েছে দেখছি! অ গোপীনাথ, ভুল করে পচা মাছ কিনে এনেছ নাকি?”
কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেললেন গোপীনাথ। তারপর একটা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে।
যা ভেবেছিলেন তাই। নরেন গাঙ্গুলি মশাই পরিতুষ্ট মুখে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরই দিকে।
“আর বলবেন না কাকাবাবু,” এতক্ষণে একজন প্রকৃত শ্রোতা পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে গর্জন করে উঠলেন দেবযানী, “দুশো বার করে বললাম, ওই ন্যাদোশ না কী নাম— ওই মাছ কিনতে হবে না। ভদ্রলোকে কখনও এরকম নামের মাছ খায় না। তা শুনবে ও? আবার বলে কিনা— ‘বাবা একবার খাইয়েছিল। খাসা টেস্ট।’ ভাবুন একবার কাকাবাবু! যার নাম ন্যাদোশ, তার টেস্ট কখনও ভাল হতে পারে? নাম শুনলেই তো বোঝা যাচ্ছে একেবারে অখাদ্য জঘন্য কিছু একটা হবে! নিশ্চয়ই গরিব লোকেরা খায়!”
নরেন গাঙ্গুলীর জীবনের একমাত্র ব্রত হল অন্যদের ঝগড়া উসকে দেওয়া। মাছওয়ালার সঙ্গে ক্রেতার ঝগড়া হলে তিনি এই বয়সেও বীরের মতো তার মধ্যে ঢুকে পড়েন, এবং পর্যায়ক্রমে একবার বিক্রেতা এবং একবার ক্রেতাকে যুক্তি সরবরাহ করে ঝগড়াটাকে পাকিয়ে তোলেন, যতক্ষণে না মাছওয়ালা আঁশবটি তুলে “তবে রে, শালা!” বলে লাফিয়ে উঠে কাস্টমারকে তাড়া করছে। এই দৃশ্যটা দেখাই নরেন গাঙ্গুলির জীবনের একমাত্র ব্রত। বলতে গেলে, কলপুকুর নামের এই মফস্বলের নব্বই শতাংশ সফল ঝগড়াই নরেনবাবুর অপরিসীম পরিশ্রম এবং উদ্যোগের ফলাফল।
কিন্তু আজ তিনি ভুল জায়গায় খাপ খুলতে এসেছিলেন। দেবযানীর কথা শুনতে শুনতেই তিনি যে নিজের হাতের প্লাস্টিকের প্যাকেটটা চট করে আড়াল করলেন, সেটা চোখ এড়ায়নি গোপীনাথের। অত্যন্ত নরম গলায় বিনীতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কাকার ব্যাগেও বুঝি ওই ন্যাদোশ মাছ? মালতীকেই কাটতে দেবেন?”
একটা ঢোক গিলে নরেন গাঙ্গুলি বললেন, “না হে, মালতির সামনে আজ বড্ড লাইন পড়ে গিয়েছে। যাই, যদি জলের ট্যাংকের নিচে যারা বসে, ওদের কাছে একটু তাড়াতাড়ি হয়।”
সুড়সুড় করে তিনি সরে পড়ার পর গোপীনাথ এতক্ষণে সাহস করে ভুরুতে প্রসেনজিতের মতো একটা ঢেউ খেলিয়ে তাকালেন দেবযানীর দিকে। তিনি এখনও অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে রয়েছেন নরেনবাবুর হনহন করে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্যটার দিকে।
“এইজন্যেই ছোট পিসেমশাই বলেছিলেন, খবরদার বুজু, উদ্বাস্তু কলোনীতে বিয়ে করতে যাস নে! ওখানে চারিদিকেই ছোটলোক!” চাপা গলায় বললেন দেবযানী। তারপর হিম দৃষ্টিতে গোপীনাথের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এদের নিয়েই থাকো তুমি। আমাকে আজ বিকেলেই গাড়ি ডেকে দেবে। আমি ভবানীপুর চলে যাব।”
এইবার গোপীনাথবাবুর মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাসে অন্তত একবার রাগ করে ভবানীপুরের বাপের বাড়িতে চলে যাওয়াটা দেবযানীর কুড়ি বছরের অভ্যাস। এমনিতে অত্যন্ত খুশির খবর হলেও প্রচুর খরচা হয় এতে, কারণ তিনি ট্রেনে বা বাসে ওঠেন না। আজেবাজে লোকেরা ওরকম ঘাড়ের উপর চেপে এলে তাঁর নাকি বেজায় গা-ঘিনঘিন করে, শ্বাসকষ্ট হয় রীতিমতো। কাজেই কলপুকুর থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত তিনি ভাড়া করা গাড়িতেই যান। গোপীনাথবাবু ক্যানেল স্ট্রিটের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে মাঝারি মাপের চাকরি করেন। স্বভাবতই গাড়ি কেনা হয়নি তাঁর। বহু কষ্টে ভাড়াবাড়ি থেকে নিজের একটি বাড়ি করে উঠে আসতেই তাঁর আজীবনের সম্বল বিসর্জন দিতে হয়েছে। ফলে দেবযানী যখন রেগেমেগে বাড়ি ছেড়ে চলে যান, তখন স্বাধীনতার অনাবিল উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও গোপীনাথের একটু মন খারাপ হয়। না-হোক হাজার টাকা খরচ আছে এই গৃহত্যাগের জন্য। সম্ভবত আজ সেই টাকাটা খরচ হবে।
“আহা, এত রাগারাগি করছ কেন? তোমাকে তো খেতে বলিনি! ওই দ্যাখো, ডানদিকের দু’নম্বর দোকানটায় চমৎকার পার্শে উঠেছে। ওই কিনে নিচ্ছি আরও চারখানা। সোমা রেঁধে দেবে।”
ইতিমধ্যেই অবশ্য গোপীনাথবাবু হিসেব করে ফেলেছেন, ওই চারটে মাছ কিনতে তাঁর বড়জোর একশো টাকা খরচ হবে। গৃহত্যাগের খরচের তুলনায় সেটা কিছুই নয়।
“মাছটা বড় কথা নয়। আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুমি কিনলে কী করে? এত সাহস হল কী করে তোমার?” আগুনে গলায় বললেন দেবযানী।
ব্যাপারটা বাজারেই মিটিয়ে ফেলার জন্য নরম গলায় গোপীনাথ বললেন, “আসলে বাবার কথা খুব মনে পড়ে গেল গো! বড্ড ভালোবাসত এই মাছটা খেতে।”
দেবযানী দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, “যে মানুষ সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখে ফিরে এসে ছেলের নাম রাখে গোপীনাথ, তার পক্ষে এই মাছই ঠিক আছে। বাঘা রাখলে আরও ভালো হত।”
গোপীনাথবাবু একটা দুঃখিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেবযানী আজ তাঁর অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে আঘাত করেছেন।
কথাটা খুবই সত্যি। ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসে তাঁর বাবা হেমকান্ত সেন ছেলে হওয়ার পর তার নামকরণ করেছিলেন গোপীনাথ। অনিবার্যভাবেই তাঁর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল গুপী। একটি বাঘার আশায় এরপর হেমকান্তের পরপর তিনটি মেয়ে হয়। ফলে দুই ছেলেকে একসঙ্গে গান-বাজনা করতে দেখার যে স্বপ্নটা হেমকান্তর মনে বাসা বেঁধেছিল, তা আর ইহজীবনে পূরণ হল না।
মাঝখান থেকে সারা জীবন ধরে এই নামটা বহন করতে হল গোপীনাথবাবুকে। ইস্কুলে থাকতে ক্লাসের বদমাইশ ছেলেরা তাকে দেখলে ছড়া কাটত, ‘আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটি পাবেন গুপি,’ কিংবা ‘আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপি হাসছে কেন খালি?’ উপেন্দ্রকিশোর ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ লিখেছেন, সুকুমার রায় ‘নন্দ গুপি’ লিখেছেন এবং সত্যজিৎ রায় ঠাকুরদার গল্প নিয়ে ফিলিম বানিয়েছেন। গোপীনাথবাবু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন এক রায়বাড়িই তাঁর জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।
বড় হয়ে যখন তিনি অফিসে জয়েন করলেন এবং মাঝারি গোছের একজন কর্মচারী হয়ে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল— অবশেষে বুঝি তাঁর শাপমোচন ঘটল। এবার আর তাঁর নাম নিয়ে পিছনে লাগার সাহস হবে না কারোর।
দুর্ভাগ্যবশত, ডেলি প্যাসেঞ্জারদের আশ্চর্য রসবোধ সম্পর্কে তাঁর ধারণাই ছিল না। আটটা ছেচল্লিশের ডাউন ট্রেন ধরার সময় যে কামরার ভিতর থেকে তাঁকে দেখামাত্র সম্মিলিত কণ্ঠে ‘মোরা গুপি-বাঘা দুজন ভায়রাভাই’ গাওয়া হতে থাকবে, এটা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। জানলার পাশের সিটের পাকাপাকি অধিকারী দত্তবাবুর কুশল জিজ্ঞাসার প্রথম লাইনটাই ছিল, ‘আজ বাঘাকে আনলেন না?’
আর কী বলব, এই সেদিনও রেকিট বেঙ্কাইজারের ক্যাশিয়ার বিশ্বাসদা, তিনিও গোপীনাথবাবুর বহুকালের সহযাত্রী, করুণ মুখ করে তাঁকে বললেন, “না মশাই, আর যাই হোক, আপনাকে স্বনামধন্য বলতে পারছি না। বাঘা হিসেবে নাহয় আপনি ওই চঞ্চলকেই রেখে দিন। ও ছোঁড়া ট্রেনের দেওয়াল পিটিয়ে খাসা তাল তুলতে পারে। কিন্তু গানটা তো আপনাকে গাইতে হবে! কই, ধরুন দেখি— মহারাজা, তোমারে সেলাম!”
এই মাঝবয়সে এসেও এসব কথা শুনলে গোপীনাথ মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করেন, আর মনে মনে রায়বাড়িকে গালাগাল দিতে থাকেন। এদিকে আবার শৈশবে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার আর লীলা মজুমদার, কৈশোরে ফেলুদা, এবং বড় হয়ে ইস্তক সত্যজিতের সিনেমাগুলো তাঁকে এমনই সম্মোহিত করে রেখেছে যে, বেখেয়ালে গালাগালি করেই তিনি আঁতকে উঠে জিভ কাটেন; এবং মনে মনে বলতে থাকেন, “পাপ দিও না ঠাকুর! রাগের মাথায় ভুল করে বেরিয়ে গিয়েছে।”
সব মিলিয়ে গোপীনাথের জীবন যে খুব একটা সোজা পথে চলেনি, সেটা আশা করছি এতক্ষণে স্পষ্ট করতে পেরেছি আমরা। আর সেই কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিয়েছিল তাঁর বিয়ে।
ভবানীপুরের প্রখ্যাত ও বনেদি ‘দাশগুপ্ত বাড়ি’ যে আদতে একটি তালপুকুর, সেটা গোপীনাথবাবু মেয়ে দেখতে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন। প্রকাণ্ড কিন্তু জরাজীর্ণ বাড়ি, একুশজন শরিকের একুশখানা ঘর; সেসব ঘরে বাইরে থেকে এক লাফে সরাসরি খাটে উঠে পড়তে হয়। রান্না হয় খাটের নিচে। কত্তারা সব খাটে বসে রাজা-উজির মারেন, ‘ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন টুয়েন্টিফোর, এ বাড়িতে ছোটলাট এসেছিলেন চা খেতে’— এইসব গপ্পো ছাড়েন, আর বাড়ির বউরা হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ে চারাপোনার ঝোল বসাতে। এজমালি কলঘর, উঠোনে পুরু শ্যাওলা। এ তালপুকুরে যে ঘটি ডুববে না, ওই উঠোনে পা দিয়েই পিছলে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন গোপীনাথ সেন।
তবে কী, দেবযানীর মুখে তখন এমন একটা লাবণ্যময় মায়া ছিল, এমনভাবেই পশ্চিমের রোদ— বইয়ে যার নাম লেখা থাকত ‘কনে দেখা আলো’—এসে পড়েছিল তাঁর মুখে, যে…
এক কথায়, বিনা বাক্যব্যয়ে দেবযানীকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন গোপীনাথ।
এবং সেই থেকে তাঁর অনন্ত কারাবাস শুরু হয়েছিল। বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলে তাঁর বিচারের কোনও আশা নেই, মুক্তিরও কোনও তারিখ নেই। বউয়ের গম্ভীর ব্যক্তিত্বের সামনে কেঁচো হয়ে গিয়েছিলেন গোড়াতেই। হয়তো সেই কারণেই সন্তানাদিও হয়নি তাঁর।
তবে কী, এই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে এসে এসব নিয়ে হাহাকার করার কোনও মানে হয় না। গোপীনাথবাবুও বহুকাল হল এসবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সুখেদুঃখে একরকম ভালই আছেন…
ছিলেন বলাই ভালো।
এই অতীতকাল ব্যবহারের কারণ আর কিছুই নয়। আজকে তাঁর সাধের ন্যাদোশ মাছ চারটে আর কোনমতেই সোমার হাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। বাজারের ব্যাগটা রান্নাঘরের দরজায় সাবধানে নামিয়ে রেখে হাত ধুতে বাথরুমে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরে এসে দেখলেন, মাছ চারটে চেটেপুটে খাচ্ছে দেবযানীর পোষা বেড়াল মিউ। পাশেই অগ্নিগর্ভ চাউনিতে সেই বীভৎস দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন খোদ দেবযানী।
কয়েক মুহূর্ত বজ্রাহত হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে গোপীনাথ হনহন করে হেঁটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দেবযানী নয়, আজ তিনিই গৃহত্যাগী হবেন।
“একটার মধ্যে না ফিরলে লাঞ্চ বন্ধ।” পিছন থেকে কঠোর স্বরে ঘোষণা করলেন দেবযানী। রাগের মাথায় ফিরেও তাকালেন না গোপীনাথ।
ভয়ানক রেগেমেগে মোড়ের মাথার কালুর চায়ের দোকানে গিয়ে বসলেন গোপীনাথবাবু। কিন্তু এখানে ইতিমধ্যেই রোববারের আড্ডা জমে উঠেছে। মুশকিল হল, এত রকম আশকথা পাশকথার মধ্যে রাগ ধরে রাখা একটু সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই চায়ের অর্ডার দিয়েও সেটা ক্যান্সেল করে উঠে পড়লেন তিনি। তারপর গটগট করে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলেন কলপুকুর নামের বিশাল দিঘীটার পাশে, যার নামে এই জায়গাটার নাম হয়েছে।
কয়েকদিন আগেই বর্ষা থেমে গিয়েছে। আকাশের রং চমৎকার নীল। কলপুকুরের জলও তাই আজ সামান্য নীল-রঙা বলে মনে হচ্ছে। অন্যদিন হলে নির্ঘাত গোপীনাথবাবু এতক্ষণে মাথা নেড়ে তুড়ি দিয়ে ‘আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে’ গানটা ধরে ফেলতেন; কারণ আজকাল আর পুকুরপাড়ে এসে কেউ বসে থাকে না। কিন্তু আজ তিনি সত্যি সত্যিই সাংঘাতিক রেগে গিয়েছেন। এতটা দেবযানী না করলেও পারত।
আর ঠিক এই সময় তাঁকে সামান্য চমকে দিয়ে বেজে উঠল পকেটের মোবাইলটা।
বাপ্পা ফোন করেছে। বাপ্পাদিত্য তাঁর ছোটবেলার বন্ধু। এখন নানান ধরনের ব্যবসা করে। সব খবর ঠিক জানেন না গোপীনাথ, তবে যে হারে বাপ্পা গাড়ি পাল্টায়, তাতে বুঝতে অসুবিধা নেই, ব্যবসা ভালই চলছে। থানার বড়বাবু থেকে এম.এল.এ. পর্যন্ত সবাইকে যে বাপ্পা নাম ধরে ডাকে আর যখন-তখন ফোন করার ক্ষমতা রাখে, সেটা গোপীনাথবাবু নিজের চোখেই দেখেছেন।
অনিচ্ছা সত্বেও ফোনটা রিসিভ করলেন গোপীনাথবাবু, “হ্যাঁ রে, বল। খবর কী?”
“এই চলছে। তোর বাড়িতে এসেছিলাম। শুনলাম তুই বেরিয়েছিস।”
কারণটা আর ভাঙলেন না গোপীনাথ। হ্যা হ্যা করে হাসবে হয়তো বাপ্পা। গম্ভীর গলায় বললেন, “কোনও দরকারে এসেছিলি, না এমনিই?”
“ঠিক দরকার না… আসলে আমি একটা লোক খুঁজছি, বুঝলি!” বাপ্পা বলল, “খুবই দরকার। তুই তো হরেক রকমের লোকজনের সঙ্গে মিশিস, ট্রেনে-বাসে যাতায়াত করিস, তাই ভাবলাম যদি কাউকে…”
“কীসের লোক? তোর ব্যবসার কাজে লাগবে?”
“হ্যাঁ, রে। পাহাড়ে একটা হোমস্টে নিয়েছি লিজে। এমনিতে যাদের বাড়িতে হোমস্টে হয়, তারাই দেখভাল করে। এখানে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্যেই একটা বিশ্বাসী লোক দরকার।”
ট্রেনে ‘বারো ভূতের সঙ্গে’ যাতায়াত করাটা দেবযানীর পছন্দ নয় বলে গোপীনাথবাবু বছরে একবার গাড়ি ভাড়া করে দিঘা যান। পাহাড়ে হোমস্টে— ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না তিনি। বললেন, “হোমস্টে কী বস্তু? হোটেল ধরনের কিছু নাকি, রে?”
“উমমম্… বলতে পারিস। পাহাড়ের গাঁয়েগঞ্জে ইদানিং স্থানীয় মানুষদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।”
“এই খেয়েছে! খামোখা পরের বাড়িতে থাকতে যাব কেন? তারাই বা দেবে কেন?” গোপীনাথবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে।
“ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। বাড়ির একটা অংশ এরা ছেড়ে দিচ্ছে টুরিস্টদের জন্য, নইলে এক্সট্রা কয়েকটা ঘর বানিয়ে দিচ্ছে। ভাড়া দেওয়া হয় একটা ঘর আর টয়লেট। খাওয়ার দায়িত্বও ওদের। মাথাপিছু থোক একটা টাকা নিয়ে নেওয়া হয়।”
“আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছি,” বললেন গোপীনাথবাবু, “কিন্তু টুরিস্টরা হোটেল ছেড়ে সেখানে উঠতে যাবে কেন?”
“গ্রামেগঞ্জে তো আর হোটেল পাওয়া যাবে না! বলল বাপ্পা, “অথচ আমাদের এদিককার পাহাড়ের বহু গ্রাম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দুর্দান্ত ভিউ পাওয়া যায়। দার্জিলিংয়ের হই-হট্টগোলটাও নেই। যারা নিরিবিলি পরিবেশে বসে শান্তিতে পাহাড়ের রূপ দেখতে চায়, তারা আজকাল হোমস্টেতেই যাচ্ছে।”
ব্যাপারটা মন্দ লাগল না গোপীনাথবাবুর। সেই কোন ছেলেবেলায় একবার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং গিয়েছিলেন। তা সে কথা তাঁর মনেও নেই। কাজেই একটা নিরিবিলি গ্রামের বাড়িতে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে দার্জিলিং চা খাওয়ার ব্যাপারটা তাঁর পছন্দই হল। নাহয় তাঁর কপালে নেই। তাই বলে কি অন্য লোকেরা যাবে না?
“তার মানে সোজা করে বললে, তুই হোমস্টের জন্য একজন ম্যানেজার খুঁজছিস, তাই তো?” জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।
“একদমই তাই। কঠিন কাজ তো কিছু নয়। টুরিস্টদের খেয়াল রাখা। রান্নাবান্না করার জন্য লোক রাখাই আছে। ক্লিনিং স্টাফ আলাদা। ম্যানেজারের কাজ শুধু সব নিয়ম মেনে চলছে কিনা— সেদিকে লক্ষ রাখা।”
“এখানে তো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের বিশেষ দরকার দেখছি না!”
“নেইও। উটকো ঝামেলা সামলানোর মেন্টালিটিটা থাকলেই হবে; কারণ টুরিস্ট নানারকম, আর তাদের আবদারের কোনও সীমা নেই।”
মনে মনে একটু হাসলেন গোপীনাথবাবু। যে ঝামেলা তিনি প্রতিদিন সামলে চলেছেন, তার চাইতে বেশি ঝামেলা কোন টুরিস্ট করতে পারে?
“কীরকম বয়সের লোক চাইছিস?” এই প্রশ্নটা না করলেই নয়, কারণ সত্যিই ট্রেনে-বাসে আর অফিসে নানা বয়সের লোকের সঙ্গে আলাপ করতেই হয় গোপীনাথবাবুকে।
“অ্যাকচুয়ালি আমি খুজছিলাম আমাদের বয়সী একটা লোক। পিছুটান কম থাকে। আর তাছাড়া, এই বয়সে এসে ধৈর্যটা বেশ পোক্ত হয়। ওটা আবার এই ব্যবসার প্রধান মূলধন কিনা!” হাসতে হাসতে বলল বাপ্পা।
এইবার হঠাৎ গোপীনাথবাবুর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। বাপ্পার ওই শেষ কথাটা তাঁর মাথায় একটা সাংঘাতিক আইডিয়ার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সেটাকে কাজে পরিণত করতে হলে আরও একটু ভাবনাচিন্তা করার দরকার।
কোনক্রমে নিজের উত্তেজনাটাকে গিলে নিয়ে ঠাণ্ডা গলায় গোপীনাথবাবু বললেন, “আমাকে একটু সময় দে। আজ রাতের মধ্যেই তোকে ফোন করছি।”
২
এই কথপোকথনের ঠিক তিনদিন পর ভোরে যখন গোপীনাথবাবু এসে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামলেন, তখন তাঁকে দেখে আর চেনার উপায় নেই। ইতিমধ্যেই হেয়ার স্টাইল পাল্টেছেন তিনি, অর্থাৎ বাঁদিকের বদলে সিঁথিটা ঘুরিয়ে নিয়েছে ডানদিকে। আর সবচাইতে বড় কথা, এত বছরের সাধের গোঁফটা বিসর্জন দিয়েছেন। পরনেও আর আগের সেই ঢোলা প্যান্ট বা সুতির ফুলশার্ট নেই। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে আছে ব্লু জিন্সের প্যান্ট, আর সাদার উপরে লাল স্ট্রাইপ দেওয়া ফুল-হাতা টিশার্ট। সব মিলিয়ে জেল্লা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, তাঁকে চেনাই মুশকিল।
পাহাড়ে এখনও টুরিস্টদের ঢল নামেনি বলেই অনায়াসে দার্জিলিং মেলের টিকিটটা পেয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথবাবু। তার আগে যে কাজগুলো করতে হল, সেগুলো অবশ্য ঠিক অনায়াসে হয়নি। প্রথমত, দুপুরবেলা না খেয়ে এবং দেবযানীর সঙ্গে একটিও কথা না বলে ঝগড়াটাকে ঘোরালো করে তুলতে হল। এর ফলে বিকেলের মধ্যে ভবানীপুরে চলে যাওয়া ছাড়া দেবযানীর হাতে সম্মানরক্ষার অন্য কোনও উপায় বাকি রইল না। চারটের সময় রাগে ফুলে ওঠা মুখ নিয়ে গোঁসাঘর থেকে দেবযানী বেরিয়ে এলেন। সোজাসুজি বাইরের ঘরে সোফায় বসে টিভিতে মগ্ন গোপীনাথবাবুকে ডেকে থমথমে গলায় বললেন, “জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছি। একটা ট্যাক্সি দেখে দাও।”
একবারও দেবযানীর দিকে না তাকিয়ে মোবাইল তুলে সৌরভকে ডেকে নিলেন গোপীনাথবাবু। এর আগে অন্তত কুড়িবার সৌরভ বৌদিকে ভবানীপুরের বাপের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। তার প্রায় প্রতি মাসের একটা বাঁধা রোজগার এটা। কাজেই বিনাবাক্যব্যয়ে পনের মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল সে। আড়চোখে গোপীনাথবাবুকে আরও একবার ভস্ম করে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন দেবযানী।
রাগ দেখানোর জন্য এতক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থাকার ফলে হাতে-পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গিয়েছিল গোপীনাথবাবুর। এইবার এক লাফে উঠে পড়ে প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি। চট করে এক পাক ঘুরে নেচে নিলেন, যাতে পায়ের আর হাতের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে যায়। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। সবার আগে কিছু খাওয়া দরকার। ফ্রিজ থেকে মাছ-ভাত পাওয়া গেল। সাঙ্ঘাতিক খিদে পেয়ে গিয়েছিল। তারপরের কাজ হল বাপ্পাকে ফোন করে কনফার্ম করা। কাজটা কঠিন ছিল, কারণ তখন বাপ্পা গাড়ি চালাচ্ছিল। তাঁর কথা শুনে আর একটু হলেই রাস্তার পাশের খানায় পড়ে যেত গাড়িটা।
“বাপ্পা, শোনা যাচ্ছে, রে?”
“দিব্যি যাচ্ছে। বল। বললি যে রাতের দিকে ফোন করবি?”
“উঁহু! ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি, তাই আর দেরি করলাম না। ঠিক করেছি— তোর ওই চাকরিটা আমিই নেব।”
“ক্কী! কী উল্টোপাল্টা বকছিস? আজকাল নেশা-টেশা করছিস নাকি দিনেমানে? তোর তো এসব দোষ ছিল না!”
“ভেবেচিন্তে, সুস্থ অবস্থায় বলছি। আমি আর এই নিত্যদিনের অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না রে ভাই! বয়েস হচ্ছে। দু’দিন পর হয়তো পটকে যাব এমনিতেই। শেষ ক’টা দিন অন্তত শান্তিতে থাকার একটা সুযোগ দে! তুই না আমার ছেলেবেলার বন্ধু?” বলতে বলতে গলাটাকে সাধ্যমতো কাঁদো কাঁদো করে ফেললেন গোপীনাথ।
তবু বাপ্পা প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। ‘আরও কয়েক বছর তো চাকরি বাকি আছে তোর’— ইত্যাদি বলেছিল। কিন্তু গোপীনাথ তাকে রাজি করিয়ে ফেললেন একটি মোক্ষম চাল দিয়ে।
“ভাবতে পারিস বাপ্পা, সাধ করে কিনে আনলাম বাবার ফেভারিট মাছ, আর সেই মাছ কিনা বেড়াল ডেকে খাইয়ে দিল?” তাঁর নিজেরও যে মাছটা দেখে বেজায় লোভ হয়েছিল, সেই কথাটা বেমালুম চেপে গেলেন তিনি।
আরও খানিক গাঁইগুঁই করার পর বাপ্পা বলল, “বেশ। তবে আমার একটা কথা শোন। এক্ষুনি রিজ়াইন দিতে যাস না চাকরি থেকে। আমি তোকে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপাতত মাস খানেকের জন্য চলে যা। এত বছর চাকরি করছিস, ছুটি তো কিছু জমেছে নিশ্চয়ই। এক মাসের ছুটি নিয়ে নে। ওখানে গিয়ে হালচাল দ্যাখ, তোর পোষাচ্ছে কিনা দ্যাখ। দু’দিনের জন্য পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া আর মাসের পর মাস ওখানে থাকার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। এই বয়সে তুই সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করে উঠতে পারবি কিনা, সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন।”
তিনি যে দু’দিনের জন্যও কখনও পাহাড়ে যাননি, সে কথাটা এখন আর তোলার কোনও মানে হয় না। তবে কথাটা পছন্দ হল গোপীনাথবাবুর। অকারণেই ঘাড় নাড়লেন তিনি। সেটা যে বাপ্পা দেখতে পাচ্ছে না, সেটা তাঁর মাথায় রইল না।
“তার চেয়েও বড় কথা হল, সবাই সব কাজ পারে না গুপী। হয়তো পনেরো দিন পর তোর মনে হল— নাহ্, এটা আমি পারব না। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে মাতাল টুরিস্টের আবদার সামলানো আমার কম্ম নয়। এমনটা মনে হতেই পারে— কোনও অন্যায় নেই এর মধ্যে। কাজেই আপাতত তুই একটা টেস্টিং কল দে। পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে দে। আমি এদিকে লোক দেখছি। তোর যদি অসুবিধা না হয়, তুই থেকে যাবি। আর আমার যদি অসুবিধা হয়, আমি পাহাড়ে উঠে তোকে মারতে মারতে নামিয়ে নিয়ে আসব।”
আর নামিয়ে নিয়ে আসা মানে যে কী, তা গোপীনাথবাবুর চাইতে ভালো করে কে জানে?
“ঠিক আছে,” এবার একটু দোনোমনা করে বললেন গোপীনাথবাবু। বাপ্পা একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছে বটে, কিন্তু তারই সঙ্গে তাঁর উৎসাহের আট আনা কমিয়ে দিয়েছে।
তবে পরামর্শটা খাসা। গোপীনাথবাবু সেটুকু সাদরে গ্রহণ করলেন; এবং পরদিনই অফিসে গিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে এক মাসের ছুটি বাগিয়ে ফেললেন। এই এক মাসের স্যালারি তিনি পাবেন। তারপরও যদি ছুটি এক্সটেন্ড করতে হয়, তাহলে উইদাউট পে হবে।
মনে মনে হাসলেন গোপীনাথবাবু। তিনি ধাতুগতভাবেই কিছুটা কৃপণ মানুষ। এতদিন চাকরি করে যা জমিয়েছেন, তার অধিকাংশটাই আছে অন্য একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, যার হদিস তিনি ছাড়া আর কেউ রাখে না। দেবযানীর এসব ব্যাপারে আগ্রহও নেই। বাড়ি করতে গিয়ে তার অনেকটাই খরচ হয়ে গিয়েছে বটে, তবে যা আছে, সেটাও কম নয়। বরং স্যালারি অ্যাকাউন্টে পড়ে আছে সামান্য কিছু টাকা। শ্রীমতি দেবযানী সেন এবার টের পাবেন— এই লোকটার থাকা আর না থাকার মধ্যে ঠিক কতটা পার্থক্য।
আর এর পরের ধাপ তো আমরা আগেই জেনে গিয়েছি। রাতের দার্জিলিং মেল ধরে সোজা এন.জে.পি. স্টেশন। বাইরেই তাঁর জন্য একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। বাপ্পা ব্যবস্থা সমস্তই করে রেখেছে। খুশি মনে তাগড়াই গোছের সুটকেসটা ডিকি-তে চালান করে দিয়ে ড্রাইভারের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসলেন গোপীনাথ সেন। আজ তাঁর জীবন বদলে যেতে চলেছে। এখন থেকে তিনি আর তিন নম্বর ক্যানাল স্ট্রিটের দুশোটা অফিসের মধ্যে একটার মাঝারি গোছের কর্মচারী নন। ‘তিনখোলা মেঘমা হোমস্টে’-র ম্যানেজার। ছোকরা ড্রাইভারটিও যে তাঁকে ক্রমাগত ‘স্যার স্যার’ করে চলেছে, সেটা খেয়াল করে তাঁর চওড়া হাসিটা আরও দু’ইঞ্চি চওড়া হয়ে গেল।
কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তার হাঁ হয়ে যাওয়া মুখটা আর বন্ধ হওয়ার উপায় রইল না; কারণ এইবার তাঁর সামনে ফুটে উঠতে শুরু করেছে হিমালয়। চোখ ছানাবড়া করে সেই আশ্চর্য দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন গোপীনাথবাবু। প্রথম পাহাড় দেখার প্রচণ্ড আঘাতে এমনকী ‘এবারে দ্যাখো গর্বিত বীর, চির তুষারমণ্ডিত শির’ গানটাও তাঁর মনে রইল না।
এই মুগ্ধতা চরমে পৌঁছল হোমস্টেতে পৌঁছে। তিনখোল আসলে ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রামের নাম। খুব বেশি হলে খান ত্রিশেক পরিবার বাস করে গ্রামটায়। তাদেরই মধ্যে একজনের বাড়ির সামনের খানিকটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে মেঘমা হোমস্টে। তিনকোনা লাল ছাদ আর সবুজ কাঠের দেওয়ালের চারটে মাত্র কটেজ, একেকটা কটেজে দুটো করে ঘর। সাকুল্যে ষোলজন ট্যুরিস্ট থাকতে পারবেন একবারে। ইতিমধ্যেই গোটা উঠোনটা সাজিয়ে তোলা হয়েছে ফুলগাছ দিয়ে।
এই কটেজগুলোর সারিটার ঠিক পিছনেই আর একটা কটেজ। এটাই ম্যানেজারের বাসস্থান। অর্থাৎ আপাতত গোপীনাথবাবুই সেটার মালিক।
খানিকক্ষণ বড় বড় চোখে ক্ষুদে কটেজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন গোপীনাথবাবু। জীবনে কখনও এরকম দৃশ্য চোখে পড়েনি তাঁর। কটেজটার সামনে এক ফালি বারান্দা। পেছনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ফুলের বাগান। তারপর মালিকের ছোট বাড়িটা। তার ঠিক পেছন থেকে শুরু হয়েছে চা-বাগান। একেবারে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেই সবুজ একটানা ঢেউ। তার পেছনে পাইনের জঙ্গল, আর তারও অনেক পেছনে ঘন নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা।
গোপীনাথবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর চোখে জল চলে আসছে। নিতান্তই গিন্নিকে টাইট দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। আর এখন তাঁর মনে হচ্ছে, সারাটা জীবন নিছক শান্তি রক্ষা করতে গিয়ে অমূল্য দিনগুলো তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালির মতো গলে পড়ে গেছে। কোথাও যাওয়া হয়নি, কিচ্ছু দেখা হয়নি।
ঘরের ভেতরে না ঢুকে বারান্দাটাতেই চেয়ার টেনে বসে পড়লেন গোপীনাথবাবু। মনে হচ্ছে, ঘরে ঢুকলেই যেন কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে। কেন যে এ কথাটা তাঁর মনে হল, সেটা অবশ্য বুঝতে পারলেন না তিনি।
ইতিমধ্যে হোমস্টে-র আসল মালিক নিজেই চলে এলেন চায়ের কাপ হাতে। বেঁটেখাটো মাঝবয়সী মানুষ; এককালে আর্মিতে ছিলেন, বয়স ষাটের কাছাকাছি। এঁর ভাই কলকাতায় চায়ের ব্যবসা করেন। সেই সূত্রেই নাকি বাপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের। নাম মিংমা তামাং। এর আগে কখনও একটা নামের মধ্যে দুটো অনুস্বার দেখেছেন কিনা, কিছুতেই মনে করতে পারলেন না গোপীনাথবাবু। তিড়িংবিড়িং শব্দে দুটো অনুস্বার আছে বটে, কিন্তু এরকম নাম কেউ রাখতে রাজি হবে বলে তো মনে হয় না।
ভদ্রলোক বেজায় আলাপী; চা খাওয়ার পর পুরো গ্রামটা ঘুরিয়ে আনলেন গোপীনাথবাবুকে। পাহাড়ের ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা গ্রাম। অসম্ভব নির্জন, অসম্ভব রূপবান। গোটা গাঁয়ে একটা মোমো আর চায়ের দোকান ছাড়া আর কোনও দোকান নেই। সমস্ত দরকারী জিনিসপত্র পেডং থেকে নিয়ে আসতে হয়। তবে গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ গাড়ি চালায়, ফলে জিনিসপত্র নিয়ে আসার ব্যাপারটা এখানে কোনও সমস্যা নয়। মেয়েরা মূলত খেতির কাজ করে।
এই সব কথাই ঘুরতে ঘুরতে মিংমা বুঝিয়ে দিলেন গোপীনাথবাবুকে। হোমস্টের কাজও বিরাট ঝামেলার কিছু নয়। সেটাও মোটের উপর মিংমাই বুঝিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে বলে দিলেন— তিনদিন পর থেকে গেস্ট আসা আরম্ভ হবে। এর মধ্যেই যেন গোপীনাথবাবু কাজকর্ম সব ভালোভাবে বুঝে নেন।
কুক এবং অন্য একজন কর্মচারী ইতিমধ্যেই জয়েন করে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর আসার খবর পেয়ে তারা দেখা করে গেল। দুপুরের খাবারটা অবশ্য খেতেই হল মালিকের বাড়িতে। গরম গরম ভাত, ডাল, একটা নেপালি সবজি আর মুরগির ঝোল দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলেন গোপীনাথবাবু। বড় হয়ে ইস্তক এই প্রথম দূরপাল্লার ট্রেনে রাত কাটিয়েছেন তিনি। অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে। ঘুম হয়নি মোটেই।
ঘুম ভাঙার পর আরও একবার একা একাই গ্রামটাকে চক্কর দিয়ে এলেন গোপীনাথবাবু। চায়ের দোকানে বসে চা খেলেন। বহুদিন পর গোল্ড ফ্লেক কিনে ফেললেন এক প্যাকেট। আপাতত বেশ কিছুদিন আর প্রত্যেকটা ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে না তাঁকে।
সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পায়ে পায়ে নিজের কটেজটার দিকে ফিরে চললেন তিনি। দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠছে আলো। পশ্চিম আকাশে এখনও লেগে রয়েছে একটুখানি সিঁদুরে রং। আর সব কিছুর উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে রঙের খেলা। তার বর্ণনা দেওয়া মানুষের ভাষার সাধ্য নয়।
হঠাৎ গোপীনাথবাবু আবিষ্কার করলেন, বহু, বহু বছরের মধ্যে কখনও এমন নির্ভার বোধ করেননি তিনি। মানুষের মন যে এমন ফুরফুরে হয়ে থাকতে পারে, এমন কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না তাঁর!
সন্ধের পর চারিদিকে নিঝুম হয়ে গেল। হোমস্টের কটেজগুলো অন্ধকার। বাইরের রাস্তাটায় টিমটিম করে কয়েকটা আলো জ্বলছে অনেকটা দূরে দূরে। কেমন একটা পরিপূর্ণ মন নিয়ে বারান্দায় চুপ করে বসে রইলেন তিনি।
এমন সময় একটা গলা খাঁকারির শব্দ শুনে সেদিকে ফিরে তাকালেন গোপীনাথবাবু। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ তুলে মিংমা উঠে আসছেন বারান্দায়।
“এরকম একা বসে আছেন কেন?” সামান্য ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন মিংমা, “বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগছে না তো?”
নিজের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি গোপীনাথবাবু। বাড়িতে থাকলে এই সময়টায় তিনি সিরিয়াল দেখতেন, যদি অবশ্য যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ফিরতে পারতেন।
আজ এই পাহাড় আর জোনাকি জ্বলা পাইনের জঙ্গলের মধ্যে বসে সেই কথাটা পর্যন্ত কেমন একটা বেখাপ্পা মনে হল তাঁর। কাজেই তাড়াতাড়ি বললেন, “সে বয়েস কি আর আছে মিস্টার তামাং? আসুন, আপনার সঙ্গেই বরং গল্প করা যাক।”
মিংমা তার ডানহাতটা তরোয়াল চালানোর ভঙ্গিতে একবার চালিয়ে দিয়ে চোখ কুঁচকে হাসলেন, “প্লিজ কল মি মিংমা, স্যর। তবে একটা কথা কী— সন্ধ্যের পরে আমি আবার শুধু মুখে গল্প করতে পারি না। জাস্ট ওয়েট ফর এ মিনিট।”
ঠিক এক মিনিট না হলেও, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গোপীনাথবাবুর সামনের টেবিলটায় নেমে এল সিকিম রামের বড়সড় একটা বোতল, দু’খানা গ্লাস, জল, মায় চিপসের প্যাকেট।
একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে গোপীনাথ ভাবলেন, আসলে তিনি এতদিনে জীবন শুরু করলেন।
বারো বছর আগে এক শীতের সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধবের অসংখ্য অপমানজনক কথায় রেগেমেগে এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। রাত আড়াইটে পর্যন্ত তাঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। দেবযানী তাঁকে ঢুকতে দেননি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বলেছিলেন, “স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। সন্ধ্যেবেলায় আড্ডা মারতে পাঠিয়েছি মানে তুমি মদ খেয়ে ফিরবে? মাতাল-দাতাল মানুষ ড্রেনে পড়ে থাকলেই মানায়। যেখান থেকে ওইসব ছাইভস্ম গিলে এসেছ, সেখানেই থাকো গে যাও। বাবা কোনদিন এসব ছুঁয়েও দেখেনি।”
এরপর থেকেই রাগ করে দেবযানীর বাপের বাড়ি যাওয়াটা তাঁর কাছে স্বাধীনতা দিবস হয়ে গিয়েছিল। আর স্বাধীনতা মানেই ছিল স্বেচ্ছাচারিতা; অর্থাৎ লো ভলিউমে রফি সাহেবের গান চালিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত আআস্তে আআস্তে হুইস্কির একটা নিব শেষ করা। ‘কভি খুদ পে, কভি হালাত পে রোনা আয়া।’ বোতল যখন শেষের পথে, ততক্ষণে তাঁর চোখে জল এসে যেত নিজের হালাতের কথা ভেবে।
কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে। রামের গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বড় একখানা গোল্ড ফ্লেক ধরালেন গোপীনাথ। আজ তিনি নির্ভয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারেন।
৩
“স্যর! ও স্যরজি!” চাপা গলায় কেউ ডাকছে বাইরে থেকে।
চোখ খুলতে প্রথম যে কথাটা গোপীনাথবাবুর মনে পড়ল, সেটা হল— আজ প্রথম হোমস্টেতে গেস্ট আসবে।
আপাতত বুকিংয়ের ব্যাপারটা বাপ্পার হাতেই রয়েছে। ফেসবুকে, সফর আর ভ্রমণের পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কাস্টমারদের জানানো হচ্ছে নতুন খোলা হোমস্টের ব্যাপারে। সেখানে যে ফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে, সেটা আছে বাপ্পার এক সহকারীর হাতে। গেস্টের সঙ্গে কথা বলে, সব ব্যাপার-স্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে এবং অ্যাডভান্সের টাকা নিয়ে বুকিং কনফার্ম করে সে খবর দিচ্ছে বাপ্পাকে। আর বাপ্পা সঙ্গে সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ করে সেই খবরটা পাঠিয়ে দিচ্ছে গোপীনাথবাবুর নতুন নম্বরে। অজ্ঞাতবাসের প্রথম ধাপ হিসেবে পুরনো ফোন নাম্বারটা স্বভাবতই বিসর্জন দিতে হয়েছে তাঁকে। আর এই নতুন নম্বরটা জানা আছে কেবল বাপ্পার। গোপীনাথবাবুর পলায়ন পর্বের সবটুকুই যেহেতু তার জানা আছে, কাজেই এখান থেকে ফোন নম্বর ফাঁস হয়ে যাবার কোনও আশঙ্কা নেই।
ডাক দিয়েছে রনিত থাপা। হোমস্টের তিনজন কর্মচারীর অন্যতম এবং কুক দিলীপের হেল্পার। দরজা খুলে দিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করে চটপট তৈরি হতে লাগলেন গোপীনাথবাবু। আজ কাজকর্ম একটু আগে শুরু করা চাই বইকি! প্রথম দিন বলে কথা।
“গুড মর্নিং, স্যরজি।!” আজ মিংমাও চলে এসেছেন এই সাত-সকালেই, “আজ তাহলে আমাদের ব্যবসা শুরু হয়ে যাচ্ছে?”
হাত বাড়িয়ে মিংমার ডান হাতটা চেপে ধরলেন গোপীনাথবাবু, তারপর এক গাল হেসে বললেন, “লেটস প্রে ফর দ্য বেস্ট।”
“গাড়ি চলে গেছে?” জিজ্ঞেস করলেন মিংমা।
“অবশ্যই! ঠিক রাত তিনটের ফোন করে দিয়েছিলাম বসন্তকে। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই।”
বলতে বলতেই বেজে উঠল গোপীনাথবাবুর ফোন। ফোনটা করেছে ড্রাইভার বসন্ত থাপা। গেস্টরা গাড়িতে উঠে গিয়েছে।
“নিশ্চিন্দি। এইবার ঘণ্টা খানেক পর ব্রেকফাস্টের কাজ শুরু করলেই হবে।” মাথা নাড়লেন গোপীনাথ, “আপনি বসুন। চা খান। আমি ঝট করে একবার ঘর দুটো দেখে আসি।”
মিংমা ভুরু কুঁচকে বললেন, “এই তো কাল মাঝরাতে একবার সব চেক করে এলেন। আবার দেখে আসার কী আছে? আগে চা খান ধীরেসুস্থে। সময় আছে ঢের। তাড়াহুড়োর কিচ্ছু নেই।”
“আহা, সে তো তিন পেগের পর। রাত নটার পর যে দেখাটা হয়, তার উপরে বেশি ভরসা না করাই ভাল।”
আজ অবশ্য একটাই বুকিং আছে। চারজনের বুকিং। দুটো ফ্যামিলি না একটা, সেটা গোপীনাথবাবুর ঠিকমতো জানা নেই। এক-একটা কটেজে দুটো করে ঘর। তেমনই একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছেন এঁরা। পরশু থেকে অবশ্য টানা প্রায় দিন পনেরোর জন্য সব কটা ঘরই বুকড্ হয়ে রয়েছে। তা পুজোয় বাঙালি যদি পাহাড়েই না এল, তাহলে আর সে কেমন বাঙালি?
মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে মিংমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন গোপীনাথবাবু। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সব ঠিকঠাক রয়েছে।
“আজকে তো একটাই কটেজের বুকিং আছে, তাই না?” জিজ্ঞাসা করলেন মিংমা।
“হ্যাঁ, একটা কটেজের দুটো ঘর।” বললেন গোপীনাথ, “নাম আর আধার কার্ড হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছে সিটি অফিস থেকে। দুজন ব্যানার্জি, তাদের বয়স ষাটের উপরে; আর দুজন চৌধুরী, তাদের বয়স ত্রিশের নিচে। এর থেকে এদের মধ্যে সম্পর্ক আন্দাজ করা আমার সাধ্যি নয়।”
“সম্ভবত প্রৌঢ় ব্যানার্জি দম্পতি, তাঁদের মেয়ে এবং জামাই। ছবি দেখে আমার তো তাই মনে হল।” স্বাভাবিকভাবেই হোমস্টের আসল মালিক মিংমাকেও বুকিংয়ের ডিটেলস পাঠানো হয়েছে, “তবে ওসব নিয়ে আমাদের ভেবে লাভ নেই। আপনার গ্রাউন্ড ওয়ার্ক যে চমৎকার হয়েছে, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। রুম খুব ভালোভাবে গুছিয়েছেন। কিচেনের জিনিসপত্র রেডি আছে। মনে রাখবেন মিস্টার সেন, এই পর্যন্তই আমাদের হাতে আছে। বাকিটা…”— এই বলে চোখের ইশারায় উপরের দিকটা দেখিয়ে দিলেন মিংমা।
চা খেতে খেতেই উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাতে হাত ঘষলেন গোপীনাথবাবু। নতুন একটা কাজ শুরু করতে চলেছেন তিনি, নতুন একটা জগতে প্রবেশ করতে চলেছেন। এটা ভেবে এই ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও দস্তুরমতো টেনশন হচ্ছে তাঁর। আর তার পাশাপাশি যেটা তৈরি হচ্ছে, সেটা হল নিজের প্রতি একটা ভালোবাসা, যেটা বহুকাল আগেই হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এটাও তাঁর খুব ভালো করেই জানা আছে, প্রথম বুকিংটা তিনি যদি ঠিকঠাক উৎরে দিতে পারেন, তাহলে বাকি যে শব্দটা দরকার আছে, সেটাও ঢুকে যাবে তাঁর পকেটে।
শব্দটা হল আত্মবিশ্বাস।
অন্তত প্রথম দফায় যে গোপীনাথবাবু এবং তাঁর দলবল একবারে ডিস্টিংশন পেয়ে উৎরে গেলেন, কিছুক্ষণ পরই সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকল না।
এগারোটা নাগাদ এসে পৌঁছল বসন্তের গাড়ি। আর সেই গাড়ি থেকে নেমে আসা মানুষেরা যে শুধু হোমস্টের পজিশন আর কটেজের বাহার দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেছেন, তা তাঁদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়।
গোপীনাথবাবু এবং মিংমা প্রায় সমবয়সী। তাঁরাই সবার আগে এগিয়ে গেলেন অতিথিদের স্বাগত জানাতে। ‘আসুন আসুন’ আর ‘আইয়ে স্যরজি’ মিলিয়ে হাসিমুখেই অতিথিদের গাড়ি থেকে নামিয়ে আনলেন তারা। গলায় পরিয়ে দেওয়া হল ‘খাদা।’ এই প্ল্যানটা স্বভাবতই মিংমা তামাংয়ের; এবং অতিথিরা যে রীতিমতো অভিভূত, সেটা আর বলে দেওয়ার দরকার হল না। তাছাড়া দু’জন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেস্টদের স্বাগত জানাচ্ছেন, তাঁদের একজন সমতলের মানুষ, অন্যজন পাহাড়ের— এই দৃশ্যটাই একেবারে অন্যরকম।
যাঁরা এলেন, তাঁরাও অবিশ্যি উঁচু দলের মানুষ; অন্তত প্রথম দেখায় তাই মনে হল। ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা ভদ্রলোকই যে এই পরিবারটির কর্তা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আধার কার্ডের ছবি দেখে মানুষ চিনতে পারার ক্ষমতা গোপীনাথবাবুর নেই। দেবযানীকে দেখতে মোটেই মন্দ নয়; এবং আধার কার্ড করাবেন বলে তিনি পাড়ার ‘বিউটি কুইন সালোন অ্যান্ড স্পা’ নামের ছোট্ট বিউটি পার্লারে আড়াই ঘন্টা ধরে মেকআপ নিয়েছিলেন। তার পরেও তাঁর ছবিটা হুবহু বাংলা সিনেমার কুটনি পিসিমাদের মতো এসেছিল, যে কারণে গোপীনাথবাবুকে প্রায় আধঘন্টা ধরে ধমকা-ধমকি করেছিলেন তিনি।
কিন্তু হিমাদ্রি বন্দোপাধ্যায় নামের এই ভদ্রলোকের ছবি এমনকি আধার কার্ডেও রীতিমত ভালো লাগছিল। গাড়ি থেকে তাঁকে নেমে আসতে দেখে গোপীনাথ রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ধবধবে ফর্সা রং, লম্বায় ছ’ফুটের কাছাকাছি, পরনে স্যুট এবং হাতে একটি বাহারি ছড়ি; সব মিলিয়ে ভদ্রলোককে দেখাচ্ছিল ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ সিনেমার ছবি বিশ্বাসের মতো। মাঝের সিট থেকে নেমে এলেন আরও তিনজন। মোটামুটি গোপীনাথবাবুর সমবয়সী এক ভদ্রমহিলা, তাঁর পরনে একটি দামি শাড়ি, তার উপরের শালটার দাম আরো বেশি; যদিও ছোটখাটো চেহারায় আর তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। সঙ্গের মেয়েটি যে এই ভদ্রমহিলারই, সেটা আর বলে দিতে হয় না। প্রায় হুবহু একই চেহারা, শুধু বয়সটা বছর পঁচিশ কম। সঙ্গের যুবকটির পরিচয় অবশ্য ঠিক বোঝা গেল না, কারণ জিন্স আর জ্যাকেট পরা ছেলেটা সকলের শেষে নেমে এল দু’হাতে দুটো লেডিস পার্স নিয়ে।
অভ্যর্থনা পর্ব মিটে যাবার পর ভদ্রমহিলা এক পা এগিয়ে এসে বললেন, “নমস্কার। আমার নাম সুতন্দ্রা ব্যানার্জি। ওর নামে বুকিং করেছিলাম।” বলে সেই সুপুরুষ ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিয়ে যোগ করলেন, “ওর নাম হিমাদ্রি।”
ভদ্রলোক তখন ঘাড় উঁচু করে মুগ্ধ হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা দেখছিলেন। এইবার বোধহয় নিজের নাম শুনতে পেয়ে একটু চমকে উঠে বললেন, “হ্যাঁ, আমারই নাম হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকিং আমার নামে আছে।”
গোপীনাথবাবু একমুখ হেসে বললেন, “আসুন হিমাদ্রিবাবু। আপনারাও আসুন। রুম রেডি। সবার আগে একটু ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিন।”
ভদ্রলোক অবশ্য ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বিধাগ্রস্ত মুখে। ভদ্রমহিলা বললেন, “হ্যাঁ, আগে রুমটা দেখিয়ে দিন। ও আগে টয়লেটটা দেখে নেবে। আমার মেয়ের যদি টয়লেট পছন্দ না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা থাকব না।”
গোপীনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, “ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ম্যাডাম।”
ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বললেন, “আমরা যখনই কোথাও বেড়াতে যাই, ওর দায়িত্ব হল আগে ভিতরে গিয়ে টয়লেটটা দেখে আসা। ততক্ষণ পর্যন্ত সুচরিতা বাইরেই থাকে। ওর রিপোর্ট ঠিক হলে, মানে টয়লেট যদি পছন্দ হয়, তাহলেই মেয়ে ঘরে ঢুকবে। এটাই নিয়ম।”
গোপীনাথ একবার আড়চোখে মিংমার দিকে তাকালেন। তিনিও কেমন একটু ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে রয়েছেন ভদ্রমহিলার দিকে।
মা আর মেয়ে ঘুরে ঘুরে ফুল দেখতে লাগল। হিমাদ্রিবাবু ঢুকে পড়লেন রুমে। গোপীনাথবাবু কী করবেন বুঝতে না পেরে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।
এমন সময় সুচরিতা নামের সেই মেয়েটি গম্ভীর গলায় বলল, “বাবু! এদিকে এসো।”
ছেলেটি এতক্ষণ দুটো লেডিস পার্স দু’হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। এবার তাড়াতাড়ি দুটোকেই বাঁহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ডানহাতে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আনল, তারপর ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।
মেয়ে আর মা এইবার ফুলগাছের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুচরিতা ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে, ঠিক কীভাবে ছবি তুলতে হবে। “হাঁটু গেড়ে বসো। মোবাইলটা এইভাবে ধরবে। আমার পা যেন না আসে। পেছনে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে?”
ছেলেটি বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। আদেশ অনুযায়ী উবু হয়ে বসে, হামাগুড়ি দিয়ে, কিংবা নিলডাউন হয়ে ছবি তুলে চলেছে।
খান কুড়ি ছবি তোলার পর মেয়েটি বলল, “ঠিক আছে। এবার মোবাইলটা দাও। আমি দেখে নিচ্ছি, এর মধ্যে একটাও ওকে হয়েছে কিনা।”
মিনিট দুয়েকের মধ্যে ছবি দেখা শেষ করে মেয়েটি বলল, “চার নম্বর আর আঠেরো নম্বর ছবি দুটো ঠিকই আছে। ওই দুটো ফেসবুক আর ইনস্টায় আপলোড করে দাও। এগারো নম্বর ছবিটা আমার হোয়াটসঅ্যাপের ডিপি করে দেবে। মা, তুমি কি ওই নীল ফুলগুলোকে নিয়ে আরেকটা ছবি তুলবে?”
ভদ্রমহিলা অবশ্য উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেলেন না, কারণ ইতিমধ্যে ছবি বিশ্বাস বেরিয়ে এসেছেন রুম থেকে।
“মোটামুটি ঠিকঠাক। সব পরিষ্কার আছে। সবকটা কল দিয়ে জল পড়ছে। গিজার কাজ করছে।” রিপোর্ট দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক।
“দুটো ওয়াশরুমই দেখে নিয়েছ তো? তোমাকে তো আবার কোনও কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।” বললেন ভদ্রমহিলা। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে গোপীনাথবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “বাবার সঙ্গে একবার ফ্লাইটে নেপালে গিয়েছিলাম। কাঠমান্ডুর বেস্ট হোটেলে উঠেছিলাম আমরা, বুঝলেন। সেই হোটেলে তিরিশখানা ঘর। বাবা প্রত্যেকটা ঘর চেক করে, তারপর তেইশ নম্বর ঘরটা সিলেক্ট করেছিল। শুধু সতেরো নম্বর ঘরে এক সাহেব ছিল। সে মদের বোতল হাতে নিয়ে তাড়া করেছিল বলে সেই ঘরটা চেক করা যায়নি। অসভ্য লোক আর কী।”
একবার ঢোক গিলে গোপীনাথবাবু বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই। কনফার্ম না হয়ে ঘর নেবেনই বা কেন?”
“আপনারা ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করুন। আমরা ফ্রেশ হয়ে আসছি। কী আছে ব্রেকফাস্টে?”
“আজ আছে লুচি আর স্কোয়াশের তরকারি। কাল মোমো হবে। মিষ্টি আছে। আর সেরা কোয়ালিটির দার্জিলিং টি তো থাকবেই, হেঁ হেঁ…!”
“লুচি যেন গরম থাকে। আমার মেয়ে কিন্তু গরম লুচি ছাড়া খেতে পারে না। আয় সুচি। ফ্রেশ হয়ে নীল জিন্স আর লাল ফুলহাতা টিশার্ট-টা পরবি। ওই ইয়েলো ফুলটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে দুটো ছবি তুলে নিবি।”
মেয়ে আর মা ডানদিকের রুমটাতে ঢুকে পড়লেন। তার আগে সুচরিতা নামের সেই মেয়েটি শুধু একবার মুখ ঘুরিয়ে বলল, “বাবু, পার্স দুটো রুমে দিয়ে যাও।”
সকলে ঘরে ঢুকে পড়ার পর মিংমা আর গোপীনাথবাবু একই সঙ্গে লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। আর কী আশ্চর্য, দুজনে একই সঙ্গে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হুবহু একই রকম গলায় বলে উঠলেন, “সাবধান! সাবধান!”
অতিথিরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলেন খাওয়ার জায়গায়। ততক্ষণে লুচি ভাজা কমপ্লিট। ভদ্রমহিলা বসলেন মেয়ের পাশে, এবং সে হাত দেওয়ার আগে নিজে লুচিতে আঙুল ছুঁইয়ে একবার চেক করে নিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে ঘড়ি দেখে বললেন, “একটু বেশি গরম আছে। তিন মিনিট পরে খাবে।”
মেয়ে মাথা নেড়ে বলল, “আচ্ছা। বাবু, একবার এদিকে এসো তো!”
ছেলেটি খেতে বসতে যাচ্ছিল। মেয়েটির গলা শুনে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পকেট থেকে মোবাইল বের করে গিয়ে দাঁড়াল সামনে।
“উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসো। হ্যাঁ, এইবার মন দিয়ে শোনো। ব্যাপারটা বুঝে নাও। এমনভাবে ছবি তুলবে, যাতে আমার মুখের সামনে লুচির ধোঁয়াটা দেখা যায়। বুঝতে পেরেছ?”
মেয়েটির মা বললেন, “এক মিনিট দাড়াও, শুভজিৎ। আমি একটা লুচি ফাটিয়ে দিচ্ছি। তাহলেই ধোঁয়াটা ঠিকমতো উঠবে, আর তুমি অমনি ছবিটা তুলে ফেলবে।”
ছেলেটি ভারী বাধ্য। ঘাড় কাত করে মোবাইল উঁচিয়ে রেডি হয়ে রইল।
“রেডি? ফুস!”
সত্যিই শব্দটা করে উঠলেন ভদ্রমহিলা! এই মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে দু’দিকে হাত ছড়িয়ে অদ্ভুত একটা মুখ করল। ছবি উঠল কিনা, সেটা অবশ্য গোপীনাথ বুঝতে পারলেন না; তবে ছেলেটি যেরকম গাম্ভীর্যের সঙ্গে মোবাইলটা এগিয়ে দিল, তাতে বোঝা গেল, ছবি উঠেছে। প্রায় মিনিট খানেক গভীর পর্যবেক্ষণের পর মেয়েটি রায় ঘোষণা করল, “ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে। মা, একবার দেখে নাও তো!”
শুভজিৎ নামের ছেলেটি যেরকম উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে রইল ভদ্রমহিলার দিকে, তাতে গোপীনাথের একবার মনে হল— এর উপরেই সম্ভবত ছেলেটার ব্রেকফাস্ট পাওয়া নির্ভর করছে। ছবি খারাপ হলে এ’বেলার খাওয়া বন্ধ।
তেমন ভয়ানক কিছু অবশ্য ঘটল না। চশমাটা কপালের উপরে তুলে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে ভদ্রমহিলা বললেন, “ওই আর কী। মোটামুটি ঠিকই আছে।”
“বেশ, তাহলে বরং এটাকে ফেসবুক স্টোরিতে দিয়ে দাও। এটার সঙ্গে কোন গান দেওয়া যায় বলো তো মা?”
গোপীনাথবাবুর একবার ইচ্ছে হল বলে ওঠেন, গুপী গাইন বাঘা বাইনের ‘আয় রে তবে খাওয়া যাক, মণ্ডা-মিঠাই চাওয়া যাক’ গানটা এর সঙ্গে চমৎকার মানাবে। তারপরেই তাঁর মনে পড়ল, মণ্ডা বা মিঠাই— কিছুই এই ছবিতে নেই। আর লুচি দিয়ে কোনও গান হয় কিনা, সেটাও তাঁর মনে পড়ল না। সবচাইতে বড় কথা হল, একটা মেয়ে লুচি খাচ্ছে, এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে গান লাগবেই বা কোন্ কর্মে?
খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা গোপীনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, “এইবার বলুন, এই গ্রামে দেখার মত কী কী আছে। আমি ওকে বলেছিলাম দার্জিলিংয়ের কথা। সেখানে গ্লেনারিজ আছে, কেভেন্টার্স আছে, ম্যালেও ছবি তোলা যায় চমৎকার। এখানে?”
গোপীনাথবাবু একটা গদগদ ধরনের হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললেন, “গ্রামে তো তেমন কিছু থাকে না, ম্যাডাম! তবে একটা বৌদ্ধ মনাস্ট্রি আছে। দেখলে ভাল লাগবে। আর একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। এই রাস্তাটা দিয়ে একটু এগোলেই গ্রাম শেষ হয়ে পাইনের জঙ্গল শুরু হয়ে যাবে। আধ ঘণ্টা মতো হাঁটলেই আপনারা পৌঁছে যাবেন ভিউ পয়েন্টে। নিচের দিকে তাকালে দেখা যাবে তিস্তা, আর উপরের দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ফ্যান্টাস্টিক ভিউ!”
ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, “আধ ঘন্টা ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হবে? আপনারা গাড়ির ব্যবস্থা রাখেননি?
“ও রাস্তায় গাড়ি যাবে না, ম্যাডাম। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।” বললেন মিংমা, “পাইনের বনের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। চমৎকার লাগবে হাঁটতে।”
“রাস্তাটা আরও চওড়া করা উচিত ছিল আপনাদের। আমাদের সেন্ট্রাল এভিনিউ দেখবেন। ইয়া চওড়া!”
“মা, রিলগুলো আগে তুলে নিই? বাগানটা তো ভালই! ফুল-টুল আছে।” মেয়ে বলল, “ওই গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি’ গানটার মাঝের লাইনের সঙ্গে নাচব। ‘ওই যে ঘুম পাহাড়…’— মনে পড়ছে?”
মা মুগ্ধ গলায় বললেন, “তুই গানও ভেবে এসেছিস? এইজন্যই এত ভিউ হচ্ছে তোর। গুড, ভেরি গুড। এই শুভজিৎ, খাওয়া হয়েছে? চলো, এবার রিলটা করে নাও।”
সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর ফের একটা সমবেত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হল। থম মেরে বসে রইলেন গোপীনাথ আর মিংমা। কিছুক্ষণ পর জানলা দিয়ে খুব সাবধানে উঁকি মেরে গোপীনাথ দেখলেন, হিমাদ্রি বসে আছেন কটেজের বারান্দায়। মেয়েটি বাগানে অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে। মা গান চালাচ্ছেন আর মাঝেমাঝে ডিরেকশন দিচ্ছেন। শুভজিৎ নামের ছেলেটি ঘাসের মধ্যে গুবরে পোকার মতো গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, হাতে মোবাইল।
মিংমাও যে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছেন, সেটা গোপীনাথবাবু খেয়াল করেননি। এখন কানের কাছে শুনতে পেলেন ফিসফিস শব্দ, “আগেভাগে বিয়ে করে ফেলে খুব বেঁচে গিয়েছি, মশাই!”
আগে বিয়ে করলেই সবাই যে বেঁচে যায় না, সেটা বলে আর হাসিখুশি ভদ্রলোকের মন খারাপ করে দিতে ইচ্ছে করল না গোপীনাথের। তিনি শুধু বললেন, “লাঞ্চের ব্যবস্থা করে ফেলি?”
“সেই ভাল। এঁরা কোথাও যাবেন বলে তো মনে হচ্ছে না।”
এমন চমৎকার দিনটা এঁরা কেন বাগানে হামাগুড়ি দিয়ে নষ্ট করছেন, সেটা গোপীনাথবাবুর মাথায় ঢুকল না। তিনিও আর সে চেষ্টা না করে ঢুকে পড়লেন ডাইনিংয়ের লাগোয়া কিচেনে। লাঞ্চের ব্যবস্থাটা সত্যিই আগেভাগে করে ফেলা উচিত। বোঝাই যাচ্ছে এঁরা কোথাও যাবেন না।
দুপুরে খেতে বসে ভদ্রমহিলা সামান্য নাক সিঁটকে বললেন, “শুনলাম সব হোমস্টেতেই নাকি দুপুরে এই একই খাবার দেয়? ডিমের ঝোল আর ভাত!”
গোপীনাথবাবু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এঁদের খাওয়ার তদারকি করছিলেন। একটু হেসে বললেন, “পাহাড়ে তো মাছ পাবেন না, ম্যাডাম। তবে রাতে রুটি আর চিকেন থাকছে।”
“তাও ভালো। আমি যখন বাবার সঙ্গে ফ্লাইটে নেপালে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছিলাম— চিকেনটা ওরা উইথ স্কিন রান্না করে। তার যা টেস্ট হয় না!”
গোপীনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, “এখানেও ওটাই পাবেন। উইথ স্কিন। আপনি বোধহয় আপনার বাবার সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছেন, তাই না?”
ভদ্রমহিলা বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “কোথায় আর যাওয়া হল? বাবা খুব বিজি থাকত কিনা! ওই একবারই নেপালে গিয়েছিলাম ফ্লাইটে চেপে।”
গোপীনাথবাবু বুঝতে পারছিলেন, প্লেনে চেপে নেপালে যাবার ব্যাপারটা ভদ্রমহিলার কাছে আজও একটা গৌরবজনক ব্যাপার। বেড়াতে যাবার কথা উঠলেই নেপাল, আর নেপালের উল্লেখ এলেই ফ্লাইট চলে আসছে।
“সন্ধ্যেবেলা কিন্তু পকোড়া আছে।” উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন গোপীনাথ, “আর তার সঙ্গে খাঁটি দার্জিলিং টি। ওই উপরের যে চা-বাগান দেখছেন, সেখান থেকেই আসবে পাতাটা।”
এতক্ষণে মুখ খুললেন হিমাদ্রিবাবু। মাথা নেড়ে বললেন, “ব্রেকফাস্টের পর যে চা-টা খেলাম, সেটাও খুব ভালো ছিল। আমি যখন শিলিগুড়িতে পোস্টেড ছিলাম…”
“এখানে তো চারিদিকেই জঙ্গল!” ভদ্রলোক কথাটা শেষ করতে পারলেন না, কারণ এবার মুখ খুলেছে মেয়ে, “বাঘ আছে? ভাল্লুক?”
“নেই আবার!” চোখ বড় বড় করে গোপীনাথ বললেন, “এই তো, কালকেই রাতের বেলা আমার কটেজের বারান্দায় বসে আছি। এমন সময় দেখি, চা-বাগানের দিক থেকে একটা লেপার্ড নেমে আসছে। এইরকম বড় হবে!” বলে তিনি যে মাপটা দেখালেন, যেকোনও লেপার্ড সেই আকারে পৌঁছতে পারলে অত্যন্ত গর্বিত হত।
মিংমা বসেছিলেন ডাইনিং হলের এক কোণের একটা চেয়ারে। কথাটা শুনে তিনি গম্ভীরভাবে মুখ নিচু করলেন হাসি চাপার জন্য। গোপীনাথবাবু টুরিস্টের মন রাখার জন্য যে আস্ত একটা লেপার্ড একেবারে বাড়ির মধ্যে এনে ফেলবেন, সেটা তিনিও ভাবতে পারেননি।
মেয়েটার মুখ ঝলমল করে উঠল এবার, “ভিডিও করেছেন?”
গোপীনাথ ঠোঁট উল্টে বললেন, “সাহস পাইনি। সিধে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল কিনা!”
“আজকেও আসবে? মানে রোজই আসে?”
বেখেয়ালে গোপীনাথ বলে বসলেন, “তেমন কিছু বলে যায়নি অবশ্য। কেন বলুন তো? আপনি কি বন্যপ্রাণী দেখতে ভালোবাসেন?”
“না না, তা কেন হবে? আসলে আমার একটা লেপার্ড প্রিন্ট ড্রেস আছে। ওইরকম চাকা চাকা দাগ।” সোৎসাহে বলল মেয়েটি, “মনে করুন, আমি সেটা পরে ওইখানে কটেজের বারান্দায় নাচছি, ঠিক সেই সময় একটা সত্যিকারের লেপার্ড বারান্দার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! উফফ! কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হত ভাবুন একবার!”
“বোঝো কাণ্ড!” বললেন ভদ্রমহিলা। বোঝা গেল, মেয়ের মা বেশ অবাক হয়েছেন। এতেও যদি কেউ অবাক না হত, তাহলে অবশ্য অভিধানে ‘অবাক’ শব্দটা রাখার কোনও দরকারই পড়ত না!
পরক্ষণেই তিনি যা বললেন, সেটা শুনে অবশ্য গোপীনাথ বুঝতে পারলেন, অবাক শব্দটা আসলে কেন ডিকশনারিতে রয়ে গেছে।
“এ কেমন কথা, সুচি! তুমি আগে বলব তো, এইরকম একটা রিল করার ইচ্ছে আছে তোমার! তাহলে আমরা আগেই চলে আসতাম এখানে!”
তারপর গোপীনাথবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে আবদারের সুরে বললেন, “দেখুন না, সন্ধ্যার পর যদি একটা লেপার্ডের ব্যবস্থা করা যায়! তেমন কিছু না, আমাদের কটেজের পাশ দিয়ে একবার হেঁটে গেলেই হবে।”
একেবারে আক্ষরিক অর্থেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন গোপীনাথবাবু। চোখ দুটো রাজভোগ সাইজের হয়ে গেল তাঁর।
বাপ্পা বলেছিল বটে— টুরিস্টদের আবদারের কোনও সীমা নেই। কিন্তু হলফ করে বলা যায়, আস্ত একটা লেপার্ডের আবদারের কথা বাপ্পারও মাথায় ছিল না।
“আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার দিকে এলে কথা বলে জানাব আপনাদের।” বলে বসলেন গোপীনাথ।
৪
সকাল ন’টা নাগাদ আর্লি ব্রেকফাস্ট সেরে চার গেস্ট গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাবার পর তাঁদেরই ভাড়া করা কটেজের বারান্দার চেয়ারটাতে ধপাস করে বসে পড়লেন গোপীনাথবাবু। এই দু’দিন যা গেল, তাতেই তাঁর দু’বছরের অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে মনে হয়।
কিন্তু এখন বসার সময় নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার গেস্ট আসবে। এবার আর মোটে একটা কটেজ নয়। সব ক’টা কটেজ ভাড়া নিয়েছে একটি কোম্পানি।
“বাপ্পা যা খবর দিল, তা থেকে মনে হচ্ছে— কোনও অফিসের বড় সাহেবেরা সব একসঙ্গে পাহাড়ে আসছেন ছুটি কাটাতে।” পাশে বসা মিংমাকে বললেন গোপীনাথবাবু, “অফিস বন্ধ করে ঘুরতে আসছে নাকি, মশাই?”
এই ক’দিনে মিংমার বাংলা জ্ঞান যে রীতিমতো উন্নতি করে ফেলেছে, সেটা গোপীনাথবাবু দিব্যি বুঝতে পারছিলেন। তাঁর নিজের হিন্দিটা বিশেষ সুবিধের নয়, যাকে বলে কাজ চালানো গোছের। মিংমার হিন্দিটাও তাই। কিন্তু প্রায় সমবয়স্ক এই পাহাড়ি মানুষটির সঙ্গে তাঁর যে এত দ্রুত একটা চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে, সেটা তিনি এর আগে ভাবেননি।
মিংমার হাতে চায়ের কাপ। লম্বা একটা চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, “আপনি ভুলে গিয়েছেন। আজ থেকে পুজো শুরু হচ্ছে।”
“বোঝো কাণ্ড!” গোপীনাথবাবু চোখ ছানাবড়া করে বললেন, “আজ সপ্তমী নাকি?”
“জি। আপনি হলেন খাঁটি বাঙালি। এটা কি আমার মনে করিয়ে দেওয়ার কথা?” হাসতে হাসতে বললেন মিংমা।
তাও তো বটে। আসলে এই ক’দিনের টেনশনে পুজোর কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন গোপীনাথবাবু। প্রথম অভিজ্ঞতাটাই যে এরকম বিচিত্র হতে চলেছে সেটা তার ধারণার মধ্যে ছিল না।
“আজকাল বেশিরভাগ লোক মোবাইল বাগিয়েই ঘুরে বেড়ায়, স্যরজি। অমন আঁতকে উঠলে চলবে না।” বললেন মিংমা, “আচ্ছা এবার উঠে পড়া যাক। রনিতদের ডাকি। সবার আগে তো ঘরগুলোকে সাফ করে ফেলতে হবে।”
গোপীনাথবাবুও চটপট চা শেষ করে উঠে পড়লেন। রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে। একদিকে চলবে রুম পরিষ্কার করে ফের গুছিয়ে ফেলা। তারপর ব্রেকফাস্টের জোগাড়যন্ত্র। ডাইনিং হলটাকেও নতুন করে সাজাতে হবে। এঁরা আবার সন্ধ্যের পর পার্টি করবেন। অফিস ট্যুর বলে কথা। বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার এই দিক থেকে বড় ভালো ছিল। সন্ধে হলেই লেপার্ডের ভয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। খাবার সময় হলে ঘরে গিয়ে ডিনার দিয়ে আসতে হত। ওই সময়টা ছিল তাঁর ছুটি। নিজের বারান্দায় বসে দিব্যি মিংমার সঙ্গে গল্প করতে করতে দু’ পেগ মেরে দেওয়া যেত। আপাতত আর সেই সুযোগ হবে না।
কাজ সারতে সারতেই দু’খানা গাড়ি এসে দাঁড়াল হোমস্টের উঠোনে। আর সবার আগে যিনি নেমে এলেন, তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথবাবুর মগজে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল। হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সাক্ষাৎ ছবি বিশ্বাস হয়ে থাকেন, তাহলে ইনি স্বয়ং কমল মিত্র। হুবহু তেমনি লম্বা-চওড়া গড়ন, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, পরনে একটা বেজায় দামি স্যুট। বয়স গোপীনাথবাবুর চাইতে বড়জোর বছর পাঁচেক বেশি হবে; কিন্তু ভদ্রলোকের সাংঘাতিক ব্যক্তিত্বের সামনে গোপীনাথবাবু দাঁড়াতেই পারবেন না।
তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গোপীনাথ বললেন, “নমস্কার। মেঘমা হোমস্টেতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই।”
ভদ্রলোক যখন মুখ খুললেন, তখন গোপীনাথবাবু রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের গলাটাও হুবহু কমল মিত্রের মতোই। গুরুগম্ভীর, ব্যক্তিত্ববান গলা।
“নমস্কার। আপনার সঙ্গেই বুঝি ফোনে কথা হয়েছিল?”
“না, সে আমাদের সিটি অফিসের স্টাফ। আমি এই হোমস্টের ম্যানেজার। তবে আমাকে ইতিমধ্যেই সব বলে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের রুম রেডি আছে। চলে আসুন, স্যর।”
বাঙালি যে ‘স্যর’ শব্দটা শুনতে অসম্ভব পছন্দ করে, সেটা গোপীনাথবাবুর এমনিতেও জানা ছিল। এই ক’দিনে সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। সত্যিই ভদ্রলোকের গম্ভীর মুখে খুব সামান্য একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।
“মোক্ষম জায়গাটি বেছে নিয়েছেন কিন্তু হোমস্টে করার জন্য।” কটেজের পিছনের পাইন বনের উপর দিয়ে উঁকি দেওয়া দুধ-সাদা পাহাড়ের রেখার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “বাঙালির অক্ষয় ব্যবসা আসলে দুটো। সমতলে রবীন্দ্রনাথ, আর পাহাড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা।” বলে একবার পিছন ফিরে তাকালেন।
ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে পড়া অন্য সাহেবরা যেভাবে মাথা নেড়ে হেসে উঠলেন, তাতে গোপীনাথবাবুর বুঝতে অসুবিধা হল না— দলপতি তাঁদের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রাখেন। দলপতির শুধু ইশারায় বুঝিয়ে দিলেই চলে, তিনি একটা রসিকতা করেছেন।
গোপীনাথবাবু নিজেও হাসতে হাসতে দলটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন হোমস্টের দিকে। মিংমা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এটা অবশ্য তাঁর ডিউটির মধ্যে পড়ে না, কিন্তু মূলত গোপীনাথবাবুর টানেই মিংমা নিজে থেকে তাঁর অনেকখানি কাজ হালকা করে দিচ্ছেন গোড়া থেকেই। আজও তার অন্যথা ঘটেনি।
“আমার পাঁচটা ফ্যাক্টরি আছে। এঁরা হলেন সেই সব ফ্যাক্টরির কর্তা। আর একটা আমি নিজে দেখি।” গোপীনাথবাবুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রাশভারী চালে বললেন ভদ্রলোক, “আমার নাম প্রশান্ত বসাক। শোভাবাজারে বাড়ি। বোঝেনই তো, সারা বছর ভয়ানক খাটাখাটনি যায়। যেমন আমার, তেমনই এদের। তাই বছরে একবার এই পুজোর দিনগুলোয় আমি সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি কাছেপিঠে কোথাও; এবার যেমন এলাম এখানে। খরচা কোম্পানির। কর্তাগিন্নির ট্রিপ। এঁরা প্রত্যেকেই কাপল। আমিও গিন্নিকে নিয়েই এসেছি। ছেলেমেয়ে বাদ। এই হোমস্টে-টা বোধহয় নতুন হয়েছে, তাই না?”
গোপীনাথবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, “আপনারা হলেন সবে দ্বিতীয় অতিথি। এর আগে কেবল একটা ফ্যমিলি ঘুরে গিয়েছে। একেবারে ব্র্যান্ড নিউ প্রপার্টি যাকে বলে।”
“আপনি কি মালিক? মানে এই হোমস্টে ব্যাপারটা কীভাবে চলে, সেটা সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই।”
‘খাঁটি ব্যবসায়ী যাকে বলে’— মনে মনে ভাবলেন গোপীনাথবাবু, ‘এসেই লেগে পড়েছেন ব্যবসার পদ্ধতিটা জানতে।’
অল্প কথায় এবং খুব ওপর ওপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বলতেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন প্রথম কটেজের সামনে। গোপীনাথবাবু কিছু বলার আগেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন মিংমা। তাঁর হাতে একটা খাদা। কোনও অদৃশ্য লক্ষণ দেখে তিনি বুঝে ফেলেছেন, এই ভদ্রলোককে সম্মান জানালেই গোটা দল সম্মানিত হয়ে যাবে।
“ওয়েলকাম, স্যর। ওয়েলকাম টু তিনখোলা।” বলে খাদাটা পরিয়ে দিলেন মিংমা।
অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ভদ্রলোক যখন নেপালি উত্তরীয়টা পরে নিলেন, তখনও তিনি মিংমার থেকে প্রায় ছ’ইঞ্চি লম্বা রয়ে গেলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতি-নমস্কার করে বললেন, “তা এই বুঝি আমাদের রুম?”
গোপীনাথবাবু বললেন, “ইটস্ অল ইয়োরস্। চারটে কটেজের আটটা ঘরই আপনাদের জন্য রেডি করার আছে, স্যর। এবার আপনারা শুধু একটু ঠিক করে নিন, কে কোনটায় থাকবেন।”
প্রশান্তবাবু পিছনে ফিরে একটু গলা তুলে বললেন, “শ্যামলী, একটু এখানে এসো তো!”
এতক্ষণে গোপীনাথবাবু খেয়াল করলেন, দলের বাকিরা একটা নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে দলপতির পিছন পিছন আসছিলেন। এইবার তাঁদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন ছোটখাটো চেহারার শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলা। সামান্য নার্ভাস পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোকের পাশে।
“আলাপ করিয়ে দিই। আমার গৃহিণী— শ্যামলী বসাক। আর শ্যামলী, ইনি হলেন…ইয়ে…”
গোপীনাথ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, “নমস্কার, নমস্কার। আমার নাম গোপীনাথ সেন। এই হোমস্টের ম্যানেজার বলতে পারেন। আর ইনি হলেন মিঃ তামাং। বলতে গেলে ইনিই এখানকার ওনার।”
“ইনি যদি ওনার হবেন তাহলে মিঃ কুণ্ডু কে? ওয়েবসাইটে তো তাঁর নাম লেখা ছিল!” একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রশান্তবাবু, “তিনি তার মানে ওনার নন?”
মিঃ কুণ্ডু বলতে যে বাপ্পার কথা বোঝানো হচ্ছে, সেটা গোপীনাথবাবু জানেন। ওর আসল নাম বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু।
ভদ্রলোক যে আবার ব্যবসার দিকে ঢুকে পড়ছেন, সেটা বুঝতে মিংমারও অসুবিধা হল না। তিনি একটু হেসে বললেন, “আমরা দুজনে মিলেই ব্যবসাটা শুরু করেছি বলতে পারেন। আমি বরং এদিকের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। এখানে চারটে কটেজ আছে। প্রত্যেকটা কটেজে দুটো করে রুম। একেকটা রুমে দুজন খুব ভালোভাবেই থাকা যাবে।”
ভদ্রলোক আবার স্ত্রীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, “দেখে নাও কোনটায় থাকবে। আমি ততক্ষণে একবার ডাইনিং রুমটা ঘুরে আসি। আসুন মিঃ সেন।”
ডাইনিংয়ে পৌঁছে একবার কড়া চোখে চারিদিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন প্রশান্তবাবু। রাতের পার্টির জন্য ঢেলে সাজানো হয়েছে ডাইনিং হলের চেয়ার-টেবিলগুলোকে। সেসব খুঁটিয়ে পরখ করে নিয়ে তারপর বললেন, “মোটামুটি সব ঠিকই আছে। আগে থেকেই একটা কথা বলে রাখি। রাতে কিন্তু এখানে একটা ককটেল পার্টি দেওয়া হবে। আশা করছি আপনাদের কোনও আপত্তি নেই।”
গোপীনাথ হাসিমুখে বললেন, “বিন্দুমাত্র নয়, স্যর। এসব নিয়ে পাহাড়ি মানুষদের কোনও ছুঁৎমার্গ নেই। আপনি বললে বাইরের বাগানেও অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারি।”
“ঠাণ্ডা কীরকম এখানে? রাতের দিকে অসুবিধে হবে না? এখনই তো বেশ শীত শীত করছে!” জিজ্ঞাসা করলেন প্রশান্তবাবু।
“সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। রাতের দিকে উত্তরের দিক থেকে একটা হাওয়া দেয়। আপনাদের সহ্য হবে না। আর তাছাড়া…”
এক মুহূর্ত থেমে গিয়ে চটপট চিন্তা করে নিলেন গোপীনাথবাবু। সবে এসেছেন এঁরা। এখনই লেপার্ডের গল্পটা ঝুলি থেকে বের করার দরকার নেই। কাজেই এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তিনি বললেন, “তাছাড়া হঠাৎ করে বৃষ্টি নামার একটা চান্স থেকেই যায়। তখন খামোখা হুড়োহুড়ি করতে হবে। তার চাইতে এখানেই ভালো।”
“বেশ। এখানেই করা যাক। জিনিসপত্র আমরা সব নিয়েই এসেছি। কাজেই আপনাদের কোনও চিন্তা নেই। আপাতত ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করুন।”
“একদম, স্যর। সব রেডি আছে। আপনারা ফ্রেশ হয়ে এলেই…।” বলে গোপীনাথ ঢুকে পড়লেন কিচেনে।
ব্রেকফাস্ট, এবং তার পরের ঘণ্টা দুয়েক সময়ের মধ্যেই গোপীনাথবাবু একটা ব্যাপার বুঝতে পারলেন। প্রশান্তবাবুকে শুধু দেখতেই কমল মিত্রের মতো নয়। তাঁর ফ্যাক্টরির কর্তারাও তাঁকে দস্তুরমতো সমীহ করেন, সোজা করে বললে বলতে হয়, বেশ ভয় পান। প্রাতরাশ সেরে নিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই প্রশান্তবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, “এইবার বলুন ম্যানেজার সাহেব, কী কী দেখার আছে এখানে। কী করা যায় এবার?”
গোপীনাথ বলেছিলেন, “একবার ভিউ পয়েন্টটা ঘুরে আসুন, স্যর। তিন হাজার ফুট নিচে তিস্তা, আর উপরের দিকে তাকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা— দেখার মতো দৃশ্য। এই রাস্তাটা ধরে আধঘণ্টা এগোলেই পৌঁছে যাবেন।”
“আপনার কি এই মুহূর্তে জরুরি কোনও কাজ আছে?”
“না, তেমন কিছু নেই। কেন, স্যর?”
“তাহলে চলুন, একসঙ্গে ঘুরে আসি। দিব্যি কথা বলতে বলতে হাঁটা যাবে।”
গোপীনাথবাবু বুঝতে পারলেন, ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই প্রশান্তবাবু দলের লোকেদের সঙ্গে বেশি কথা বলাটা ঠিক সমীচীন বলে মনে করছেন না। তার চেয়ে বরং হোমস্টের ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়াটাই উচিত হবে বলে ঠিক করেছেন তিনি।
কাজেই কিচেনের ছেলেদের সব আরও একবার ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গোপীনাথ। এখানে এসে পৌঁছানোর পরের দিনই মিংমা তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এই রাস্তাটা দিয়ে। ডানদিকে উঠে গেছে পাহাড়, তাতে ঘন পাইনের বন। বাঁয়ে নেমেছে খাদ। অজস্র পাখির ওড়াউড়ি, বাঁদরের চিৎকার, অর্কিড আর ফার্ন দেখতে দেখতে হেঁটে যাওয়াটা একটা অভিজ্ঞতা বটে। প্রশান্তবাবু চললেন দলবল নিয়ে তাঁর সঙ্গে।
এইবার গোপীনাথ বুঝতে পারলেন, দলপতির অনুসরণে এই অফিসের কর্তাব্যক্তিরা সকলেই বেদম সাহেবি কালচারের অনুগামী। একে অপরকে এঁরা ‘মিঃ ডাট’ বা ‘মিসেস বিসোয়াস’ বলেই সম্বোধন করেন। কথাবার্তার অর্ধেকটাই চলছে ইংরেজিতে। ফলে ঘন ঘন ‘ওয়াও’ শব্দটা শোনা যাচ্ছে এবার। সে হোক গে, গেস্টরা যে জঙ্গল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, এতেই গোপীনাথ খুশি হয়ে গেলেন। শুধু একবার দূর থেকে ভেসে আসা হাম্বা ডাক শুনে মিঃ ভাট্চারিয়া “টাইগার! টাইগার!” বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন। এটুকু বাদ দিলে যাতায়াত নির্ঝঞ্ঝাটে চুকে গেল। ভিউ পয়েন্টে পৌঁছেও সকলেই এন্তার তারিফ করলেন। গোপীনাথ বুঝতে পারলেন, তাঁর গেস্টরা মোটের উপর সন্তুষ্টই হয়েছেন।
দুপুরের ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে আর এক কাপ তোফা চা খেয়ে সকলেই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এইবার শুরু হবে ককটেল পার্টি। গোপীনাথ ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, এখানে তাঁর ভূমিকা কী হতে চলেছে। প্রশান্তবাবু অবশ্য উদারভাবে বললেন, “সকাল থেকে আমরা ছিলাম গেস্ট। আপনি হোস্ট। এইবার আমি হোস্ট, আপনি এবং মিঃ তামাং আমার অতিথি। তাঁকেও ডেকে আনুন প্লিজ।”
বাঙালি পর্যটক দিঘায় গেলে বারমুডা আর লাল গেঞ্জি অথবা লিঙ্গভেদে নাইটির উপরে গামছা জড়িয়েই ঘুরে বেড়ায়। পাহাড়ে এলেও বারমুডা পরা মাস্ট। মেয়েরা তাও ফটো-সেশনের জায়গা বেশি বলে কিঞ্চিৎ সাজগোজ করে থাকেন। আগেকার মত মাংকি টুপি পরা পর্যটক আজকাল আর চোখেই পড়ে না।
এই দলের সদস্যরা অবশ্য এই নিয়মের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বলে প্রমাণিত হলেন। ঠিক সন্ধে সাতটার সময় পুরোদস্তুর কোট-প্যান্ট পরে তাঁরা হাজিরা দিলেন ডাইনিং হলে। ততক্ষণে রনিত আর দিলীপ চিকেন পকোড়া এবং অন্যান্য খাবারদাবারের ব্যবস্থা সেরে ফেলেছে। সাজিয়ে ফেলা হয়েছে দামি ব্র্যান্ডের স্কচ। গোপীনাথবাবুর দৌড় রয়্যাল চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত। কাজেই ব্লু লেবেল বা টিচার্সের সমাহার দেখে তাঁর চোখ গোল গোল হয়ে গেল। প্রশান্তবাবু যে একজন উদার-হৃদয় মালিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
খুবই সভ্যভব্য ভঙ্গিতে একে একে ডাইনিং হলে ঢুকে পড়লেন কর্তারা। সঙ্গে মিসেসরা। তাঁরাও শাড়ি-টাড়ি পরে একেবারে রেডি।
এবং যথারীতি, আধঘণ্টার মধ্যেই দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেল।
ইংরেজিতে যাকে বলে ‘ব্রেকিং দ্য আইস’— সেই কাজটা করলেন মিঃ ভাট্চারিয়া। ততক্ষণে দুটো লার্জ মেরে দিয়েছেন তিনি। সামান্য লালচে চোখে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, “এইবার একটা গান গেয়ে শোনাব আমি। পার্টিটা ঠিক জমছে না।”
সকলেই যেভাবে মাথা নেড়ে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন, তাতে আর সন্দেহ থাকে না, গায়ক হিসেবে উঁচু মহলে তিনি ইতিমধ্যেই বেশ বিখ্যাত।
“প্রথমে আমি একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইছি। তার আগে একটু সুরটা ধরে নিই।” বলে তিনি লম্বা করে বললেন, “সা আ আ আ…”
গোপীনাথবাবু গানের তেমন কিছু বোঝেন না। তবু এটুকু বুঝতে পারলেন, সেই সা টলমলে পায়ে রে গা মা পা পার হয়ে কোমল ধা-এ পৌঁছে থিতু হল। তা বাপু, দুটো লার্জের পর সা একটু টলতেই পারে। গায়ক তো আর টলছেন না!
“নাহ্, গলাটা ঠিক লাগছে না। দেখি ভাই আরেকটা।” বলে মিঃ ভাট্চারিয়া গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলেন রনিতের দিকে।
আর একটা লম্বা চুমুক দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রইলেন গায়ক। তারপর গম্ভীর গলায় গাইতে শুরু করলেন, “আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছ তুমি হৃদয় জুড়ে।”
গোপীনাথবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এটা যে রবীন্দ্রসংগীত, তা তাঁর জানাই ছিল না! সুরটাও বোধহয় গায়ক নিজেই দিয়ে নিচ্ছেন; কারণ তাঁর চেনা সুরের সঙ্গে এই সুরের কোনও মিল নেই। এদিকে বাকিরা এমন তন্ময় হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনতে লাগলেন যে, গোপীনাথবাবু নিজের সন্দেহটার প্রতিই কেমন সন্দিহান হয়ে পড়লেন। কে জানে— তিনিই হয়তো ভুল জানতেন! এখনও রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ইতিউতি ছাপা হয়েই চলেছে— এটা তাঁর জানা আছে। একটা নতুন রবীন্দ্রসংগীত যে পাওয়া যাবে না, এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই!
ক্রমে নির্জীব বোতল থেকে সজীব মনুষ্যশরীরে ঢুকে পড়ে স্কচ বেজায় হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলল। মিঃ ডাট দাবি করতে লাগলেন, “অল্প বয়সে আমাকে হুবুহু মিঠুনের মতো দেখতে ছিল, বুঝলেন। এখন কাজের চাপে টাক পড়ে গেছে বলে বুঝতে পারবেন না; কিন্তু এখনও আমি যদি নাচি… মিঃ ভাট্চারিয়া, আপনি ‘আই এম এ ডিসকো ড্যান্সার’ গানটা জানেন? দু’লাইন গাইলে আমি নেচে দেখিয়ে দিতে পারতাম।”
মিঃ ভাট্চারিয়া একজন কালচার্ড মানুষ। নাক সিঁটকে বললেন, “ওসব ফালতু গান আমি গাই না। একটা নতুন রবীন্দ্রসংগীত তুলেছি— ‘দ্যাখো আলোয় আলো আকাশ।’ ওটার সঙ্গে যদি নাচতে পারেন, তাহলে গাইতে রাজি আছি।”
মিঃ ডাট ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, “গানটা আমি শুনেছি। নট ব্যাড। কিন্তু ওটার সঙ্গে ডিস্কো ঠিক জমবে না।”
শ্রীজাতর মুখটা মনে করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন গোপীনাথবাবু। পার্টির শুরুতেই একটা গ্লাস নিয়ে কোণের টেবিলে গিয়ে বসেছিলেন তিনি আর মিংমা। এতক্ষণ চুমুক দিতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। এইবার ভয়ে ভয়ে গ্লাসটাকে ঠেলে সামান্য সরিয়েই দিলেন। দেখাই যাচ্ছে, স্কচ জিনিসটা সুবিধের নয়। খোদ রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও টানাটানি করতে ছাড়ে না, তা শ্রীজাত কোন ছার!
তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন গোপীনাথও। কর্তারা যতই বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ুন, ম্যাডামরা কিন্তু বসে রইলেন যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই। তাঁদের বোধহয় সর্বসমক্ষে ড্রিংক করার অভ্যেস নেই, নইলে এটাই এই আপিসের নিয়ম। মোদ্দা কথা, সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই তাঁরা উঠে পড়লেন, এবং ঠিক ন’টায় ডিনার রুমে পাঠিয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। মিসেস বসাক অবিশ্যি বসে বসে চিকেন পকোড়া খেতে লাগলেন নির্বিকার মুখে।
“এই এতদিনে একজন ভদ্রমহিলাকে দেখলাম, যিনি হাসব্যান্ডের সামনে জব্দ।” অন্যদের কান বাঁচিয়ে মিংমাকে বললেন গোপীনাথ, “একটাও কথা বলতে শুনেছেন এখন পর্যন্ত? প্রশান্তবাবু সাক্ষাৎ পুরুষসিংহ।”
“হুঁ, শক্ত মানুষ। সেই যে একখানা পেগ ঢেলেছিলেন, তারপর থেকে আর এগোননি।” মিংমা ফিসফিস করে বললেন, “বাকিদের দশা দেখে ভয় খেয়ে গেছেন বোধহয়। নইলে বড়কর্তার গ্র্যাভিটি ধরে রেখেছেন।”
কথাটা মিথ্যে নয়। এতক্ষণে গোপীনাথ খেয়াল করলেন, সেই প্রথমেই একখানা গ্লাস হাতে নিয়ে বসেছিলেন প্রশান্তবাবু। সেটা শেষ হয়েছে প্রায় আধঘণ্টা আগে। আর নেননি ভদ্রলোক।
বাকিদের অবস্থা অবশ্য সত্যিই সুবিধের নয়। এই মুহূর্তে তাঁদের মধ্যে রীতিমতো উত্তেজিত কথা কাটাকাটি চলছে কার অফিসের রিসেপশনিস্ট বেশি সুন্দরী, তাই নিয়ে। কেউই দাবী ছাড়তে রাজি নন। মিসেসরা ঘরে ফিরে যাওয়ার ফলে যে এঁদের সাহস অন্য একটা মাত্রায় পৌঁছেছে, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।
গোপীনাথ ধরে নিয়েছিলেন, আলোচনাটা রিসেপশনিস্টদের ফিগার পর্যন্ত পৌঁছলে মিসেস বসাক সম্ভবত উঠে পড়বেন। দেখা গেল, তাঁর এই ধারণাটা ভুল ছিল। খুব মনোযোগ দিয়ে ফিঙ্গার চিপস খেতে লাগলেন তিনি।
একটু পরে আর একটা ব্যাপার চোখে পড়ল তাঁর। মিসেস বসাক অবিচল থাকলেও, মিঃ বসাকের চেহারায় এবার কেমন যেন একটা অধৈর্য ভাব ফুটে উঠছে।
“তুমি বরং এবার রুমে গিয়ে একটু রেস্ট নাও। একটু পরেই ডিনার সার্ভ করবে এরা। তাই তো, গোপীনাথবাবু?” গম্ভীর গলায় বললেন প্রশান্তবাবু।
গোপীনাথ হেসে বললেন, “একদম কাঁটায় কাঁটায় নটায়।”
“পৌনে ন’টা তো বাজতে গেল। এবার তুমি বরং রুমে গিয়ে বিশ্রাম নাও।” আবার বললেন প্রশান্তবাবু।
মিসেস বসাকের শান্ত মুখচ্ছবি অবশ্য বদলাল না। ঠাণ্ডা গলায় তিনি বললেন, “আমি এখানেই ঠিক আছি।”
“বটে!” বলে চুপ করে গেলেন প্রশান্তবাবু।
“ভদ্রলোক এমন উসখুস করছেন কেন বলুন তো?” চাপা গলায় বললেন মিংমা, “কিছু একটা অস্বস্তি হচ্ছে মনে হয়।”
গোপীনাথবাবু কৌতূহলের চোখে সেটাই দেখছিলেন। কোনও কারণে প্রশান্তবাবুর মানসিক প্রশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন তিনি। পা দোলাচ্ছেন ঘন ঘন। তিন-চারবার ঘড়ি দেখলেন।
হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সটান গোপীনাথের দিকে হেঁটে এলেন প্রশান্তবাবু। থমথমে গলায় বললেন, “একটা ফোন আসার কথা ছিল আটটায়। এল না, বুঝলেন?”
মিংমা বললেন, “হ্যাঁ, এখানে সিগনাল খুব উইক। কালেভদ্রে লাইন পাওয়া যায়।”
গোপীনাথবাবু স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন প্রশান্তবাবুর দিকে। একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা এইমাত্র তাঁর মাথায় উদয় হয়েছে। আর সেটা পরখ করার একটাই উপায় আছে।
ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বুকপকেটের উপরে একবার হাত রাখলেন গোপীনাথ। প্রশান্তবাবু যে স্থির চোখে তাঁর হাতটার দিকে তাকিয়ে আছেন, সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। নিশ্চিত হয়ে নিয়ে তিনি বললেন, “একটা উপায় অবশ্য আছে। আমাদের হোমস্টের বাইরের রাস্তাটা দিয়ে মিনিট দুয়েক নিচের দিকে হাঁটলে একটা মোড় আছে, বুঝলেন স্যার। সেখান থেকে চমৎকার কথা বলা যায়। ফোনটা যদি আর্জেন্ট হয়ে থাকে…”
“খুবই আর্জেন্ট! মানে অসম্ভব আর্জেন্ট একটা ফোন, বুঝলেন! একজন ডিস্ট্রিবিউটার… চলুন না একটু আমার সঙ্গে। বাইরে তো দেখছি ঘুটঘুটে অন্ধকার।”
মিসেস বসাক ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “ও মা! এই অন্ধকারের মধ্যে এখন তুমি একা একা ফোন করতে যাবে? খেপেছ নাকি? দাঁড়াও, ঘর থেকে শালটা নিয়ে আসি। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।”
এতক্ষণে সুযোগ বুঝে পুরনো তাসটা খেললেন গোপীনাথ। মাপা আতঙ্কের ভাব মুখে ঘনিয়ে এনে বললেন, “সেটা বোধহয় ঠিক হবে না ম্যাডাম। গতকাল রাতে ঠিক এই সময় আমি আমার কটেজের বারান্দায় বসে ছিলাম। এমন সময় দেখি, একটা প্রকাণ্ড লেপার্ড ওই চা-বাগানের দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে আসছে।”
ভয়ের চোটে মিসেস বসাকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, “বলেন কী? লেপার্ড— মানে চিতা বাঘ?”
লেপার্ড আর চিতা ঠিক এক জিনিস নয়। কিন্তু এখন সেটা বুঝিয়ে বলার সময় নয়। মুখটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে গোপীনাথবাবু বললেন, “চিতাই বটে। পাহাড়ে এই একটি প্রাণীর অভাব নেই। আর তার সাইজ দেখলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।”
“আর তার মধ্যে…”
“দু’তিনজন একসঙ্গে বেরুলে অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ নেই। মুশকিল হল— শাড়ি পরে আপনি তো দৌড়ে পালাতে পারবেন না!”
অসম্ভব উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশান্তবাবু বললেন, “শোনো শ্যামলী। বুঝতেই পারছ, ফোনটা খুব জরুরী। ফ্যাক্টরির কাজ ফেলে রাখা যায় না। তুমি এখানেই বসো। আমি দু’ মিনিটের মধ্যে ফোন করে আসছি। আসুন গোপীনাথবাবু।”
আর কাউকে একটিও শব্দ উচ্চারণ করার সুযোগ না দিয়ে প্রশান্তবাবু প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ডাইনিং হল থেকে। সেখান থেকে শোনা গেল তাঁর থমথমে গলা, “কোথায় গেলেন মশাই! তাড়াতাড়ি আসুন। এরপর দেরি হয়ে যাবে আমার।”
মিংমার দিকে একবার ইশারা করে চটপট উঠে পড়লেন গোপীনাথ। মিংমাও তাঁর সঙ্গ নিলেন।
হোমস্টের আলো রাস্তায় খুব একটা পৌঁছয় না। রাস্তায় দূরে দূরে আলো। ডানদিকে ঘুরে দু’পা হাঁটলেই রীতিমতো অন্ধকার। কোনক্রমে সেই পর্যন্ত পৌঁছেই ঘুরে দাঁড়ালেন প্রশান্তবাবু। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে হাত বাড়িয়ে দিলেন গোপীনাথের দিকে; বললেন, “শিগগির দিন মশাই! শ্যামলী এসে পড়লে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।”
গোপীনাথ চওড়া হেসে বললেন, “যা ভয় দেখিয়েছি, তাতে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে রুমে যাওয়ারও সাহস হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”
এই বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন সকালে কেনা গোল্ড ফ্লেক কিং সাইজের প্যাকেটটা।
তাঁর হাত থেকে সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট বের করে প্রশান্তবাবু বললেন, “লাইটার! দেশলাই! কুইক, কুইক!”
অবশেষে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে মুখ আকাশের দিকে তুলে অসম্ভব আরামের সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়লেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যবসায়ী, পাঁচখানা ফ্যাক্টরির মালিক প্রশান্ত বসাক। তারপর ‘আআআহ্’ করে একটা শব্দ করলেন।
“আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, এই সময় একটা সিগারেটের বড্ড দরকার, বুঝলেন স্যার।” হাসিমুখে বললেন গোপীনাথ, “আমারও ওই ইয়ে খাওয়ার সময় একটু সিগারেট না হলে চলে না।”
প্রশান্ত বললেন, “বাঁচালেন মশাই! এই জাঁদরেল গিন্নির ভয়ে সিগারেট খাওয়াটা আজকাল একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত দামী স্কচ; সেও মেপে এক পেগ।”
“ডাক্তারের বারণ আছে বুঝি?” জিজ্ঞাসা করলেন গোপীনাথ।
“মোটেই না! আসলে ওঁর বাবা নাকি এসব খেতেন না, কাজেই… বাড়িতে অবশ্য আমিও খাই না। ওই বেড়াতে এসে এক-আধ পেগ। তাই নিয়েও তুলকালাম। তাই বলে এই সময় একটা সিগারেট না খেলে… তা আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ধরিয়ে ফেলুন একটা!”
সিগারেটটা ধরিয়ে হতাশ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন গোপীনাথ সেন। এই একটু আগেই কিনা তাঁর মনে হচ্ছিল, এতদিনে একজন সত্যিকারের পুরুষসিংহের দেখা পেয়েছেন! তিনি নাহয় ছোটখাট চাকরি করা সাদামাটা মানুষ। ইনি তো পাঁচখানা ফ্যাক্টরির মালিক!
আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির কোনও ভেদ নেই?
৫
সত্যি বলতে কী, এরকম কোনও নবদম্পতির দেখা পেলে গোপীনাথবাবুর বয়সী মানুষদের প্রথমেই যেটা মনে পড়তে বাধ্য, সেটা হল নিজের বিয়ের ঠিক পরের দিনগুলো। সত্যিই ওই সময় আকাশ একটু বেশি নীল লাগে, ট্রেনের ভিড় গায়ে লাগে না, বাজারের মাছওয়ালা পরেশ ওজনে ঠকাচ্ছে বুঝলেও খিঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। দেবযানীর মুখে, কপালের সিঁদুরে তখন জড়িয়ে থাকত স্বপ্ন আর লজ্জা। একদিন হয়েছে কী…
“ডিম লাগবে, স্যর। চিকেন শেষ। আজ রাতেই লাগবে। টম্যাটো সস খতম। আচ্ছা, তারপর…”
গোপীনাথবাবুর সমস্ত দিবাস্বপ্ন ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই যে ঈশ্বর রনিত থাপা নামের এক নবযুবককে ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন, সেটা তাঁর আগেও মনে হয়েছে। আজ শুধু এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন তিনি। নীরস গলায় বললেন, “লিস্ট করেছিস?”
“দিলীপ ভাই করছে।”
“দে। রাইকে দিয়ে আসি। ওর সাড়ে নটায় ট্রিপ না?”
“নটা বেজে গেছে তো! ও দিলীপ ভাই, জলদি লিস্ট বানাও!” বলতে বলতে কিচেনের দিকে ছুট লাগাল রনিত।
তিনখোলা থেকে পেডং শেয়ার গাড়ি চলে। দেড়শো টাকা করে ভাড়া। এই শেয়ার গাড়ির ড্রাইভাররাই পাহাড়ের কুরিয়ার বলো কুরিয়ার, হোম ডেলিভারি বলো হোম ডেলিভারি। গোপীনাথবাবুর কাজ হল পেডংয়ের দোকানদারকে ফোন করে দেওয়া, যদি অবশ্য লাইন পাওয়া যায়; আর রাইয়ের হাত দিয়ে লিস্টি পাঠিয়ে দেওয়া। দোকানিই রাইয়ের গাড়িতে মালপত্র প্যাক করে তুলে দেবে। রাই— মানে সুমন রাই প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফেরার সময় সেই মালের বস্তা আবার নামিয়ে দিয়ে যাবে হোমস্টে-তে। এসব সিস্টেম বুঝে নিতে গোপীনাথবাবুর লেগেছে সাকুল্যে তিনটে দিন; আর তার পিছনে যে আছে মিংমা তামাংয়ের ট্রেনিং, সে কথা বলাই বাহুল্য।
এই মুহূর্তে অর্পণ আর সৌমিলী দাঁড়িয়ে আছে কটেজের সামনে, কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুখ করে। এইমাত্র ওরা ফিরেছে ভিউ পয়েন্ট দেখে। এখনও ওদের মুখে-চোখে লেগে আছে মুগ্ধতা। আজকের সানরাইজটাও হয়েছে দুর্দান্ত। সব মিলিয়ে ওদের অবস্থা তাই, ভাল বাংলায় যাকে বলে মন্ত্রমুগ্ধ।
এবার গোপীনাথকে ডাইনিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখে একসঙ্গে হাত তুলল দুজনে। চেঁচিয়ে বলল, “গুড মর্নিং, আংকেল!”
“গুড মর্নিং, গুড মর্নিং!” এক গাল হাসলেন গোপীনাথ, “কেমন লাগল ভিউ পয়েন্ট থেকে তিস্তা? আজ তো কাঞ্চনজঙ্ঘাও একেবারে ক্লিয়ার!”
“দুর্ধর্ষ! আর ততটাই ভাল লেগেছে জঙ্গলের রাস্তাটা।” সৌমিলী বলল, “এক ধরনের পাখি দেখলাম, এইটুকুনি, কিন্তু খুব উজ্জ্বল কমলা রঙ বুকের দিকটা…”
“বললাম যে, ব্লু ফ্রন্টেড রেডস্টার!” বলে উঠল অর্পণ, “আরে বাবা, এইটুকু জানি!”
গাঢ় অবিশ্বাসের চোখে একবার বরের দিকে তাকিয়ে আবার গোপীনাথের দিকে তাকাল সৌমিলী, “সত্যি আংকেল? এই নামের কোনও পাখি আছে?”
এইবার একটু বিপন্ন বোধ করলেন গোপীনাথ। কাক শালিক চড়াই— এসবের বাইরে পাখির নাম বিশেষ জানা নেই তাঁর। আর তিনখোলার আশেপাশের জঙ্গলে নানান রঙের এন্তার পাখি আছে। হামেশাই চোখে পড়ে তারা। গোপীনাথ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন— এই পর্যন্তই। কিন্তু তাই বলে তাদের নাম বা কুষ্টিঠিকুজি জানার আগ্রহ কখনও বোধ করেননি। এখন তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, “না থাকার কী আছে? অর্পণ কি আর না জেনে বলছে?”
সৌমিলী খুব একটা কনভিন্সড হল না। আরও একবার অর্পণের দিকে তাকিয়ে বলল, “কে জানে বাবা! কাজ করে তো কম্পিউটার নিয়ে বসে বসে। জীবনে একটা বইয়ের পাতা উল্টে দেখেনি। জানল কবে এসব, ভগবান জানে।”
“কী মুশকিল! ওরে বাবা, আমি এককালে ক্যামেরা ঘাড়ে শুধু পাখির ছবি তোলার জন্য বর্তির বিল চলে গিয়েছিলাম। জানো সে কথা?”
গোপীনাথবাবু হেসে ফেলে বললেন, “তোমরা দুজনে কথা বলো। আমি চট করে একটু ঘুরে আসি। কিছু জরুরী কাজ আছে। স্ট্যান্ডে যেতে হবে একবার।”
সত্যিই এখন নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। গোপীনাথবাবু দৌড় পায়ে হাঁটতে লাগলেন গাড়ির স্ট্যান্ডের দিকে। রাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলে কপালে দুর্ভোগ আছে।
এই ছেলেমেয়ে দুটি গতকাল সকালে এসেছে। দেখলেই বোঝা যায় হানিমুন কাপল। চারদিন এখানেই থাকবে। মেয়েটি ভারী নরম-সরম; আর দিব্যি গুছিয়ে কথা বলতে জানে। প্রথম দিনই গোপীনাথবাবুকে বলেছিল, “বায়ুবদলের বায়ুগ্রস্ত হয়ে চারদিনে চারটি জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে কোনও লাভ হয় না। এক জায়গায় নোঙর নামিয়ে বসতে হয়। একমাত্র তাহলেই কোনও জায়গার আত্মাকে স্পর্শ করে চলে।”
এমনভাবে যে কথা বলা যায়, সেটাই জানা ছিল না গোপীনাথবাবুর। তিনি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিলেন মেয়েটির দিকে। ওর নাম সৌমিলী, বরের নাম অর্পণ, আইটিতে বড় চাকরি করে, দিন সাতেক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে— এইসব কথা মেয়েটিই বলে গিয়েছিল রিসেপশনে নামধাম লিখতে লিখতে। ভারী আলাপি মেয়ে। দিব্যি লেগেছিল গোপীনাথবাবুর। আর সবচাইতে বড় কথা হল, দুটিকে এমন সুন্দর মানিয়েছে যে, সে আর বলার নয়। দুজনেই বেশ লম্বা, রং ফর্সার দিকে, ধারালো কাটা কাটা মুখচোখ। সব মিলিয়ে একেবারে হরগৌরী কম্বিনেশন যাকে বলে। আজকাল আইটির দৌলতে অল্প বয়সেই চাকরি-বাকরি হয়ে যাচ্ছে কারো কারো। আর তারা আগেকার দিনের মতো হাপিত্যেশ করে বসে না থেকে টুক করে বিয়েটাও সেরে ফেলছে। এরাও তেমনই এক দম্পতি। দুজনেরই বয়স কম। রিসেপশনে যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল, স্বভাবতই গোপীনাথবাবু একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন— তাঁর যা বয়স হয়েছে, তাতে এরকম বয়সের ছেলেমেয়ে থাকতে পারত তাঁর।
স্ট্যান্ডের পাশেই এই গ্রামের একমাত্র দোকানটা। এখানে মোমো আর চা-সিগারেট পাওয়া যায়, আবার শাকসবজি, টুকিটাকি মনোহারি জিনিসপত্র থেকে শুরু করে মুদি দোকানের মালপত্রও কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাইয়ের হাতে জিনিসপত্রের লিস্টটা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেখানেই এসে বসলেন গোপীনাথ। আপাতত এক কাপ চা খেয়ে নেওয়ার মতো সময় আছে তাঁর হাতে।
এই দোকানটা চালায় সবিতা গুরুং। বয়েস গোপীনাথবাবুর ধারেকাছেই হবে, যদিও বাঙালিদের সর্বজনীন উপাধি হিসেবে সবিতা তাঁকে ডাকে ‘দাদা’ বলে। এখন তার উদ্দেশ্যে একটা হাঁক দিয়ে বাইরে পাতা চেয়ারটাকে রোদে টেনে নিয়ে গিয়ে আরাম করে বসলেন গোপীনাথবাবু। তিনি পাহাড়ে এসেছেন এখনও একমাসও হয়নি। অথচ নিজের ভিতরে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন টের পাচ্ছেন তিনি। শুধু তিস্তা, কাঞ্চনজঙ্ঘা বা পাইনের জঙ্গল নয়। এখানকার হাসিখুশি আর সোজাসাপ্টা লোকগুলোও তাঁকে চুম্বকের মতো টানছে। তার উপর তিনখোলা ছোট গ্রাম। সকলেই সকলকে চেনে। এই ক’দিনেই তাঁকেও সবাই চিনে গেছে। কাজেই এই দোকানের বাইরের চেয়ারে এসে বসা মানেই ঘণ্টাখানেকের আড্ডার ব্যবস্থা করে ফেলা। রাস্তার উল্টোদিকেই উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। তার গায়ে ঘন পাইনের বন। সেদিকে তাকিয়েও দিব্যি সময় কেটে যায়।
আজ অবশ্য তার আগেই তাঁর চোখে পড়ল, উদ্ভ্রান্তের মতো এদিকেই হেঁটে আসছে অর্পণ। যেভাবে চারদিকে তাকাচ্ছে, তাতে সন্দেহ হয়, সে বোধহয় কাউকে বা কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বভাবতই গোপীনাথবাবু হাত তুলে জোর গলায় বলে উঠলেন, “অর্পণ! এই যে, এদিকে! কিছু খুঁজছ নাকি?”
তাঁকে দেখতে পেয়ে যেন অকূলে কূল পেল অর্পণ। তাড়াতাড়ি করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, “আঙ্কেল, এখানে কোনও বইয়ের দোকান আছে?”
খাবি খেলেন গোপীনাথবাবু। এই অজ-পাড়াগাঁয়ে বইয়ের দোকান আসবে কোত্থেকে? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কেন বলো তো?”
একটু অধৈর্য গলায় অর্পণ বলল, “কেউ বইয়ের দোকান কেন খোঁজে আঙ্কেল? একটা বই দরকার আমার। এখানে নেট কানেকশন থাকলে দরকার হত না। কিন্তু…”
গোপীনাথবাবু খানিকক্ষণের জন্য কেমন একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি নিজে হানিমুনে গিয়েছিলেন দীঘায়। স্বপ্নময় সেই তিনটি দিন এখনও মাঝে মাঝে বড় সাইজের কাতলা মাছের মতো তাঁর হৃদয়ের ঝিলে ঘাই মারে। তখনও দেবযানী ভবানীপুরের ইতিহাস-বিশ্রুত দাশগুপ্ত পরিবার সংক্রান্ত ধর্মপ্রচার শুরু করেনি; টিঙ্টিঙে রোগা, ফর্সা এবং ট্রামলাইন পার হতে ভয় পাওয়া ওর বাবাকে নিয়ে বাঘ শিকারের গল্প-টল্প বলার সুযোগ পায়নি। এরকম সিচুয়েশন নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের কোনও গান না থাকায় বাধ্য হয়েই সি-বিচে বসে গোপীনাথ কেবলই গুনগুন করে গান গাইতেন, “এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার।”
কথা হল, হানিমুনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়— এমন দু-একটা জিনিসের নাম এখনও চেষ্টা করলে মনে করতে পারেন গোপীনাথবাবু। কিন্তু সেই তালিকায় বই নেই। মানে একেবারেই নেই। কাজেই বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ অর্পণের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, “বই লাগবে কেন? মানে বই দিয়ে এই সময় কোন কাজটা হবে?”
অর্পণ হতাশ ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “সৌমিলি যে কবিতা লেখে! ও যে বাংলা নিয়ে পিএইচডি করছে!”
গোপীনাথবাবু আরও হতভম্ব হয়ে গেলেন, “তাতে কী হল? ও কি এখন পড়তে বসবে নাকি? এই হানি… মানে বেড়াতে এসে? সামনে কোনও পরীক্ষা-টরীক্ষা আছে?”
“আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি যে ‘সোনার তরী’ কবিতাটা মুখস্থ বলতে পারছি না!”
এইবার গোপীনাথবাবুর মাথাটা সম্পূর্ণ গুলিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড অর্পণের বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, “তুমি আগে আমার পাশে বসো বাবা। বড্ড হাঁপিয়ে গিয়েছ। পাহাড়ের রাস্তাঘাট বড্ড উঁচুনিচু কিনা! ও সবিতাদি, জলদি-সে অওর এক কাপ চায়ে লাও।”
অর্পণ সত্যিই আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপাস করে গোপীনাথবাবুর পাশে বসে পড়ল। তারপর করুণ গলায় আবার বলল, “কাছাকাছির মধ্যে কোথাও বইয়ের দোকান নেই আঙ্কেল?”
কয়েক সেকেন্ড ভেবে গোপীনাথবাবু বললেন, “বইয়ের দোকান… মানে তোমার কী ধরনের বই চাই? পেডংয়ে দু-একটা দোকান আছে বটে, কিন্তু তাতে স্কুলের বই-টই পাওয়া যায়। তুমি তো বোধহয় বাংলা বই খুঁজছ? কাছেপিঠের মধ্যে সেভাবে বইয়ের দোকান বলতে সেই কালিম্পং। সেটাও মেইনলি ইংরেজি বইয়ের দোকান। বাংলা বই পাওয়া যায় কিনা, আমি ঠিক জানি না। তোমার কোন কবিতাটা দরকার বলো তো?”
অর্পণ একটু অধৈর্য গলায় বলল, “ওই যে বললাম— ‘সোনার তরী!’ বইটার নামও বোধহয় ওটাই। মানে আমার ঠিক জানা নেই। সৌমিলী বলল।”
এই সময় চা চলে এল। গোপীনাথবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, “চা খাও, চা খাও। এই তো একটু আগে দেখলাম দিব্যি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাখি-টাখি নিয়ে গল্প করছিলে, পাহাড় দেখছিলে। এই পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ সোনার তরী চলে এল কোত্থেকে?”
অর্পণ চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বলল, “চলে আসেনি আঙ্কেল! সারাক্ষণই সঙ্গে চলেছে!”
“কী চলেছে? তরী? মানে নৌকো? এই পাহাড়ের মাথায়?”
“কবিতা। দিনের মধ্যে বারো ঘন্টা কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকি, আর বাগ ফিক্স করি। বলুন দেখি, আমার কি কবিতা মুখস্থ করার সময় আছে? একটুখানি মেঘ করেছিল। সেই দিকে তাকিয়ে সৌমিলী বলল— ওই দ্যাখো, ‘গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।’ আমি বললাম, আজকে বর্ষা হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। একটু পরেই মেঘ কেটে যাবে। আর তুমি একেবারে ঘন বর্ষা এনে ফেললে? কেমন একটা বিচ্ছিরি চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ‘সোনার তরী’ পড়নি? আমি অতশত খেয়াল করিনি। বুক টান করে বললাম, ওটা সিলেবাসে ছিল না। বলল, এর পরের লাইন কী? এইটুকু না বলতে পারলে আজকে দুপুরে তোমায় ঘরে ঢুকতে দেব না। ভাবুন আঙ্কেল! এই সময়… মানে ইয়েতে… দুপুরবেলা যদি ঘরে ঢুকতে না দেয়…”
গোপীনাথবাবুর মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। তিনি একবার ঢোক গিলে বললেন, “দুপুরে ঘরে ঢুকতে দেবে না? সোনার তরী মুখস্থ না বলতে পারলে? কী ভয়ানক! কী সাংঘাতিক!”
“এর আগেও এরকম হয়েছে আঙ্কেল! বিয়ের আগে মোটে চার-পাঁচ দিন দেখা করেছি আমরা। অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ তো! প্রত্যেকবার তার আগের রাতে হোয়াটসঅ্যাপে একটা করে কবিতার ফার্স্ট লাইন পাঠিয়ে দিত। আমাকে গিয়ে সেইটা মুখস্থ বলতে হত। ইয়ে… মানে ফুলশয্যার রাতের জন্যও আলাদা কবিতা সিলেক্ট করে রেখেছিল! রবীন্দ্রনাথের ‘রাত্রে ও প্রভাতে।’ পুরোটা মুখস্থ না বলতে পারলে… এই দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে আঙ্কেল?”
গোপীনাথবাবু কাঁপা হাতে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, “তুমি এখান থেকেই খাও বাবা। বড্ড চাপ যাচ্ছে তোমার উপর! কিন্তু ওই কবিতাটাই কেন?”
“আপনিও জানেন না তার মানে। অবশ্য জানার কথাও নয়। ওই কবিতার ফার্স্ট লাইনগুলো হল… দাঁড়ান, এটা মুখস্থ ছিল। টেনশনে গুলিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে— ‘কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে, ফেনিলোচ্ছ্বল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে। তুমি চেয়ে মোর আঁখি ’পরে, ধীরে পাত্র লয়েছ করে, হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে।’ এবার বুঝতে পারছেন?”
সত্যি বলতে— যৌবন, চুম্বন, সরস— এই শব্দগুলো ছাড়া আর কিছুই গোপীনাথবাবুর মাথায় ঢুকল না। তবু ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন তিনি। মাথায় যে ক’টা চুল বাকি আছে, সেগুলোও ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল। তিনি আবার ফিসফিস করে বললেন, “কী ভয়াবহ! তোমার মনে ছিল? মানে ঠিকঠাক বলতে পেরেছিলে?
অর্পণ বলল, “না বলে উপায় আছে? ফেল করলে যে…! বিয়ের আগের রাত্তিরে বন্ধুরা যখন ছাদে বসে আমার পয়সায় ব্ল্যাক লেবেল খাচ্ছিল, আমি তখন ঘরে বসে দুলে দুলে কবিতা মুখস্থ করছিলাম! ভাবতে পারেন!” বলে ফস করে সিগারেট ধরিয়ে ফেলল।
“আর কী কঠিন কঠিন শব্দ!” বলে আরও একবার আঁতকে উঠলেন গোপীনাথবাবু।
“আর এবার হানিমুনে এসে ‘সোনার তরী’। এক রবীন্দ্রনাথই আমার জীবনটা শেষ করে দিলেন। বলেছে, ভাস্কর চক্রবর্তী পর্যন্ত পড়িয়ে ও আমাকে মানুষ করে দেবে। আমার সিলেবাসের লাস্ট কবিতা হল ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা।’ আচ্ছা আঙ্কেল, আপনি সুপর্ণা নামের কাউকে চেনেন? মৌসম ভবনে জিজ্ঞেস না করে, গুগলে সার্চ না করে তাকে কেন কবি জিজ্ঞেস করছেন— শীতকাল কবে আসবে? সে বেচারি জানবে কোত্থেকে? আর এই ভাস্কর চক্রবর্তীর বাড়ি কোথায়, আপনার জানা আছে আঙ্কেল?”
গোপীনাথবাবু এমন কোনও কবির নাম শোনেননি। কবিতার ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান মূলত ক্লাস টেনের সিলেবাস পর্যন্ত। ইনি বোধহয় তখনও লিখতেন না। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললেন, “না, আমি চিনি না তাঁর বাড়ি। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পেলে তুমি কী করবে বাবা?
“হাতে-পায়ে ধরে অন্তত আপাতত যাতে তিনি আর কবিতা না লেখেন, সেই ব্যবস্থা করতাম। নইলে সেগুলোও যে মুখস্থ করতে হবে আমাকে! যে ক’টা কমে, সেটুকুই লাভ। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হচ্ছে, সব রোমান্টিক কবিতা মুখস্থ হওয়ার আগেই আমি বুড়ো হয়ে যাব। তখন আর কবিতা মুখস্থ করেও লাভ হবে না।” বলে অর্পণ প্রায় দু’ মাইল লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল।
ওর কাঁদো কাঁদো মুখটার দিকে তাকিয়ে গোপীনাথের মনটা হু হু করে উঠল। আহা রে! কী কষ্টই না পাচ্ছে ছোকরা! বিষণ্ন গলায় বলেও বসলেন, “সামান্য একটা কবিতার জন্য এমন শীতের দুপুরে…”
অর্পণ একটু শিউরে উঠে বলল, “সামান্য একটা কবিতা! ভুলেও সৌমিলীর সামনে কথাটা বলবেন না! আমি একবার বলে ফেলেছিলাম। বারিস্তায় বসে তিন ঘণ্টা আটত্রিশ মিনিট ধরে আমাকে বাংলা কবিতার ইতিহাস পড়িয়েছিল। চারবার কফি নিতে হয়েছিল। স্ন্যাক্স সমেত সাড়ে চার হাজার টাকা বিল হয়েছিল। তার চেয়েও বড় কথা, বাড়ি ফিরে আমার জ্বর এসে গিয়েছিল, জানেন?”
“একসঙ্গে অত কবিতা শুনলে জ্বর আসবে না?” সহানুভূতির সুরে বললেন গোপীনাথ।
“এসব বাদ দিন।” অর্পণ বলল, “এখন কী করা যায়, সেটা বলুন প্লিজ। কালিম্পং চলে যাব একটা গাড়ি ভাড়া করে? কতক্ষণ লাগে এখান থেকে?”
গোপীনাথবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, “দাঁড়াও। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।”
“কী? বলুন, বলুন! এখন সবে সাড়ে নটা। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে যদি মুখস্থ করে ফেলতে পারি…”
গোপীনাথবাবু ওর কথায় কান না দিয়ে উঁচু গলায় বললেন, “সবিতাদি! ও সবিতাদি! আপনার মোবাইলটা একবার দিন দেখি!”
“ফির সে লাইন নেহি মিল রহা হ্যায়?” ফোনটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গোলগাল চেহারার সবিতা।
“লাইন নয়, নেটওয়ার্ক। এই ছেলেটার একটা জিনিস দরকার। এখানে একমাত্র বি.এস.এন.এল- এর লাইনটা মোটামুটি… বুঝলে অর্পণ… এইত্তো! এসেছে! সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা… এই তো পুরোটা খুলেছে! এইবার চটপট তোমার মোবাইলে টুকে নাও। তারপর মুখস্থ করে ফেলো।”
অর্পণ আরেকটু হলেই গোপীনাথবাবুকে প্রণাম করে ফেলছিল। সামলে নিয়ে বলল, “বাঁচালেন আঙ্কেল! আমি লিখে নিচ্ছি নোটপ্যাডে।”
“হ্যাঁ, তুমি লেখো। আমাকে এবার ফিরতে হবে। সবিতা দিদি! এই ছেলেটি আমাদের হোমস্টের গেস্ট। একটা জিনিস তোমার ফোন থেকে লিখে নিচ্ছে। পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।”
চায়ের টাকা মিটিয়ে রওনা দিলেন গোপীনাথবাবু। একটা বিপন্ন প্রাণকে উদ্ধার করতে পেরেছেন, এই ভেবে মনটা বেশ হালকা লাগছে তাঁর।
পেডং যাওয়ার রাস্তা থেকে বাঁদিকে পাইনবনের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা উঠে গেছে, সেটাই গিয়েছে মেঘমা হোমস্টের দিকে। এই রাস্তায় একটাই বাড়ি, ফলে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। দু’দিকে ঝুপসি জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে একেবেঁকে চলে গেছে চকচকে কালো রাস্তা। এখন সেই রাস্তায় ঘন নীল আকাশের রং পিছলে যাচ্ছে। পাখির ডাক, আর দূর থেকে ভেসে আসা গাড়ির হর্ন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। আর একটু এগোলেই হর্নটাও শোনা যাবে না।
পাহাড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এইবার ডাইনে বাঁক নিয়েছে রাস্তা। পিছনের রাস্তা বা সামনের হোমস্টে— কিছুই দেখা যায় না এখান থেকে। সেই অনাবিল নির্জনতার মাঝখানে এসে হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ালেন গোপীনাথবাবু।
আজ একটা মোদ্দা কথা বুঝতে পেরেছেন তিনি। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই বোধহয়, যে বউকে ভয় খায় না। যে ক’জন অমন সিংহহৃদয় পুরুষ ছিল, তাদের খুব সম্ভবত সরকার সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে সযত্নে কোনও অভয়ারণ্যে লুকিয়ে রেখেছে।
কিন্তু ওটুকু ভয়ে ভালোবাসা কিছু টোল খেয়ে যায় না। ও হল বাঙালি চাউমিনের উপর ছড়িয়ে দেওয়া টোম্যাটো সস। ওটা না থাকলে দাম্পত্যের স্বাদ হত না।
আরও একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলেন গোপীনাথবাবু। তাঁর রোগা বুকটা ফুলে উঠল পাহাড়ের ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার হাওয়া ঢুকে।
নাহ্, এবার ফিরে যাবেন তিনি। বরাবরের জন্য নয় অবিশ্যি। কিন্তু একবার ফেরা চাই। চাকরিটা ছেড়ে দেবেন এবার পাকাপাকিভাবে। অনেকদিন তো করলেন। যথেষ্ট হয়েছে। বাপ্পাকে ফোন করে বলে দেবেন— এখন থেকে তিনি এখানেই থাকবেন। এই তিনখোলায়। হোমস্টের ম্যানেজারের চাকরিটা তিনি আর ছাড়বেন না। বাপ্পা নিজেও ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, কাজটা তিনি নেহাত মন্দ চালাচ্ছেন না। গেস্টরা ফিরে গিয়ে চমৎকার রিভিউ দিয়েছেন। প্রশংসা করেছেন প্রাণ ভরে। খুব খুশি তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুটি। আর ছেলেবেলার বন্ধুর মানরক্ষা করতে পেরে গোপীনাথবাবুও যে বেজায় খুশি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানকার ঠাণ্ডা হাওয়া, পাইনের বন আর কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তিস্তা, এখানকার লোকজন— এসব ছেড়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। তার উপর প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে…
শুধু দেবযানীর না থাকাটা বড্ড ভোগাচ্ছে তাঁকে। সস ছাড়া চাউমিন। ধুস!
এইবার ফিরে গিয়ে দেবযানীকেও নিয়ে আসবেন তিনি। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসতে একটু হিম্মতের দরকার হবে বটে, কিন্তু সেটুকু এই পাহাড় ইতিমধ্যেই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে রাতের দিকে এই রাস্তা ধরে ফেরার সময় সত্যি সত্যিই লেপার্ডের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। কিচ্ছু করেননি। চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন শুধু। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে ফের ডানপাশের খাদের জঙ্গলের মধ্যে নেমে গিয়েছিল লেপার্ড।
এখন দেবযানীকে বোঝানোর মতো সাহস তাঁর হয়েছে বৈকি! বোঝাতে হবে— দুনিয়াটা মস্ত বড়, আর খাসা সব লোকজনে ভরা। সবাই যে ভাল, এমন নয়; তবে ওই— সকলেই যে মন্দ, এমনও নয়। তারা নানান ধরনের। আর সেটাই মজা।
সে বেচারি কেমন আছে, কী করছে— কে জানে?
বাপ্পাকে ফোন করে তৎকালের টিকিট কাটতে বলে দেওয়া যাক বরং।
যাওয়ার একটা, ফেরার দুটো।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন
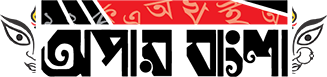
এবারের পুজোর প্রথম পুজোবার্ষিকীর প্রথম পাঠ। দারুণ লাগল।
খাসা গল্প, থুড়ি উপন্যাস। গোপীনাথ বাবুর কথা পড়তে পড়তে বাবার কথা মনে পড়ছিল!