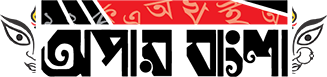রনির অসুখ
ভগীরথ মিশ্র
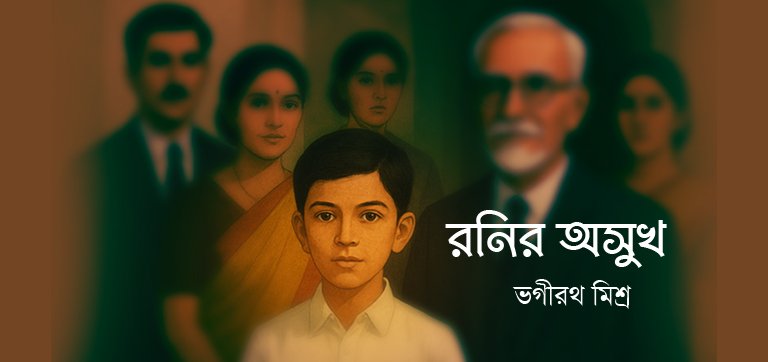
পর্ব – ১
১
অন্তরা’র মুহুর্মুহু তাড়নায় ড্রইংরুমের দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে এতদিন বাদে হঠাৎই যারপরনাই বিস্মিত হ’ন সৌম্যদেব৷
সহসা তাঁর মনে হয়, ঘড়িটা বুঝি ব্যাটারি কমে যাবার দরুণ না-চলার মতো করেই চলছে৷ আর, ওই থেকেই বিস্ময়টা পয়দা হয় মনে৷
মনে পড়ে যায়, সেই কতকাল আগে ওদের স্কুলের ফিজিক্সের স্যার ব্রতীনবাবু আইনস্টাইনের থিয়োরি অব্ রিলেটিভিটি বোঝাতে গিয়ে সর্বপ্রথম সৌম্যদেবের মনের মধ্যে এই বিস্ময়ের বীজটি পুঁতেছিলেন৷ এমন একটি বিষয়কে তিনি উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সেদিন, ভাবতে গিয়ে বিস্মিতই হয়েছিলেন সৌম্যদেব৷ সেই কারণেই আজও ভোলেননি সৌম্যদেব, অমন কঠিন একটা থিয়োরি, অথচ ক্লাস টেনের ছাত্র হয়েও তত্ত্বটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গিয়েছিলেন৷ পরবর্তীকালে, জটিল তত্ত্বটা বোঝাতে গিয়ে, কতজনের কাছেই যে ওই উদাহরণটা ব্যবহার করেছেন!
আসলে, এমনিতে আমরা সবাই জানি ওটা৷ সকলের ক্ষেত্রে সেটাই হয়৷ বন্ধুদের সঙ্গে যখন চুটিয়ে আড্ডা মারছি, তিন-ঘন্টা যে কখন কেটে গেল, টেরই পেলাম না৷ আবার, চরম দুঃসময়ে, বিপদের কালে, তীব্র উদ্বেগ নিয়ে যখন কোনও-কিছুর অপেক্ষা করছি, তখন দেখছি, সময় যেন কিছুতেই কাটছে না৷ পরীক্ষার হলে যখন হাতে আর মাত্র কুড়ি মিনিট সময় রয়েছে, অথচ দেড়খানা জানা প্রশ্নের জবাব তখনও অবধি লিখতে বাকি, তখন ঝড়ের বেগে লিখে চলেছি, আর ঘন ঘন মুখ তুলে ঘড়ি দেখছি৷ অবাক হয়ে লক্ষ করছি, সময় যেন দুরন্ত এক্সপ্রেসের গতিতে ছুটে চলেছে৷ একসময় ঢং-ঢং করে বেজে উঠল ফাইনাল বেল, আর আমার মনে হল, কুড়ি মিনিট সময়টা যেন দু’মিনিটের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল! আবার, কেউ মারা গেলে ওর শোকসভায় যখন মাত্র একমিনিটের নীরবতা পালন করছি, স্পষ্ট মনে হয়, মাত্র এক মিনিট, অর্থাৎ ষাটটি মাত্র সেকেন্ড, অথচ কত দীর্ঘ! যেন কাটছেই না, কাটছেই না…! কিন্তু এটাই যে হরেদরে রিলেটিভিটি তত্ত্বের মূল কথা, এটা যেদিন ব্রতীনবাবু বুঝিয়ে বললেন, সৌম্যদেব বিস্মিত হয়েছিলেন এটাই ভেবে যে, এমন একজন মানুষের মাথা খাটিয়ে আবিষ্কার করা এমন একটি জটিল তত্ত্বের মূল কথাটি হরেদরে এটাই!
নিজেদের ড্রইংরুমে বসে এতদিন বাদে আইনস্টাইনের ওই তত্ত্বটাই উঠে আসে সৌম্যদেবের ভাবনায়৷ বাস্তবিক, নিজেদের চরম উদ্বেগের মুহূর্তে সময় যেন কাটছেই না৷ সেই কত আগে দেয়াল-ঘড়িটায় দেখেছিলেন পাঁচটা ছাব্বিশ৷ অথচ এতক্ষণ বাদে মাত্র পাঁচটা ঊনত্রিশ! এতক্ষণ বাদে মাত্র তিন মিনিট কাটল! অথচ সৌম্যদেবের মনে হচ্ছিল, না-হোক আধঘন্টা-চল্লিশ মিনিট!
বিষয়টাকে নিয়ে সৌম্যদেব আরও বিস্মিত হয়েছেন চিরটাকাল৷ কারণ, তাঁর বিবেচনায়, ব্যাপারটা সব্বাই জানে, দুনিয়ার সব্বাইয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে এটা, আনন্দের মুহূর্ত অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কেটে যায়, আবার দুঃখের মুহূর্তগুলি যেন কাটতেই চায় না কিছুতেই। অথচ ওটা যে বিজ্ঞানের দুনিয়াটাকে নাড়িয়ে দেবার মতো একটা যুগান্তকারী তত্ত্বের মূল কথা, আইনস্টাইন সাহেব বলে দেবার আগে কে-ই বা জানত!
কিংবা ধরা যাক, নিউটনের মাধ্যাকর্ষ তত্ত্বের ভিত্তি-কাহিনিটি৷ নিউটন বসে ছিলেন পার্কে৷ আচমকা ওঁর চোখের সমুখে গাছ থেকে একটা আপেল পড়ল মাটিতে৷ এদেশের কেউ হলে তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলত, কিন্তু নিউটন ব্যাপারটা নিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন, কিনা, আপেলটা বোঁটা থেকে খসে মাটিতেই-বা পড়ল কেন? বোঁটাচ্যুত হওয়ামাত্র মহাকাশের দিকেও তো ছুটে যেতে পারত৷ ব্যস, শুরু হল ভাবনা, আর তার ফলে দুনিয়া পেয়ে গেল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওলোট-পালোট ঘটিয়ে দেবার মতো একটি তত্ত্ব!
ওই নিয়ে ক্রমশ ভাবনার অতলে যাচ্ছিলেন বুঝি সৌম্যদেব, কিন্তু সহসা অন্তরা’র কথায় ভাবনা-জালটি কেটে যায়৷
অন্তরা গলায় আরও খানিক উদ্বেগ মিশিয়ে বলে ওঠেন, ওরা আসছে না কেন বলো তো?
আর, ওই মুহূর্তে সৌম্যদেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন, পাঁচটা ঊনত্রিশ!
মনের মধ্যে যত উদ্বেগই তৈরি হোক, কিছুতেই একেবারে হেদিয়ে পড়েন না সৌম্যদেব৷ একেবারে ছেলেবেলা থেকেই এটা রয়েছে ওঁর মধ্যে৷ স্কুলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও কৃতী ছাত্র হয়েও, অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্নপত্রটি হাতে আসামাত্র সৌম্যদেব দেখেন, তাঁর মতো ছাত্র, যে-কিনা সব পরীক্ষাতেই অঙ্কে একশো’তে একশো পেয়েছে, সেই কিনা টেনেটুনে বড়জোর চল্লিশ নম্বরের জবাব দিতে পারবে৷ গোটা হল জুড়ে ওই মুহূর্তে কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেলেও, সৌম্যদেব কিন্তু ভেঙে পড়েননি৷ কঠোর ধৈর্যে বেঁধেছেন বুক৷ ঠাণ্ডা মাথায় প্রশ্নগুলোকে আবারও পড়েছেন…বারবার৷ প্রশ্নের গভীরে ঢুকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন৷ অবশেষে ওই প্রশ্নপত্র দিয়েই পঁচাত্তর নম্বরের জবাব লিখে এসেছেন খাতায়৷
আজ বোঝেন, কেবল মনের মধ্যে অখণ্ড ধৈর্য ছিল বলেই ওই সাফল্যটুকু পেয়েছিলেন সেদিন৷ অস্থির হয়ে ছোটাছুটি জুড়ে দিলে ক্লাসের অন্যদের মতো নির্ঘাত ফেল করতেন ওই পরীক্ষায়৷ সৌম্যদেব সান্যাল, অবিশ্বাস্য মেধার অধিকারী হিসেবে যাঁর নাম তখনই ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়, তিনি কিনা, অ্যানুয়াল পরীক্ষায় একটা বিষয়ে ফেল!
এই যে চরম বিপদের মুহূর্তেও অস্থির হয়ে ওঠেন না, এটা বাবা অনঙ্গমোহনই তিলতিল শিখিয়েছেন সৌম্যদেবকে৷ বীরভূমেরই একটা হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন অনঙ্গমোহন৷ শিক্ষক হিসেবে তিনি গোটা জেলায় অনুকরণীয় একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন৷ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়েছিলেন অনঙ্গমোহন৷
শিশুকালে সৌম্যদেবকে বিছানায় নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দেশ-বিদেশের কত কাহিনি যে শোনাতেন অনঙ্গমোহন! কাহিনির বাইরে আরও কত কথাই যে বলতেন! আর, এমনভাবে বলতেন, শিশুমনে একেবারে গভীর হয়ে ঢুকে যেত তা৷
রবার্ট ব্রুশের গল্পটা মাঝে মাঝেই বলতেন অনঙ্গমোহন৷ বলতেন, বিপদে পড়লে দশজনের মধ্যে ন’জনই ঠাকুরের কাছে কী চায় বল্ তো খোকা?
ওই বয়েসের ক্ষুদ্রবুদ্ধি নিয়ে সৌম্যদেব জবাব দিতেন, যেন বিপদ থেকে তিনি বাঁচিয়ে দেন৷
—- তাই তো? অনঙ্গমোহন বুঝি দ্বিগুণ উৎসাহ পেয়ে যেতেন, কিন্তু কবিগুরু তা চাননি৷ তিনি ঠাকুরকে একবারের তরেও বলেননি, এই বিপদ থেকে আমায় বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর৷ তিনি তবে কী চেয়েছেন ঠাকুরের কাছে? বলেই উদাত্ত গলায় আবৃত্তি জুড়তেন অনঙ্গমোহন, বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা, / বিপদে যেন না করি আমি ভয়—৷ তাহলেই বোঝ্, বিপদের মুহূর্তে ভয় পেতে নেই, ঘাবড়ে যেতে নেই, অস্থির হয়ে উঠতে নেই। ওই মুহূর্তে যদি ঠাণ্ডা মাথায় বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজিস, সেইমতো চেষ্টা করিস, তবে যত বড় বিপদই হোক, তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবিই পারবি৷ কিন্তু বিপদে ভয় পেলে, ঘাবড়ে গেলে, অস্থির হয়ে ছোটাছুটি জুড়ে দিলে, অল্প বিপদও বড়-বিপদ হয়ে দাঁড়ায়৷
বাবার কথাগুলো আজীবনকাল মন্ত্রের মতো মেনে এসেছেন সৌম্যদেব৷ ফলটাও পেয়েছেন হাতে হাতে৷ নিচু ক্লাসে অঙ্কের পরীক্ষাতেই কেবল নয়, আজ, এতদিন বাদে, নিজেদের কোম্পানিতেও বসদের বিবেচনায়, ক্রুশিয়াল মুহূর্তে মিঃ সান্যালের জবাব নেই৷ ধৈর্য তো হারানই না, বিপদ যত জটিল হয়, মিঃ সান্যালের মগজটি ততই ঠাণ্ডা হতে থাকে! বারংবার ওটা দেখে দেখে, মালিকপক্ষের কাছে তিনি এখন সাক্ষাৎ মিঃ কুল৷
না, এজন্য কোনও অলৌকিক টোটকা নেই সৌম্যদেবের কাছে৷ কেবল ছেলেবেলায় বাবার শেখানো, ওই একটি মোক্ষম কথা, বিপদে ভেঙে পড়তে নেই, ধৈর্য হারাতে নেই, তাহলেই সোজা বিপদটি বাঁকা হয়ে ওঠে৷ ছোট্ট বিপদটিও দুরতিক্রম্য হয়ে যায়৷ ওই একপংক্তির মন্ত্রটি, বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা, / বিপদে যেন না করি আমি ভয়…৷ ওই মন্ত্রটাই সমস্ত জাদুর মূল কথা৷
কিন্তু অন্তরা ঠিক এর উল্টো৷ সামান্য সমস্যাতে এমনই ভয় পেয়ে যায়! আর ভয় পেলেই এমনই ভুলভাল পরামর্শ দিতে থাকে, এমনই সারাক্ষণ অস্থির করে মারে সৌম্যদেবকে! বাস্তবিক, ইদানীং পারিবারিক কোনও সমস্যায় পড়লে তার সমাধান করতে যদি একটুখানি বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় সৌম্যদেবকে, যদি একটুখানি বেশি বিব্রত হতে হয়, তবে তা স্রেফ অন্তরা’র কারণেই৷ এমন চেঁচিয়ে, ভয় পেয়ে, অস্থির হয়ে, ছটফট করতে থাকবে, মিনিটে মিনিটে এমনই তাড়া দিতে থাকবে সৌম্যদেবকে, মুহুর্মুহু এমন ভুলভাল পরামর্শ দিতে থাকবে, সোজা জিনিসটাও জটিল হয়ে উঠবে৷ উঠবেই।
এমনিতেই সৌম্যদেবদের ড্রইংরুমটা বেশ সুসজ্জিত৷ একটা মাল্টি-ন্যাশন্যাল কোম্পানির সিনিয়র এক্জিকিউটিভের মতো অর্থবান মানুষের ড্রইংরুম যতখানি সাজানো গোছানো হওয়া উচিত, তার চেয়েও বেশি সুসজ্জিত বলেই মনে হয় সৌম্যদেবের৷ এর জন্য যাবতীয় কৃতিত্ব অন্তরা’রই প্রাপ্য৷ ও-ই চারপাশ থেকে তিলে তিলে সংগ্রহ করেছে যাবতীয় মহার্ঘ সামগ্রী৷ ওই দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে বাড়ির বহির্কক্ষটি৷
দামি সোফা-কৌচ, দামি শো-কেস, মহার্ঘ টি-পয়, পায়ের তলায় পুরু কার্পেট, দেয়ালে দুর্মূল্য-সব পেন্টিং…৷ কিন্তু সবকিছু দিয়ে মোড়া সৌম্যদেবদের ড্রইংরুমটি জুড়ে আজ এই মুহূর্তে শ্মশানের স্তব্ধতা৷ সোফায় পাথরের স্তব্ধতায় বসে রয়েছেন সৌম্যদেব৷ অন্তরা কখনো বসছেন পাশটিতে, কখনো-বা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে ঘনঘন তাকাচ্ছেন দেয়াল-ঘড়ির দিকে…, আর, নিজের ঘরে শুয়ে রয়েছে নিজেদের একমাত্র ছেলে রনি৷ এই মুহূর্তে সে-ই অন্তরাদের যাবতীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারিগর৷
আর, বাইরে কোথাও, সম্ভবত, পাড়ার ক্লাবেই বেজে চলেছে একটি হিন্দি গানের কলি, – ‘মাম্মি…মাম্মি, তেরি মুন্না বিগড়্ যায়ে….’। সেই গানের মৃদু আওয়াজ ভেসে ভেসে এসে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সৌম্যদেবের কানে৷
অন্তরা অধীর গলায় বলে ওঠেন, দিদি-জামাইদা’রা এখনও আসছে না কেন বল তো? আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না৷
বাস্তবিক, এই মুহূর্তে অন্তরার কাছে দিদি সুরূপা আর জামাইদা মৃন্ময়ই একমাত্র আশ্রয়৷ কেবল যে বয়েসেই বড় তাই নয়, একটি মাল্টি-ন্যাশন্যালের কর্তাব্যক্তি মৃন্ময়ের বিচারবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ওপর চিরকালই বেজায় ভরসা অন্তরা’র৷ সে পদে পদে দেখেছে, মৃন্ময় সর্বদাই সাহেবদের মতোই সুসজ্জিত, ফিটফাট৷ বুদ্ধিদীপ্ত, ক্যারিয়ারিস্ট, করিতকর্মা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ৷ সমস্ত ধরনের পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় ট্যাকেল করতে ওস্তাদ৷ জটিল সমস্যায় ও কঠিন সংকটেও তিলমাত্র বিচলিত হ’ন না৷ এই সবকিছুর জন্য অন্তরা’রা ওকে খুব মানে৷ বলতে গেলে, মৃন্ময় অন্তরাদের পরিবারের অভিভাবকতুল্য৷ এই বিপদের মুহূর্তেও, সেই কারণেই, প্রথমেই অন্তরা’র মনে হয়েছিল মৃন্ময়ের কথা৷ টেলিফোনে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বায়না ধরেছিল, জামাইদা, আপনি একটিবার চলে আসুন, প্লিজ৷ আমার বড্ড ভয় করছে৷
এই মুহূর্তে খুব মুহ্যমান লাগছিল সৌম্যদেবকে৷ খবর-কাগজের একটি নির্দিষ্ট পাতায় চোখদুটি পেতে রেখেছেন তিনি সেই তখন থেকে৷ কিন্তু অন্তরাও জানেন, এক বর্ণও পড়ছেন না তিনি৷ পড়ায় মনই লাগাতে পারছেন না৷
অন্তরা’র কথায় খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ তোলেন সৌম্যদেব, তুমি ঠিক ক’টায় ফোন করেছিলে সুরূপাদিকে?
—তোমাকে ফোন করেই তো দিদিকে করলাম৷ এই ধরো পৌনে পাঁচটা৷
—তাহলে তো এতক্ষণে এসে পড়া উচিত৷ তবে, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, কেউ চাইলেও রাইট-টাইমে পৌঁছতে পারবে না৷ এখন তো আবার অফিস ছুটির সময়৷
বলেই পুনরায় খবরের কাগজের পাতায় মুখ লুকোন সৌম্যদেব৷
আসলে, অন্তরা’র সীমাহীন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার আক্রমণ থেকে এভাবেই নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন তিনি৷ অন্তরা’র এই মুহূর্তের অস্থিরতা যাতে ছোঁয়াচে রোগের মতো তাঁর মধ্যেও সংক্রামিত না হয়, সেই চেষ্টাই করে চলেছেন৷ ওই ফাঁকে নিজের শান্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মগজটি সমানে বিশ্লেষণ করে চলেছে, রনি আজ কেন ঘটাল এমন অস্বাভাবিক ঘটনাটি!
একসময় খবরের কাগজের আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে আসেন সৌম্যদেব৷ অন্তরা’র দিকে তাকিয়ে শুধোন, রনি ও-ঘরে কী করছে?
—কে-জানে! অন্তরার সারা মুখে রাজ্যের বিরক্তি, টিনটিন পড়ছে, নয়তো ঘুমোচ্ছে..নয়তো…ধুশ আমার শরীরটা কেমন জানি কচ্ছে৷ এখনও অবধি আসছে না কেন গো ওরা?
ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজায় কলিং বেল বেজে ওঠে৷
২
সদর দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ শোনামাত্র অন্তরা’র সারা শরীর বেতস লতার মতো সোজা হয়ে ওঠে৷ সমগ্র ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ঔৎসুক্য নিয়ে তাকান সদর-দরজার দিকে৷
— ওই বুঝি ওরা এল!
সৌম্যদেব তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ান৷ দ্রুতপায়ে হাঁটা দেন দরজার দিকে৷ এক ঝটকায় দরজাটা খুলে দেন৷
দরজার বাইরে সুরূপা আর মৃন্ময় দাঁড়িয়ে রয়েছেন৷ সুরূপার চোখেমুখে গাঢ় উদ্বেগ থাকলেও মৃন্ময়ের মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত৷
সুরূপা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন৷ মৃন্ময় বেশ ছন্দোবদ্ধ পায়ে ঘরে ঢুকে সোফায় গ্যাঁট হয়ে বসেন৷
সুরূপার যেন তর সইছিল না৷ সারা মুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে শুধোন, কী হয়েছে রে? রনি কী করেছে?
সহসা এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে উঠতে পারেন না অন্তরা৷ মৃদু গলায় বলেন, বলছি৷ কিন্তু তোরা এত দেরি করলি কেন?
— বা-রে, তুই তো ফোনে কিছুই খুলে বললি না৷ কেবল তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললি৷ আমি ভাবি কী-না-কী! ভাবলাম, তেমন যদি কিছু ঘটে থাকে, তবে আমি একা গিয়ে করব কি? বিপদের সময় আমি আবার ঘাবড়ে যাই৷ ভাবলাম, তোর জামাইদাকেও ডেকে নিই৷ তুইও তো ওকে ফোন করেছিলি৷ তো, সে একটা জরুরি মিটিং কনডাক্ট করছিল৷ ফোন পেয়ে আসতে তো খানিক দেরি করলই৷ কিন্তু হয়েছেটা কি? রনি কোথায়? তোদেরই বা এমন দেখাচ্ছে কেন?
অন্তরা খুব অসহায় দষ্টিতে মৃন্ময়ের দিকে তাকান৷ চোখদুটো সহসা ছলোছলো হয়ে ওঠে৷
অন্তরা’র চোখমুখ দেখেও বড়-একটা উদ্বেগ ফোটে না মৃন্ময়ের মুখে৷ খুব নির্বিকার গলায় বলেন, এনিথিং রং?
জবাব দিতে গিয়ে গলাটা ধরে আসে অন্তরা’র৷ সহসা আঁচলে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কান্না জোড়েন৷ তাতে করে সুরূপার চোখেমুখে উদ্বেগটা আরও বেড়ে যায়৷
অস্থির গলায় বলে ওঠেন, আরে, কী হয়েছে, বলবি তো?
— আমার আর তিলমাত্র বাঁচতে ইচ্ছে করে না দিদি৷ সহসা কান্নায় ভেঙে পড়েন অন্তরা, এই ছেলেই আমায় বাঁচতে দেবে না৷ আমার পূর্বজন্মের শত্তুর!
মৃগাঙ্ক খুব ক্যাজুয়াল দৃষ্টিতে তাকান অন্তরা’র মুখের দিকে৷ বলেন, কী করেছে রনি?
অন্তরা সহসা স্বামীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকান, চুপ করে রয়েছ কেন? বল না৷
— আমি কী বলব? আমি তো ছিলামই না৷ তোমার ফোন পেয়েই তো তড়িঘড়ি ছুটে এলাম৷ তুমি দেখেছ, তুমি বল৷
অন্তরার দিকে তাকিয়ে মৃগাঙ্ক খুব নিরুত্তাপ গলায় পুনরায় বলেন, কী হয়েছে, খুলে বল দেখি?
অন্তরা খুব ধীরপায়ে হেঁটে গিয়ে সৌম্যদেবের পাশটিতে বসেন৷ বলেন, শুনবেন? ওইটুকুন ছেলে কী পরিমাণ পাজি আর ধড়িবাজ হয়েছে! শুনুন তবে৷ স্কুল থেকে ফিরেছে দুটোয়৷ ললিতা পড়াতে আসবে চারটেয়৷ আমি ওর গা মুছিয়ে পাউডার মাখিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বললাম, রনিসোনা, তুমি হোমটাস্কগুলো করতে থাকো৷ কিংবা টিনটিন পড়৷ কিংবা ছবি-টবি আঁক৷ আমি একটুখানি তৃষা-আন্টিদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি৷ ও নাকি একটা ভ্যাক্যুয়াম-ক্লিনার কিনেছে৷ বারবার দেখতে ডেকেছে৷ আমি যাব আর আসব৷ আর, ললিতা-আন্টি এলে ওর কাছে পড়তে বসে যেও৷
— কিন্তু—ও মা—! সোওয়া-চারটে নাগাদ ফিরছি, মোড়ের মাথায় ললিতার সঙ্গে দেখা৷
বলল, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে বৌদি? আমি তো বাড়িতে কাউকে না দেখে ফিরে যাচ্ছি৷
বললাম, সে কি! রনি বাড়িতে নেই?
ললিতা বলল, না তো৷ দরজায় তো তালা লাগানো৷
ততক্ষণে সুরূপার সারা মুখ জুড়ে দুশ্চিন্তার মেঘ জমেছে৷ বলেন, সে কি! তারপর?
— আমার বুকের মধ্যে তখন কী যে হচ্ছে, দিদিভাই! অন্তরা’র গলায় নিপাট ভয়, তড়িঘড়ি বাড়ি এসে দেখি, বারান্দার গ্রীলে তালা লাগানো! আমার মনের অবস্থাটা তখন ভাবো!
সুরূপা সারা মুখে একরাশ দুশ্চিন্তার মেঘ জমিয়ে শুধোন, তারপর?
— কী করি, কোথা যাই—, পাশের পার্কটায় রোজদিন কিছু ময়লাগোছের বাচ্চা খ্যালে৷ সাত-পাঁচ ভেবে ছুটতে ছুটতে গেলাম পার্কে৷ যদি মূর্তিমান গিয়ে থাকে ওখানে৷ কিন্তু না, সেখানেও নেই৷ আমি চটজলদি ফোন করলাম সৌম্যকে৷ তোকেও ওইসঙ্গে৷ তারপর মৃন্ময়দাকে৷ …ওইসব করে-টরে যখন ফিরলাম, দেখি, মূর্তিমান তালা খুলে ঢুকছে! জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গিয়েছিলি? জবাব দেয় না কিছুতেই৷ তারপর…একটু বাদেই সৌম্য ফিরল৷ সেও কত্তো পীড়াপীড়ি করল৷ কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলছে না!
বলতে বলতে গলাটা পুনরায় ধরে আসে অন্তরা’র৷ কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, অথচ এর অর্ধেক জেরায় হার্ড-কোর ক্রিমিন্যালরাও সবকিছু কবুল করে ফেলে৷ সত্যি বলছি দিদিভাই, ওর ভাবগতিক দেখে আমার তো হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার জোগাড়!
সুরূপা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন অন্তরা’র কথাগুলো৷ ভুরু কুঁচকে বলেন, কিছুই বলছে না?
—সেটাই তো বলছি৷ ছেলেটা ভেতরে ভেতরে যে এতটা পাজি হয়েছে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা হয়৷
সুরূপা এতক্ষণে সত্যি সত্যি নিদারুণ ভাবনায় পড়ে যান৷ বলেন, কিন্তু তোর কী মনে হচ্ছে? কোথায় গিয়েছিল ও? এতক্ষণ কোথায় ছিল?
— আমি যদি ওটার আন্দাজ পেতাম, তাহলে তো—৷ অন্তরা গলায় যাবতীয় বিরক্তি ফুটিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকান, ওকেই জিজ্ঞেস কর্৷ দরজায় তালা লাগিয়ে কোথায় গিয়েছিল, ও-ই বলুক৷ আমরা তো শুধিয়ে শুধিয়ে আলা৷
মৃন্ময়ের কিন্তু তখনও অবধি নির্বিকার মুখ৷ ওই মুখে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই৷
একসময় একটা দামি কিং-সাইজ সিগারেট ধরান মৃন্ময়৷ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে খুব সাবলীল গলায় শুধোন, রনি কোথায়?
— ওই তো শোবার ঘরে৷ ডাকব?
— একটুখানি ডাকো না ওকে৷
অন্তরা গলা ছেড়ে ডাক পাড়েন, রনি—৷ সাড়া না পেয়ে কড়া গলায় ধমক লাগান, রনি—, তোমার ভালো-মেশো তোমায় ডাকছেন—৷
সবাই একদৃষ্টিতে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে৷
একটুবাদে ড্রইংরুমে ঢোকে রনি৷ ঘুম-ঘুম চোখদুটিতে চাপা ভয়৷ আড়চোখে অন্তরা’র দিকে একঝলক তাকিয়ে নেয়৷ দরজার মুখে দ্বিধাগ্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে৷
হুকুমের সুরে অন্তরা বলেন, যাও, ভালো-মেশোর কাছে গিয়ে বোসো৷
রনি এগিয়ে গিয়ে মৃন্ময় ও সুরূপার মাঝখানটিতে গিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বসে৷
অন্তরা প্রায় হুকুমের স্বরে বলে ওঠেন, ভালো-মেশো যা জিজ্ঞেস করছেন—৷
অন্তরাকে কথাটা শেষ করতে দেন না মৃন্ময়৷ মাঝপথেই হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দেন৷ তারপর অতি সাবলীল ভঙ্গিতে রনির কাঁধে আলতো হাত রাখেন৷
রনি ঘাড় ঘুরিয়ে মৃন্ময়ের মুখের পানে তাকায়৷ তার জবাবে মিষ্টি করে হাসেন মৃন্ময়৷
জামাইদা রনির কেসটা নিয়ে নেবার সুবাদে এতক্ষণে বুঝি খানিকটা হালকা বোধ করেন অন্তরা৷ এতক্ষণে তাঁর মনে হয়, দিদি-জামাইবাবুর আপ্যায়নের একটা ব্যবস্থা করা উচিত৷ অর্থাৎ কিনা, অতিথিদের জন্য কিছু খাবার-দাবার আনা দরকার৷ সৌম্যদেবের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে সেটা বোঝাতে চান৷
সৌম্যদেব তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলেন অন্তরা’র ইঙ্গিত৷ উঠে দাঁড়ান৷ ভেতর-ঘরে গিয়ে একটা থলি নিয়ে বেরিয়ে আসেন৷
মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, মৃন্ময়দা, তোমরা কথা বল৷ আমি একটুখানি আসছি৷ এক্ষুনি ফিরব৷
সদর দরজা ঠেলে বেরিয়ে যান সৌম্যদেব৷
সৌম্যদেবকে হাতের ইঙ্গিতে বিদায় দিয়ে রনির দিকে পুনরায় তাকান মৃন্ময়৷ খুব নরম গলায় বলেন, রনি, মা কী বলছে? গ্রীলে তালা লাগিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?
রনি জবাব দেয় না৷ সে ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে থাকে মৃন্ময়ের মুখের দিকে৷
মৃন্ময় আরও নরম গলায় বলেন, বল— একদম ভয় পেও না— কেউ তোমায় কিচ্ছু বলবে না৷ কারণ, আমার বিশ্বাস, তুমি কোনও অন্যায় করনি৷ বল৷ কী হল, বল৷
রনি মৃন্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্রয় খোঁজে বুঝি৷
মৃন্ময় পুরোপুরি আশ্বাস দেন রনিকে, বলছি তো, তোমার কোনও ভয় নেই৷
মৃন্ময়ের আশ্বাসে বুঝি এতক্ষণে খানিক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে রনির চোখমুখ৷
কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, একটুখানি কিং’দের বাড়ি গেছলাম মেশো৷
— কিং কে রে? পাশ থেকে অন্তরাকে শুধোন সুরূপা৷
— ওর ভালো নাম কিংশুক৷ একমুখ বিরক্তি নিয়ে বলে ওঠেন অন্তরা, ওই যে গলির মুখে একটা দেবদারু গাছ, ওই গলির মধ্যে দু’তিনখানা বাড়ির পরে ৷ কিং’রা ভাড়া থাকে একতলায়৷
খুব স্নেহভরা দৃষ্টিতে রনির মুখের দিকে তাকান মৃন্ময়, কিং তোমার বন্ধু?
তার জবাবে মাথা দুলিয়ে সায় দেয় রনি৷ বলে, ও খুব ভালো রিসাইট করতে পারে৷ সারদাময়ীতে পড়ে৷ ফার্স্ট হয়৷
— হুহ্, সারদাময়ী আবার স্কুল, তার আবার ফার্স্ট! অন্তরা খেঁকিয়ে ওঠেন, আসল কথাটা বল না৷
—কিং-এর বাবা কী করেন? অন্তরার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন মৃন্ময়৷
— ঠিক জানিনে৷ অন্তরা’র চোখেমুখে তাচ্ছিল্য, কাটা-কাপড়ের না কীসের যেন ব্যাবসা করে৷
—কী কাণ্ড! এমন বাড়িতে বেমালুম চলে গেলি? রনির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন সুরূপা৷
মৃন্ময় আরও নরম গলায় শুধোন, কিং-দের বাড়ি গেছলে কেন?
রনি সারামুখে গভীর দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে বলে, ওর খুব অসুখ, মেশো৷ শুয়ে রয়েছে বিছানায়৷
বলতে বলতে রনির চোখদুটি সহানুভূতিতে ভরে যায়৷
— ওর যে অসুখ, তুমি জানলে কী করে? পাশ থেকে ফুঁসে ওঠেন অন্তরা৷
— আমাকে মৃদুল বলল৷ ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় রনি৷
— মৃদুল? সে আবার কে? সুরূপা বুঝি ক্রমশ রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছেন৷
রনির দিকে তাকিয়ে মৃন্ময় শুধোন, মৃদুল কে, রনি?
—কিং’দের পাশের বাড়িতেই থাকে৷ ওর বাবার কারখানা বন্ধ৷
শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন অন্তরা, শুনে উদ্ধার হয়ে গেলাম আমি!
একটু থেমেই পুনরায় ফুঁসে ওঠেন অন্তরা, মৃদুলকে তুমি পেলে কোথায়?
— আমি মৃদুলদের বাড়ি গিয়েছিলাম৷ খুব মৃদু গলায় জবাব দেয় রনি৷
কথাটা শোনামাত্র যেন আকাশ থেকে পড়েন অন্তরা৷ সুরূপার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, শুনলি? আমি ওকে হোমটাস্ক করতে বলে গেলাম, আর ও গেল মৃদুলদের বাড়ি! সাহসখানা দ্যাখ্!
— কেন গিয়েছিলি মৃদুলদের বাড়ি? সুরূপা ব্যাকুল গলায় শুধোন৷
— ওকে একখানা হিস্ট্রির বই দিয়েছিলাম তো৷ ওটাই ফেরৎ নিতে গিয়েছিলাম৷
অন্তরা পুনরায় ধমক দিতে যাচ্ছিলেন রনিকে৷ ওকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে রনির দিকে তাকান মৃন্ময়৷ খুব অনুত্তেজিত গলায় বলেন, কেন? ওকে তুমি বই দিতে গেলে কেন? ওর হিস্ট্রি-বই নেই?
জবাবে মাথা নাড়ায় রনি, ওর বাবা ওকে সব বই কিনে দিতে পারেনি মেশো৷ আমার কাছে বারবার চাইল—৷
—ও চাইল, আর তুমি দিয়ে দিলে? পাশ থেকে খেঁকিয়ে ওঠেন অন্তরা, যদি ছিঁড়ে ফেলত? ফেরৎ না দিত?
সমানে গজগজ করতে থাকেন অন্তরা, তোমায় বই কিনে দেওয়া হয় অন্যকে বিলোবার জন্যে? দুনিয়ার সব্বাইকে বই বিলোবার দায় বর্তেছে তোমার ওপর? তুমি দাতাকর্ণ হয়েছ?
মৃন্ময় হাত নাড়িয়ে থামান অন্তরাকে৷ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ গলায় বলেন, যেতে দাও৷ কিংয়ের কথাটা শোনা যাক৷
— হ্যাঁ, অন্তরা, বড্ড রেগে যাচ্ছিস তুই৷ সুরূপা পাশ থেকে মৃদু ধমক দেন অন্তরাকে, এমন করলে ও ভয় পেয়ে যাবে আরও৷ ভেতরের সিক্রেটগুলো বলবে না৷ হ্যাঁ, রনিসোনা, সবকিছু খুলে বল তো তোমার ভালো-মেসোকে৷ কেউ তোমায় কিচ্ছু বলবে না৷ বলেই অন্তরা’র দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে ওকে চুপ থাকবার পরামর্শ দেন৷
মাসির থেকে ভরসা পেয়ে পুনরায় বলতে থাকে রনি, তো, বইটা আনতে যেতেই মৃদুল বলল, জানিস তো, কিংয়ের খুব অসুখ৷
— অমনি তুমি মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়লে! আবার ক্ষেপে যান অন্তরা, তুমি বুঝি ডাক্তার?
অন্তরা’র রাগটাকে বড়-একটা পাত্তা না দিয়ে রনিকে অল্প উসকে দেন মৃন্ময়, হ্যাঁ, যা বলছিলে— কিংয়ের কী হয়েছে?
একটুখানি চুপ করে থাকে রনি৷ একসময় খুব অস্ফূট গলায় বলে, টাইফয়েড৷
— মাই গড! টাইফয়েডের রোগী—তুমি ওর ঘরে ঢুকলে? প্রায় আঁতকে ওঠেন সুরূপা, গিয়ে বসলি কোথায়?
রনি মাথা নিচু করে বসে থাকে৷
তাই দেখে রাগে একেবারে ফেটে পড়েন অন্তরা, কী হল? কোথায় বসলে, বলতে পারছ না?
— ওর বিছানারই পাশে৷ ফাঁসির আসামীর মতো মুখ করে জবাব দেয় রনি৷
— শুনলি? চোখেমুখে নাজেহাল ভাব ফোটান অন্তরা, টাইফয়েড রোগীর বিছানায় বসে এসেছে ছেলে!
সহসা বেজায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন সুরূপা, আরে, ওকে তো আগে ডিস-ইনফেক্ট করা দরকার৷
অন্তরা চাপা গলায় বলেন, কোথায়-না-কোথায় গিয়েছিল ভেবে সাবান-ডেটল দিয়ে চান করিয়ে দিয়েছি৷ রাত ন’টার পর সৌম্যকে ডাঃ সান্যালের কাছে পাঠাব৷ আরও কিছু করার থাকলে জেনে আসবে৷
অতঃপর কেউ আর কোনও কথা বলে না৷ অন্তরা’র গলা চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে৷ বলির পাঁঠার মতো বসে বসে ফাঁসির রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে রনি ৷
মৃগাঙ্ক চুপচাপ বসে সিগারেট খেতে থাকেন৷ পরিবেশটা আচমকা বড়ই থমথমে হয়ে ওঠে৷
—কী হবে মৃন্ময়দা? মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন অন্তরা, ছেলেটা কি আমার এইভাবে বকেই যাবে? আমাদের দুজনের যাবতীয় স্বপ্ন…সাধ…৷ আমি তো আর কিছুই ভাবতে পারছি না৷
— তোকে কে বলেছে ভাবতে? সুরূপা আলতো ধমক দেন অন্তরাকে, তোর জামাইদা যখন এসে গিয়েছে, একটা সলিউশন ঠিকই বের করবে? অফিসে ওকে ওর বসেরা কী নামে ডাকে জানিস? মিঃ সলিউশন৷
বলতে বলতে স্বামীর দিকে তাকান সুরূপা, কী গো? খালি সিগারেট খেয়ে গেলেই চলবে? অন্তরা’র প্রব্লেমটা কীভাবে সল্ভ করবে, মাথা থেকে কিছু বেরোলো?
মৃন্ময় তাও চুপচাপ সিগারেট খেতেই থাকেন৷ তারই মধ্যে, সুরূপার কথার জবাবে, সম্মতিসূচক মাথা দোলান বার-কয়৷ তাতে করে সুরূপার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে৷
অন্তরা’র দিকে তাকিয়ে সুরূপা একঝলক বিজয়িনীর হাসি হাসেন নিঃশব্দে, দেখলি তো? মগজ খাটিয়ে ঠিক একটা সল্যুশন বের করে ফেলেছে!
মৃন্ময়ের মুখ থেকে লাখটাকা মূল্যের সলিউশনটি শোনার জন্য দুজনেই উদ্গ্রীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন৷
৩
সিগারেটে একটা লম্বা টান দেন মৃন্ময়৷ বেশ কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়েন৷ তারপর চোখেমুখে যারপরনাই প্রাজ্ঞতা ফুটিয়ে শুরু করেন।
— আসলে, ব্যাপারটা কী জানো, এই বাংলাদেশের জল-হাওয়ায় এই রোগটা খুব হয়৷
—টাইফয়েড? সুরূপা ও অন্তরা একসঙ্গে আঁতকে ওঠেন৷
মন্ময় মৃদু হাসেন৷ বলেন, টাইফয়েডের চেয়েও মারাত্মক ওটা৷
শুনেই সুরূপা ও অন্তরা, দুজনের মুখই ভয়ে কালো হয়ে যায়৷
মৃন্ময় বলে চলেন, বাংলাদেশে বেশ নরম-নরম ভেজা পলিমাটি…বাতাসে হিউমিডিটিও প্রচুর…চতুর্দিকে গাছ-গাছাল…পাখি-পাখাল…, .সারাক্ষণ কেমন একটা জলো-জলো হাওয়া বয়….., বাতাসে এক ধরনের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব….৷ এমন জল-হাওয়ায় রোগটা বড়ই আস্কারা পায়৷ দুর্বল ফুসফুস আর হৃদপিণ্ড পেলে সহজেই জাপটে ধরে৷
শুনতো শুনতে সুরূপা ও অন্তরার সারামুখে ঘনিয়ে আসে সীমাহীন আতঙ্ক৷
মৃন্ময় ওদের আতঙ্কটাকে উপভোগ করতে করতে বলেন, আর, জানো তো, রোগটা বড়ই ছোঁয়াচে৷
অন্তরা আর সইতে পারে না৷ কাঁদো কাঁদো মুখে ব্যাকুল হয়ে শুধোয়, আপনি কোন রোগের কথা বলছেন মৃন্ময়দা? টাইফয়েডের চেয়েও মারাত্মক……৷
— ওই যে, আমাদের রনিবাবুকে যেটায় ধরেছে৷ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মৃন্ময় টেনে টেনে বলেন, প-রো-প-কা-র!
এতক্ষণে অন্তরা বোঝেন, সত্যি সত্যি কোনও মারাত্মক রোগে ধরেনি রনিকে৷ এতক্ষণে কিঞ্চিৎ ভরসা পান বেচারা৷
মৃগাঙ্ক অন্তরা’র দিকে এক ঝলক তাকান৷ তারপর পুনরায় বলতে থাকেন, দ্যাখোনি? স্বাধীনতার লড়াই শুরু হল দেশ জুড়ে… কিন্তু কেবল বাংলাদেশেই এপিডেমিকের মতো ছড়িয়ে পড়ল তা! জেলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল! ফাঁসিতে ঝুলবার কমপেটিশন! কে একজন কবি তাই নিয়ে রাতারাতি লিখে ফেলল পদ্য, ‘পড়ি গেলা কাড়াকাড়ি / কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি তাড়াতাড়ি’৷ ….ইন ফ্যাক্ট, ভারতের স্বাধীনতা- আন্দোলনে বেঙ্গলে যত মানুষ জান দিয়েছে, অন্য কোথাও তা দেয়নি৷ আবার দ্যাখো, সমাজ বদলানোর বেলায়….। দেশে কমিউনিজ্ম আনতে হবে….। দেখতে দেখতে খেপে গেল কেবল বেঙ্গলের ছেলেপিলেগুলোই৷ ব্রিলিয়্যান্ট ছেলে সব…..পড়াশোনা ছেড়ে, বোমা-পিস্তল ধরল৷ কতক শহর ছেড়ে চলে গেল গ্রামে৷ কতক পুলিশের হাতে মরল৷ কতক জেলে পচল বছরের পর বছর৷ কতক নিখোঁজ হয়ে গেল৷ কতক পঙ্গু হয়ে গেল সারা জীবনের মতো৷ কি? না, মানুষের ভালো করবে! ইন ফ্যাক্ট, ঘরের ভাত খেয়ে পরের মোষ তাড়ানোর রোগটা বুঝি বাঙালির রক্তে রয়েছে৷ অথচ অন্যদের দ্যাখো, কী ব্যাবসাতে, কী অল-ইন্ডিয়া সার্ভিসে, কী পোলিটিক্সে, আমাদের চেয়ে কত্তো এগিয়ে গেল!
সারা মুখে তেতো হাসি ফুটিয়ে বলে চলেন মৃন্ময়, হু—হু, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, বাঘা যতীন, সূর্য সেনের দেশের ছেলে এরা, পরোপকারে চাম্পিয়ন! পরোপকার করতে না পারলে এদের গা গুলোয়, মাথা ধরে, চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে, বদহজম হয়…৷
একটুখানি থামেন মৃন্ময়৷ তারপর গলায় রাজ্যের শ্লেষ জড়ো করে বলেন, আমার শ্রীমানের ঘাড়েও কিছুদিন পরোপকারের ভূতটি চেপেছিল৷ আশেপাশের গরিব ছাত্রদের ফ্রি-কোচিং দেওয়া শুরু করেছিল৷ বললুম, বাপু হে—আগে নিজে তৈরি হও, তার পরেই না অন্যকে তৈরি করা৷ তোমার নিজেরই পা রাখবার জায়গা নেই, তুমি অন্যকে পাট্টা বিলি করে বেড়াচ্ছ! সেই নিচু ক্লাস থেকে ছ’ছটা টিউটর যে লাগিয়ে রেখেছি তোমার পেছনে, সে কি এই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করবার জন্যে? তখন থেকেই ভাবছিলুম, এদেশে আর রাখা নয়৷ ফার্স্ট চান্সেই এই পরোপকারভূমি থেকে বিদেয় করব ছোঁড়াকে৷
—সত্যি! ভালো ছেলেগুলো যে কেন অমন করে স্পয়েল্ড হয়ে যায়! সুরূপা হাহাকার করে ওঠেন, কেন যে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়!
—এসব হল, সিভাল্রি’র আর এক নাম৷ নিজেকে মহা—ন করে তোলা৷ মৃন্ময় ফিক করে হাসেন৷
অন্তরার দিকে তাকিয়ে সুরূপা বলে ওঠেন, আমাদের পাড়ার একটি ছেলে, জানিস,—এইচ-এস’এ চারটে লেটার— অনার্সে সেভেনটি সিক্স পারসেন্ট—, কী যে ভূত চাপল মাথায়, দুম করে নকশাল হয়ে গেল! ঘরে থাকে না, খায় না, দায় না, একদিন শোনা গেল, পুলিশে ধরেছে৷ বাবা-মা গেল দেখা করতে, গিয়েই শুনল, লক-আপ ভেঙে পালিয়েছে৷ সেই যে পালিয়েছে, আজ অবধি কোনও খোঁজই নেই৷
— আসলে, এর জন্যে দায়ী আমাদের সেঞ্চুরি-ওল্ড বস্তাপচা ভ্যালু’জ৷ বড্ড মিসগাইড করে৷ সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলেন মৃন্ময়, ভাবো দেখি, ক্ষুদিরাম— তেরো-চোদ্দ বছরের বাচ্চা সে, দেশ বোঝে না, রাষ্ট্র বোঝে না, ইমপেরিয়ালিজম, কলোনিয়ালিজম, কিচ্ছু বোঝার বয়েসই হয়নি তার, কিন্তু সব্বাই ‘দেশমাতৃকা দেশমাতৃকা’ বলে এইসান পাম্প দিল, একটা ডিফেক্টিভ কন্ডেম্ড পিস্তল নিয়ে দৌড়ল ইংরেজ মারতে! আর, তার যখন ফাঁসি হল, দেশ জুড়ে কী জয়ধবনিই না উঠল তার নামে! আজও ছোঁড়াটার কী ক্যারিস্মা! আর, এমনই এই বাঙালি জাতটা, এই ধরনের ইমপ্র্যাকটিক্যাল ইমপশিব্ল ক্যারেক্টারগুলোকেই হিরো বানিয়ে রেখে দিয়েছে! ওদের নিয়ে গল্পগাথা, মিথ, গশিপ….শুনতে শুনতে বাচ্চাগুলোর মাথার ঠিক থাকে কখনো? ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন, বাঘা যতীন, সূর্য সেন, মায় তোমাদের নেতাজী, যে কিনা বাঘ মারবার জন্য ঘোঘ কিনতে গেল বিদেশে, —কাকে ছেড়ে কাকে ধরি ! মাঝের থেকে হল কি? ইংরেজরা ভয় পেয়ে, প্যানিকি হয়ে, ইন্ডিয়ার ক্যাপিটেলটাই সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লিতে৷ অথচ ভাবো দেখি, ক্যালকাটা ইন্ডিয়ার ক্যাপিটেল থাকলে কী ব্যাপারটাই না হত! বাঙালি কতখানি অ্যাডভানটেজ পেত! আর এক ওই বিবেকানন্দ৷ ফার্স্ট হাফটা বাউণ্ডুলের মতো দেশময় ঘুরে বেড়াল, সেকেন্ড হাফে মাঠে নামল, তাও পুরো সময় খেলল না, মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়েসে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল! কিন্তু যতটুকু সময় মাঠে রইল, খালি লেফ্ট-এন্ড রাইট জ্ঞান দিয়ে গেল! হে ভারত, ভুলিও না, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, মুচি-মেথর, সব তোমার ভাই—৷ জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর…এটসেট্রা…এটসেট্রা..৷
রনি ততক্ষণে বুঝেছে, তার ওপর ঝড়-ঝাপটাটা কখন যেন থেমে গিয়েছে৷ এই মুহূর্তে বন্দুকের নলটা তার দিকে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক তাক করা নেই৷ মৃন্ময়-মেশো রসিয়ে রসিয়ে কথা বলছেন৷ শুনতে ভালোই লাগছিল রনিরও৷ কাজেই, সেও একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল বড়দের ওইসব রসসিক্ত কথাবার্তায়৷
আচমকা রনির দিকে তাকালেন মৃন্ময়৷ বড়ই শীতল নিস্পৃহ সেই দৃষ্টি৷
মেশোর অকস্মাৎ ভাবান্তর দেখে রনি পুনরায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে৷ ঠোঁটের কোণায় হাসতে চায়৷ কিন্তু মাঝপথে আটকে যায় সেই হাসি৷
ওকে দেখতে দেখতে একসময় সুরূপা ও অন্তরার দিকে মুখ ফেরান মৃন্ময়৷
খুব সিরিয়াস মুখে বলেন, তবে, আমার কিন্তু মনে হয়, ব্যাপারটাকে তোমরা যতখানি সোজা ভাবছ, অত সোজা নয়৷
— কোন ব্যাপারটার কথা বলছো? সুরূপা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে৷
— এই আমাদের রনির ব্যাপারটা৷ একখানা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতে দিতে মৃন্ময় বলেন, আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটার মধ্যে একটা মিস্ট্রি রয়েছে৷
— মিস্ট্রি? সারা মুখে যারপরনাই উৎকণ্ঠা জমিয়ে অন্তরা তাকিয়ে থাকেন জামাইদার মুখের দিকে৷
— ইয়েস৷ মিস্ট্রি৷
— এমনটা কেন মনে হচ্ছে আপনার? অন্তরা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন৷
— মনে হচ্ছে এই কারণে যে, ব্যাপারটা কেবল আজই ঘটল, এমনটা মনে হচ্ছে না আমার৷ আচ্ছা, এর আগে এমনকিছু করেনি ও?
—কীসের কথা বলছেন, মৃন্ময়দা?
—ওই যে, তোমাদের লুকিয়ে এখানে-ওখানে চলে যাওয়া, উলটো-পালটা কাজ করা…৷
মৃন্ময়ের কথায় নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করেন অন্তরা৷ একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন৷ একসময় কবুল করবার ভঙ্গিতে বলেন, করেনি আবার! পাড়ার কেউ মরো-মরো, অমনি দৌড়ে যেতে চায় ওর বাড়ি৷ বন্যাত্রাণের চাঁদা তুলছে পাড়ার বখাটে ছোঁড়াগুলো, সেই দলেও ওর গিয়ে ভেড়া চাই! বলতে বলতে অন্তরার গলায় ফুটে ওঠে তীব্র হাহাকার, মাসটাক আগে আরও একটা যা ব্যাপার ঘটিয়েছে না! শুনলেই বুঝতে পারবেন, কপালখানা কতটা পুড়েছে আমার৷
বলতে বলতে রনির দিকে তাকান অন্তরা৷ গলায় যারপরনাই বিদ্বেষ ফুটিয়ে বলেন, বল, তোমার সেই রক্তদানের কথাটা বল৷
— রক্তদান? রক্তদান মানে? আঁতকে ওঠেন সুরূপা৷
— তবে আর বলছি কি! উনি রক্তদান করতে গিয়েছিলেন! রনির দিকে কটমট করে তাকান অন্তরা৷
—ও মা, কা—কে? বুঝি আকাশ থেকে পড়েন সুরূপা৷
— কাকে আবার, কোন্ এক মরণাপন্ন বন্ধুকে৷ বলতে বলতে অন্তরা’র সারা মুখে ফুটে ওঠে নিমপাতা চেবানোর বিকৃতি, বন্ধু না ছাই! এই পাড়ারই কার যেন অসুখ করেছিল— তার নাকি রক্ত দরকার—শুনেই উনি বায়না ধরলেন রক্ত দেবেন!
— তারপর? সুরূপা নড়েচড়ে বসেন৷
— তারপর…. আমরা সবাই মিলে বোঝানোয়, ওইটুকুন ছেলের রক্ত দেওয়া চলে না বলায়, উনি রক্ত কেনার খরচ বাবদ দেড়শো টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছেন ছেলেটার বাপের হাতে৷
— কী কাণ্ড! অন্তরার দিকে গোল গোল চোখে তাকান সুরূপা, টাকা কোথায় পেল?
— সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কর্ না৷
বলেই দু’চোখে গনগনে রোষ নিয়ে তাকান রনির দিকে, বল—, টাকাটা কোথায় পেলে, বল মাসিকে৷ তোমার কীর্তির কথা সব্বাই শুনুক৷ বুঝুক, তোমার কত উন্নতি হয়েছে৷
মায়ের গঞ্জনা শুনতে শুনতে ততক্ষণে রনির মুখখানা এতটুকু হয়ে গিয়েছে৷ ফাঁসে পড়া ইঁদুরের মতো কেবলই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে৷ বুঝি-বা পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে৷
রনি চুপ মেরে রয়েছে দেখে ওকে জোর ধমক লাগান অন্তরা, কী হল? টাকাটা কোথায় পেলে, বলতে পারছ না?
— মাউথ-অর্গানটা বেচে দিয়েছি৷ অপরাধীর গলায় বিড়বিড় করে বলে রনি৷
—ও মা—, কাকে? সুরূপা বুঝি বিস্ময় রাখবার জায়গা পান না৷
রনি আগের চেয়েও নিচু গলায় জবাব দেয়, ভ্যারাইটি স্টোর্সের বাদলদাকে৷
— শুনলি? সুরূপার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকান অন্তরা, পাঁচশো টাকার মাউথ অর্গান উনি দেড়শো টাকায় বেচে দিলেন! আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছে৷
মৃন্ময় চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিলেন৷ তাঁর মধ্যেও রনি-অন্তরার কথোপকথন শুনছিলেন নিঃশব্দে৷ এতক্ষণে মুখ খোলেন তিনি৷
অন্তরার দিকে তাকিয়ে বলেন, ওকে বেশি বকাঝকা করো না৷ ওই যে বললুম, নির্ঘাত এ-সবের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে৷ কারণ, একদিনেই তো আচমকা একটা দুধের বাচ্চা দুম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রক্ত দেবার কথা ভাবতে পারে না৷ মাউথ-অর্গান বেচে দুঃস্থ বন্ধুকে পয়সাও দিতে পারে না৷ এর একটা প্রস্তুতিপর্ব তো আছেই৷ একটা ইনার স্টোরি৷
মৃন্ময়ের কথার ধরনে সুরূপা আর অন্তরা একটা গভীর রহস্যের গন্ধ পান বুঝি৷ রহস্যটা অন্য কাউকে নিয়ে হলে নির্ঘাত এতক্ষণে জুত করে শুনতে চাইতেন মৃন্ময়ের মুখে৷ কিন্তু রহস্যটা যেহেতু রনিকে নিয়ে, এবং অবশ্যই অতি অশুভ রহস্য, দুজনের চোখে-মুখে ঘনিয়ে আসে গাঢ় আশঙ্কা৷ ভয়ে ভয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন ওঁরা৷
অন্তরা ব্যাকুল গলায় বলে ওঠেন, ইনার স্টোরিটা কী হতে পারে মৃন্ময়দা?
— সেটা অফ-হ্যান্ড বলা মুশকিল৷ খুব ভারিক্কি ভঙ্গিতে বলেন মৃন্ময়, হতে পারে, অন্তরাল থেকে কন্সট্যান্ট কোনও প্রোভোকেশন৷ ইনস্পিরেশনের নামে ইনস্টিগেশন৷ হতে পারে, ফ্রয়েড পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন ওইটুকুন বাচ্চার মধ্যে৷
— ফ্রয়েড!! অন্তরা ভয়মেশানো গলায় উচ্চারণ করেন৷
— ইয়েস, সিগ্মুন্ড ফ্রয়েড৷ অবাক হয়ো না৷ কিছুই অসম্ভব নয়৷
সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অন্তরা’র দিকে তাকান মৃন্ময়, আচ্ছা, যাকে রক্ত দিতে চেয়েছিল রনি, ওই ছোঁড়াটার কোনও বোন-টোন রয়েছে? কিংবা অল্পবয়েসি দিদি-টিদি?
— জানিনে৷ সারা মুখে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বলেন অন্তরা, ছোঁড়াটাকেই চিনিনে আমি৷
মৃন্ময় খানিক কী যেন ভাবেন৷ একসময় অন্তরাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, কিছু যদি মনে না কর, আমি একা একটুখানি কথা বলতে চাই রনির সঙ্গে৷ এক্কেবারে একা৷ কেউ থাকবে না এখানে৷
সুরূপা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান৷ অন্তরার দিকে তাকিয়ে বলেন, চল রে, আমরা শোবার ঘরে যাই৷
দুজনে পা বাড়ায় শোবার ঘরের দিকে ৷
যেতে যেতে অন্তরার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসেন সুরূপা৷ চাপা গলায় বলেন, এবার তোর জামাইদার খেল্টা দেখবি৷
৪
সৌম্যদেব যখন মৃন্ময়দের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে ফিরলেন, তখন ড্রইংরুমে কেবল মৃন্ময় আর রনি৷
মৃগাঙ্ক বেশ মন দিয়ে কিছু বোঝাচ্ছেন রনিকে৷ রনি মনোযোগ সহকারে শুনছে, আর বারংবার সম্মতিসূচক মাথা দোলাচ্ছে৷ সৌম্যদেব লক্ষ করেন, মেশোর কথায় তার সারা মুখ প্রসন্নতায় ভরে যাচ্ছে৷ বোঝা যাচ্ছে, মৃন্ময় যা-যা পরামর্শ দিয়েছেন, সবই সানন্দে মেনে নিয়েছে সে৷
ওদের কথার মধ্যে আর দাঁড়ান না সৌম্যদেব৷ খাবারের প্যাকেটগুলো নিয়ে ভেতর-ঘরে ঢুকে যান৷
একটুবাদে ভেতর-ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক পাড়েন মৃন্ময়, এবার তোমরা আসতে পার৷
শোবার ঘরে যেন তৈরি হয়ে বসেছিল সবাই৷ মৃন্ময় ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়৷ তিনজনের চোখেমুখেই উদ্বেগ৷
রনি’র দিকে বেশ নরম দৃষ্টিতে তাকান মৃন্ময়৷ মিষ্টি করে বলেন, অনেকক্ষণ বসে রয়েছ তুমি৷ আজ স্কুল থেকে ফিরে ঘুমোওনি বোধ করি৷ যাও, শোবার ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও৷ আমরা বড়রা একটু গল্প করি। কেমন?
মেশোর কথায় বুঝি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রনি৷ খুশি খুশি মুখে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে৷
মৃন্ময় একে একে চোখ রাখেন সবাইয়ের মুখের ওপর৷ সারা মুখে হালকা উদ্বেগ৷
একসময় অন্তরার দিকে তাকিয়ে শুধোন, কামিনী কে? চেনো নাকি?
— কোন কামিনী? বলেই সৌম্যদেবের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান অন্তরা৷
মৃন্ময় খানিকটা সূত্র ধরিয়ে দেবার মতো করে বলেন, কামিনী রায়? মহিলাটি কে?
— চিনিনে তো৷ কোথায় থাকে?
— ‘কাব্যসুধা’ বলে বেঙ্গলি কবিতার একখানা বই আছে নাকি রনি’র?
— ওটার নাম ‘কাব্যসুধা’ নাকি? অন্তরার দিকে তাকান সৌম্যদেব, হতে পারে৷
— নিয়ে এস তো বইটা৷
অন্তরা তড়িঘড়ি শোবার ঘরে গিয়ে বইখানা নিয়ে ফিরে আসেন৷
বইটা উলটে পালটে দেখতে থাকেন মৃন্ময়৷ একসময় শুধোন, এই বই রনির কোন কাজে লাগে?
— ওই যে, ইংরেজি বাদেও একটা অ্যাডিশন্যাল ল্যাংগুয়েজ শিখতে হয় এদের৷ রনি বেঙ্গলি নিয়েছে৷ এই বইখানা এদের সিলেবাসে রয়েছে৷
— হুম্৷ মৃন্ময় গুম মেরে খানিক ভাবেন৷ একসময় খুব গম্ভীর গলায় বলেন, যতটুকু বোঝা গেল, এই বইখানাই ওকে স্পয়েল করছে৷
সবাই হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকেন মৃন্ময়ের মুখের দিকে৷
— অ্যান্ড, দিস ওল্ড লেডি, কামিনী রায়৷ বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা পাতায় গিয়ে থেমে যান মৃন্ময়, — শোনো, পড়ছি৷ ‘পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি / এ জীবন মন সকলি দাও—/ তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? / আপনার কথা ভুলিয়া যাও’৷
ঝপ করে বইটা বন্ধ করে দেন মৃন্ময়৷ বলেন, সম্ভবত, এই কবিতাটি পড়েই শ্রীমানের হৃদয়ে পরোপকারের বান ডেকেছে৷ অন্তত ওকে ইন্টারোগেট করে তেমনটাই মনে হল৷
বলতে বলতে মৃন্ময়ের ঠোঁটের কোণায় তুমুল ভাঙচুর ঘটতে থাকে, আ-হা, কী কথা ! সকলে—র তরে সকলে আমরা—, প্রত্যেকে আমরা পরে—র তরে! আ-হা! আপনা—র কথা ভুলিয়া যাও! আসলে, ব্যাপারটা কী জানো, আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকেরা এমন ইউটোপিয়ায় ঘোরাঘুরি করে, এমন ইমপ্র্যাক্টিক্যাল কনসেপ্ট প্রীচ করে…! আর, এদেশের এডুকেশন সিস্টেমটাও এমন মিসগাইডিং! বাচ্চাদের কী দোষ? ওদের কচি বয়েস৷ নরম কাদার মতো মন৷ সবকিছুর ছাপ পড়ে যায় পলকের মধ্যে৷
খুব আত্মগত স্বরে বলতে থাকেন মৃন্ময়, এইখানেই সাহেবদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ৷ ওরা টপ-টু-বটম প্র্যাক্টিক্যাল৷ গাঁজাখুরি কথাবার্তায় ওরা নেই৷ আমাদের গ্রেট পোয়েট লিখলেন, ‘যে-পথ দিয়া চলিয়া যাব, সবারে যাব তুষি’৷ সাহেবরা অমন অ্যাবসার্ড প্রপোজিশন করবে না কিছুতেই৷ তাদের মতে, ‘হি—হু ট্রাই’জ টু প্লিজ এভরিবডি, ক্যান প্লিজ নো-বডি৷’ যে সবাইকে তুষ্ট করতে চায়, সে কাউকেই তুষ্ট করতে পারে না৷’ এক্কেবারে কারেক্ট অ্যাপ্রোচ৷
বলতে বলতে মৃন্ময় পাতা ওলটাতে ওলটাতে চলে যান বইটার আর একটি পাতায়৷ বলেন, তোমাদের এই ‘কাব্যসুধা’র আরও একখানা কবিতা পড়ছি, শোনো৷
মৃন্ময় গলায় যারপরনাই বিদ্রুপ ফুটিয়ে পড়তে থাকেন, ‘অন্ধের যষ্টির মতো কর গো আমারে, / দুঃখীর নির্ভর, / প্রাণপণে আমি যেন দুঃখী-অনাথেরে / সেবি নিরন্তর…’৷ আ-হা! বাচ্চাদের জন্য কী-সব মেসেজ! অথচ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজের বইখানা উলটে দেখো, এমন ড্যামেজিং কবিতা ওরা বাচ্চাদের সিলেবাসে ঢোকায়ইনি৷ কত প্র্যাক্টিক্যাল জাত ওরা!
এতক্ষণ প্রায় কিছুই বলেননি সৌম্যদেব৷ এতক্ষণে মুখ খোলেন তিনি৷ খুব কুণ্ঠিত গলায় বলেন, ইয়ে—মানে— মৃন্ময়দা— বলছি— সাহেবরা কি তবে চ্যারিটিতে কিংবা সোস্যাল-ওয়ার্কে বিশ্বাস করে না?
— করে বৈকি৷ মৃন্ময় যেন সৌম্যদেবের কথার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেছেন, — কিন্তু সেটা আগাগোড়া প্র্যাক্টিক্যাল অ্যান্ড ব্যালান্সড৷ এই ধর না, ওই কবিতাটা৷ আমাদের সময়ে ক্লাস সেভেন-এইটে পাঠ্য ছিল—ওই যে হে—কী যেন নাম—‘সামবডি’জ মাদার’৷ মনে আছে তো কবিতাটা?
— আছে বৈকি৷ সৌম্যদেব গড়গড় করে বলতে থাকেন কবিতাটার সারাংশ, একটা বাচ্চা ছেলে একটা বুড়িকে রাস্তা পার করিয়ে দিচ্ছে ….
— রাইট৷ মাঝপথেই সৌম্যদেবকে থামিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন মৃন্ময়, কিন্তু রাস্তা পার করাচ্ছে কোন যুক্তিতে? ছেলেটা ভাবছে, এই বুড়ি নিশ্চয় কারোর মা৷ আমি যদি একে রাস্তা পার হতে সাহায্য করি, তবে অন্য কেউ নিশ্চয় কোনওদিন আমার মা’কেও রাস্তা পার করিয়ে দেবে৷ ব্যাপারটা বুঝলে? পিয়োর্লি গিভ অ্যান্ড টেক অ্যাপ্রোচ৷ তুমি আমাকে হেল্প করবে, প্রতিদানে আমিও তোমায় হেল্প করব৷ পরিষ্কার কথা৷ হুঁ-হুঁ, বাবা—, অমনি – অমনি অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর হয়নি৷
বলতে বলতে একটা সিগারেট ধরান মৃন্ময়৷ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে খুব প্রসন্ন গলায় বলেন, যাগ্গে, রনি অবশেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে৷
— পেরেছে! অন্তরা ও সুরূপা একযোগে বলে ওঠেন, সত্যি!!
মুচকি হেসে মাথা দোলান মৃন্ময়, কেবল তাই নয়, ও আমার কাছে প্রমিস করেছে, আর কক্ষনো পরোপকার আর উটকো দান-ধ্যানের খপ্পরে পড়বে না৷
স্বামীর কথা শুনে অন্তরার দিকে বিজয়িনীর দৃষ্টিতে তাকান সুরূপা৷ বেশ বিগলিত গলায় বলেন, দেখলি তো, তোর জামাইদার এলেম!
— হ্যাঁ, আজকের সিটিংটা খুব কাজে লেগেছে৷ মৃন্ময় চোখেমুখে বেশ রাশভারী গুমোর ফুটিয়ে বলেন, ইট্ হ্যাজ বিন অ্যান এফেক্টিভ সাইকো-থেরাপি৷
— যাক বাবা, ফাঁড়াটা ভালোয় ভালোয় কাটল ৷ বলতে বলতে অন্তরা’র দিকে তাকান সুরূপা, এই অন্তরা— ছেলেটা কোথায় গেল রে? ডাক্ ওকে৷ ওকে নিয়ে একটু সেলিব্রেট করি৷
— ডাকছি দিদিভাই৷ রনি— রনি— রনিসোনা—৷ বাইরে এসো৷ মাসি তোমায় ডাকছেন—৷
একটুবাদে রনি ঘুম-ঘুম চোখ নিয়ে ড্রইংরুমে ঢোকে৷
ওকে দেখামাত্র সুরূপা সোহাগে গদগদ হয়ে ওঠেন৷ রনিকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, এই-যে—, সোনা মানিক আমার! বলতে বলতে রনিকে নিজের কোলে বসান৷ তারপর অন্যদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, আসলে, বাচ্চা তো, যে-যেমন উলটো-পালটা বুঝিয়ে দেয়! যাগ্গে— সারা সন্ধে অনেক বকাঝকা হয়েছে৷ এবার সবাই একটু আদর কর ওকে৷
সুরূপার গলায় স্নেহ উথলে ওঠে, ওলে–আমার সোনামণি রে—৷
বলেই লম্বা করে চুমু খান রনির গালে৷ বলেন, এবার আমার গালে একটা হাম দাও তো সোনা৷
বেশ হালকা ঝরঝরে লাগছিল রনিকে৷ কিন্তু সুরূপার কথায় সে নড়ে না৷ চুপ মেরে বসে থাকে৷
— কই, দা-ও৷ সুরূপা তাড়া লাগান৷
মাসির দিকে তাকিয়ে চালাক চালাক হাসে রনি৷ হালকা গলায় বলে, হাম দেব? তোমাকে? কেন?
— বা-রে, আমি তোর মাসি হইনে?
— তাতে কী? এমনি-এমনি একটা হাম তোমায় দেব কেন? হামের বদলে তুমিও আমায় কিছু দাও৷
— ওরে শয়তান ছেলে! কপট রোষে চোখ পাকান সুরূপা, মাসির কাছে চুমার দাম চাস? পরমুহূর্তে হেসে ফেলে বলেন, ঠিক আছে, কী নিবি বল্?
রনি একটুখানি ভাবে৷ একসময় বলে ওঠে, চুমার বদলে আমায় একখানা ভিডিও-গেম দাও৷
—ঠিক আছে, দেব৷ এবার চুমাটা দে৷
— আগে ভিডিও-গেমটা দাও৷ রনির সারা মুখে রগুড়ে হাসি৷
—কী ছেলে রে, বাবা! এক্কেবারে কাবলিও’লা! পুনরায় চোখেমুখে কপট রোষ ফোটান সুরূপা, ওরে দুষ্টু, আমি কি ভিডিও-গেম সঙ্গে করে এনেছি নাকি? কাল দেব৷
রনি সমানে হাসছিল৷ সুরূপার কথা শুনে হাসতে হাসতেই বলে ওঠে, তবে কালই ভিডিও-গেমটা দিয়ে চুমাটা নিয়ে যেও৷
বলতে বলতে অকস্মাৎ রনির চোখমুখের অভিব্যক্তি দ্রুত বদলে যেতে থাকে৷ সহসা কঠিন মুখে বলে, আমি ধারে কারবার করি না৷
বলেই রনি লাফিয়ে সুরূপার কোল থেকে নামে৷ তারপর গটগটিয়ে শোবার ঘরে চলে যায়৷
ড্রইংরুমের সবাই ততক্ষণে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছে৷ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ওরা৷
পাড়ার ক্লাবঘরে তখনও অবধি বেজে চলেছে ওই হিন্দি গানের কলিটি, মাম্মি দেখ্, মাম্মি দেখ্, তেরি মুন্না বিগড়্ যায়ে….৷
পর্ব-২
৫
অবসর নেবার পর অনেকের কাছেই সময়টাকে নিয়ে নিদারুণ সমস্যা তৈরি হয়৷
যেমন সৌম্যদেবের বেলায়৷
অবসরকালীন ভাতা হিসেবে যেমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একগাদা টাকা জমা পড়ল, পাশাপাশি তার জীবনের অ্যাকাউন্টেও আচমকা জমা পড়ল এক লপতে অনেকখানি সময়৷ একসঙ্গে এতগুলো টাকা নিয়ে যেমন খরচ করবার উপায় খুঁজে পান না, এতখানি বাড়তি সময় নিয়েও তাঁর একই সমস্যা৷ সারাক্ষণ কাজ নিয়ে থাকা মানুষটা কীভাবে যে খরচ করবেন এতখানি বাড়তি সময়, তাই ভেবে দিশেহারা হন সৌম্যদেব৷
একটা গোটা দি—ন! মানে সাকুল্যে চবিব—শ ঘন্টা!
যখন চাকরি করতেন, এখন ভাবলে অবাক হ’ন সৌম্যদেব, সময়টাকে নিতান্তই কম বলে মনে হত৷ সকাল থেকে গভীর রাত অবধি অফিসের গাদা গাদা ফাইল পড়েই কেটে যেত৷ তার ওপর ছিল মিটিং, সেমিনার, ফিল্ড-ইনস্পেকশন…৷ সন্ধের পর পার্টি, খানাপিনা…৷ তাছাড়া, মাঝে মাঝেই দেশের হরেক জায়গায়, এমনকি বিদেশেও যেতে হত সৌম্যদেবকে৷ সব মিলিয়ে একটা দিনের গোটা সময়টাকেও নিতান্তই কম বলে মনে হত সৌম্যদেবের৷
কিন্তু কোনও কাজকম্মো না থাকলে সেই সময়টাই যে একটা বিশাল বোঝার মতো ঘাড়ের ওপর চেপে থাকে, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন সৌম্যদেব৷ বাস্তবিক, এখন তাঁর সময় কাটানোটা সত্যি সত্যি সমস্যার৷
চবিবশ ঘ—ন্টা ! রাতের বেলায় পুরো সময়টা ঘুমুতে পারলে, খানিকটে সময় ওইভাবে খরচ হত৷ তার ওপর, এই বয়েসে দুপুর নাগাদ একটা ঘুম লাগাতে পারলে আরও কিছুটা সময়৷ কিন্তু তেমন কপাল করে আসেননি বুঝি সৌম্যদেব৷ রাতের ঘুম তাঁর মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছে৷ দিনের বেলায়ও চোখের পাতা এক করবার অভ্যেস নেই কোনওকালেই৷
এই দুনিয়ায় সবকিছু দিয়েই যে নেশা করা যায়, যৌবনে সেটা তিলতিল উপলব্ধি করেছেন সৌম্যদেব৷ আর, যতই উপলব্ধি করেছেন, ততই নেশাটা বাড়িয়ে দিয়েছেন৷ আজীবনকাল কাজের পেছনে পাগলের মতো দৌড়েছেন সৌম্যদেব৷ তার ফলে, যতই ঝপাঝপ প্রমোশন জুটেছে কপালে, কাজের নেশাটা ততই বেড়েছে৷
ফলে, দুপুরে ঘুমোনোর ব্যাপারটা কোনওকালেই ছিল না তাঁর৷ বস্তুতপক্ষে, একজন পুরুষ-মানুষ যে দিনের বেলায় ঘুমোতে পারেন, নিদেন বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারেন, এটাই সৌম্যদেবের কাছে অ্যাবসার্ড বলে মনে হয়েছে চিরটাকাল৷ সেই ধারণাটা অবসরের পরও থেকে গিয়েছে৷
কাজেই, সময় কাটানোর প্রশ্নে ওঁর সঞ্চয়ে থেকে যায় দিনের প্রায় পুরো সময়টাই৷
মর্নিং-ওয়াকে ঘন্টাটাক সময় খরচ করা যায়৷ কিন্তু মর্নিং-ওয়াক সেরে এসে চা’ খাওয়ার পর থেকে সময় আর যেন কাটতেই চায় না সৌম্যদেবের ৷
গোটা তিনেক খবরের কাগজ রাখেন তিনি৷ কিন্তু তিনটে মিলিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়৷ আসলে, আগডুম-বাগডুম খবরই বারোআনা৷ সৌম্যদেব ওগুলোর দিকে ফিরেও তাকান না৷ ফলত সারাটা দিন তাঁর বলতে গেলে বসে-শুয়েই কাটে৷
অনেক সংসারে বুড়োবুড়িরা নিজেদের মধ্যে তামাশা-খুনসুটি করে দিব্যি কাটিয়ে দেন৷ কেউ কেউ কারণে-অকারণে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাঁটি করেও খরচ করেন দিনের খানিকটে সময়৷ নিদেন, নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখের গল্পও থাকে কারোর কারোর৷ কিন্তু ওই তিনটের কোনওটাই ধাতে সয় না ওঁদের৷ না সৌম্যদেবের, না অন্তরা’র৷
কাজেই, সৌম্যদেবের হাতে ইদানীং অঢেল সময়৷ সময় তো নয়, সারাক্ষণ ঘাড়ের ওপর এক বিশাল বোঝা!
সাতসকালে ড্রইংরুমে বসে বসে সেই কথাটাই ভাবছিলেন সৌম্যদেব৷ সময় নামক গন্ধমাদনটিকে ঘাড়ে নিয়ে সারাটা সকাল কাটাতে হবে তাঁকে!
ড্রইং-রুমটাকে এখনও অবধি খুব সাজিয়ে রেখেছেন অন্তরা৷
ঘরের এককোণে রাখা মিউজিক-সিস্টেমে একটা রবীন্দ্রসংগীত বাজছে৷ আমার শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলাম….৷
গানটা খুব অন্যমনস্কভাবে শুনছিলেন সৌম্যদেব৷ চোখ ছিল একটা ইংরেজি খবরের কাগজের পাতায়৷ কিন্তু কাগজে তাঁর বড়-একটা মন নেই৷
হঠাৎই ঘরের এককোণে টুলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে ওঠে৷
আচমকা একটা কাজ পেয়ে গিয়ে একটু বেশি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন সৌম্যদেব৷ সারামুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! রনি’র ফোন নাকি! উঠে গিয়ে ফোনটা ধরেন৷
কিন্তু রিসিভারে কান ঠেকিয়েই নিভে আসে চোখের যাবতীয় ঔজ্জ্বল্য৷
— সৌম্যদেব সান্যাল বলছি৷ হ্যাঁ, কে? তারক? বল৷ না, না, আরে ভুলব কেন? ভালোই আছি—মানে, অবসর-জীবনে যতখানি ভালো থাকা যায় আর কি৷ আসছ? এখন? চলে এসো না৷ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ফ্রি-ই আছি৷ এই বয়েসে সারাক্ষণ ফ্রি থাকাটাই আমাদের নিয়তি৷ হা-হা-হা৷ আচ্ছা৷ ঠি—ক আছে৷ ওক্কে৷ বা—ই৷
ফোন রেখে দিয়ে ফিরে আসেন সৌম্যদেব৷ সোফায় বসে আবার পেপারে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করেন৷
অন্তরা ঘরে ঢোকেন৷ ড্রইংরুমের একটা সেলফ-এ একটা ফ্লাস্ক ও কয়েকটা কাপ-ডিস সাজানো রয়েছে৷ অন্তরা ওইদিকে এগিয়ে যান৷ ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে কাপটা এনে নামিয়ে দেন সৌম্যদেবের সামনে রাখা টি-টেবিলে৷ তারপর পাশের সোফায় বসেন৷
বলেন, ফোন বাজছিল না?
— হ্যাঁ৷ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সৌম্যদেব জবাব দেন৷
— রনি’র ফোন? অন্তরা প্রায় হামলে পড়েন৷
সৌম্যদেব ধীরে ধীরে মাথা নাড়ান, রনি’র ফোন হলে তোমায় ডাকতাম না?
চোখেমুখে রাজ্যের হতাশা ফুটিয়ে অন্তরা বলেন, আজ দু’মাস হয়ে গেল! একটা ফোন করছে না কেন বল দেখি? ওদের শরীর-টরীর ঠিক আছে তো?
চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সৌম্যদেব হঠাৎই আনমনা হয়ে যান৷ খুব পলকা গলায় বলেন, শরীর ওদের ঠিকই আছে৷ সময় পাচ্ছে না হয়তো৷
সৌম্যদেবের কথায় অন্তরা’র গলা থেকে অভিমান ঝরে পড়ে, কী যে বল! এত ব্যস্ত যে মা’কে একটা ফোন করবার অবধি সময় পাচ্ছে না! ভেবে দ্যাখ, বাড়ি আসার কথা তো ভুলেই গিয়েছে—
বহুকষ্টে দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে করতে উঠে দাঁড়ান অন্তরা৷ গোটা ড্রইংরুম ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা করতে থাকেন৷ সৌখিন সামগ্রীগুলোকে ঝাড়পুছ, সামান্য স্থান পরিবর্তন…এইরকম টুকিটাকি করতে করতেই বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, আগে হপ্তায় হপ্তায় ফোন করত৷ খোঁজখবর নিত৷ তারপর মাসে বার-দুয়েক৷ এখন তো মাসের পর মাস ফোনই করে না৷ একটিবার আসতে বল না ওকে৷ কতদিন দেখিনি!
সৌম্যদেব একটুক্ষণ চুপ থাকেন৷ একসময় মৃদু গলায় বলেন, বলেছিলাম৷ বলল, অফিস থেকে ছুটি পাওয়া যাবে না৷ আসলে, আসতে চায় না৷ ছুটি না-পাওয়াটা বাহানা৷
—ও আসতে চাইলেও রিয়া ওকে আসতে দেবে না৷ অন্তরা ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, দ্যাখ না, রনি যখন স্কাইপে কথা বলত আমার সঙ্গে, রিয়া আর দিদিভাই আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করত৷ রনিকে কতবার বলেছি, রিয়াকে একটিবার দে’না, একটু কথা বলি৷ অন্তত দিদিভাইকে একটু দে৷
— দেখেছি৷ বউকে দু’চারবার সেধে একসময় বলত, রিয়া মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছে৷
— তুমি লক্ষ করেছ?
সৌম্যদেবের হাতে চায়ের কাপটা থেমে যায়৷ অন্তরা’র মুখের দিকে আলগোছে তাকান, আসলে—৷ ওর কাছে আমাদের প্রয়োজনটাই ফুরিয়ে গিয়েছে৷
সৌম্যদেবের কথায় ওর মুখের পানে ব্যথাতুর মুখে তাকান অন্তরা, কেন ফুরিয়ে গেল বল তো?
— ফুরোবেই তো৷ সোফা থেকে উঠে বইয়ের র্যাকের কাছে যান সৌম্যদেব৷ একটা বই খুঁজতে খুঁজতে বলতে থাকেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমেরিকায় বড় কোম্পানিতে চাকরি কর— মোটা অঙ্কের ডলার কামাচ্ছে— রাজার হালে রয়েছে, প্যালেসের মতো ফ্ল্যাট, দুজনের জন্যে পৃথক পৃথক গাড়ি… — উইক-এন্ডে যেখানে খুশি বেড়াতে যাচ্ছে— একমাত্র বাচ্চাটিকেও রাজার হালে রেখেছে—৷ আমাদেরকে আর কী দরকার ওর!
একখানা বই নিয়ে পুনরায় সোফায় এসে বসেন সৌম্যদেব, ওদের এখনকার জীবনযাপনের মধ্যে আমরা কোত্থাও আসিনে৷
অন্তরা একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন৷ একসময় বলে ওঠেন, আমাদের সময় কিন্তু বাবা-মা’দের প্রয়োজন অত জলদি ফুরোত না৷ আমি তো এখনও মা’কে রেগুলার ফোন করি৷ আসতে বলি৷
অন্তরা’র কথায় উদাস হয়ে আসে সৌম্যদেবের চোখমুখ৷ মৃদু গলায় বলেন, বাবা বেঁচে থাকলে, আমিও করতাম৷ ৷
— সত্যি, রনিটা যে অত জলদি এমন বদলে যাবে, আমি ভাবতেই পারিনি৷ অথচ ওকে মানুষ করতে আমরা দুজনে কী কষ্টটাই না করেছি! নিজেদের সাধ-আহ্লাদ শিকেয় তুলে—৷ কোনওকিছুর অভাব তো রাখিনি৷ না চাইতেই সবকিছু কিনে দিয়েছি ওকে৷ তিলেকের তরেও চোখের আড়াল করিনি৷ বলো?
—সেই পাঁচ বছর বয়েস থেকে আধা-গণ্ডা টিউটর রেখেছি ওর জন্যে৷ পড়াশোনা ছাড়াও সাঁতার, গান, ছবি আঁকা, রিসাইটেশন, ডিবেট, কুইজ, সবকিছুর জন্য পৃথক পৃথক ট্রেনার রেখেছি৷ পাছে কুসঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে পাড়ার কারোর সঙ্গে মিশতে অবধি দিইনি৷ দুনিয়ার কোনও সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাতে দিইনি ওকে৷ অথচ সেই ছেলে এখন সামান্য খোঁজখবরটুকুও নেয় না! আসলে, আমাদের প্রতি টানটাই চলে গিয়েছে৷ তোমার মনে আছে, বছর দুয়েক আগে যখন তোমার খুব অসুখ হল, রাতারাতি অ্যাপোলো’র আই-সি-ইউ’তে ভর্তি করতে হল, ফোন পেয়ে ক্রাইসিস যখন ওভার— একদিনের জন্যে এল৷ দেখেটেখে— গুটিকয় শুকনো সান্ত্বনা দিয়ে রাতের ফ্লাইটেই ফিরে গেল৷ মনে আছে?
—নেই আবার! আমি তো লক্ষ করেছি, যতক্ষণ ছিল, সারাক্ষণ চোখেমুখে একটা উড়ুউড়ু ভাব৷ যেন ফিরে যেতে পারলেই বাঁচে৷
— আসলে, আজকের ছেলেদের কাছে বাবা-মায়ের প্রয়োজন বড় অল্পেতেই ফুরিয়ে যায়৷ এক্কেবারে পাখির বাচ্চাদের মতো৷ সামান্য উড়তে পারলেই ফুড়ুৎ৷ বলতে বলতে ম্লান হয়ে আসে সৌম্যদেবের মুখ৷ বিড়বিড় করে বলেন, একসময় দুজনের আকাশটাই পৃথক হয়ে যায়৷
— পাখির বাচ্চারা তবু দিনকতক সময় নেয়৷ নিঃশব্দে চায়ের কাপের শেষটুকুতে চুমুক দেন সৌম্যদেব, অন্য পশুরা তো জন্মাবার পরপরই টলোমলো পায়ে হাঁটতে শিখে যায়৷ তারপর ক’দিন মাত্র মায়ের পিছু পিছু দৌড়তে না দৌড়তেই সাবালক হয়ে ওঠে৷ তারপরই শুরু হয়ে যায়, তার নিজস্ব জীবন— নিজস্ব লড়াই—৷ সেই জীবনে বাবা-মা’রা এক্কেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়৷ দুজনে মুখোমুখি হলে একে-অন্যকে চিনতেই পারে না৷
অন্তরা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকান স্বামীর মুখের দিকে৷ ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, পশুপাখিদের কথা তুলছ কেন? মানুষ কি পশু কিংবা পাখি নাকি? মানুষ- মানুষই৷
ততক্ষণে সৌম্যদেবের গলায় বুঝি ফিরে এসেছে অ্যাকাডেমিক ডিসকাশনের মানসিকতা৷ বলেন, মানুষও এককালে তো পশুই ছিল৷
— ছিল, কিন্তু এখন তো আর সে পশু নয়৷ বিবর্তনের পথ ধরে বদলাতে বদলাতে সে এখন পুরোপুরি মানুষ৷
— কে জানে৷ সৌম্যদেব পুনরায় অন্যমনস্ক হতে থাকেন, বিবর্তন-প্রসেসটা ক্লাইমেক্স-এ পৌঁছে গিয়েছে হয়তো৷ রিভার্স প্রসেসটা হয়তো-বা শুরু হয়ে গিয়েছে৷
— রিভার্স-প্রসেস মানে? অন্তরা পুরোপুরি মুখ ফেরান সৌম্যদেবের দিকে৷
— বলছি— যে-পথ ধরে এই অবধি পৌঁছেছিল মানুষ, আবার হয়তো ওই পথ ধরেই পিছু হাঁটতে শুরু করেছে৷ হয়তো পূর্বাবস্থায় পৌঁছতে চাইছে গোটা প্রজাতিটা৷ বিবর্তনের শুনেছি, সেটাই ধর্ম৷
—কী বলছো! অন্তরা সামান্য চমক খান, সেটাই ধর্ম? পশু থেকে শুরু করেছে বলে, মানুষকে আবার ওই পথ ধরে পশুদের দিকেই ফিরতে হবে?
— ইয়েস৷ সৌম্যদেব বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলতে থাকেন, ইট্স আ জার্নি৷ কোনও জার্নিই তো আর অনির্দিষ্টকাল, অনির্দিষ্ট রুটে চলতে পারে না৷ সমস্ত ধরনের জার্নির ক্ষেত্রেই—একসময় তাই শুরুর পর্যায়ে ফিরতেই হয়৷ নইলে জার্নিটাই সাঙ্গো হবে না৷ সূর্য-চন্দ্র-গ্রহগুলো, ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে ফিরে আসে৷ নইলে দিনরাত্রি, মাস-বছর হত না৷ প্রকৃতিতেও দ্যাখো, ঋতুগুলোর বেলায়ও তাই৷ গ্রীষ্ম থেকে বদলাতে বদলাতে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত পেরিয়ে পুনরায় গ্রীষ্মকালে ফিরে আসে৷ নইলে ঋতুচক্রটাই কমপ্লিট হবে না৷
অন্তরা জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকেন৷ তবে বোঝা যায়, সৌম্যদেবের কথাগুলো ওর মনঃপুত হল না ৷
সৌম্যদেব বেশ হালকা গলায় বোঝাতে থাকেন অন্তরাকে, বাচ্চারা যখন লাট্টু ঘোরায়, লক্ষ করে দেখো, দড়ি দিয়ে লাট্টুটাকে একদিকে পাক দিয়ে মেঝেতে ছেড়ে দেওয়ামাত্তর ওটা বনবন করে উলটোদিকে ঘুরতে থাকে৷ ইন ফ্যাক্ট, উলটোদিকে ঘুরতে না-পারলে ওটা তো থামতেই পারবে না কখনোই৷ অনাদি অনন্তকাল ধরে ঘুরেই যেতে হবে৷
সৌম্যদেবের কথাগুলো একেবারেই মনঃপুত হচ্ছিল না অন্তরা’র৷ ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন, কী বলতে চাইছো বল তো?
— বলতে চাইছি, লাট্টুর ক্ষেত্রেও ঘোরাটা যেমন একটা জার্নি— প্রথম পাকটাতে একদিকে এগোল, দ্বিতীয় পাকে ওই রুট ধরে আগের অবস্থায় ফিরল— মানুষের ক্ষেত্রেও তাই৷
— তুমি বলতে চাইছ, মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম পাকটা শেষ হয়ে গিয়েছে? দ্বিতীয় পাক শুরু হয়ে গিয়েছে? অর্থাৎ আগের অবস্থায় ফিরছে মানুষ?
— সেটাই তো বলতে চাইছি৷ বলতে বলতে সৌম্যদেব ম্লান হাসেন৷
— হাসলে যে?
— তুমি খেয়াল করেছ, আমরা দুটিতে বসে বসে রীতিমতো দর্শন আলোচনা করছি!
— হ্যাঁ৷ অন্তরা আবার টুকিটুকি কাজে মন দেন, তুমি তো একটু একটু করে ফিলোসফার হয়ে উঠছো! ইদানীং মাঝে মাঝেই ভারী ভারী কথা আওড়াও৷
—অথচ ভেবে দ্যাখ৷ সৌম্যদেব দু’চোখ কপালে তুলে বলেন, একটা সময় ছিল, যখন দার্শনিক কথাবার্তা বলা তো দূরের কথা, আমরা দম নেবার অবধি সময় পেতাম না৷
—হ্যাঁ—তখন তো চবিবশঘন্টা তোমার অফিস মিটিং সেমিনার প্রজেক্ট… আর, আমার তো রনির পেছনেই কেটে যেত সারাটা সময়৷ আর, এখন তো— বলতে বলতে অন্তরা’র চোখেমুখে রাজ্যের হতাশা ফুটে ওঠে৷
— এখন তো পুরোপুরি বেকার৷ কাজ নেই কম্মো নেই। সংসারে দুটিমাত্র প্রাণী — সময় যেন কাটে না, বলো? কাঁহাতক আর টিভি দেখা কিংবা বই পড়া যায়! এখন যা-করলে সবচেয়ে ভালো হত—
অন্তরা স্বামীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান৷
— এখন সবচেয়ে ভালো হত, একটা জমজমাট অ্যাসোসিয়েশন পেলে৷ যেমনটা রোজ দেখি পার্কে৷
— পার্কে কী দ্যাখ?
— মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে রোজ দেখি, জনাপাঁচেক আমাদেরই বয়েসি লোক একসঙ্গে হাঁটছে৷ হাঁটতে হাঁটতে খোসগল্পে মজে রয়েছে ওরা৷ আশেপাশের পাড়াগুলোরই হবে৷ ফিরতি পথে দেখি, ওরাই পার্কে ঢুকে আড্ডার আসর জমিয়েছে৷ চা’ওয়ালার থেকে চা খাচ্ছে, আর আড্ডা মারছে৷
— তুমিও তো ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেই পারো৷
— পারলে তো ভালোই হত৷ সৌম্যদেবের চোখের তারায় প্রচ্ছন্ন বিষাদের ছায়া, কিন্তু ওদের কারোর সঙ্গেই তো আলাপ নেই৷
— আলাপ করে নাও৷
— সেটা আর সম্ভব নয়৷ দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন সৌম্যদেব৷
— কেন?
সৌম্যদেব একটুখানি একটু সময় নেন৷ একসময় বলেন, সারাটা জীবন বলতে গেলে আইসোলেটেড লাইফই লিড করেছি৷ নিজের গোত্র ছাড়া মিশিনি৷ নিজের গোত্রেও সব সময় বেছেবুছে মিশেছি৷ কাজেই—৷ তাছাড়া, ওরা সব্বাই অন্য গোত্রের৷
—এই বয়েসে আর গোত্র!
—তা ঠিক, তবুও অ্যাদ্দিন বাদে এখন আর যার-তার সঙ্গে হামলে পড়ে ভাব জমানো সম্ভব নয়৷ অভ্যেসটাই তৈরি হয়নি৷ এই যেমন তোমার নিজের কথাই ধর না৷ সময় কাটে না বলে তুমিও কি পাশের বাড়ির মহিলার সঙ্গে ভাব করে আচার-কাসুন্দির গল্প জুড়তে পারবে? কাজেই—
—কাজেই—
—কাজেই, সেলফিস-জায়েন্টকে উঁচু পাঁচিলঘেরা প্রাসাদটাতেই বাকি জীবনটা তিলতিল কাটাতে হবে৷ সৌম্যদেব হেসে ফেলেন ৷
অন্তরা একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন৷ বুঝি পরিপাক করতে থাকেন সৌম্যদেবের কথাগুলো৷ একসময় বলে ওঠেন, হ্যাঁ—ভালো কথা— কার ফোন এসেছিল, সেটাই তো বললে না৷
—কোন্ ফোন? ও—ওই ফোনটা? আমার এক ক্লাসমেট ফোন করেছিল৷ তোমার মনে আছে, খানিক দূরের একটা পাড়ায় আমার এক ক্লাসমেট থাকে? আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম৷ তোমার মনে নেই, একবার ওর ছেলের মুখেভাত নাকি পৈতের সময় আমাদের বাড়ি বয়ে ইনভাইট করে গিয়েছিল?
—মনে পড়ছে বৈকি৷ আমরা তো গেলামই না৷
—রাইট৷ আসলে, ও তখন কোন্ এক অফিসের কেরানি ছিল৷ শেষ জীবনে বড়বাবু গোছের একটা প্রমোশন পেয়েছিল বুঝি৷ আর, আমি তখন এতবড় কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার! কাজেই—৷
—তো, এ্যাদ্দিন বাদে তোমায় ফোন করছিল যে বড়?
—সেটাই বলতে ভুলেছি তোমায়৷ ওই মর্নিং-ওয়াকারদের দলে ও-ও রয়েছে৷ দিনকয় আগে আমায় দেখতে পেয়ে নিজেই এগিয়ে এসে কথা বলল৷ একদিন ওদের বাড়িতে যেতেও বলল৷ বাধ্য হয়ে আমিও ওকে বললাম, একদিন তুমিও এসো আমার বাড়িতে৷
—আসবে?
— আসতে চেয়েই ফোন করেছিল৷
— ভালোই তো৷ যদি আসে-টাসে— মাঝে মাঝে আনাগোনা করে— তোমার কথা বলবার একজন হয়৷ এখন তো আর তুমি তোমার কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার নও৷
— হ্যাঁ—৷ আমি এখন ওল্ড হ্যাগার্ড৷ আসতে বলেছি ওকে৷
— আজই আসবে?
— তাই তো বলল৷
অন্তরা সহসা সামান্য চঞ্চল হয়ে ওঠেন৷ হাত চালিয়ে কয়েকটি অসম্পূর্ণ কাজ সেরে নিতে চান৷ সৌম্যদেব পুনরায় বইয়ের পাতায় মন দেবার চেষ্টা চালান৷
এমনি সময় সদর দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে ৷
৬
— ওই বুঝি উনি এলেন৷ হাতের ডাস্টারটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে, টি-টেবিল থেকে কাপটা তুলে নিয়ে ভেতর-ঘরের দিকে রওনা দেন অন্তরা।
সৌম্যদেব উঠে গিয়ে দরজা খোলেন৷
দেখেন, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রৌঢ় তারকনাথ৷ অতি সাধারণ বেশভুষা, তবে বেশ ধারাল, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ৷ সঙ্গে বছর-ছয়েকের একটি বাচ্চা৷ তারকের একটা হাত শক্ত করে ধরে রয়েছে সে৷ অপরিচিত পরিবেশে চোখে-মুখে শিশুসুলভ আশঙ্কার অভিব্যক্তি দেখতে পান সৌম্যদেব৷
— আরে এসো, এসো৷ সৌম্যদেব আন্তরিক গলায় বলে ওঠেন৷
বাচ্চাটিকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন তারকনাথ৷ দুজনেই অপার বিস্ময়ে চারপাশে চোখ চারিয়ে সৌম্যদেবদের বৈভব দেখতে থাকেন৷
—বাপ রে! এ’ তো প্যালেস! একসময় বলে ওঠেন তারকনাথ৷
— আরে, না, না, অতকিছু নয়৷ সৌম্যদেব সামান্য লজ্জা পান, বোসো, বোসো৷
তারকনাথ সোফায় বসেন৷ বাচ্চাটিকে নিজের কোলে বসিয়ে নেন৷ বলেন, অনেকদিনই ভেবেছি, ছেলেবেলার বন্ধু, কাছেই থাকে, একটিবার যাই৷
— আসোনি কেন? এলেই পারতে৷ মৃদু অনুযোগের সুরে বলেন সৌম্যদেব৷
— আসলে কি জানো, আমি তো পাতি কেরানি—আর, তোমার যা স্টেটাস, খুব একটা ভরসা পাইনি ভাই৷
সৌম্যদেবের এঁটো কাপটাকে ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকেন অন্তরা৷ কাপটাকে র্যাকে তুলে রাখেন৷
সৌম্যদেব বলেন, এসো৷ আলাপ করিয়ে দিই৷ এ হল আমার স্কুল জীবনের বন্ধু৷ তারকনাথ৷ এর কথাই একটু আগে বলেছিলাম তোমায়৷ আর, আমার স্ত্রী অন্তরা৷
তারকনাথ ও অন্তরা পরস্পর নমস্কার বিনিময় করেন৷
— এটি নিশ্চয় তোমার নাতি?
মাথা দুলিয়ে সায় দেন তারকনাথ৷ বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলেন, যাও — কাকু-কাকিমা’কে প্রণাম কর৷
বাচ্চাটা দুজনকে পর পর প্রণাম করে পুনরায় দাদুর কোলে গিয়ে বসে৷
— কত করে বললাম, আসিস্নে। তারকনাথ সস্নেহে নাতির মাথায় হাত বোলাতে থাকেন, ওরা সব বিশাল বড়লোক! মেঝের ওপর কার্পেট, ঘরের মধ্যে কত-কত দামি জিনিসপত্র সাজানো৷ কোনগতিকে হাত-টাত যদি লেগে যায় —৷ তা, আমার কথা শুনলে তো! স্কুলের বাইরে আর একটি দণ্ডও আমায় ছেড়ে থাকতে চায় না। আমি দোকান-বাজার যাব—পাড়া বেড়াতে যাব— সর্বত্র আমার সঙ্গে যাওয়া চাই৷ আমি বলি, চ—ল্৷ বাইরে যত বেরোবি, ততই চারপাশটাকে দেখতে পাবি৷ আর, যত দেখবি,ততই চিনবি, ততই বুঝবি৷ মানুষের চারপাশটাই তো তার সবচেয়ে বড় স্কুল,—ঠিক কিনা, বলো?
তারকনাথ যখন কথাগুলো বলছিলেন, ওই ফাঁকে অন্তরা ভেতর-ঘরে গিয়ে একটা ক্যাডবেরির বার্ নিয়ে ফিরে আসেন৷ বাচ্চাটার দিকে চকোলেটটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, এই নাও৷ নাম কি তোমার?
—বাপ্পা? বলতে বলতে চকোলেটটা নেয় বাপ্পা৷ দাদুর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে জানতে চায়, বস্তুটিকে নিয়ে কী করবে?
তারকনাথ সস্নেহে বলেন, পরে খেও৷
চকোলেটটা বুক পকেটে রেখে দেয় বাপ্পা৷
তারকনাথের দিকে তাকিয়ে অন্তরা অনুযোগের সুরে বলেন, একা কেন? মিসেসকেও আনতে পারতেন৷
—বলেছিলাম—, কিনা, খুব তো আমায় হ্যাটা কর৷ চল৷ আমার বন্ধুরা-সব কোন স্ট্যান্ডার্ডের, দেখে আসবে! বলল, তুমি একাই যাও আজ, আমি আর একদিন যাব৷ আসলে—৷ মুচকি হাসেন তারকনাথ, যতটুকু খবর পেয়েছি, ওরা শাশুড়ি-বউমাতে মিলে কী যেন ষড়যন্ত্র করেছে৷
— ষড়যন্ত্র!
— কী-এক নতুন পিঠে তৈরির ফরমুলা শিখেছে টিভিতে, আজ তারই মহড়া হবে৷ সেই প্রস্তুতিই শুরু হয়েছে৷
বলতে বলতে তারকনাথের চোখেমুখে কপট দুর্ভাবনা ফুটে ওঠে, ওই ভাবনাতেই মরছি বউঠান৷
— কেন? পিঠে বানাচ্ছেন ওঁরা, আপনার ভাবনার কী হল?
— ভাবনা আছে বৈকি৷ সাপ-ব্যাঙ যা বানাবে, ওগুলোকে গলাধঃকরণ করবার গিনিপিগ তো আমরা তিনজন৷
— তিনজন মানে?
— আমি, আমার ছেলে, আর এই পুঁচকেটা৷ কেবল খেলেই তো চলবে না, আ-হা আ-হাও করতে হবে৷
তারকনাথের কথার ধরনে অন্তরা খিলখিল করে হেসে ওঠেন, এইজন্যেই এখন থেকে ভয় পাচ্ছেন?
— পাব না? টিভিতে রান্নাগুলো যা শেখায়, ওগুলো খেতে হবে ভাবলেই তো গায়ে জ্বর আসে!
— তা—ই?
— তাই নয়? ভেবে দেখুন বউঠান, কলমি শাকের মোগলাই ভাজা রাঁধবে! তার জন্যে কলমি শাককে হাজারগণ্ডা জিনিস দিয়ে মাখিয়ে মেরিনেট করছে! বুঝুন!
সৌম্যদেব ও অন্তরা একসঙ্গে হেসে ওঠেন ৷
—দাঁড়ান, আপনাকে একটু চা খাওয়াই৷ বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান অন্তরা৷ চা ঢালতে থাকেন ফ্লাস্ক থেকে৷ চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, ও আজই বলছিল, আপনারা স্কুল-জীবনের বন্ধু৷ শুনেই আমি বললাম, তা বন্ধু যখন—, পাশের পাড়াতেই থাকেন—, বাড়িতে আসতে বলোনি কেন? নিন, চা খান৷
— সারাদিনের চা ফ্লাস্কে ভরে রেখেছেন বুঝি? তারকনাথ চমৎকৃত, বাহ্! বুদ্ধিটা তো বেশ!
বলতে বলতে চায়ের কাপে চুমুক দেন তারকনাথ৷ তৃপ্ত মুখে তাকান৷ —আ—হ্! বেশ দামি চা! পাকস্থলি অবধি সুগন্ধে ভরে গেল৷ আমি আবার একটু বেশি বার চা খাই৷ সেই কারণেই, আমিও বাড়িতে চালু করতে চেয়েছিলাম এটা৷ কিন্তু বউমা রাজি হল না কিছুতেই৷
— কেন? ব্যবস্থাটা তো ভালোই৷ সৌম্যদেব বলেন, একবার অনেকখানি করে রাখলে বারবার করবার ঝামেলাটা থাকে না৷
— আমিও তো তাই বলেছিলাম৷ বলল কি জানেন? আপনি বারকয় চা খাবেন, তার জন্যে পুরো চা’টা বানিয়ে রাখতে হবে? বলতে বলতে চোখ নাচান তারকনাথ, পরের কথাটা বেশ মজার!
অন্তরা ও সৌম্যদেব একযোগে তাকান তারকনাথের দিকে ৷
— বউমা বলল, আপনার ছেলে যখন বাচ্চা বয়েসে রাতের বেলায় বারবার হিসি করত, গোটা রাত ধরে বারবার ওর ভিজে ন্যাপকিন বদলে দিতেন না? হা-হা-হা৷ বোঝো মেয়ের কথা!
বলতে বলতে চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা মারেন তারকনাথ৷ নাতিকেও একচুমুক খাওয়ান৷
—ওইটুকু বাচ্চা, চা খায়? অন্তরার গলায় মৃদু অনুযোগের সুর৷
নাতির দিকে সস্নেহে তাকান তারকনাথ৷ বলেন, ও সর্বভুক৷ সব খায়৷ আমিই বলেছি৷ সব খাবে৷ মাছ-মাংসের পাশাপাশি উচ্ছে, বরবটি, থোড়, কলমিশাক, ওল, কচু — স-ব৷ কারণ, বড় হয়ে কপালে যে কোন্ বস্তুটি জুটবে, তার তো কোনও ঠিক নেই৷ তাছাড়া, এই দুনিয়ায় সব সবজির মধ্যেই কিছু-না-কিছু খাদ্যগুণ রয়েছে৷
প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘোরান সৌম্যদেব? অন্তরা’র দিকে তাকিয়ে বলেন, জানো তো, ছেলেবেলায় তারক কিন্তু খুব ভালো ফুটবল খেলত৷
—হ্যাঁ, খেলতাম৷ তারকনাথের গলায় ব্যঙ্গ, খেলা আর দুষ্টুমি৷ আর, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো—৷
সৌম্যদেব বলে ওঠেন, হ্যাঁ, তারকটা খুব পরোপকারীও ছিল৷ কারোর বিপদ-আপদে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ত৷ ওই এলাকায় কারোর অসুখ-বিসুখ হলে, কিংবা কেউ মারা গেলে, সবার আগে তারক একপায়ে খাড়া৷
—ওই ঘোড়ারোগটা আজ অবধি যায়নি ভাই৷ তারকনাথ মুচকি হাসেন, এখনো পাড়ার কারোর ঠেকায়-বেঠেকায় দৌড়ে বেড়াই৷
— তাই?
— হ্যাঁ—কিন্তু ওই অবধি৷ তারকনাথ ম্লান হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলেন, ফুটবলে লাথি মেরে আর মড়া পুড়িয়েই কাটিয়ে দিয়েছি দিনগুলো৷ কাজের কাজ কিছুই হয়নি৷ ফলে, ছেলেবেলার ঘোর যখন কাটল, দেখলাম, চারদিক অন্ধকা—র! নেহাৎ কপাল ভালো, কেরানির চাকরিটা পেয়েছিলাম৷ নইলে টোল পড়া বাটি নিয়ে পথের ধারে বসতে হত৷
— না, না৷ সৌম্যদেব আপত্তি জানান তৎক্ষণাৎ, তোমার মতো মানুষের কোথাও একটা জুটে যেত৷ তুমি তো ডিস্ট্রিক্ট টিমেও খেলেছ৷ যদ্দুর মনে পড়ে, ফরোয়ার্ডেই খেলতে। অন্তরার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন সৌম্যদেব, জানো, ও ছিল অপর পক্ষের ডিফেন্সের ত্রাস! মাঝমাঠের পর তারকের পায়ে বল গেলে, আমরা ধরে নিতাম, গোল হচ্ছেই৷
— তুমি আর আমাদের খেলা দেখতে কোথায়! নষ্ট করবার মতো সময়ই ছিল না তোমার৷
বলতে বলতে অন্তরা’র দিকে তাকান তারকনাথ, জানেন বৌঠান, সৌম্যর মতো স্টুডেন্ট আমাদের স্কুলে আগেও আসেনি, পরেও না৷
— আরে না, না৷ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন সৌম্যদেব, তুমি বাড়িয়ে বলছো৷
— একটুও বাড়িয়ে বলছি না৷ তারকনাথ থামেন না, জানেন বৌঠান, সৌম্য নিজের ক্লাসের ছেলেদেরই পড়া বুঝিয়ে দিত৷ টিচারদের কাছে কেউ কোনও প্রোব্লেম নিয়ে গেলে তাঁরা সটান বলে দিতেন, সৌম্য’র থেকে বুঝে নে’গে যা৷
অন্তরা বেশ উপভোগ করছিলেন তারকনাথের কথাগুলো৷ এতক্ষণে মুখ খোলেন তিনি৷ বলেন, বেশি বলবেন না৷ লেজ আরও মোটা হয়ে যাবে৷
— সত্যি, তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছো৷ সলজ্জ মুখে বলেন সৌম্যদেব৷
— কিছুই বাড়িয়ে বলছি নে৷ তারকনাথ আরও জোর গলায় বলতে থাকেন, আমি তো পাড়ার সব্বাইকে বলি, পাশের পাড়াতেই আমার একটি ক্লাসমেট থাকে৷ তার মতো ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র আমরা দুটি পাইনি৷
কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই ঘরটাকে বেশ হ্যাংলার দৃষ্টিতে দেখছিলেন তারকনাথ৷ একসময় বলে ওঠেন, বাপরে! কী পেল্লায় বাড়ি বানিয়েছ! বোঝাই যাচ্ছে, খরচ করেছ বেশ৷
তারকনাথের কথায় খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন সৌম্যদেব৷ মাঝপথে তারকনাথকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তুমিও তো বানিয়েছ একটা৷
— তা বানিয়েছি একটা৷ তবে তোমাদেরটার সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না৷ আসলে, আমার তো সরকারি লোন আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাই ছিল ভরসা৷ যেমন-যেমন পেয়েছি, তেমন-তেমন একটু একটু করে করেছি৷ সেই কারণেই, যদি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দাও, দেখবে, কোনও ছিরিছাঁদ নেই৷ খানিকটা হিন্দুস্তান, খানিকটা পাকিস্তান—৷
বলেই হো-হো করে হেসে ওঠেন তারকনাথ৷
সৌম্যদেব মৃদু গলায় বলেন, না, না, বাড়ির আবার ভালো-খারাপের কী আছে? থাকবার ঠাঁই হলেই হল৷
— আসলে, আমার কোনও উপায় ছিল না ভাই৷ তারকনাথ খুব থমথমে গলায় বলেন, একে তো মাইনে কম, তারপর দু-দুটো মেয়ের বিয়ে৷ বাই-দি-বাই, তোমার মেয়েটেয়ে—?
— আমার তো একটাই ছেলে৷
— মেয়ে নেই তো? বেঁচেছ! একটা মেয়ে থাকা যে আজকের দিনে কী ঝকমারি!
— তা ঠিক৷ যা-সব শুনি চারপাশে—৷
— তবে আমার দুটি ভগবানের দয়ায় ছেলেপিলে নিয়ে ভালোই আছে৷ খুশি খুশি মুখে বলেন তারকনাথ, দুটি জামাই-ই বড়ই ভালো— শ্বশুর-শাশুড়িরাও মাটির মানুষ৷ ছেলেটারও বিয়ে হয়ে গেছে৷ আমরাই দেখেশুনে দিয়েছি ৷ বউমা’টি তোফা৷ ভদ্র, নম্র…৷ তাদেরও এই একটিমাত্র ছেলে৷ ছ’ বছরে পড়ল৷
— দেখে তো মনে হচ্ছে, বেশ শান্ত৷ বাপ্পার দিকে সস্নেহে তাকান অন্তরা৷
— শান্ত? এখানে এমনটি সেজে রয়েছে৷ বাড়িতে ওর দুরন্তপনা যদি দেখতেন! তারকনাথের সারা মুখে মিষ্টি হাসি, আমি অবশ্য ওর দামালপনায় বাধা দিইনে৷ ছেলে-বউমা বকলে-টকলে ওদেরই ধমকাই৷ বলি, বাচ্চাদের একটু দামালপনা ভাল৷ ছেলেবেলার আমাকে তো দ্যাখনি! সারাক্ষণ গোটা বাড়িটাকে মাথায় তুলে রাখতাম৷
অকস্মাৎ চারপাশে তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে থাকেন তারকনাথ, ইয়ে— আর কাউকে দেখছিনে যে বড়? বাড়িতে কেউ নেই বুঝি?
— এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না৷ কেবল আমি আর অন্তরা।
— বল কি! তারকনাথ স্পষ্টতই আঁতকে ওঠেন, এতবড় বাড়িটাতে তোমরা মাত্র দুজন থাকো! ছেলে বুঝি অন্যত্র ফ্ল্যাট নিয়ে—৷
— ও এদেশে থাকে না৷ আমেরিকায়৷ ডাক্তার৷
— অ—৷ তা—বউমা’—?
— ওর কাছেই থাকে৷
— কাচ্চাবাচ্চা?
— একটাই মেয়ে৷ ওখানকার স্কুলে পড়ছে৷
— তা—ই? বাংলাটা নির্ঘাত ভুলেছে?
— ওদেশেই তো জন্মেছে৷ বড়ও হচ্ছে৷ বাংলাটা আর শিখবে কেমন করে?
— সেটাই তো বলছি৷ আমাদের পাড়ার একজনের ছেলেটি কানাডায় থাকে৷ একবার সপরিবারে এসেছিল৷ বাঙালির ছেলে, বাংলাটাই প্রায় ভুলে গিয়েছে! আর ওদের ছেলেটা তো বাংলার একটি বর্ণও বোঝে না!
— তোমার ছেলেটি কী করে?
— পড়াশোনাতে ভালো ছিল তো, একটা ভালো সরকারি চাকরি পেয়ে গেছে৷ সেন্ট্রাল গম্মেন্টের ক্লাস-ওয়ান অফিসার৷ বলতে বলতে তারকনাথের সারা মুখে ফুটে ওঠে গুমোর, ওই চাকরিতে আবার সারাজীবন কোলকাতাতেই পোস্টিং৷ আমি বলি, ভালোই হল, মরবার সময় মুখে একটু জল দিতে পারবি৷
— ওরা তোমাদের সঙ্গেই থাকে?
— আবার কি! আমি অবশ্য দিনকালের হাওয়া বুঝে বলেছিলাম, ইচ্ছে হলে কোথাও একটা ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যা বাবা৷ আমাদের কোনও অসুবিধেই হবে না৷ শুনে ছেলে বলে কি জানো? বলে, তোমাদের সঙ্গে থাকব বলে এই চাকরিটা নিলাম৷ ট্রান্সফারেবল হলে নিতামই না৷ বোঝো!
একটুখানি থেমে তারকনাথ ফিক করে হাসেন, আর, এখন তো ইচ্ছে থাকলেও কোত্থাও যেতে পারবে না৷
— কেন?
— কেন আবার, এই যে, নাতি৷ দাদু-দিদার এমনই ন্যাওটা, একদণ্ডও চোখের আড়ালে থাকবার জো নেই৷ আর, যত দস্যিপনা সবই দুটো বুড়োবুড়ির ওপর! বলি, আমরা কি এখন তোমার দস্যিপনার ধকল নিতে পারি দাদুভাই? বুড়ো হয়েছি না!
— পড়াশোনা করছে তো?
— নেতাজী বিদ্যাভবনে৷ ক্লাস-ওয়ান৷
— দু’বেলা টিউটর রেখেছেন তো? পাশ থেকে বলে ওঠেন অন্তরা৷
— টিউটর? চোখ কপালে তুলে তারকনাথ বলেন, তাও আবার দু’বেলা?
— বলছি এই কারণে যে, তাতে বাচ্চাদের বেসটা ভাল হয়৷ উঁচু ক্লাসে গিয়ে সহজেই সামলে নিতে পারে৷
— হুহ্! একবেলা পড়তেই ওর গায়ে জ্বর আসে৷ তাও আমার কাছে পড়া চাই৷ বউমাকে বলি, বউমা, তুমি তো এম-এ পাশ৷ তুমিই পড়াও ওকে৷ আমরা সেই কবে এককালে পড়াশোনা করেছি— আজকের দিনের পড়াশোনাটাও তো বদলে গিয়েছে৷ কিন্তু মায়ের কাছে বসলে তো! পড়াতে হবে আমাকেই৷ যত বলি, ওরে, আমরা সেকালের মানুষ, পড়াশুনো তেমন করিনি, মায়ের কাছে পড়-গা যা৷ কিন্তু কে কার কথা শোনে!
— ওর বাবা পড়ায় না? অন্তরা শুধোন৷
— ওর বাবা? ও তো ঠিক আমার ধাতটি পেয়েছে বউঠান৷ বাপকা বেটা৷ বনের মোষ তাড়াতে ওরও জুড়ি নেই৷ পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি৷ পাড়ার একটি কাজও ওকে ছাড়া হবে না৷
— চাকরি-বাকরি করে সময় পায়?
— দ্যাখো, আন্তরিকভাবে কিছু করতে চাইলে, সময় ঠিকই জুটে যায়৷ ধর, যারা নেশা করে, হাজার ব্যস্ত থাকলেও তাদের কি নেশা করবার সময় অকুলান হয়?
— তা অবশ্য ঠিক৷
— আসলে, ছেলেবেলা থেকেই ওকে কোনও কিছুতে বাধা দিইনি তো৷ পড়াশোনা, খেলাধুলো, সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, সমাজের কাজ, — কোনও কিছুতেই নয়৷
— তাতে করে ওর পড়াশোনার কোনও ক্ষতি হত না?
— পড়াশোনা করতে করতেই তো ওসব করত৷ দেখুন বউঠান, স্কুল-কলেজের তো সিলেবাসবদ্ধ পড়াশোনা৷ ছেলেবেলায় তার জন্য খানিক সময় দেওয়া উচিত, মানছি৷ কিন্তু সেটা দিয়েও অনে—ক সময় থাকে৷ বরং সারাক্ষণ বাচ্চাকে বই নিয়ে বসে থাকতে বাধ্য করলে, তার মগজটাই একসময় টায়ার্ড হয়ে পড়ে৷ আর, এটা তো আপনি মানবেন, টায়ার্ড ব্রেন, কোনওকিছুই বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না৷
— তা ঠিক, তবে যা দিনকাল পড়েছে, স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় সাইন করতে না পারলে, ভবিষ্যতে কোনও সুযোগই পাবে না কোত্থাও৷
— সাইন করা বলতে আপনি ঠিক কী মিন করছেন বউঠান? তারকনাথ সরাসরি চোখ রাখেন অন্তরার মুখে, সব পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে হবে? তা না হয় হল, কিন্তু স্কুল-কলেজের বাইরেও যে একটা বিশাল য়্যুনিভার্সিটি রয়েছে, সেখানে না পড়লে—৷
— আর একটা য়্যুনিভার্সিটি— মানে—?
— আমাদের চারপাশের পৃথিবীটা৷ সেটাই তো মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান৷ স্কুল-কলেজের পরীক্ষা তো একদিন-না-একদিন সাঙ্গো হয়ে যায়, কিন্তু ওই য়্যুনিভার্সিটি সারা জীবন ধরে পরীক্ষা নিয়েই চলে৷ সেখানে ফেল করলেই আপনি গেছেন৷ ছেলেকে চারপাশের সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি বিদ্যের জাহাজ বানিয়ে লাভ কি বলুন? মৃদু হাসেন তারকনাথ, তেমনটা করলে, শেষ অবধি পীযূষের ছেলের মতো হাল হবে?
— কে পীযূষ?
— পীযূষকে মনে নেই তোমার? তাই কি হয়? ওই যে, আমাদের ক্লাসের যে- ছেলেটি সব ক্লাসেই ঠিক থাকত, কেবল সংস্কৃতের ক্লাসেই তোতলা হয়ে যেত! মনে পড়ছে?
— ও—পীযূষ—! তাকে ভুলব কেমন করে? ও তো পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল৷ আমাদের ভূগোল-স্যারের ভাগনে তো?
— ইস, এই মেমোরিটার জন্যই চিরকাল ঈর্ষা করেছি তোমায়৷
— কেন? ওই ক্লাসটাতেই তোতলা হয়ে যেত কেন? অন্তরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন৷
— কেন আবার, তাতে করে সংস্কৃতের ক্লাসে সঠিক উচ্চারণ না করেও সে পার পেয়ে যেত৷ আমাদের পণ্ডিতমশাই ছিলেন ও-ব্যাপারে বড়ই কড়া৷ সংস্কৃতের ক্লাসে উচ্চারণে একটুখানি ভুল হলেই আর রক্ষে থাকত না৷ কেবল পীযূষই তোতলা সেজে পার পেয়ে যেত৷
— মনে পড়ছে৷ তা, পীযূষ এখন কোথায়? তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে?
— আরে, ও আর আমি তো এক দপ্তরেই চাকরি করতাম৷ ইন্সিডেন্টালি অফিসে কিছুদিন ও আমার বস ছিল৷ যাগ্গে, যা বলছিলাম, পীযূষের ওই একটিই ছেলে৷ একেবারে পাখির মায়ের মতো আগলে আগলে মানুষ করল ওকে৷ তারপর পাখনাজোড়া পোক্ত হওয়ামাত্র পাখি ফুড়ুৎ৷
— ফুড়ুৎ মানে?
— চাকরি পেয়েই সোজা ব্যাঙ্গালোর৷ এখন বউ-বাচ্চা নিয়ে ওখানেই থাকে৷ পেল্লায় ফ্ল্যাট কিনেছে…৷ বলতে পারো ওখানেই সেটেল্ড৷
— বাপ-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে নিশ্চয়?
— মাত্র ছ’মাস মতো রেখেছিল৷ তারপর কানেকশন পুরোপুরি কেটে দিয়েছে৷
— মানে?
— বছর তিনেক বাড়ি আসেনি, বছরটাক আর ফোনও করে না৷ এখন কর্তা-গিন্নি বাড়িতে সারাক্ষণ টেলিফোনের দিকে কান পেতে বসে থাকে, আর সারাক্ষণ চোখের জল ফেলে৷
অন্তরা ও সৌম্যদেব নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করেন৷ কিন্তু অতি দ্রুত নিজেদের সামলে নেন৷
— ভেরি স্যাড৷ কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করেন সৌম্যদেব৷
— ঠিকই৷ পাশ থেকে অন্তরা বলেন, একটিমাত্র ছেলে — এত কষ্ট করে মানুষ করবার পর যদি বাপ-মায়ের খোঁজটুকু না নেয়—৷
— কিচ্ছু স্যাড নয়৷ ও একেবারে ওপরওয়ালার ঠিকঠাক বিচারটাই পেয়েছে৷
— ও মানে?
— আমি পীযূষের কথাই বলছি বউঠান৷ ওর পরিণতিটা ঈশ্বরের সুবিচারেরই ফল৷
— মানে?
—মানে, হি হ্যাজ বিন পেইড বাই হিজ ওন কয়েন৷
তারকনাথের কথায় বুঝি কিঞ্চিৎ রহস্যের গন্ধ পান সৌম্যদেব৷ বলেন, কী বলতে চাইছ?
— দ্যাখো, আমার মতে, ছেলেটার সঙ্গে পীযূষ অন্তত দুটো মারাত্মক অবিচার করেছে৷
— অবিচার?
— হ্যাঁ, বউঠান, আমি অবিচারই বলি একে৷ প্রথমত, ওর যখন ছেলে হল, বছরটাক বাদে আমি ওকে পই পই করে বললাম, ছেলেমেয়ে মিলে আমার তিনটে। তুমি অন্তত দুটি নাও৷ এবং পরেরটা মেয়ে হলেই ভাল হয়৷
—কেন, মেয়ে হলে ভাল হয় কেন?
— সেটা পরে বলছি৷ আগে অবিচারের কথাটা বলি৷ তো, আমার কথার জবাবে পীযূষ কী বলল জানো? বলল, আরও একটা! ক্ষেপেছ! একটাকে মানুষ করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত—৷ বরং উইশ কর, যাতে ওই একটাকে ঠিকঠাক মানুষ করতে পারি৷ আমি বললাম, পারবে না৷ ও বলল, কেন? বললাম, ফ্যামিলিতে একটামাত্র বাচ্চা থাকলে সে অমানুষ হবেই৷
তারকনাথের কথায় খুব মজা পান সৌম্যদেব৷ বলেন, আচ্ছা! এ বিষয়ে তোমার তত্ত্বটা শুনি?
—তত্ত্ব নয় ভাই, এটাই সত্যি৷ তো, পীযূষকে বললাম, অমানুষ হবে এই কারণে যে, বাবা-মায়ের যত আদর তো ও-ই পাবে, না কি? বাবা অর্থবান হলে তো কথাই নেই, সচ্ছল হলেও সারাক্ষণ এটা-ওটা কিনে দেবেই৷ গাদা গাদা জামা-কাপড়, খেলনাপাতি, খাবার-দাবার, সখ-সাধের হাজারো সামগ্রী—দেবেই৷ ওরও মজা দ্যাখো, সেই বাচ্চা বয়েস থেকে এত-এত জিনিস, ও একাই সবটুকু ভোগ করল৷ এমনিতে তো অপর্যাপ্ত ভোগ মানুষের অনেক জাতের ক্ষতি করে, কিন্তু তার চেয়েও ছেলেটার বড় ক্ষতি হয়ে গেল অন্যত্র৷ কোথায় জানো?
— কোথায়?
— ছেলেটা কারোর সঙ্গে কিছু শেয়ার করতেই শিখল না৷ অথচ দ্যাখো, এই পৃথিবীতে কেবল পাওয়ার অভ্যেস গড়ে উঠলে, পাশাপাশি অন্যদের কিছু দেবার অভ্যেস গড়ে না উঠলে, সমাজটাই ধবংস হয়ে যাবে৷ আর, আজকের দিনের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটছে৷ জ্ঞান হওয়া অবধি সে দেখল, সে কেবল সবকিছু পাওয়ার জন্যেই জন্মেছে৷ কাউকে কিছু দেবার দায় তার তিলমাত্র নেই৷ এই মনোভাবটাই তাকে চরম স্বার্থপর করে তুলবেই৷ অথচ দ্যাখ, বাড়িতে দুটো বাচ্চা থাকলে, ওদের মধ্যে ওই শেয়ার করবার অভ্যেসটা গড়ে ওঠে৷ করে কিনা?
— তা অবশ্য করে—৷
— তার ওপর, সেই দুজন যদি ভাই-বোন হয়, তবে ওদের মধ্যে জমে ভাল৷
— দুটোই ভাই কিংবা বোন হলে জমে না?
— জমে—তবে আমার কেন জানি মনে হয়েছে, দুটি সন্তান অপোজিট সেক্স-এর হলে আরও বেশি জমে৷
— হয়তো তাই৷ সৌম্যদেব বুঝি খেইটা ধরিয়ে দিতে চান, তারপর…তোমার ওই দ্বিতীয় অবিচারটা কি?
— সেটা আরও মারাত্মক৷ নিজের বাচ্চাটিকে একটা দরজা-জানলাহীন বাড়িতে থাকতে বাধ্য করা৷
— দরজা-জানলাহীন বাড়ি মানে? বাড়িতে তো দরজা-জানলা থাকবেই৷ বাড়ি আবার দরজা-জানলা ছাড়া হয় নাকি?
— তুমি আমার কথাটাকে লিটেরেলি নিলে ব্রাদার৷ আমি সেই দরজা-জানলার কথা বলছিনে৷
— তবে?
— আমি বলছি—আজকের অধিকাংশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা-মা তাদের একমাত্র বাচ্চাটিকে কেমন করে বড় করে? সে কারোর সঙ্গে মিশবে না, কোনও দিকেই তাকাবে না, আশেপাশে কে বাঁচল, কে মরল, কে খেলো, কে খেলো না, সেদিকে সে যেন তিলমাত্র নজর না দেয়৷
বলতে বলতে একটুখানি থামেন তারকনাথ৷ তারপর পুনরায় চলে যান পীযূষের প্রসঙ্গে৷ বলেন, ওই পীযূষের ছেলেটা, আমি তো দেখেছি, পীযূষ আর তার বউ — সর্বক্ষণ হাজারো জিনিসপত্র দিয়ে একেবারে ভরিয়ে রাখত বটে, কিন্তু বেচারাকে সারাক্ষণ থাকতে হত একেবারে প্রিজ্নারের মতো৷
— কী রকম?
—পাড়ার কেউ মরো-মরো, কান্নার রোল উঠেছে, পড়শিদের মধ্যে কেউ খুব বিপদে পড়েছে, বাপ-মা’র কড়া শাসনে বাচ্চাটার সেসব দিকে তাকাবার অবধি জো নেই৷ দুঃস্থদের জন্য ফ্রি-ট্রিটমেন্টের শিবির খুলেছে বড়রা, ওদিকে তার যাওয়া বারণ৷ স্কুলের সহপাঠীটির টিফিন আনার ক্ষমতা নেই, বাচ্চাটা ভুলেও তার সঙ্গে নিজের টিফিন শেয়ার করলে তাকে ফাস্ করা হবে৷ আত্মীয়দের মধ্যে কেউ খুব অনটনে রয়েছে, সে ওই নিয়ে সহানুভুতিটুকুও জানাতে পারবে না৷ ইয়েস, আমি নিজের চোখে দেখেছি তেমনটা৷ পীযূষের এক মাসির খুব খারাপ অবস্থা ছিল৷ পীযূষরা তাকে তিলমাত্র সাহায্য তো করেইনি, বরং ছেলের সামনেই বেচারিকে কড়া কথা বলে বিদেয় করে দিয়েছিল৷ মাসি চলে যাবার পর বাচ্চাটা ওই নিয়ে মৃদু অনুযোগ করেছিল, কিনা, মাসিদের খুব কষ্ট, তাই না বাপী? তৎক্ষণাৎ খিঁচিয়ে উঠেছিল পীযূষের বউ৷ বলেছিল, তোমাকে ওই নিয়ে মাথা ঘামাতে কে বলেছে? তুমি পড়ার টেবিলে গিয়ে হোমটাক্সগুলো কর৷ মনে রেখো, সামনে তোমার এক্জাম৷ ফার্স্ট যদি না হতে পারো—৷ বোঝো!
দাদুর কোলে বসে উশখুশ করছিল বাপ্পা৷ তাই দেখে তারকনাথ বলেন, বুঝতে পারছি, তোমার খেলার সঙ্গীরা জড়ো হয়ে গিয়েছে৷ ঠিক আছে, একটুবাদেই আমরা উঠব৷ তার আগে কিন্তু কাকু-কাকিমাকে একটা পদ্য শোনাতে হবে৷ শোনাবে না?
বাপ্পা ঘাড় দুলিয়ে সায় দেয়৷
সৌম্যদেবের দিকে তাকিয়ে তারকনাথ বলেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম—৷
কিন্তু কথা শুরু করবার আগেই তারকনাথ লক্ষ করেন, বাপ্পা তখনও উশখুশ করছে৷
বাপ্পার দিকে পুনরায় মুখ ফেরান তারকনাথ৷ বলেন, আবার কী হল? ওই ব্যালকিনটাতে যাবে? বাইরেটা দেখবে? যাও৷ কিন্তু কোনওকিছুতে হাত লাগিও না৷
ছাড়া পাওয়ামাত্র দাদুর কোল থেকে নেমে বাপ্পা চলে যায় ব্যালকনিতে৷
— হ্যাঁ, যা বলছিলাম—৷ তারকনাথ শুরু করেন, মা-বাবার ক্রমাগত চাপের মধ্যে থাকতে থাকতে বাচ্চাটা তবে কী করবে? মা-বাবার ইচ্ছে পূরণ করতে সে আর কোনওদিকে তিলমাত্র না তাকিয়ে সারাক্ষণ কেবল দৌড়তে থাকবে৷ দিনরাত পড়ে পড়ে ফার্স্ট হবে৷
চোখদুটো কপালে তুলে দিয়ে তারকনাথ বলেন, কেবল ওই করলেই চলবে না৷ ওইসঙ্গে তাকে শিখতে হবে সাঁতার, ছবি আঁকা, রেসিটেশন, ডিবেট, কুইজ…৷ এবং এই সবকিছুতেও ফার্স্ট হতে হবে৷ তার ফলটা হল কি? ওইসব করতে গিয়ে সারাক্ষণ সে শুধু পাগলের মতো ছুটল৷ সে দেখতে পেল না তার দেশটাকে৷ চিনল না দেশের মানুষগুলোকে৷ গ্রাম-আকাশ, নদী-বন, ফুল-ফল, গাছ, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, রামধনু, গঙ্গাফড়িং… কিছুই দেখবার ফুরসৎ পেল না সে৷ তার বুকের মধ্যে কোনও ছবিই তৈরি হল না৷ তৈরি হল না কোনও কল্পনা৷ সেই কারণেই, লক্ষ করো, আজকের বাচ্চাগুলোর মধ্যে কোনও উথলে ওঠা আবেগ নেই৷ সে কিছুই কল্পনা করতে পারে না৷ সে কেবল ছুটছে — প্রাণপণে— প্রবল যন্ত্রণায়— শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে৷ আর, তার ফলে—৷
কথা শেষ করেই সৌম্যদেবের চোখে সরাসরি চোখ রাখেন তারকনাথ৷
— তার ফলে?
— তার ফলে ওই বাচ্চাটি বড় হয়ে যদি একটা কল্পনাহীন, আবেগহীন, টাকা আয় করবার যন্ত্রে পরিণত হয়, যদি নিজেকে ছাড়া আর কারোর কথা না ভাবে, সেটা কি তার দোষ? যে-বা-যারা ওকে তেমন করে বানাল, তারা সাজা পাবে না?
এর জবাবে বুঝি সহসা কোনও কথা জোগায় না সৌম্যদেবের মুখে৷ বিড়বিড় করে বলেন, তা ঠিক৷
— আমার তো মনে হয়—৷ তারকনাথ খুব উত্তেজিত গলায় বলতে থাকেন, পীযূষ আর ওর বউ ওর ছেলেটাকে যা-যা শিখিয়েছে, ছেলেটি সেই অর্জিত বিদ্যেটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছে তার বাবা-মা’র ওপর৷
বলতে বলতে তারকনাথের ঠোঁটের ডগায় উঁকি মারে একচিলতে ব্যঙ্গের হাসি৷ বলেন, ইংরেজিতে একটা কথা রয়েছে না, চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম, এদের ক্ষেত্রে আমি বলি, ওদের সেল্ফিস্নেস বিগিন্স অ্যাট হোম৷ কাজেই, আশৈশব অর্জিত তাবৎ শিক্ষা ছেলেটি নিজের বাবা-মায়ের ওপরই প্রয়োগ করবে, এ-তো জানা কথাই৷
ততক্ষণে বুঝি এক ধরনের দ্বিধায় পড়ে গিয়েছেন সৌম্যদেব৷ বিড়বিড় করে বলেন, তুমি হয়তো ঠিকই বলছো তারক, কিন্তু তাও, আজকের এই সার্প কমপেটিশনের যুগে— বাচ্চাকে মানুষ করতে হলে—৷
— একমিনিট৷ সৌম্যদেবকে মাঝপথেই থামিয়ে দেন তারকনাথ৷ বলেন, কী বললে? বাচ্চাকে মানুষ করতে হলে? আচ্ছা, মানুষের বাচ্চা যখন, মানুষ হয়েই তো জন্মাবে সে৷ মানুষের ঔরসে, মানুষের গর্ভে তো আর গরু-গাধা জন্ম নিতে পারে না৷
— আসলে, উনি ওই মানুষ করবার কথা বলছেন না৷ পাশ থেকে স্বামীর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্য এগিয়ে আসেন অন্তরা, উনি বলছেন, বাচ্চার ভবিষ্যতটা তো গড়ে দিতে হবে৷
— ভবিষ্যত মানে? তারকনাথ অন্তরার দিকে তাকান৷
— মানে, ভবিষ্যতে সে যেন আয়-উপায় করে বেঁচেবর্তে থাকতে পারে—৷
— বউঠান— আপনি বলতে চাইছেন, স্কুল-কলেজের ফি-পরীক্ষায় ফার্স্ট না হলে, সেই ছেলে ভবিষ্যতে আয়-উপায় করতে পারবে না?
— পারবে না কেন? তবে আজকের দিনে ভালোভাবে বাঁচতে হলে—৷
— প্রচুর—প্রচুর টাকা চাই৷ এই তো?
তারকনাথের কথায় সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেও দমে যান না অন্তরা৷ জোরগলায় বলেন, আপনি যাই বলুন দাদা, টাকার প্রয়োজনটা আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন না৷ আর, তার জন্য—৷
— বুঝলাম৷ তাহলে, ছেলেকে মানুষ করা বলতে আপনি বলতে চাইছেন, সে যেন বড় হয়ে প্রচুর টাকা আয় করতে পারে? এই তো?
— কথাটা শুনতে যতই খারাপ লাগুক—৷
— না, না, খারাপ লাগবে কেন? টাকা তো আয় করতেই হবে৷ নইলে খাবে কি? বড় বাড়ি, বড় গাড়ি, দামি দামি শাড়ি-গয়না—এসব হবে কী করে? কিন্তু আমি বলছি, এই প্রক্রিয়াটিকে আপনি ‘মানুষ করা’ বলছেন কেন? অন্য কিছু বলুন৷ একটা বাচ্চার মানুষ হয়ে ওঠা মানে তো ওটা নয়৷ আরও স্বতন্ত্র কিছু হওয়া৷
— মানুষ হওয়া বলতে তুমি তবে কী বলতে চাইছ? পাশ থেকে বলে ওঠেন সৌম্যদেব, মানুষ হওয়া মানে তাহলে কি?
— রাইট৷ মানুষ হওয়া মানে কি?
— হ্যাঁ, কী এমন, যা না-হতে পারলে, সে মানুষের পেটে জন্মেও পশুই থেকে গেল?
একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারকনাথ৷ তারপর বলেন, ঠিক আছে৷ সেটাই তবে বলি?
— বল৷
ওদের কথার মাঝে উঠে দাঁড়ান অন্তরা৷ বলেন, আপনারা কথা বলুন, আমি বাচ্চাটার জন্য একটু-কিছু বানাই৷ বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ান তিনি৷
— প্রথমেই বলতে চাই—৷ এভাবেই শুরু করেন তারকনাথ, এমনিতে মানুষে আর পশুতে কিন্তু বড় একটা তফাৎ নেই৷
— সে কি? মানুষ আর পশুতে কোনও তফাৎ নেই?
— কোথায় তফাৎ বুঝিয়ে দাও আমায়৷
— তুমি বলতে চাইছ মানুষ আর পশু এক?
একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারকনাথ৷ একসময় বলেন, ভাবতে যতই সংস্কারে বাধুক ব্রাদার, দুটো প্রজাতিই কিন্তু হরেদরে একই৷ আরে, ইংরেজিতে তো রয়েইছে, ম্যান ইজ এ সোস্যাল অ্যানিম্যাল৷ ওই ‘সোস্যাল’ কথাটা বাদ দিলেই সে কিন্তু অ্যানিম্যালই৷ দ্যাখ না, পশুরা যা-যা করে, মানুষও চোদ্দআনা ক্ষেত্রে তাই তাই করে৷ আহার-নিদ্রা-মৈথুন-বংশবৃদ্ধি এবং একসময় মরে যাওয়া৷ দুই ক্ষেত্রেই হুবহু একরকম৷ পশুরা খিদে পেলে খাবার খায়, তেষ্টা পেলে জল খায়, ভয় পেলে পালায়, রেগে গেলে ঝগড়া-মারামারি করে, দুঃখ পেলে কাঁদে, খুশি হলে স্ফূর্তি করে,— মানুষও তাই করে ভাই৷ পশুরা সকাল হলেই খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে, মানুষও ওই একই কারণে চাকরি করতে বেরোয়৷ পশুরা দিনের শেষে একটি খাদ্য পায়, মানুষ ওটা মাসটি ফুরোলে খামের মধ্যে পায়৷ কিন্তু হরেদরে ব্যাপারটা একই৷ খাবারের খোঁজে বেরোনো৷
তারকনাথের কথাগুলো শুনতে শুনতে মিটিমিটি হাসছিলেন সৌম্যদেব৷ একসময় ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন, মানুষ ঘরবাড়ি বানায়, বড় বড় ইমারত…৷
— তা বানায়৷ পশুরা বাড়িঘর কিংবা প্রাসাদ-ইমারত বানাতে পারে না বটে৷ তবে ওগুলো তো থাকবার জন্যই বানানো হয়৷ প্রত্যেক জাতের পশুই কিন্তু নিজেদের থাকবার উপযোগী ডেরাগুলো নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেয়৷ এবং সেগুলো নির্মাণবিদ্যায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত মানের হয়৷ ধর, বাবুই পাখির বাসা৷ ধর, পিঁপড়েদের ঢিবি৷ ঢিবির তলায় রহস্যময় সুড়ঙ্গ-নগরী…৷ ধর, মৌচাক…৷ তুমি পারবে বাবুইয়ের মতো একখানা বাসা বানাতে? কিংবা মৌমাছিদের মতো একটি মৌচাক?
— তা হয়তো পারব না৷ তবে কেবল ডেরা তৈরিই তো নয়৷ আরও কতকিছুই মানুষ জানে, যা পশুরা জানেই না৷
— যেমন?
— যেমন ধর, কথা বলবার জন্য মানুষ ভাষা আবিষ্কার করেছে৷ পশুরা তা এখনও পারেনি৷ কোনওদিন পারবেও না৷
— কে বলল পশুদের ভাষা নেই? ভাষা তো ভাব প্রকাশের মাধ্যম বৈ কিছু নয়৷ ভালোভাবে লক্ষ কোরো, দেখবে, প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজস্ব ভাষায় ভাব বিনিময় করে৷ এমনকি, পিঁপড়েরাও৷ তুমি-আমি ওদের ভাষাটা বুঝতে পারিনে, এই যা৷ তা, আমরা তো পৃথিবীর বহু মানুষের ভাষাই বুঝতে পারিনে, কোনও কোনও ভাষাকে তো কিচির-মিচিরের মতো শোনায়, তবে কি ওগুলো ভাষা নয়?
তারকনাথের কথায় বুঝি খুবই মজা পাচ্ছিলেন সৌম্যদেব৷ বলেন, কেবল ভাষাই কেন, মানুষ স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে, কত জ্ঞান লাভ করে৷ পশুরা কি তা করে?
— করে বৈকি৷ ওদের স্কুলটা তো আরও বিশাল৷ সেই স্কুলের আবার কোনও সিলেবাসই নেই৷ সবটাই আন্সিন৷
— কীসের কথা বলছো?
— এই যে, দুনিয়া নামক স্কুল। প্রকৃতির স্কুল৷ কোথায় বাস করাটা নিরাপদ, কোন ঋতুতে বেশি খাবার-দাবার মেলে, কোন অসুখে কোন গাছের শিকড় কিংবা পাতা খেয়ে নিতে হয়—কখন বৃষ্টি নামবে, ঝড় উঠবে, ভূমিকম্প হবে —, স—ব ওরা আগাম জানতে পারে৷ মানুষের তৈরি অসংখ্য যন্ত্রপাতিও যা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না, ওরা কিন্তু তা অতি সহজেই বুঝে ফেলে৷
এত করেও তারকনাথের সঙ্গে তর্কে হার মানতে চান না সৌম্যদেব৷ বলেন, তুমি বলছো বটে, তবে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে পশুদের বুদ্ধির কি সত্যি সত্যি কোনও তুলনা চলে?
— না, চলে না৷ মানছি৷ সেক্ষেত্রে মানুষকে বড় জোর বলা যেতে পারে ‘একটি প্রখর বুদ্ধিমান পশু’৷ কিন্তু তাকে মানুষ বলতে গেলে ওগুলোয় কুলোবে না ভাই৷ অন্তত আরও কিছু স্বতন্ত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্য না থাকলে মানুষ কিন্তু হরেদরে পশুই৷ বড়জোর একটি বুদ্ধিমান পশু৷
— তুমি তবে বলতে চাইছ, কেবল বাড়তি বুদ্ধি ছাড়া, মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনও ফারাকই নেই?
— কে বললে নেই? তবে তা বাড়িঘর বানানোয় আর স্কুল-কলেজে পড়ায় নয়৷
— তবে?
— মানুষের সঙ্গে পশুদের ফারাকটা অন্যত্র৷
— কোথায় বলো তো?
— অন্তত দুটো ক্ষেত্রে মানুষে আর পশুতে ফারাকটা হয়ে যায়৷ এক, মানুষ কল্পনা করতে পারে, পশুরা তা পারে না৷ আর দুই, মানুষ সমাজ গড়েছে, পশুরা আজ অবধি কোনও সমাজ গড়তে পারেনি৷
— কে বললে পারেনি? পশুরাও তো এক-একটি প্রজাতি একসঙ্গে থাকে৷
— সেটা হল যুথবদ্ধ জীবন৷ সমাজবদ্ধ নয়৷ যুথবদ্ধ জীবন আর সমাজবদ্ধ জীবনে আকাশ-পাতাল ফারাক৷ পশুরা খাবার-দাবার, জল, নিরাপত্তা ইত্যাদির কারণে একসঙ্গে একটি এলাকায় দলবদ্ধ হয়ে থাকে মাত্র৷ কিন্তু —৷ আচ্ছা, তুমি ডিসকভারি চ্যানেলটা দ্যাখ না?
— দেখি তো৷
— তাহলেই তো দেখেছ— কয়েক হাজার বাইসন একটা বিশাল প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে, একটামাত্র বাঘ ওদের পালে হামলা করে একটাকে ধরে ফেলল৷ ওর জীবন্ত শরীরটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল৷ সবগুলো বাইসন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে দৃশ্যটা৷ অথচ সবাই যদি একসঙ্গে তেড়ে যেত বাঘটার দিকে, যদি সবাই একটা করে সিংয়ের গুঁতো মারত, তবে বাঘ বাবাজী তৎক্ষণাৎ অক্কা পেত৷ কিন্তু তারা কি তা করে? এখানেই যুথবদ্ধ জীবনের সঙ্গে সমাজবদ্ধ জীবনের মূল ফারাক৷ সমাজবদ্ধ জীবনের মূল স্লোগানই হল, ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে৷’ লিভ অ্যান্ড লেট লিভ৷ নিজে বাঁচো, অন্যদেরও বাঁচতে সাহায্য কর৷ না ভাই, পশুদের মধ্যে ওটা আজ অবধি গড়ে ওঠেনি৷
এতক্ষণে মুচকি হাসেন তারকনাথ৷ বলেন, এতক্ষণে কি বোঝা গেল, একটা বাচ্চাকে মানুষ করা মানে কি? তাকে সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে গড়ে তোলা৷ নইলে, যতই স্কুল-কলেজে পাশ দিক, যত টাকাই কামাক, সে কিন্তু সারাটা জীবন পশুদের কাছাকাছিই থেকে গেল৷
৭
একসময় ব্যালকনি থেকে ফিরে আসে বাপ্পা৷ তারকনাথের কোলে এসে বসে৷
তারকনাথ সস্নেহে তাকান নাতির মুখের দিকে, কী? দেখা-টেখা হয়ে গেল?
বাপ্পা মাথা দোলায়৷
— কী দেখলে?
— ওরা একটা কুকুরকে খুব মারছে৷
— কারা?
— ওই লোকগুলো৷
— সেটা খারাপ?
বাপ্পা নিঃশব্দে মাথা দোলায়৷
— কেন? তারকনাথ জেরা শুরু করেন৷
—ওরা তবে যাবে কোথায়? খাবে কি?
বাপ্পার কথা শুনে সৌম্যদেব অবাক দৃষ্টিতে তাকান ওর মুখের দিকে৷ চোখেমুখে ফুটে ওঠে তারিফ৷
সৌম্যদেবের দিকে তাকিয়ে তারকনাথ বলেন, রোজ পাখিপাখালদের, রাস্তার কুকুর-বেড়ালকে নিজের খাবার থেকে অল্পস্বল্প দেবেই৷ বলে, কেবল একা খেলেই তো চলবে না৷ সবাইকে দিয়েথুয়ে খেতে হবে৷
— কে শেখাল? তুমি?
— ওর মা৷ ওকে বউমা বেশ কয়েকটা পদ্য আর গানও শিখিয়েছে৷ বলতে বলতে বাপ্পার দিকে তাকান তারকনাথ৷ বলেন, দাদুভাই, ওই গানটা গেয়ে শোনাও তো তোমার কাকু-কাকিমাকে৷
— কোন গানটা? দাদুর মুখের পানে তাকায় বাপ্পা৷
— ওই যে তোমার বন্ধুদের গেয়ে শোনাচ্ছিলে? মানুষ হইয়া—৷
বাপ্পা শুরু করে : মানুষ হইয়া জনম লইলাম, মানুষের করিলাম কি…৷
খুব সুরেলা গলায় পুরো গানটাই গায় বাপ্পা৷
গান শেষ হলে পর সৌম্যদেবের দিকে তাকান তারকনাথ৷ খুব তৃপ্ত গলায় বলেন, এটাই আমি সবাইকে বোঝাই৷ জন্মে অবধি এই পৃথিবী থেকে কেবল কাঁড়িকাঁড়ি নেব— খিদেয় খাবার, তেষ্টায় জল, দম নেবার অক্সিজেন, আরও কতকিছু— দেবার বেলায় খালি কেবল রাশিরাশি মল আর মূত্র!
এমনি সময়ে দু’হাতে দু’ প্লেট খাবার নিয়ে ঢোকেন অন্তরা৷ বলে ওঠেন, বাহ্, গানের গলাটি তো বেশ! ওখান থেকে শুনছিলাম৷
প্লেটদুটো সেন্টার-টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে সৌম্যদেবের দিকে তাকান অন্তরা, তোমাদের মানুষ-পশুর সমস্যা মিটল?
জবাবে কেবল একটুখানি হাসেন সৌম্যদেব৷ বলেন, তারকনাথ এক আজব তত্ত্ব শোনাল৷
— আজব তত্ত্ব বলছো এটাকে?
— আজব মানে, বেশ ইউনিক৷ ভাববার মতো৷
বাপ্পার মুখের দিকে সস্নেহে তাকান তারকনাথ৷ বলেন, দাদুভাই, এই দ্যাখ, কত দামি দামি খাবার! কিন্তু খাওয়ার আগে কাকু-কাকিমাকে একটা পদ্যও শুনিয়ে দাও৷
বাপ্পা বুঝি ততক্ষণে লজ্জা পেয়েছে বেশ৷ দাদুর বুকে মুখ লুকোতে চায় সে৷
তারকনাথ মিষ্টি গলায় বলেন, কী হল? কাকিমা তোমার জন্য কত ভালো খাবার বানিয়ে দিলেন, তুমি তাঁকে একটা পদ্য শোনাবে না?
দাদুর বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে রেখেই মাথা দোলায় বাপ্পা৷
— তবে শোনাও৷ আমাদের এবার উঠতে হবে৷ তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করে রয়েছে না?
বাপ্পা ধীরে ধীরে মুখ তোলে৷ প্রস্তুত হয়৷ একসময় শুরু করে : পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এজীবন-মন সকলি দাও/ তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও/ পরের কারণে মরিলেও সুখ / সুখ-সুখ করি কেঁদো না আর / যতই কাঁদিবে, ততই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয় ভার / আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে / সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে৷৷
পদ্যটা শুনতে শুনতে সৌম্যদেব ও অন্তরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন৷
একসময় স্বামীর দিকে তাকিয়ে অন্তরা বলেন, এই কবিতাটা রনির পড়ার বইতেও ছিল না?
সৌম্যদেব জবাব দেন না৷ কেবল সম্মতিসূচক মাথা দোলাতে থাকেন৷
নাতির দিকে তাকিয়ে তারকনাথ বলেন, এবার খাও৷
বাপ্পা খেতে থাকে৷
তারকনাথ বলেন, আমি কিন্তু এই সময়ে বড় একটা খাইনে৷ একটা নিচ্ছি৷
খেতে খেতে তারকনাথ বলেন, বাই-দি-বাই, তোমার ছেলের কথাটা তো জিজ্ঞেস করাই হল না৷ কেমন আছে সে? তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে?
তারকনাথের কথায় সৌম্যদেব ও অন্তরা খুবই অস্বস্তি বোধ করেন৷ আচমকা আক্রান্ত বোধ করেন ওরা৷ দুজনেই পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন৷
পরক্ষণে নিজেকে অদ্ভুত দক্ষতায় সামলে নেন সৌম্যদেব৷ খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন, আমার ছেলের ক্ষেত্রে অবশ্য তোমার তত্ত্বটা খাটেনি৷ আমারটা ঠিক উলটো৷
— তাই? বাহ্! তুমি তবে বেঁচে গিয়েছ৷
—বছরে না-হোক পাঁচ-ছ’বার তো আসেই৷ সারা মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে সৌম্যদেব বলেন৷
অন্তরাও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন নিজেকে৷ সৌম্যদেবের কথার খেই ধরে বলেন, ছেলে ছুটিছাঁটার কারণে গড়িমসি করলে বউমাই তাড়া লাগায়৷
—আর, এই দ্যাখ না—৷ সৌম্যদেব সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, সেই কবে থেকে বায়না ধরেছে, ওদের কাছে যেতে হবে৷
— হ্যাঁ, একবার তো যাবার এয়ার-টিকিট পাঠিয়ে দিল৷ পাশ থেকে বলে ওঠেন অন্তরা৷
— তা—ই? তারকনাথ মুগ্ধ গলায় বলেন, তা গেলেন না কেন?
— কী করে যাব? অন্তরা জবাব দেবার আগেই বলে ওঠেন সৌম্যদেব, আমার এই সাম্রাজ্যটি দেখবে কে? এতবড় বাড়িটা—ক’মাস না থাকলেই তো ভূত আর চামচিকের বাসা হবে৷
— দু’মাস কী বলছো? পাশ থেকে পোঁ’ ধরেন অন্তরা, সাতদিনের মধ্যেই তালা ভেঙে সর্বস্ব নিয়ে যাবে৷
— সে কি! বাড়িতে কোনও বিশ্বস্ত চাকর-টাকর নেই? ওকে রেখেই তো—৷
— চাকর? তুমি হাসালে! সৌম্যদেব তেতো গলায় বলেন, দুটো বুড়োবুড়ি মাত্তর থাকি৷ চাকর রাখলে একদিন ও-ই তো গলাটি টিপে খুন করে সবকিছু নিয়ে ভাগবে৷ পেপারে দ্যাখ না?
— ওই ভয়ে একটা রান্নার লোক অবধি রাখতে পারিনে৷ অন্তরা বলেন, একটা বুড়িমতো ঠিকে-ঝি রোজ একবেলা আসে—৷ ঝাঁটপাট দিয়ে, বাসন-টাসন মেজে দিয়ে চলে যায়৷ ব্যস৷
তারকনাথ বলেন, কিন্তু এখন তো অনেক সিকিউরিটি এজেন্সি গজিয়েছে৷ তারাও নাকি বাড়ি পাহারা দেবার লোক সাপ্লাই করে?
— তাদেরই-বা ভরসা কি? দু’চোখ কপালে তুলে বলে ওঠেন সৌম্যদেব, ওই সিকিউরিটিই হয়তো সাগরেদদের জুটিয়ে নিয়ে সর্বস্ব নিয়ে গেল৷
— হ্যাঁ, যাবার সময় ওই সিকিউরিটিকে লোকদেখানো বেঁধে রেখে গেল৷ এমনটাই তো ঘটছে৷
— তো, ছেলেকে সেটা বোঝায় কে? সৌম্যদেব বড় তৃপ্তির হাসি হাসেন, বলে কি জানো?
— ছেলেকে বোঝাতে পারলেও, বউমা তো এককাঁটা সরেস৷ মাঝপথে সৌম্যদেবকে থামিয়ে দিয়ে অন্তরা বলে ওঠেন, কী বলে জানেন? বলে, বাড়িঘর বেচে দিয়ে পাকাপাকি চলে এসো আমাদের কাছে৷ বুঝুন! ওই নিয়ে দিন দু’বেলা ফোন করছে৷
— ইদানীং আবার মেয়েটাকেও লেলিয়ে দিয়েছে৷ সৌম্যদেব বলে ওঠেন, সে তো ফোনে রীতিমতো কান্না জোড়ে, কিনা, দাদু-দিদান, টোমরা এসো একটিবার৷
— আর, ছেলেটাও হয়েছে তেমনই অবুঝ৷ একবার আমি খুব অসুস্থ হয়ে হসপিটালাইজ্ড হলাম৷
— পরের দিনই এসে হাজির৷ আর যেতেই চায় না৷ তারপর—কত বুঝিয়ে-সুজিয়ে, কিনা, তোর চাকরির ক্ষতি হয়ে যাবে বাবা৷ ওদেশের চাকরির ধরন তো আমি বুঝি৷ ওরা শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, আর কাজটি আঠারোআনা বুঝে নেয়৷ ওদের কাছে, মা-বাবা, আত্মীয় পরিজন— কারোরই কোনও মূল্য নেই৷ কিন্তু ছেলে তা বুঝলে তো!
কথাগুলো বলতে বলতেই সৌম্যদেব আড়চোখে লক্ষ করেন, ক্রমশ থমথমে হয়ে উঠছে অন্তরার চোখমুখ৷ সৌম্যদেব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন৷ তার আগেই অন্তরা বলে ওঠেন, এবার তুমি থামো৷ ছেলে- বউমা’র গুণের কথা আর কত বলবে ওঁকে? ওঁনার হয়তো বোরিং লাগছে৷
— না, না, বোরিং লাগবে কেন? তারকনাথ উচ্ছ্বসিত গলায় বলতে থাকেন, বরং শুনতে ভালোই লাগছে আমার৷ চারপাশে যা দেখছি! আয়-উপায়, বিয়ে-থা করে ছেলেগুলো যেভাবে বাপ-মা’র প্রতি মিনিমাম কর্তব্যটুকু করতেও ভুলে যাচ্ছে!
তারকনাথের কথায় বুঝি আরও উৎসাহ পেয়ে যান সৌম্যদেব৷ কল্পিত স্মৃতির ঝাঁপি খুলে হাট করে দিতে চান তারকনাথের সুমুখে৷ বলেন, আর, যখন বাড়ি আসে, কাঁড়িকাঁড়ি জিনিস আনে আমাদের জন্য৷ আমার কী-কী পছন্দ, ওর মায়ের কী-কী পছন্দ, এত ব্যস্ততার মধ্যেও ঠিকই মনে রেখেছে! যতই বলি, এত-এত জিনিস কেন আনিস আমাদের জন্যে? এই বয়েসে এসব নিয়ে আমরা করব কি? কিন্তু ছেলে সেকথা কানে তুললে তো!
ততক্ষণে অন্তরার মুখখানি আরও থমথমে হয়ে উঠেছে৷ একসময় স্বামীকে মৃদু তিরস্কার করেন তিনি৷ বলেন, খালি বকবক করেই চলেছে! নিজের ছেলেকে নিয়ে এত বলারই বা কী আছে?
কিন্তু তখন বুঝি সৌম্যদেবকে নেশায় পেয়েছে৷ কিছুতেই নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারছেন না তিনি৷ কাজেই, অন্তরার কথায় কর্ণপাত না করে তিনি বলেই চলেন, ছেলেকে কোনওগতিকে বোঝাতে পারলেও বউমা’টা একেবারেই অবুঝ৷ বলে কি জানো? বলে, তোমাদের জন্যে আনব না তো কার জন্যে আনব বাপি? তোমরা ছাড়া আমাদের আর আপনজন বলতে কে আছে?
— এইবার থামো তুমি৷ সহসা খুব অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠেন অন্তরা৷
— আর, নাতনিটাও তেমনি৷ সৌম্যদেব সমানে যষ্টিমধুটি চুষেই চলেন, এখানে এসে যতদিন থাকে, একদণ্ডের তরেও আমাদের কাছ-ছাড়া হয় না৷ ওর বাবা বলে, চল্ রিয়া, কোলকাতার তো কিছুই দেখলি না তুই! কতকিছু দেখবার রয়েছে এখানে৷ কিন্তু তার ওই একটাই কথা, দাদু-দিদানকে ছেড়ে কোত্থাও যাব না৷
— আহ্, তুমি থামবে? খুব ঝাঁঝাল গলায় স্বামীকে কড়া ধমক দেন অন্তরা৷
— আরও কী বলে জানো? বলে, দাদু, আমি আর ওদেশে ফিরে যাব না৷ আমি তোমাদের কাছেই থাকব৷ এখানকার স্কুলেই পড়ব৷ রাতের বেলায় তোমাদের মাঝখানে শোবো৷ তোমরা আমায় পালা করে গল্প শোনাবে—৷
অন্তরা আর সইতে পারেন না৷ একসময় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বড় কষ্টে কান্না সামলে ছুটে বেরিয়ে যান ঘর থেকে৷
সৌম্যদেব স্থাণু’র মতো বসে থাকেন৷ ততক্ষণে তাঁর কপালের আড়াআড়ি শিরাদুটো টানটান হয়ে চাগিয়ে উঠেছে৷
অন্তরার এমন অকস্মাৎ ভাবান্তরে তারকনাথ হকচকিয়ে যান৷
সৌম্যদেবের দিকে তাকিয়ে শুধোন, কী হল বউঠানের? অমন করে চলে গেলেন যে?
তারকনাথের কথার জবাবটা সহসা দিয়ে উঠতে পারেন না সৌম্যদেব৷ কেবল অন্তরার জন্য দু’চোখে গভীর অনুকম্পা ফুটিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকেন৷
ততক্ষণে খাবারসহ বাপ্পার হাতটা মুখের কাছে থেমে গিয়েছে৷ আন্টি’র ছুটন্ত শরীরটার দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে সে৷
সহসা গোটা ড্রইংরুমটা জুড়ে শ্মশানের স্তব্ধতা৷
কেবল পার্শ্ববর্তী ক্লাব থেকে ভেসে আসে গানের কলি : মাম্মি দেখ্, মাম্মি দেখ্, তেরি মুন্না বিগড়্ গয়ে…৷