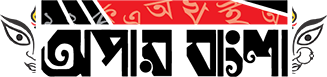বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও অনুবাদের জগত
বিতস্তা ঘোষাল
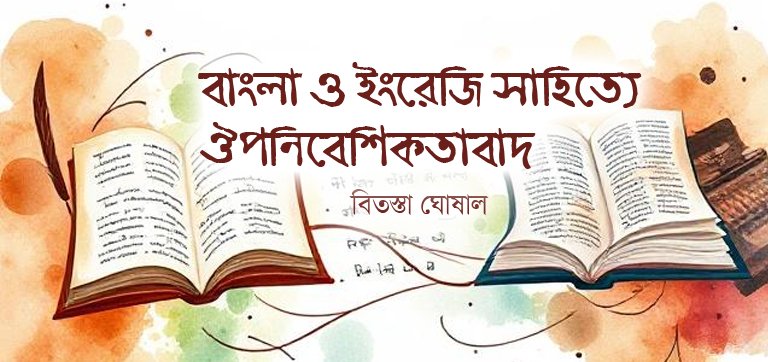
পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন আবিষ্কারের পর দেখা যায় Migratory Birds বা পরিযায়ী পাখিরা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। যদিও তখন কোনো ভূখন্ড নির্দিষ্ট ছিল না। ভূখন্ডের অধিকার কায়েম হবার পর দেখা গেল এই পরিযায়ী পাখিদের মতোই মানুষের ভাষাও সীমানা পেড়িয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা অতিক্রম করতে শুরু করল। খুব আশ্চর্যের বিষয় যে তখন থেকেই অনুবাদ নামক বিষয়টিও মানব সভ্যতার একটা অঙ্গ হয়ে উঠল। শক্তি কায়েম করার জন্য যে জিনিসগুলোকে শক্তিমান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হাতিয়ার করল, তার একটা বড়ো অংশ জুড়ে রইল ধর্ম। নিজের ধর্ম তা ভয় পেয়েই জন্ম নিক, কিম্বা শান্তির জন্যই হোক, সেই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অন্য ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার একমাত্র অস্ত্র ছিল স্থানীয় ভাষার অনুবাদ। কাজেই মানব সভ্যতার ইতিহাস যতদিনের, অনুবাদও ততদিনেরই পুরোনো। যদিও সেই সময় কারা অনুবাদ করছেন, কোন ভাষা থেকে থেকে অনূদিত হচ্ছে এই লিখিত ইতিহাস আবিষ্কার করা অনেক ক্ষেত্রেই হয়নি। তার একটা প্রধাণ কারণ অনুবাদকে স্বীকৃতি দিতে অনিহা। তবু প্রদীপের শিখার মতোই তার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
ভারতবর্ষে আদি পর্ব থেকেই একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। যে শক্তি যখন এদেশে এসেছে তখন তাদের মতো করে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভাষাকেই বেছে নিয়েছেন। তারই প্রয়োজনে যেমন এক ভাষার সঙ্গে আরেক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে, ঠিক তেমনি অনুবাদের কাজটিও চলেছে সমান্তরালভাবে।
তারই উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন, ও আদি মধ্য যুগের সূচনা অনুবাদের মাধ্যমে। কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু বাল্মীকি রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত গীতা অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালির ঘরে পৌঁছে গেল। জার্মান সাহিত্যের মার্টিন লুথার ও ইংরেজি সাহিত্যের উইলিয়াম টিণ্ডেলের মতো এনারাও আর্য ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অনুবাদকেই হাতিয়ার করেছিলেন।
আসলে অনার্য অধুষ্যিত বাংলাদেশ খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসার পর আর্য প্রভাবের যে ক্রম বিস্তার ঘটেছিল, আরো পরে দ্বাদশ–ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি বিজয়ের ফলশ্রুতিতে বিধর্মীয় রাজশক্তির প্রভাব ঠেকাতে এবং প্রতিষ্ঠিত আর্থ – সামাজিক স্থিতাবস্থার ভাঙন এড়াতে সমাজ শক্তির নেতৃত্ব স্থানীয় প্রতিনিধিরা হাতিয়ার করেছিলেন অনুবাদ সাহিত্যকে। এছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় ছিল না। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে বলেছেন “বাঙালি সমাজের পুর্নগঠনের জন্য এবং বাঙালি ঐতিহ্যের সর্ব ভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদশ্রয়ী প্রভাবের ও প্রয়োজন ছিল”।
অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই অনুবাদ সংস্কৃত, ফারসী, আরবীতেই বেশি। এই শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল দা আসসুমপ সাম ধর্মান্তরিত বাঙালি দোম আস্তোনিওর ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থটি পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন। অন্যদিকে একটি পর্তুগীজ নিবন্ধও বাংলায় ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ নাম দিয়ে অনূদিত হয়, যদিও এতে আরবী ও ফারসী শব্দের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।
১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত ধরে ইংরেজ এ দেশে প্রবেশ করলে বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের সূচনা হয়। যেমন বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে, যার লেখক একজন ব্রিটিশ – নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ। ইংরেজিতে লেখা ওই ব্যাকরণ বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’। মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও এতে অনেক অক্ষর, শব্দ, বাক্য, পদ্যাংশ ও শ্লোক বাংলা হরফেই ছাপা হয়েছিল; কয়েকটি জায়গায় কিছু ফারসি লিপিও ছিল। ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৮। এর মধ্যে মূল বইটির শুরু প্রথম তিরিশ পৃষ্ঠার পর। প্রথম শিরোনাম-পৃষ্ঠার পর পঁচিশ পৃষ্ঠা ধরে রয়েছে লেখকের ভূমিকা এবং তার পরের পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে সূচীপত্র আর রয়েছে সংশোধন ও সংযোজনের বিজ্ঞাপন।
সঙ্গীতজ্ঞ, ভায়োলেঞ্চেলো শিল্পী রুশীয় গেরাসিম স্তেফানভিচ্ লিবিয়েদেফ্ বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন ইংরেজি নাটক রিচার্ড পল জড্রেলের ‘দি ডিসগাইজ’। যেটির বাংলা রূপান্তর হল ‘কাল্পনিক সংবদল’। এটি ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর প্রথম প্রদর্শিত হয়। তিনি ‘Love is the best doctor’ নাটকটিও বাংলায় অনুবাদ করেন। কাল্পনিক সংবদল দ্বিতীয় বার মঞ্চস্থ হবার পরই তাঁর রঙ্গমঞ্চ দূরভিসন্ধি করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
কালানুক্রমে দেখা যাচ্ছে তারিণীচরণ মিত্র ১৮০৩ সালে ঈশপের গল্পের অনুবাদ করছেন। পাশাপাশি ভাষাতাত্ত্বিক উইলিয়াম জোন্স করেন ১৮০৭ সালে গায়ত্রী মন্ত্রের অনুবাদ। রেভারেন্ড লং এর ক্যাটালগে দেখা যায় ১৮০৯ সালে মঙ্কটন শেক্সপীয়রের ‘দি টেমপেস্ট’ নাটকের অনুবাদ করছেন বাংলায়। ১৮৩৬ সালে কালীকৃষ্ণ বাহাদুর অনুবাদ করছেন গে’স বাইবেল। কিন্তু এসবই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ।
কিন্তু সে অর্থে উপনিবেশবাদ পাকাপাকি জায়গা নেওয়ার পর মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বৃহৎ অর্থে অনুবাদের কাজ শুরু হয়। প্রথমত- উপনিবেশিক শাসনের সুবিধার্থে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনে, পাঠ্য বইয়ের অনুবাদ বা রাষ্ট্রশাসনের জন্য অপরিহার্য আইন কানুন, রীতিনীতি, নির্দেশনামা প্রভৃতির অনুবাদ কিম্বা ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ সংঘটিত হয়েছিল। ফল স্বরূপ ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষাতেই অনুবাদ শুরু হল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিল। পাশাপাশি সরকারী ও আদালতের ভাষা ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী হয়ে ওঠায় অনুবাদ ছাড়া উপায় ছিল না।
এই পর্যায়ে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়বার তৎকালীন একমাত্র গণমাধ্যম সংবাদপত্রকে বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছবার হাতিয়ার করে বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, এক্ষেত্রে বহু-ভাষাজ্ঞান ও অনুবাদ-দক্ষতায় তিনি প্রকাশ করলেন – এক পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে ‘Brahmanical Magazine’, আর অন্য পৃষ্ঠায় মূল রচনার বাংলা অনুবাদ ‘ব্রাহ্মণ সেবধী’ (সেপ্টেম্বর ১৮২১)। ম্যাক্সমূলারের লেখা থেকে জানা যায় “রামমোহনই প্রথম বেদান্তকে ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে পরিচিত করিয়েছেন…”।
দ্বিতীয়ত, এদেশের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেনী অনুবাদকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন রেনেসাঁর পরবর্তী বিশ্ব সাহিত্যকে জানার প্রয়াসে। অর্থাৎ এই পর্যায়ে ‘Translation then during this period, had a duel role, serving the interests of both colonizer and colonized”।
এই পর্যায়ে বহুল আলোচিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের ১৮৬০ সালে রচিত ‘নীলদর্পন’ নাটক। নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তবে আধুনিক গবেষকগণ এই বিষয়ে একমত নন। এই অনুবাদ Nil Durpan, or The Indigo Planting Mirror নামে প্রকাশ করেছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়।
অবশ্য যাঁর হাত ধরে ইংরেজি থেকে সক্রিয়ভাবে অনুবাদ শুরু হল তিনি হলেন উনবিংশ শতকের প্রবাদপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় তাঁর কৃত ‘কথা মালা’র বিজ্ঞাপনটি-
“রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বছর পূর্বে গ্রীসদেশের ইসপ্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগত গল্পের রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইংরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং য়ুরোপের সর্ব্ব প্রদেশেই অদ্যাপি আদরপূর্বক পঠিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকর্ম্মাধক্যশ্রীযুক্ত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলি তাদদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না। এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাতত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল”।
অর্থাৎ এই সময় শাসক শ্রেণীর সচেতন প্রয়াসে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে অনুবাদ হয় যার ফলশ্রুতি শ্রীরামপুর মিশন বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। কেরী অনুবাদকে ধর্ম প্রচারের প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। তিনি নিজে বা তাঁর নেতৃত্বে ৪০ টি এশীয় ভাষায় আংশিক বা সম্পূর্ণ বাইবেল অনূদিত হয়েছিল।
এছাড়াও এই সময় যারা অনুবাদ চর্চায় মন দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ নিজে অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করার পাশাপাশি তাঁর লেখাও ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন নিবেদিতা ও তিনি নিজেও। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষও অনুবাদ হচ্ছে এই পর্বে। যদিও সেই অনুবাদের মান নিম্ন হওয়ায় পরবর্তী কালে আর তা অনুবাদ নিয়ে চর্চা হয়নি। নিবেদিতা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি আরো অনেকের লেখাই অনুবাদ করেছেন এই পর্যায়ে।
অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অনুবাদের ধারা সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে প্রবাহিত, যা শুধু যে সাম্রাজ্যবাদের কারনে হয়েছিল তা নয়, বিশ্ব দরবারে বাংলা সাহিত্য নাটক বিজ্ঞান শিল্পকে পৌঁছে দেবার ও সর্বোপরি নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আলো দেখা পাবার ও প্রতিবাদের ভাষা হিসাবেই অনুবাদকেই সঙ্গী করেছিলেন যুগপুরুষরা, যার ধারা এখন ক্রমশ বর্ধিয়মান।যদিও এ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলাম ঔপনিবেশিক ভারতেই, কিন্তু অনুবাদ ছাড়া যে বিকল্প নেই তা আজ আর সংশয়ের অবকাশ রাখে না।