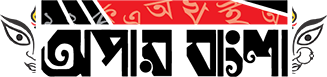অপরাজিতা
রম্যাণী গোস্বামী
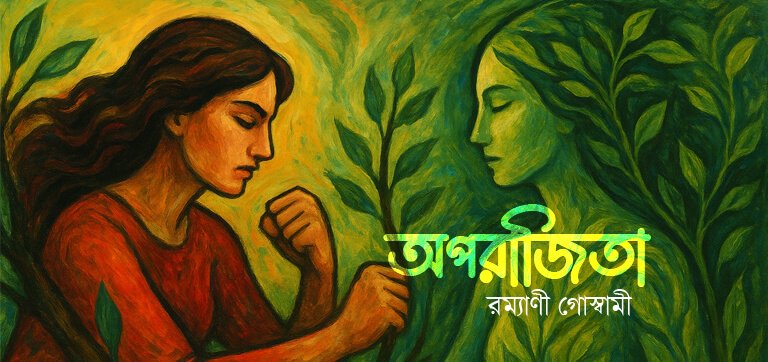
মহালয়ার ভোরে তর্পণ শেষে সূর্যপ্রণাম করে মা মহামায়াকে আহ্বান করার মাধ্যমে পিতৃপক্ষের অন্তে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। ঘটনাচক্রে এই দিনটিতেই আমার হাতে এলো মার্কিন মেরিন বায়োলজিস্ট ও পরিবেশবিদ রাচেল কারসনের লেখা বিখ্যাত বই ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’। কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার জীবজগতের সার্বিক ক্ষতির জন্য যে কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে, ১৯৬২ সালে লেখা এই বই সর্বপ্রথম বিষয়টি সম্পর্কে মানবসভ্যতাকে অবহিত করে। সকলে পড়ে চমকে ওঠেন! তবে শুধু এই বইটিই নয়, পঞ্চাশের শেষের দশকে ওই লেখিকার পরিবেশ সংক্রান্ত আরও দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বই গোটা বিশ্বে বিপুলভাবে পরিবেশ সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং তারপরেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বহু মানুষ নিজেরাই যেচে উদ্যোগী হন।
এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় আরও কয়েকজন আসামান্যা রমণীর কথা। মনে পড়ে যায় পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় তাঁদের লড়াইয়ের অনুপুঙ্খ। কথিত আছে যে প্রকৃতি ও নারী একে অপরের পরিপূরক। আদি অনন্তকাল থেকে নারী ও প্রকৃতি এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে এক অমোঘ যোগাযোগ। একজন রমণী যে পরিমাণ যত্নে নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে তিলে তিলে বড় করে তোলেন, প্রকৃতি মা-ও ঠিক তেমনভাবেই তার সন্তানকে – সে মানুষ হোক, গাছপালা বা কীটপতঙ্গ – তাদের অন্নজল, ছায়া, আশ্রয় ও ভালোবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট করে তোলেন। বিশেষ করে নারীরাই তাই আগাগোড়াই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন।
দেবীপক্ষে তেমনই কয়েকজন অপরাজেয় রমণীর কথা তুলে ধরছি। তাঁদের কঠিন সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধরে রাখার চেষ্টা করছি এই লেখায়।
পরিবেশরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য দেওয়া হয় ‘গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ’ যা বিশ্বব্যাপী ‘গ্রিন নোবেল প্রাইজ’ নামেও খ্যাত। আজ থেকে বারো বছর আগে এই পুরস্কারটি পেয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার টিমোর আইল্যান্ডের বাসিন্দা মোল্লো জনজাতির অ্যালেটা বাউন। টিমোর দ্বীপটির প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে ঘন জঙ্গল, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্যে ঠাসা মিউটিস পাহাড়। শুধু তাই নয়, দ্বীপের লোকজনের পান করার ও চাষাবাদের উপযোগী জলদায়ী নদীগুলির প্রধান উৎসস্থলও হল অরণ্য পরিবৃত ওই পাহাড়টি। ছোট্টবেলা থেকেই টিমোর দ্বীপের মোল্লো জনজাতি তাই দেবতাজ্ঞানে পুজো করে এসেছে মিউটিস পাহাড়কে।
আশির দশকে ওয়েস্ট টিমোরের স্থানীয় প্রশাসনিক মহল থেকে পাওয়া পারমিটের সুবাদে একটি মাইনিং এজেন্সি মোল্লো টেরিটরির ভিতরে মিউটিস পাহাড় কেটে মার্বেল পাথর তুলতে আরম্ভ করে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবাধে গাছ কাটার ফলে সেখানে নেমে আসে একের পর এক ভূমি ধস। নদীর সুপেয় জল অচিরেই হয়ে ওঠে দূষিত, পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মোল্লো আদিবাসীরা রুখে দাঁড়ান নিজেদের অস্তিত্বরক্ষায় ও প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে। সেই প্রতিবাদের অগ্রপথিক ছিলেন অ্যালেটা বাউন। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন তিনি। শুরু হল ভয় দেখানো, লাইফ থ্রেট, মর্যাদাহানির কুৎসিত অপচেষ্টা। নিজের প্রাণ ও সম্মান বাঁচাতে উপায়ন্তর না দেখে দুধের শিশুকন্যাকে বুকে জড়িয়ে জঙ্গলের গভীরে পালিয়ে যান অ্যালেটা। লুকিয়ে থাকেন ততদিন পর্যন্ত যতদিন না কোলের সন্তান একটু বড় হয়। তারপর তিনি আবার ফিরে আসেন লোকালয়ে। আরও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞায়।
এর পরবর্তী ঘটনা বিস্মিত করে দেওয়ার মতো। অ্যালেটা বাউনের নেতৃত্বে যে প্রতিবাদ আন্দোলন একদিন শুরু হয়েছিল মাত্র তিন-চারজন বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা মিলে, সেই জায়গায় যোগ দিলেন দেড়শজন মোল্লো আদিবাসী রমণী। ফিনিক্স পাখির মতো জীবনের স্পৃহায় দুটো ডানা প্রসারিত করে ছাইয়ের স্তূপ থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। উড়ে গিয়ে বসলেন পাহাড়ের সেই অংশে, পাথর কেটে মার্বেল খননের কাজ চলছিল যেখানে। হাতে তাঁদের নিজস্ব তাঁত বোনার যন্ত্র। রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নীরবে ঘাড় হেঁট করে তাঁত বুনে চললেন তাঁরা। নড়লেন না নিজেদের অবস্থান থেকে একচুলও। বরং চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন প্রশাসনের উদ্ধত অস্ত্রকে। বুলডোজার চালিয়ে পাথর ভাঙবে? বেশ তো। আমাদেরকেও উড়িয়ে দাও। দেখি তুমি কত শক্তিমান!
এইখানে এসে ইন্দোনেশিয়ার অখ্যাত দ্বীপের মোল্লো আদিবাসীদের গল্প এক হয়ে যায় ভারতের হিমাচল প্রদেশের আরও এক অখ্যাত গ্রামের দলিত পরিবারে জন্ম নেওয়া কিঙ্করীদেবীর সঙ্গে। সময়টা ১৯৮০। ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে জেরবার গোটা গ্রাম। কিঙ্করীদেবী দেখলেন অবৈধভাবে পাথর কেটে নেওয়াই এই দুর্গতির কারণ। সামান্য পাথর ভেঙে যার দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে, সেই নিরক্ষর রমণী শুধুমাত্র অদম্য সাহস এবং ইচ্ছেশক্তিতে ভর করে আটচল্লিশ জন বেআইনি চুনাপাথরের মালিকের বিরুদ্ধে কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন। সেই মামলার শুনানি না হওয়া অবধি প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে টানা উনিশ দিন সিমলায় আদালত চত্বরের সামনে তিনি অনশনে বসে থাকেন একঠায়। অবশেষে মহামান্য আদালতের টনক নড়ে। ১৯৮৭ সালে হিমালয় পাহাড়ে অবৈধ মাইনিং বন্ধ হয়। বিনিময়ে মেলে দুষ্কৃতিদের তরফ থেকে প্রাণনাশের হুমকি। তবে বাষট্টি বছরের অকুতোভয় রমণীটি যে তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি এতে আর সন্দেহ কী!
আজ থেকে তিনশো বছর আগে রাজস্থানের বিশনয়দের গল্পটা সকলের জানা। যোধপুরের রাজার নতুন মহল তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রচুর চুন। চুনাপাথর তো রয়েছে। কিন্তু তা থেকে চুন তৈরির জন্য চাই জ্বালানী। তাই আরম্ভ হল নির্বিচারে খেজরি গাছ কাটা। সেই খেজরি গাছ যা কিনা জন্ম থেকেই যোধপুরের বিশনয় কমিউনিটির পূজ্য, মরুপ্রধান অঞ্চলে ভূমির অভ্যন্তরে জলধারণের একমাত্র সহায়িকা। প্রতিবাদে গাছেদের নীরবে জড়িয়ে ধরা এবং রাজার সৈনিকদের কুঠারের নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া তিনশো তেষট্টিটি প্রাণের! শেষমেশ বন্ধ হয় গাছ কাটা। শোনা যায় ১৯৭৪ সালের চিপকো আন্দোলনের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল এই ঘটনাই। এই বিশনয়দের প্রতিবাদের পুরোধাও ছিলেন কিন্তু চারজন নারী। অমৃতাদেবী ও তাঁর তিন কন্যা।
কেনিয়ার গ্রিন বেল্ট মুভমেন্টের কথা কি আমরা কোনওদিন ভুলতে পারি? ভুলতে পারি ‘পৃথিবীর বৃক্ষজননী’ নামে পরিচিত ২০০৪ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কেনিয়ার সমাজকর্মী ও অধ্যাপক ওয়াঙ্গারি মাথাইয়ের অবদান? তখন ১৯৭৭ সাল। আফ্রিকার কেনিয়ায় বসবাসকারী কিছু গ্রামীণ মহিলা এসে জানান যে তাঁদের গ্রামের ঝোরাগুলি হঠাত শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। টান পড়েছে প্রাকৃতিক সম্পদে। খাদ্য ও জল এই উভয়েরই চরম সঙ্কট। ঘরে উনুন জ্বলবে। সেই জন্য জ্বালানির প্রয়োজন। বাড়ির সীমানায় বেড়া দিতেও দরকার শুকনো কাঠ। সেই কাঠের সন্ধানে তাঁদের পাড়ি দিতে হচ্ছে দূর দূরান্তের পথ। যা এর আগে কখনও হয়নি। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় এ সবই হল বনাঞ্চল ধ্বংস ও লাগাতার বৃক্ষছেদনের ফল।
প্রফেসর মাথাইয়ের নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালের ৫ জুন, অর্থাৎ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে তাঁরই বাড়ির উঠোনে অল্প কয়েকজন রমণী মাত্র সাতটি গাছ পুঁতলেন। সূচনা হল গ্রিন বেল্ট আন্দোলনের। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলো তাঁদের রোপিত গাছের পরিমাণ। যে পরিসংখ্যান একদিন গোটা পৃথিবীকে অবাক করে দিল। ২০০৫ সালের ভিতরে ৩০ মিলিয়ন গাছ লাগিয়ে ফেলেছেন আন্দোলনকারীরা! তারপর গত কুড়ি বছরে সংখ্যাটা প্রায় ৫১ মিলিয়ন ছুঁয়েছে!
বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত গ্রিন বেল্ট আন্দোলন সাক্ষী থেকেছে সফলভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করতে, বৃষ্টির জল ধরে রাখতে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরুত্থান ও সংরক্ষণ এবং নারীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার কাজেও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। গোটা বিশ্বকে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের পাঠ শিখিয়েছেন প্রফেসর ওয়াঙ্গারি মাথাই। তাঁরই একটি উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি – “It is the people who must save the environment. It is the people who must make their leaders change. And we cannot be intimidated. So we must stand up for what we believe in”.
মিউটিস পাহাড়ে যদিও কুঠার বা বুলডোজার চলেনি। বরং টানা এক বছর ধরে সেখানে বোনা হতে থাকে একের পর এক মোল্লোদের ট্র্যাডিশনাল বস্ত্রখন্ড। যার প্রতিটি বুননের প্রাকৃতিক সুতোয়, ভেষজ রঙের চোখ ধাঁধানো উজ্জলতায় নীরবে গাঁথা হতে থাকে নীরব প্রতিবাদের বাণী। সেই একটি বছর গ্রামের পুরুষেরা এগিয়ে এসে বাড়ির মহিলাদের জায়গা নিলেন। গৃহস্থালির কাজকর্ম, রান্নাবান্না, শিশুদের লালনপালনের দায়িত্ব তাঁরা স্বেচ্ছায় বহন করে চললেন দিনের পর দিন। ইকোফেমিনিজমের এ এক অনবদ্য রূপ তো বটেই! লাইমস্টোন থেকে মার্বেল উত্তোলনের বিরুদ্ধে অ্যালেটা বাউনের নেতৃত্বে ঘটে চলা সেই ‘উইভিং প্রোটেস্ট’ ছিল এমনই এক অভূতপূর্ব ঘটনা যা সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা বিশ্বে। ২০১০ সালে রাষ্ট্রকে বাধ্য হয়েই মাথা নোয়াতে হল পাথুরে জমিতে বসে তাঁত বুনে চলা একরোখা সেই দেড়শজন নারীর সামনে। বন্ধ হল মাইনিং। রক্ষা পেল পরিবেশ।
এভাবেই কোথাও যদি তাঁত বোনাকে নারীর প্রতিবাদের রূপ হিসেবে ধরা হয়, তো কোথাও আবার কবিতা, নাটক, কলম হয়ে ওঠে পরিবেশ ধ্বংসকারী অসুরের বিরুদ্ধে দশভুজার হাতের অস্ত্র। চিপকো আন্দোলনের কথা আমাদের সকলেরই জানা কিন্তু এর প্রায় সমসাময়িক সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্টের কথা আমরা কতজন জানি? সাইলেন্ট ভ্যালি। কেরালার পালক্কাড় জেলার এক চিরহরিৎ ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য। কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড প্রকল্পিত এক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গঠনের জন্য ওই জঙ্গলের বৃহৎ অংশে শয়ে শয়ে গাছ কেটে ফেলার পরিকল্পনা ছিল। বাঁধের কারণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় চলে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতো বাস্তুতন্ত্র। এই ঘটনার প্রতিবাদে নিজের কলমকে সম্বল করে এগিয়ে আসেন এক আলোকবর্তিকা। তিনি একাধারে কবি ও একজন সমাজকর্মী। তিনি পদ্মশ্রী প্রাপক সুগাথাকুমারী।
১৯৬৮ সালে কবিতার জন্য কেরালা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার শুধু নয়, কবিতা লিখে সুগাথাকুমারী পেয়েছেন আরও আরও অনেক, অগাধ সম্মাননা। এবার কবিতাকেই তিনি করলেন তাঁর প্রতিবাদের ভাষা। ১৯৭৩ সালে মূলত তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ‘সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট’। তাঁর লেখা কবিতা ‘মারাতিনু স্তুতি’ (Ode to a Tree) হয়ে ওঠে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মূল সুর। ‘সেভ সাইলেন্ট ভ্যালি’ ক্যাম্পেইনের জমায়েতের উদ্বোধনী সঙ্গীতে গর্জে ওঠে এই কবিতার পঙক্তিরা। এরপর রাষ্ট্রকে মাথা নোয়াতেই হয়। ১৯৮৩ সালে রদ করা হয় স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এবং ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে ওই একই জায়গায় গড়ে ওঠে সাইলেন্ট ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। সুগাথাকুমারীর নেতৃত্বে ধূসর পৃথিবীতে জয় হয় এক টুকরো সবুজের।
এরকম আরও অজস্র বলিষ্ঠ নাম উচ্চারণ করা যায়। সুইডেনের গ্রেটা থুনবার্ন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর। ‘এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফরেস্ট’ নামে খ্যাত পদ্মশ্রী তুলসী গৌড়া। পরিবেশবাদী ও প্রাবন্ধিক বন্দনা শিবা। বলা যায় ব্রিটিশ জুলজিস্ট ডক্টর জেন গুডল, পৃথিবী বিখ্যাত শিম্পাঞ্জি এক্সপার্টের রোমাঞ্চকর কাহিনী। কিংবা বলা যায় হন্ডুরাসের নিহত পরিবেশকর্মী বার্টা ক্যাসেরেসের মতো আরও অনেক নারী আন্দোলনকারীর কথা। কিন্তু এরপরেও উন্নয়নের নামে তথাকথিত সভ্য লোকেদের নিরন্তর প্রকৃতি ও পরিবেশকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া চলছে, চলবে। চলছে, চলবে।
‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ বইটিতে রাচেল দিয়েছেন এমন এক শহরের বিবরণ যেখানে একদা বসন্তের ভোরগুলো জেগে উঠত রবিন ও স্টারলিং পাখিদের মিষ্টি গানে আর ভ্রমরের গুঞ্জনে। কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলত নদী। মাছেরা জলে পরমানন্দে খেলা করত। পাখির বাসায় ডিম ফুটে হাঁ করত টুকটুকে ছানা। মা পাখি সেই ছোট্ট হাঁ মুখে পরম স্নেহে গুঁজে দিত খাবার। শিশুরা শান্তিতে ঘুমোত তাদের মায়ের কোলে। কিন্তু তারপর একদিন বদলে যায় পুরো চিত্রটাই। নিঝুম সকালগুলো মনে ভয় ধরায়। পাখিরা আসে না। ওদের গান হারিয়ে যায় কোথায়। বিষাক্ত নদীস্রোতে ভেসে যায় মৃত মাছের স্তূপ। পাখিদের ডিম ফুটে ছানা বের হয় না আর।
এমন এক ভয়াবহ পৃথিবীর কল্পনা যখন মনকে শিহরিত করে তোলে তখনই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে এইসব নারীদের প্রতি। পৃথিবীকে আরও কিছুটা সবুজ করার স্বপ্ন যাঁদের কখনও হার মানতে শেখায়নি।
যাঁরা প্রকৃত অর্থেই অপরাজিতা।