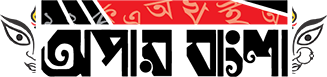এই সময়ের লেখালেখি
অরিন্দম গোস্বামী

অনেকেই এখন আর নিয়মিত ভাবে সাহিত্য পড়ার সময় পান না। হয়তো পেশাগত দায়িত্ব খেয়ে নিচ্ছে মানুষের অনেকটা সময়। বাকিটুকু চেটেপুটে নিচ্ছে সামাজিক বিভিন্ন মাধ্যম। তবুও কিন্তু নিশ্চিতভাবেই পাঠক রয়েছেন। লেখক বিশেষে পাঁচ থেকে পাঁচশো কপি বিক্রি কিন্তু হচ্ছে বছরে। হোক না সেসব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিচিত বা আধা-পরিচিত সামাজিক বৃত্তের মানুষ। তবুও লেখক লিখছেন, প্রকাশক প্রকাশ করতে উৎসাহ পাচ্ছেন। গত দশ বা কুড়ি বছরের মধ্যে এমন বেশ কিছু প্রকাশক এসেছেন, এমন বেশ কিছু পত্রিকার উন্মেষ ঘটেছে – যাঁদের নাম এখন আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। এবং এঁদের মধ্যে অনেকে কিন্তু থাকতেই এসেছেন।
বিষয়ের নতুনত্ব বা অভিনবত্বের প্রসঙ্গ যদি উঠেই পড়ে, তাহলে এর ঠিক বিপরীতে অবস্থান করে প্রথাগত বা চিরাচরিত আঙ্গিক ছেড়ে নতুন কোনো নির্মাণ পরিকল্পনার কথা। কিন্তু আমরা তো জানিই যে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেটা আপনা থেকেই কিছুটা পরিবর্তিত হতে থাকে। রচনার ভেতর দিয়ে যেমন প্রকাশ পায় যুগগত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন – ঠিক সেই হিসেবে, নতুন যুগের সাহিত্য গন্ধ মেখে আরো কিছুটা নতুন হতে তো বাধ্য। আবার বৃহৎ অর্থে বেশ কিছু বিষয় চিরায়ত। আমাদের প্রেম, হিংসা, ক্ষোভ, যৌনতা – এই সব বিষয়ে সংঘর্ষ বা মেনে নেওয়া অথবা প্রতিযোগিতার কাহিনি – ঠিক এই গোত্রের মধ্যে পড়তে পারে। কেউ কেউ যেমন বলেন পৃথিবীর সব গল্প লেখা হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ নতুন কাহিনি আর নেই। আমরা সেই কাহিনিই আবার লিখছি, নিজেদের মতো করে। কথাটা আংশিক সত্যি। তবে, কাহিনি বলার ভঙ্গি দিনে দিনে আলাদা হয়েছে, ব্যতিক্রমীও হয়েছে।
তবুও বিষয়ভিত্তিক সাযুজ্য-ও কি আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে না? একসময় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প হয়ে উঠেছিল বাংলা ছোটগল্পের একমাত্র অনুসরণ যোগ্য উদাহরণ। এখনও পর্যন্ত সেই প্রবাহ একেবারে থেমে গেছে – এমনটা মনে হয় না। তবে স্তিমিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। তেমনি কারো কারো লেখা অনুসরণ করাই যায় না। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখার বিষয় বা আঙ্গিক – সর্বত্রই এক বিশেষ ধরন – আমরা যাকে বলি সিগনেচার স্টাইল।
কিন্তু যিনি লিখছেন এই শতাব্দীতে। তিনি তো আগের শতাব্দীর সেরা লেখাগুলো পড়ে দেখেছেন। কাজেই প্রবাহিত হতে থাকে তাঁর স্মৃতি, এমনকি পঠিত বিদেশি সাহিত্যের স্মৃতিও – লেখকের অন্তরালে। কখনো বা অজান্তেই। এজরা পাউন্ড বলেছিলেন – ঐতিহ্যই হলো সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্য প্রবাহিত হয় পরবর্তীতে। জীবনানন্দ যাঁকে বলেছিলেন – ইতিহাস চেতনা; বলেছিলেন – তার মর্মে চাই পরিচ্ছন্ন কাল জ্ঞান। সেটাও তো এই ঐতিহ্যবাহীতাকেই চিহ্নিত করে। বরং ঐতিহ্যের তুলনায় ইতিহাসের কনসেপ্ট ব্যাপকতর।
কিন্তু পাঠক তো পুরোনো গল্প শুনবেন না। এমনকি শিশুরাও সেটা শুনতে চায় না। তাই, লেখককে নতুনভাবে গল্প বলতেই হয়। ছুটে বেড়াতে হয় বিভিন্ন স্থানে, যাতে সম্প্রসারিত হয় গল্পের ভূগোল। একসময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় পাঠক যে আকাঁড়া আঞ্চলিকতার স্বাদ পেয়েছেন, এখন গত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এই শতাব্দীতে আরো বেশি করে উঠে আসছেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শক্তিশালী কলমের অধিকারীরা। পশ্চিম মেদিনীপুর বা পুরুলিয়ার মানুষের জীবনকথা শুধু নলিনী বেরা বা সৈকত রক্ষিতের কলমে নয়, এঁদের পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উঠে আসছেন নবীন কথাসাহিত্যিকেরাও। বাংলাদেশের লেখকদের সম্পর্কে আমার বিস্তারিত জানাশোনা নেই বলে, তাঁদের আমি অপারগ হয়ে এই আলোচনার বাইরে রাখছি।
পশ্চিমবঙ্গের মূলধারার সাহিত্যিকদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, কিন্নর রায় বা সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় গত শতাব্দীর মতো এই শতাব্দীতেও পাঠকের দরবারে সুনামের সঙ্গে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। সাহিত্য জগতে এঁদের পরবর্তী সময়ে এসে যাওয়া তিলোত্তমা মজুমদার, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী বা বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়-রাও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন নিজেদের শক্তিমত্তায়। রয়েছেন এঁদের মুগ্ধ ভক্তসমাজ এবং অনুসরণকারী লেখককূল। বাংলা গল্প বা উপন্যাস পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ এঁরাই করে চলেছেন সবচেয়ে সার্থকতার সঙ্গে। এঁদের পাশাপাশি গবেষণা করে তথ্যসংগ্রহ করে আশ্চর্য দক্ষতায় আকর্ষণীয় কাহিনি রচনা করে এই শতাব্দীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন সন্মাত্রানন্দ এবং প্রীতম বসু।
বিভিন্ন স্থানে উৎসাহী মানুষজনের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে গল্প পাঠ ও গল্প চর্চার কেন্দ্র। চন্দননগর-চুঁচুড়া, বারাসাত-হাবড়া-গোবরডাঙা, বাঁকুড়ার সোনামুখী, বীরভূমের সিউড়ি থেকে শুরু করে সুদূর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি বা মাথাভাঙ্গা-দিনহাটা-কোচবিহার জুড়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। মানুষজন আসছেন এবং পড়া-শোনা চলছে শুধু নয়, এখান থেকে উঠে আসা লেখকরা লেখা পাঠাচ্ছেন কলকাতায় বা অন্যান্য জায়গায়। এঁদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন বিভিন্ন মহল। কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন যাপন একসময় যে বাংলা কথাসাহিত্যে বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছিল, এখন সেখানে পরিবর্তন আসছে। গত শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গ থেকে আমরা পেয়েছিলাম অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায় এবং বিপুল দাসের মতো কথাসাহিত্যিক। এবার নদীয়ার আনসারউদ্দিন-এর পাশাপাশি এই শতাব্দীতে এসে পেয়েছি, উত্তরবঙ্গের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, মেদিনীপুরের নরেশ জানা, মুর্শিদাবাদের সৌরভ হোসেন বা বাঁকুড়ার হামিরুদ্দিন মিদ্যাকে।
এই পর্যন্ত পড়ে অনেকেই ভাবতে পারেন মহিলা সাহিত্যিকদের কথা এই তালিকায় সেরকম ভাবে উল্লেখ করলাম না কেন? দূরবর্তী অঞ্চলের মাটির গন্ধমাখা সাহিত্যিক এখনও পর্যন্ত তুলনায় বেশ কম। সে পুরুষ হলেও কম, মহিলা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু শহরের মহিলারা বিচিত্র কর্ম উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়েছেন সারা ভারতে। এবং খুঁজে বের করেছেন সেখানকার মানুষের কষ্টকর জীবনের মূল কার্যকারণ। প্রথমেই মনে আসে অনিতা অগ্নিহোত্রী-র কথা। মহাশ্বেতা দেবীর পর অনালোচিত ভারতবর্ষের এতোবড় কথাকার বাংলা সাহিত্যে আর আসেননি। দীর্ঘ বিরতির পর আবার সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন প্রতিভা সরকার। মালদহের তৃপ্তি সান্ত্রা, আসানসোল- বোলপুর থেকে বেরিয়ে অহনা বিশ্বাস, চন্দননগরের সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতায় তৃষ্ণা বসাক নিঃসন্দেহে রূপ দিয়ে চলেছেন মেয়েদের নিজস্ব যন্ত্রণাকে। গত শতকের সামাজিক কথাসাহিত্যের প্রধান উপকরণ যদি হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগ বা দারিদ্র্য এবং মধ্যবিত্ত ভন্ডামি বা আত্মপ্রতারণা – তবে এই শতাব্দীর প্রধান উপকরণ নিশ্চয়ই হয়ে উঠতে পারে নারীর সমানাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। বিবাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতিমধ্যেই একটা বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সন্তান ও সম্পদ – যে দুটো জিনিসের ওপর নির্ভর করে বিবাহের ভিত্তি – সেটাই আস্তে আস্তে প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। নারীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাবলম্বন প্রাপ্তির জন্য পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে আর তাকে হচ্ছে না। এর প্রভাব সমাজের মতোই সরাসরি পড়ছে সাহিত্যের ওপরেও। একসময় কলকাতা ও কিছুটা ঢাকার মহিলাদের শিক্ষায় এগিয়ে আসা দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম – এখন প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের মেয়েরাও উঠে আসছে শিক্ষার হাত ধরে। ফলে একদিকে লেখিকা হিসেবে অপরদিকে কাহিনির নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা।
একেবারে নিচুতলার মানুষ, জাতিগত ভাবে অবহেলিত ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের বলিষ্ঠ সূচনা। অর্ধেক জীবন প্রবল ভাবে কায়িক পরিশ্রমের পরেও মনোরঞ্জন ব্যাপারি পরবর্তীতে কলমকে আশ্রয় করে ঠাঁই করে নিতে পেরেছেন পাঠকের মনোজগতে। বিগত শতাব্দীর সূচনা থেকেই বিদেশি সাহিত্যের প্রতি বঙ্গীয় লেখককূল ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। এই উৎসাহ ক্রমেই বিকশিত হয়েছে। ইংরেজি-ফরাসী-রুশ ও স্কান্ডেনেভিয়ান সাহিত্যের পাশাপাশি আফ্রিকান, জাপানি ও লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও অনুবাদ এখন অনেক সুদৃঢ় হয়েছে। বাঙালি লেখকরা এখন বাংলা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় লেখালেখি করে জগৎসভায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন – ঝুম্পা লাহিড়ি, অমিতাভ ঘোষ, অরুন্ধতী রায়, শোভা দে প্রমুখ গত শতাব্দীর শেষ থেকে এই শতাব্দীতেও তাঁদের লেখালেখির জগতে অটুট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন।
তবে সাধারণ ভাবেই একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের যে সমস্যা, সেটা চিরাচরিত খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের তো বটেই, এরসঙ্গে শিক্ষিত মানুষের আরো অনেক সমস্যার কথাও উঠে আসছে আজকের সাহিত্যে। বর্তমান যুগের অবক্ষয়, দুর্নীতি, অবিচার, প্রভূত্বকামিতা ছাপিয়ে গেছে বিগত শতকের পরিচিত অপরাধসমূহকে। ফলে সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। যৌনতা ও ভায়োলেন্স হয়ে গেছে আজকের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান এক উপাদান। সাহিত্যের কাছেও শুধু সুন্দর আত্মমগ্নতার সুর নয়, মানুষ পাঠক হিসেবে পেতে চাইছে বাড়তি উত্তেজনা, খুন-জখম-হত্যা-রাজনৈতিক ভ্রষ্টতার এক ককটেল। হয়তো সেই কারণেই রহস্য কাহিনি, থ্রিলার বা অলৌকিক কাহিনি অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। লেখকরাও তৈরি রয়েছেন এইসব চাহিদার যোগান দিতে। অনেকেই বর্তমান সময়ের বাইরে ঐতিহাসিক বিভিন্ন অনুষঙ্গে তৈরি করছেন কাহিনির বাতাবরণ কেউ বা পুরাণের অজানা তথ্য ব্যবহার করছেন কাহিনিতে। কেউ বা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন ভবিষ্যতের দিকে। কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিও অনেক লেখা হচ্ছে এখন। শুধুমাত্র শিশু বা কিশোরদের জন্য নয়, বর্তমানে সাবালক পাঠকদের জন্য লেখা হচ্ছে পরিণত মনস্ক উত্তেজক কাহিনি।
সব যুগেই এমন কিছু সাহিত্যিক থাকেন, যাঁরা নিজেদের জীবৎকালে সেরকম ভাবে সম্বর্ধনা পান না, কিন্তু পরবর্তীতে পাঠকের মুগ্ধতা লাভ করেন। তাই জনপ্রিয়তা কোনো যুগেই লেখকের মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা জগদীশ গুপ্ত এক-একটা ধরনের প্রবর্তন করেছিলেন, আজকের পড়ুয়া পাঠক ছাড়া ক’জন-ই বা তাঁদের মনে রেখেছেন? অথবা কমলকুমার মজুমদার?
মাত্র আড়াই দশক পার করা গেছে এই শতাব্দীর। এখন-ই এই তুলনা করা হয়তো খানিকটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। তবুও এইটুকু নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে – মুদ্রিত সাহিত্যের সঙ্গে অনলাইন সাহিত্য মিলিয়ে গত শতাব্দীর সঙ্গে লেখার পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোধহয় এখনকার লেখালেখি এরমধ্যেই যথেষ্ট ভালো জায়গায় পৌঁছে গেছে। ফেসবুক, ব্লগ, ওয়েবজিন মিলিয়ে লেখালেখির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন চারপাশের অনেকেই। করোনা এসে – যে কাজটা হতে প্রায় এক যুগ লেগে যেতে পারতো, মাত্র দুই বছরের মধ্যে এই অনলাইন সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন অবকাশ খুলে দিয়েছে। কিন্তু সম্ভবত এই কারণেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরিণত আর অযত্নলালিত রচনা। একেই বোধহয় বলা হয়েছিল – ‘অনির্দিষ্টের বোধপুঞ্জ’। এই প্রসঙ্গেই বোধহয় কবি বলেছিলেন – ‘এতো বেশি কথা বলো কেন?’ বলেছিলেন – ‘চুপ করো, শব্দহীন হও’।
বুদ্ধদেব বসুর একটা আক্ষেপ ছিল যে, প্রকাশনায় বাঙালি লেখক যথেষ্ট যত্নশীল নন। তাই তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন – ‘বুদ্ধিজীবী সেই লোক যিনি লেখেন কিন্তু প্রুফ দেখেন না’। ফলে, একদিকে প্রচুর বৈদগ্ধ, কিন্তু অপরদিকে আলসেমির কারণে সেটা সঞ্চারিত না হতে পারার জন্য অপচয়। এই পরিস্থিতি এখনও আমরা এড়াতে পারছি না। আর একটা আক্ষেপ-ও রয়েই গেছে – বিভিন্ন দেশে লেখক ও প্রকাশকের মাঝখানে একজন সম্পাদক থাকেন। কোনো সংকলন তৈরি করতে গিয়ে শুধু নয়, একক লেখকের সৃষ্টিও সম্পাদিত হয় এবং বইটা তার বিভিন্ন খুঁটিনাটি দোষ-ত্রুটি কাটিয়ে ওঠে এঁর অবদানে। বাংলা ভাষায় এই সম্পাদনা বিষয় নিয়ে এখনও খুব বেশি চর্চা হয়েছে বলে মনে হয় না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই কখনো এই সম্পাদকের প্রয়োজন অনুভূত হবে। হয়তো সেটাই হবে এই শতকের লেখালেখির জগতে সবচেয়ে বড় একটা মোড় ফেরার কাহিনি।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন