মিথচর্চার অপরিহার্যতা ও মুসলিম লেখকদের অসুবিধা
মোজাফ্ফর হোসেন
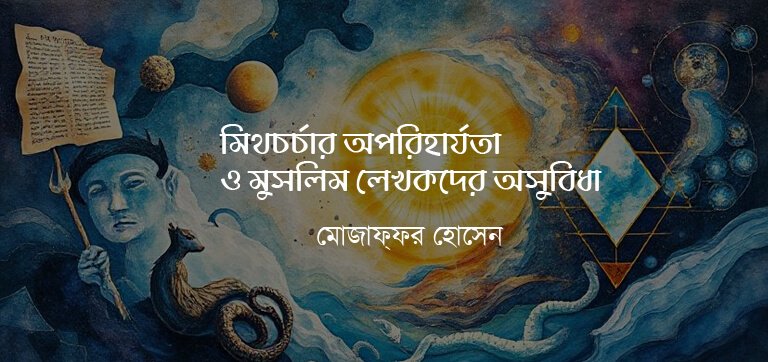
মিথ সাহিত্যের শক্তিশালী উপাদান। লেখকরা আধুনিক ও সমকালীন অনেক ঘটনা মিথের আশ্রয়ে তুলে ধরেন, এতে শিল্পের সৌকর্য-মাধুর্য যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি যে বক্তব্য সরাসরি প্রকাশ করা যায় না তার জন্য একটা ‘আড়াল’ তৈরি হয়। এটাকে আমি ‘রাজনৈতিক ঢাল’ হিসেবে আমি দেখি। এই কারণে মিথের বিনির্মাণ আধুনিক সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। উত্তরাধুনিক সাহিত্যের একটি লক্ষণ হিসেবেও এটিকে বিবেচনা করেছেন সাহিত্যের তাত্ত্বিকরা।
মিথ সাহিত্যে অনেকভাবে আসে। আমি মোটাদাগে তিনভাবে ভাগ করে বোঝার চেষ্টা করেছি — প্রথমত, সরাসরি পৌরাণিক কাহিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ বা প্রচলিত আছে সেভাবেই খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ অংশ কোনো আখ্যানে যুক্ত হয় সম্পূরক কাহিনি হিসেবে। মিথ এক্ষেত্রে এলিগরি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। মিথের আধুনিক ভাষ্য তৈরি হয় এভাবেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামায়ণকে বিনির্মাণ করে রচনা করেছেন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। রামকেন্দ্রিক ‘রামায়ণ’ চন্দ্রাবতীর সংস্করণে হয়ে গেছে সীতাক্রেন্দ্রিক সীতায়ন। অর্থাৎ, রামায়ণের নারীবাদী পাঠ তিনি তৈরি করেছেন। অতি সম্প্রতি প্যাট বারকার তাঁর The Silence of the Girls উপন্যাসে ‘ইলিয়াড’র নারীবাদী পাঠ তৈরি করেছেন। ইলিয়াডের নারী চরিত্ররা এখনো মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে। গ্রিক নাটক মিডিয়াতে আমরা মিডিয়াকে ভিলেন হিসেবে পড়েছি। কিন্তু এ বছর মিডিয়ার রিটেলিংয়ে রসি হিউলেট মিডিয়াকে নায়ক (গুণবাচক বিশেষ্য / বিশেষণের আমি লিঙ্গান্তর করতে চাই না) হিসেবে দেখিয়েছেন।
দ্বিতীয়ত, বিনির্মাণের মাধ্যমে: মিথের কাহিনি আখ্যানের প্রয়োজনমতো পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে নতুন আখ্যান তৈরি করা। অন্যভাবে বলতে পারি, লেখকের আধুনিক ভাষ্য প্রতিষ্ঠায় পৌরাণিক ভাষ্যের সাহায্য নেওয়া। ডেরেক ওয়ালকটের শ্রেষ্ঠ কাজ হলো এপিট পোয়েম Omeros। তিনি হোমার এবং ইলিয়াডের কিছু চরিত্র সেন্ট লুসিয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। এমনিতেই সেন্ট লুসিয়াকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেলেন নামে ডাকা হয়। কারণ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপটির হাতবদল ঘটেছে। ওয়ালকট চমৎকারভাবে হোমারীও হেলেন, অ্যাকিলেস, হেক্তরকে অতিসাধারণ চরিত্ররূপে তুলে ধরেছেন। ওয়ালকট ভাষাগত কাঠামোতে দান্তের ‘ডিভাইন কমেডি’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। গ্রিক কবি নিকোস কাজানজাকিসও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাটি লিখেছেন হোমারের ‘ওডেসি’ অবলম্বনে। The Odyssey: A Modern Sequel শীর্ষক এই কাব্য-আখ্যানটি অবশ্য নানাভাবে বিনির্মাণ করেছেন কাজানজাকিস।
তৃতীয়ত, লিটারারি অ্যালুশন (পরোক্ষ উল্লেখ) হিসেবে: সাহিত্যে মিথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এভাবেই। মিথ হয়ে ওঠে সাহিত্যের ইমেজ। যেমন: শামসুর রাহমান লিখেছেন: ‘হে নিশীথ, আজ আমি কিছুই করতে পারবো না। / আমার মগজে ফণীমনসার বন বেড়ে ওঠে, / দেখি আমি পড়ে আছি যুদ্ধবিধ্বস্ত পথে কী একাকী; / ভীষণ আহত আমি, নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি।’ এখানে ‘ফণীমনসা’ এবং ‘আফ্রোদিতি’ পৌরাণিক লিটারারি অ্যালুশন হিসেবে এসেছে। অ্যালিগরি ও অ্যালুশন হিসেবে মিথের চমৎকার ব্যবহার দেখি ভেন বেগামুদ্রের ‘বিষ্ণু ড্রিম’ উপন্যাসে। উপন্যাসের নাম শুনেও পাঠক কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন।
সাহিত্যের এই ‘কার্যকরী’ উপাদান হিসেবে মিথের প্রয়োগ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্য কিছুটা পিছিয়ে আছে বলে আমার ধারণা, এই ধারণা ভুলও হতে পারে। অনুমান করি, আমাদের প্রজন্মের লেখকদের ভেতর বাংলাদেশের মিথ নিয়ে একটা দ্বিধা তৈরি হয়েছে; যে সমস্যাটা কলকাতার বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে হয়নি। ভারতীয় মিথটা চিহ্নিত হচ্ছে ‘হিন্দুধর্মের মিথ’ হিসেবে। ফলে সচেতনভাবে অনেক বাংলাদেশি মুসলমান লেখক (সংখ্যাগুরু মুসলমান পাঠক—সেন্টিমেন্টের কথা ভেবে হলেও) এটা পরিহার করছেন। আবার মুসলমানদের যে মিথ, অর্থাৎ আরবীয় মিথ, সেটা ঠিক বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব মিথ না হওয়ার কারণে সহজাতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না। তারপরও, অনেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা থেকে আরব মিথকে নিজস্ব মিথ মনে করলেও ‘মিথ’ হিসেবে অ্যাড্রেস করতে পারছেন না। ফলে সাহিত্যে আরবীয় মিথের সৃষ্টিশীল ট্রিটমেন্ট বা বিনির্মাণ আমরা পাচ্ছি না। হাদিসগ্রন্থসমূহ বর্ণনাত্মক আখ্যানমূলক ধর্মগ্রন্থ হলেও এটি মহাভারত বা রামায়ণের মতো সৃজনশীল রচনা না। ফলে ইসলামের যে ঐতিহ্য বা লেজেন্ড সেটা অবিশ্বাস কিংবা বিনির্মাণের সুযোগ নেই। ধরুন, লুত (আ.)-এর সাদুমজাতি সমকামী পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মৃত সাগর / লোহিত সাগরের জন্ম হলো। এখন এই অলৌকিক কাহিনি নিয়ে যদি বাঙালি মুসলমান লিখতে চান, তবে তাকে হুবহু লিখতে হবে। এখানে বিনির্মাণের কোনো সুযোগ নেই। তাই ইসলামধর্মের চমকপ্রদ ঘটনা সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে বিবেচ্য হচ্ছে না। এই সমস্যা থেকেই হয়তো আমাদের তরুণ লেখকরা মিথ নিয়ে ব্যাপক অর্থে কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। হিন্দুধর্মে মিথ নিয়ে এই অসুবিধাটা কম। যে কারণে কবি চন্দ্রাবতী ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামায়ণকে বিনির্মাণ করতে পেরেছেন। বুদ্ধদেব বসু থেকে বিষ্ণু দে প্রত্যেকে ভারতীয় মিথকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমাদের লোকগান কবিগান বাউলগানে ভারতীয় মিথ দারুণভাবে এসেছে। কিন্তু মূলধারার সাহিত্যে কবি শামসুর রাহমানের মতো ধর্মীয় প্রথাবিরোধী কবিও যতটা না গ্রিক মিথের ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়, ততটা ভারতীয় মিথ করেননি। গ্রিক মিথ ব্যবহার করে কেউ বাংলাদেশি মুসলমান পাঠকের অদৃশ্য প্রশ্নের মুখোমুখি হন না। কিন্তু ইসলামের কোনো ঘটনাকে মিথ হিসেবে ব্যবহার ও বিনির্মাণ মুসলমান পাঠকরা মানতে চাইবেন না, অন্যদিকে ভারতীয় মিথের প্রসঙ্গ অতিমাত্রায় চলে এলে ‘হিন্দুয়ানি’ সাহিত্য হিসেবে তকমা পাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। অর্থাৎ মহাভারত, রামায়ণ, মহাপুরাণ / আঠারো পুরাণ এবং বেহুলা লখিন্দরের মতো শতশত ভারতবর্ষীয় লোকপুরাণ, উপকথা বাংলাদেশের সাহিত্যে নতুনভাবে বিনির্মাণের মাধ্যমে অথবা লিটারারি অ্যালুউশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অন্তত ষাটের দশকের চেয়ে এখন সেটা কমে গেছে। ভারতীয় পুরাণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন সম্ভবত সেলিম আল দীন তাঁর নাট্য-আখ্যানে।
বাংলাদেশে মিথ ব্যবহারের পেছনে একটা ধর্মীয় সামাজিক রাজনীতি আছে। কীভাবে তার একটা উদাহরণ দিই: ভারতীয় পুরাণে বজ্রের / স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র, গ্রিক পুরাণে বজ্রের দেবতা জিউস, স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাণে থর, এবং ইসলামধর্মে (পুরাণ বলা যাচ্ছে না) বজ্রপাত ও বৃষ্টির দায়িত্বে আছেন ফেরেশতা মিকাইল।
দেখা যাবে, ভারতীয় বাংলা সাহিত্যে যেভাবে পৌরাণিক দেবতা ইন্দ্র, ইউরোপীয় সাহিত্যে-সিনেমায় গ্রিক পৌরাণিক দেবতা জিউস ও স্ক্যান্ডিনেভীয় পৌরাণিক দেবতা থর ব্যবহৃত হয়েছে সেভাবে মুসলমানদের সাহিত্যের মিকাইল আসেনি, আসবে না, কারণ হজরত মিকাইল বিশ্বাসের জায়গায় প্রথিত, তাকে বিনির্মাণের সুযোগ নেই। আবার বাংলাদেশের সাহিত্যে ইন্দ্র বহুলভাবে আসছে না কারণ ইন্দ্রকে মুসলমান পাঠক (এবং অনেকাংশে লেখকরাও) হিন্দুধর্মীয় বিষয় বলে মনে করছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের রাজনীতিকরণ আরো তীব্র হওয়ার কারণে ইন্দ্রের চেয়ে জিউসের নাম নেওয়া ‘নিরাপদ’। কিন্তু গ্রিক মিথ যেহেতু আমাদের নিজেদের বা ভারতবর্ষীয় মিথ না, তাই সেটি ব্যবহার ও বোধগম্যতায় আমাদের লেখক-পাঠকদের সীমাবদ্ধতা খুবই স্বাভাবিক।
ফলে বিশ্বের শিল্পসাহিত্যে আঞ্চলিক মিথ যখন বৈশ্বিক হচ্ছে তখন বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য হতে চলেছে মিথবর্জিত। এতে আমাদের সাহিত্য বৈচিত্র্য হারাচ্ছে, বহুস্বর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সাহিত্যের অন্যতম কাজ যেখানে বহু বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় করা, সে দায়িত্ব থেকেও সরে আসছে। শিল্পসাহিত্যের সমন্বয়বাদী চেতনা সমাজেও প্রভাব ফেলে, তাই অসাম্প্রদায়িক বহুত্ববাদী সমাজগঠনে শিল্পসাহিত্যে মিথমুখী হওয়ার কোনো বিকল্প আমি দেখি না।
এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের লেখকদের মিথচর্চায় অসুবিধাটা কোথায়? আদৌ কোনো অসুবিধা আছে কি না? এক পরহেজগার ভাই আমাকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন: ‘হিন্দু লেখক-শিল্পীরা তাঁদের নাটকে-সাহিত্যে-সিনেমায় হিন্দুধর্মীয় বিষয়-আশয়, আচার, রীতিনীতি যেভাবে তুলে ধরেন বাংলাদেশের মুসলিম লেখকরা তাদের শিল্পসাহিত্যে ইসলাম নিয়ে সেটা করেন না। উল্টো ইসলামধর্মের রিচুয়ালগুলো সচেতনভাবে এড়িয়ে যান। জি বাংলার অধিকাংশ নাটকের কোনো পর্বই পূজা-অর্চনা ছাড়া কল্পনা করা যায় না; অথচ বাংলাদেশের নাটকে পাত্রপাত্রীদের জায়নামাজে বসতে দেখা যায় না। একটা বছরমেয়াদি উপন্যাসে রোজা, ঈদ উদ্যাপন, মিলাদ, শবেবরাত ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকে না।’
প্রসঙ্গটা গুরুত্বপূর্ণ বটে। আমার মনে হলো, বিষয়টি নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। এড়িয়ে যাওয়া কোনো সমাধান নয়। আমি তাঁকে বললাম: এটা করলে আপনি মনে করছেন ইসলামধর্মের সেবা হবে। কিন্তু আপনিই আবার এই কারণে পঁ্যাচে ফেলে লেখক-শিল্পীকে ফাঁসিয়ে দিতে পারেন। নিষিদ্ধের দাবি তুলে মামলা ঠুকে দিতে পারেন নাটক কিংবা সিনেমাটির বিরুদ্ধে।
‘কীভাবে? আপনার মাথা ঠিক আছে তো?’ তিনি তখন বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন।
ধরুন, কারো উপন্যাসের এক চরিত্র খুব ভালোমতো ওজু করে মসজিদে গেল। এতে নামাজ পড়ার বিষয়টি প্রমোট করা হলো ভেবে আপনি ঐ লেখকের প্রতি খুশি হলেন। এবার নামাজ পড়ে মসজিদের বাইরে এসে সেই লোকই যখন একজনকে গোপনে বলবে, ‘কৌশলে না হলে জোর করে জমিটার দখল নিয়ে নাও’, তখনই আপনার ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। ‘সদ্য নামাজ শেষ করা এক মুসল্লিকে দখলদার হিসেবে দেখিয়ে ইসলামের অবমাননা করা হচ্ছে’ মর্মে আপনি লেখকের বিরুদ্ধে মামলাও ঠুকে দিতে পারেন। কিংবা কোনো উপন্যাসে হুজুর হয়তো খুতবায় বলছেন: ‘নবীজী বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে কিংবা তাদের ওপর জুলুম করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি মুহাম্মদ (সা.) ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে লড়াই করব।’ কোনো দর্শক তখন এটাকে জাল হাদিস প্রমাণ করে বইটি নিষিদ্ধের দাবি তুলতে পারেন। বা নায়িকাকে নামাজ পড়া অবস্থায় দেখালে কোনো দর্শক মনে করতে পারেন নামাজের মতো সিরিয়াস বিষয়টি হালকা হয়ে গেল। হয়তো মিলাদের দৃশ্য থাকল, কেউ বললেন মিলাদ সহি আকিদা না। মাজারের দৃশ্য থাকল, কেউ অভিযোগ তুলল শিরক করাকে প্রমোট করা হচ্ছে।
মুসলমানদের মধ্যেই এখন এত বিভাজন ও বিরোধ যে এই কারণে বর্তমানে শিল্পসাহিত্যসংগীতে ইসলামধর্মীয় আচার-রীতিনীতি-জীবনাচরণ নিয়ে আসা ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তিনি এবার প্রশ্ন করলেন: ‘তাহলে সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, সংগীতে হিন্দুধর্ম কীভাবে আসছে? ওরা তো গানবাজনার মধ্য দিয়েও ওদের ধর্মটার প্রচার করে দিচ্ছে?’
এক্ষেত্রে আমার আশঙ্কার জায়গাটা হলো: ধরুন কোনো মুসলিম শিল্পী দরদ দিয়ে শেষ নবীর ভাস্কর্য তৈরি করল! আপনি সেটাকে নবীর (ইসলামধর্মের) প্রচার হিসেবে দেখে তাঁকে বাহবা দেবেন নাকি ইসলামধর্মের বিকৃতি অভিধায় শিল্পীর ফাঁসি দাবি করবেন? হিন্দি সিনেমায় ভগবান দেবতাদের চরিত্রদের দেখানো হয়, আপনি মনে করছেন হিন্দুধর্মের প্রমোশন হচ্ছে এতে, বিপরীতে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো সিনেমার চরিত্র করা হলে, চরিত্রায়ন যত ইতিবাচকই হোক না কেনো, পরিচালক জীবন নিয়ে বাঁচতে পারবেন? রামায়ণের বিনির্মাণ করলেন মাইকেল বা চন্দ্রবতী। তাদের আমরা সাহিত্যে উঁচু আসনে বসাচ্ছি। হজরত ইবরাহিম ও হজরত ইসমাইল (আ)-কে কেন্দ্র করে কোরবানির যে ঘটনা, সেটার বিনির্মাণ কোনো মুসলমান লেখক করলে সেটাকে কি ইসলামি সংস্কৃতিচর্চা হিসেবে গণ্য করা হবে? ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’কে মিথ হিসেবে মানতে হিন্দুদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বিকৃত পাপাচারে ‘সাদুম’ জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং লোহিত সাগর সৃষ্টি হওয়াকে মিথ বললে কি আমরা মানব? একটা ধর্মে যদি মিথ না থাকে, থাকলেও বলা না যায়, তাহলে সেই ধর্মের লেখকরা কোন ধর্মীয় সংস্কৃতি নিয়ে লিখবেন, কী বিনির্মাণ করবেন? পুনঃসৃষ্টি ছাড়া কি কালজয়ী সাহিত্য বা শিল্প হয়?
কখনো কখনো ধর্ম আর সংস্কৃতি আলাদা বিষয়। কখনো কখনো সংস্কৃতিটাই ধর্ম। হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি বা আচারপ্রধান। যেমন: ভাইফোঁটা, রাখীবন্ধনের মতো অনেক ধর্মাচার সনাতন ধর্মের মূল অংশ না। হিন্দুধর্ম সংস্কৃতিপ্রধান হওয়াতে সাহিত্যের সংগীতের চিত্রকলার সুবিধা হয়। হিন্দু-মৌলবাদীরা কিছু করতে পারে না। এমনকি ভগবানকে ইচ্ছামতো টানা যায়, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা যায়। হিন্দি অনেক সিনেমায় আমরা দেখি ভগবান নিজেই চরিত্র হয়ে আসছেন, অনেক সময় আবার তাঁকে নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি হচ্ছে। গোপাল ভাঁড়ের অধিকাংশ রঙ্গতামাশায় দেখা যাবে ভগবানকে নিয়ে রঙ্গতামাশা করা হচ্ছে। আল্লাহ বা নবী-রাসূলের নামে কোনো শিল্পী মশকরা করলে আমরা মেনে নেব? কাব্যশাস্ত্রে যে নয় প্রকার রস আছে তার মধ্যে হাস্যরস বা কৌতুকরস খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা। এর মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক বিষয়ও আছে। এটা ছাড়া সাহিত্য হবে কী করে?
ইসলামধর্মে ওহাবি বা কট্টরপন্থিরা ধর্মীয় সংস্কৃতিকে কীভাবে ছেঁটে ফেলছে তার একটা নমুনা দিচ্ছি: একবার আমি এক ছোটোগল্পে মিলাদ দেওয়ার কথা বললাম, আমার পরিচিত আহলে হাদিসের আমির বললেন, এটা শরিয়তে নেই। একবার আমি মুসলমানদের মাজার সংস্কৃতি নিয়ে লিখলাম, বললেন এটা বেদাত, আমার পাপ হবে। এমনকি সবেবরাতে হালুয়া-রুটি খাওয়া গর্হিত কাজ বলে আমার গল্পে পরিবর্তনের দাবি ওঠে। সুফিদের নিয়ে লিখেও শুনতে হয়েছে আমি শিরক করাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। মাজার সংস্কৃতির পক্ষে তো লেখাই যাবে না। শুধু নামাজ পড়া, রোজা আর কোরবানি দেওয়া দিয়ে সাহিত্য হয় না। তাছাড়া এখানেও সমস্যা আছে, আমি একটা গল্পে ১২ তাকবিরের নামাজের কথা লিখলাম, হানাফিরা ক্ষেপে গেলেন। তারা ৬ তকবিরে ঈদের নামাজ পড়েন। আবার মোনাজাতের কথা লিখলে জামাতুল মুসলিমিন আপত্তি করলেন, সহি হাদিসে নাকি মোনাজাত নামাজের অংশ না। সিনেমায় বিয়েতে ‘কবুল’ বলা যাবে না বলেও আদালতে সম্প্রতি রিট করা হয়েছে।
হিন্দুধর্মে যেখানে সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, ভাস্কর্যকলা ধর্মাচারেরই অংশ, সেখানে ইসলামধর্মে এগুলোকে নিরুৎসাহিত বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
তাছাড়া, শিল্প ‘হোলি টেক্সট’ অনুকরণ করে না, অনুরসণ করে মানুষের চর্চা-আচার-আচরণ। আরো সহজ করে বললে, মানুষ যা করে সেটাই সাহিত্যের বিষয়। পবিত্রগ্রন্থে কী লেখা আছে সেটা না। এজন্য একজন ব্যক্তি মুসলমানের স্ববিরোধিতা তুলে ধরা মানে ইসলামকে আঘাত করা না। কোনো বই বা মন্তব্য পড়ে ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগতেই পারে। কিন্তু ব্যক্তির আবেগ-অনূভুতি আর ধর্মের নিজস্ব সত্তা এক বিষয় না। আমি লক্ষ করে দেখেছি, কোনো কোনো ওয়াজি দিনরাত ভুলভাল ওয়াজ করলে, কোরান-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিলে কোনো মুসলমানের ধর্মানুভূতিকে আঘাত লাগে না। কিন্তু সেই ওয়াজির ভুলটা ধরিয়ে দিলে আবার ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে! কাজেই আমাদের লেখকদের সচেতনভাবে এখন অনেক কিছু এড়িয়ে যেতে হচ্ছে।
উদার সংস্কৃতি ও চিন্তাশীল সমাজ ছাড়া আন্তঃধর্মীয় বাহাস বা ‘ইন্টারফেইথ ডায়ালগ’ সম্ভব না, বিশেষ করে মুসলিম সমাজে, এখন অবশ্য ভারতীয় হিন্দুসমাজেও সম্ভব না। সেখানেও অনুরূপ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত বলি, সত্যের প্রতি মূর্খের অন্ধত্ব সেই সত্যকে ডোবানোর জন্য যথেষ্ট। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বকে তার অন্ধ ভক্তরাই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন বেশি — কে কাকে বোঝাবে!
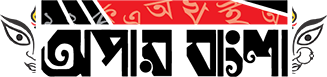

ভালো লাগলো।নতুন কিছু পেলাম।সাহসি লেখা।