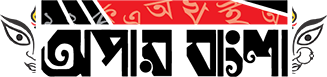দেয়ালঘড়ি কামরুল
হাসান বাদল

শুরু হলো অনেকটা ধীর লয়ে।
‘মম চিত্তে নিতি নৃত্যে,
কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ’-
মনে হলো এ গানের সুর, লয়, তালে বৃষ্টি পড়ছে আজ। ঘুম ভেঙেছে বেশ আগে। বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল জামশেদ। এত সকালে বিছানা ছেড়ে লাভ কী? এরই মধ্যে এলো বৃষ্টি। শুয়ে শুয়ে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দকে সে সুর, মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা ওর পুরনো অভ্যাস। যখনই বৃষ্টি পড়বে তার সঙ্গে একটি সুরকে মেলাবার চেষ্টা করে সে। রেল লাইনের পাশে তাদের বাড়িটি। অনতিদূরে একটি স্টেশন। ছোটবেলায় ট্রেন যাওয়ার সময় তার তালের সঙ্গে সুর মেলাবার চেষ্টা করতো সে। প্রতিদিনের প্রভাত তার জন্য একটি বিশেষ ক্ষণ হিসেবে আসে। আর সে ক্ষণকে সার্থক করে তোলে রবি ঠাকুরের কোনো না কোনো গান। আজও মনে মনে মেলাচ্ছে –
‘তারই সঙ্গে কী মৃদঙ্গে
সদা বাজে তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।’
মেলাতে মেলাতে এবার নিজেই যেন উপলব্ধি করে-
‘মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।’
সে বহুদিন আগে প্রথম যে বালিকা তার চিত্তকে নাড়া দিয়েছিল আজ বৃষ্টিমুখর প্রভাতে পুরনো টিনের বাড়িতে একাকী শুয়ে হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল। সলজ্জ বিহ্বল চোখ, যেন নজরুলের সেই, ‘আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল করে দেখা অনুক্ষণ’।
জামশেদ আরেকটি বালিশ বুকে টেনে নিয়ে পাশ ফেরে। নিজেকে নিজে শোনায়-
‘হাসি কান্না, হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দে তালে তালে।’
একসময় বৃষ্টি এই তালে থাকে না। ওস্তাদ জাকির হোসাইনের তবলার দ্রুত লহরীর মতো অস্থির আর দ্রুত লয়ে পড়তে থাকে। মনে হয় টিন ছিদ্র হয়ে ফোঁটাগুলো বিছানায় এসে পড়বে।
ভেসে ওঠা মুখচ্ছবিটা চোখ থেকে সরে না। ফুফুর বাড়ি গিয়েছিল একদিন। সে তখন নাইন কি টেনের ছাত্র। ফুফুর শ্বশুরবাড়ি ফেনী থেকে অনেক লোকজন এসেছিল সেবার। উপলক্ষটি মনে নেই। অনেক অনেক আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ের মধ্যে জামশেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এক কিশোরী। কিশোরীরও চোখ পড়েছিল জামশেদের ওপর। নইলে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ভাঁজে এক পলকের দেখায় মেয়েটি কী করে বলল, ‘রসিক চোখ তোমার!’ জামশেদের ধারণা এটাই তার প্রথম প্রেম। মেয়েটির সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। তবে সে মুখ, সে স্মৃতি জামশেদকে আজ বুঁদ করে রাখে অনেকক্ষণ। যখন সে বাস্তবে ফিরে আসে তখন অনুভব করে অঝোর ধারাপাত বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। টিনের চালে নুয়ে পড়া গাছের পাতা থেকে একটি একটি ফোটা পড়ছে চালে। যেন তুমুল লহরির পর শুধু সেতারের একটি তারে অতি ধীরে একটি আঙুলের স্পর্শে বাজছে টুং টাং কিংবা মৃদু লয়ে পিয়ানোতে কেউ আওয়াজ তুলছে ।
মোবাইলে সময় দেখল সে। সাড়ে আটটা বাজে। জামশেদ আড়মোড়া ভাঙে। নিজেকে বলে, না বাবা উঠতে হবে। নয়টার পর হলে তেলের পরোটা পাবো না।
এ সময় টিকটিকি ডেকে ওঠে। জামশেদ বলে, চুপ কর, যখন-তখন! টিকিটিকির ডাকা শেষ নাকি জামশেদের ধমকে চুপ থাকে তা বোঝা যায় না।
এ ঘরের টিকটিকি, আরশোলা, ইঁদুর এদের সঙ্গে সদ্ভাব আছে তার। এরা জামশেদের খুব অনুগত। এদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ করে সে। জামশেদ মনে করে মানুষের চেয়ে আলাপচারিতার জন্য ওরা অনেক নিরাপদ। তর্ক করে না। মতের সঙ্গে না মিললে মারমুখী হয়ে ওঠে না কখনো। এ বাড়িতে তাই নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না তার। ঘুম না এলে এদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে সময় কাটায়।
বাপের বানানো বাংলো টাইপের বাড়িটি অন্তত সত্তর বছরের পুরনো। এত বড় বাড়িটি একপ্রকার পরিত্যক্ত হয়ে আছে। তিন ভাই আর দু বোনের মধ্যে জামশেদই শুধু দেশে আছে। বাদবাকিরা ইউরোপ আর আমেরিকায় সেটল হয়ে গেছে। বাবা বেঁচে থাকতেই বড় দু’ভাই আমেরিকা গেল পড়তে। আর ফিরল না। বাবা-মা মারা যাওয়ার পরেও না। বোন দুটি তাদের স্বামীর সঙ্গে থাকে। একজন ডেনমার্কে। অন্যজন জার্মানে। ওরাও দেশে আসে না। শেষবার এসেছিল মায়ের মৃত্যুর পর তা-ও দশ বছরের কম নয়।
পরিবারের সবার ছোট জামশেদ কলেজে ঢুকে গড়ে তুলেছিল একটি ব্যান্ডদল। পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে ফেলল। অ্যালবাম বের হলো দুটো। বেশ সুনামও ছড়িয়ে পড়ল তাদের। তারপর দেখা দিল নানা জটিলতা। ব্যক্তিত্বের সংঘাত, অবিশ্বাস। ভেঙে গেল দল।
ততদিন মাস্টার্স শেষ করেছে সে। বিদেশে যাওয়ার তাড়া দিচ্ছিল মা-বাবা। কিন্তু গেল না। বড় দুই ভাইয়ের স্বার্থপরতা দেখে জামশেদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাবা-মাকে ছেড়ে সে যাবে না বাইরে।
মা মারা গেলেন আগে। তারপর বাবা বেঁচে ছিলেন আরও বছর পাঁচেকের মতো। তবে তাঁর শেষের দিনগুলো কেটেছে রোগে-শোকে। জামশেদ পাশে ছিল। কোন ফাঁকে বয়স চল্লিশ পেড়িয়ে গেছে তা বুঝতে বুঝতে বিয়ের আগ্রহটাও আর রইল না। প্রেমও এসেছিল কয়েকবার। শেষ পর্যন্ত একটাও টেকেনি। অবশ্য সে জন্য জামশেদ প্রেমিকাদের দোষ দেয় না। শেষ পর্যন্ত একজন বেকার ও উদ্দেশ্যহীন মানুষের ওপর ভরসা না করারই কথা।
এখন বাড়িতে থাকে একা। এ বাড়ি কি এ অবস্থায় বিক্রি করে টাকা ভাগাভাগি করা হবে নাকি ডেভেলপার দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট করে বিক্রি করবে তা নিয়ে ভাইবোনদের দ্বন্দ্বে বাড়ি এভাবেই পড়ে আছে। বিদেশে সেটেল হলেও বাবার সম্পত্তির এক ইঞ্চি জায়গাও কেউ কাউকে ছাড় দেওয়ার নয়। ভাইবোনদের এসব ক্যাচালের মধ্যে জামশেদ নেই। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার ভাগের অংশ দান করে দেবে কোনো বৃদ্ধাশ্রমকে। সম্পত্তির ভাগে একটি দোকান পেয়েছিল। তার ভাড়ার টাকায় টেনেটুনে চলে সে।
একসময় রাজনীতিতেও সক্রিয় হয়েছিল। একটি বাম সংগঠনের পেছনে অনেক মেধা ও শ্রম ব্যয় করার পর বুঝতে পেরেছে ওদের দিয়ে কিছু হবে না। কথা আর কাজে কোনো মিল নেই ওদের।
সম্প্রতি বসবার ঘরে একটা দেয়ালঘড়ি টাঙিয়েছে সে। সেটার বয়সও সত্তর-আশির কম হবে না। তার বাবার আমলের। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই সে ঘড়িটা দেখছে। ছোটবেলায় খুব অবাক চোখে দেখত একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা ঘড়িটায় চাবি দিতেন। আবলুশ কাঠের মতো কালো কুচকুচে ঘড়িটি অনেক লম্বা। ছ কোণা ডায়ালবক্সের নিচে অন্তত দেড় ফুট লম্বা পেন্ডুলামটা দুলতো টিক টিক টিক টিক শব্দ করে। ছোটবেলায় ঘড়িটিকে কখনো বন্ধ অবস্থায় দেখেনি জামশেদ। ডায়ালবক্সের কাচে একটা সাদা কাগজের স্টিকারে লেখা ছিল সোমবার। প্রতি সোমবার বাবা নিয়মিত ঘড়িটিতে চাবি দিতেন। চাবি দেওয়ার পর তা পেন্ডুলাম বক্সে রেখে ফ্রেমের ওপর আয়না লাগানো দরজাটি বন্ধ করতেন খুব সযত্নে। প্রতি সোমবার চাবি দিতেন বলে বোধহয় কাচের ওপর সাদা কাগজে সোমবার লেখা একটি স্টিকার সেঁটে দিয়েছিলেন।
ছোটবেলায় তার খুব শখ ছিল বড় হলে সেও টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ঘড়িতে চাবি দেবে। কিন্তু বড় হওয়ার সময়টা এত দ্রুত কেটে গেল যে ঘড়িটা কোথায় আছে সে কথাও মনে ছিল না। পুরনো মালপত্রে ঠাসা একটা রুমে কী খুঁজতে গিয়ে ঘড়িটা খুঁজে পায় সে চার-পাঁচদিন আগে। প্রায় সাড়ে চার ফিট লম্বা ঘড়িটা কিছুটা বাবার স্মৃতি কিছুটা এনটিক্স ভেবে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়। ঘড়ির তিনটি কাঁটাসহ সবকিছুই ঠিক আছে শুধু সংখ্যাগুলোর কোনো চিহ্ন নেই।
মোবাইলে আবার সময় দেখল সে। নয়টা বেজে গেছে। এখন ডুবো তেলে ভাজা পরোটা পাওয়া যাবে না। নয়টার পর বানানো হয় স্যাঁকা পরটা। তেল ছাড়া প্রায়। জামশেদের সকালে নাস্তার মেনু হলো, ঘন দুধের চায়ে ডুবিয়ে তেলেভাজা পরোটা। জামশেদ মনে করে এর স্বাদ যে পায়নি সে অসাধারণ একটি খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখন ওর মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। আজও সেই পরোটা পাবে না বলে চায়ের দোকানদারদের বাবা-মা তুলে গালি দিতে দিতে চা আনার অ্যালুমিনিয়ামের মগটা খুঁজে নিল। ফ্লাস্কটা ভেঙে গেছে মাসখানেক হলো। সময়মতো মনে পড়ে না বলে কেনা হচ্ছে না। ফ্লাস্কের বিকল্প হিসেবে মগে দু কাপ চা আর পুরনো নিউজপেপারে মুড়িয়ে দেওয়া দুটো পরোটা নিয়ে আসে। আর তাই হলো তার ব্রেকফাস্ট। যদিও চা আনতে আনতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঘরে তার রান্নাবান্না হয় না আজকাল। একসময় একটি বুয়া ছিল। দিনের বেলা এসে রান্নাবান্না করে যেত। দুপুরের অবশিষ্ট খাবার দিয়ে রাতের বেলা তার অনায়াসে চলে যেত।
শার্ট গায়ে দিয়ে মগ হাতে দরজা খুলেই সে ভূত দেখার মতো চমকে গেল। দরজার সামনেই একটি নতুন ফ্লাস্ক, পাশে একটি টিফিনবক্স। তার ওপর পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া ছোট একটি কাগজ।
কৌতূহল ও ভয় মিশ্রিত এক অনুভূতির সঙ্গে সবকিছু নিয়ে ঘরে এলো সে। ডাইনিং টেবিলে ফ্লাস্ক-চা রেখে কাগজটি দ্রুত খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে। বেশি কিছু লেখা নেই তাতে। শুধু লিখেছে, ‘রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফ্লাস্ক আর টিফিনবক্সটি দরজার বাইরে রেখো।’
সারা শরীর বেয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় জামশেদের। লেখাটি খুব চেনা চেনা মনে হয়। সে চিঠিটি নিয়ে প্রায় দৌড়ে আসে বসার ঘরে ঘড়ির সামনে। ঘড়ির ঢাকনায় কাচের ওপর লেখা ‘সোমবার’ স্টিকারটি খুঁজতে থাকে সে। পায় না। তবে ছিঁড়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া স্টিকারটির দাগ দেখতে পেল কাচের ওপর। এবং সেটা দেখতে গিয়ে জামশেদ দেখল, ঘড়িটা চলছে, পেন্ডুলামটি দুলছে, টিক টিক টিক শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। জামশেদ ভাবল এই একটু আগে যে টিকটিকি ডেকেছিল সেটি কি সত্যি সত্যি টিকটিকির শব্দ ছিল?
ঘড়িটি তো চলার কথা না। চলছে কীভাবে? এটার চাবি এলো কোথা থেকে? চাবির কথা মনে হতেই সে ভাবল, আজ কি সোমবার? সে মোবাইলের দিকে ছুটে গেল। সেখানে দেখল ‘মানডে’ সোমবার।
এমন সময় ট্রেনের হুইশেলের শব্দ পায় সে। দেখে স্টেশনের ডানদিকের হোম সিগনাল ডাউন হয়েছে। সে সিগনাল পেরিয়ে আরও দূরে দখিনমুখী ইঞ্জিনটি দেখা যায়। এতক্ষণ ঝিমিয়ে থাকা স্টেশনটি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে। লাল কুর্তাপরা রেলের কুলিরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। হকারেরা তৎপর হয়ে উঠেছে। অনেক যাত্রী খামোখা তাড়াহুড়ো করছে ট্রেন যেন ফেল না হয়। আর সে ব্যস্ততার মধ্যে একটি কিশোর একাকী একটি বেঞ্চে বসে ছড়া কাটে-
ট্রেন চলে ঝিক ঝিক
ঘড়ি চলে টিক টিক।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন