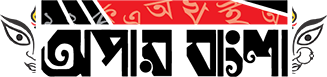রেথিয়ানা বোটানিকা বা গজদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার
সুমন ভট্টাচার্য

অদৃশ্য অশ্রুকণাগুলি ক্রমশ ঘন হতে হতে প্রস্তরবৎ। বিবর্ণ রক্তাক্ত আর কর্তনযন্ত্রনার নৈঃশব্দ্য ঘন কুয়াশা – তা বীভৎস শ্বাসরোধী চারপাশ নীরবতার ভারে অসহনীয়— অতঃপর
১
গৃহপ্রপাত
একেবারে হুরমুড় করে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মাটিতে যেন ঝরে পড়লো একটা আস্ত দশতলা বাড়ি। যারা কাছাকাছি ছিল চেষ্টা করছে বুঝবার। তারপর আরো তিনটি-চারটে-পাঁচটা বাড়িগুলো যেন থেবড়ে বসে পড়ছে বা মিশে যাচ্ছে মাটিতে!
জনকয়েক লোক বার বার চোখ রগড়ে কচলে বুঝবার চেষ্টা করছিল- ঠিক দেখছে তো! একটি মেয়ে তার বালক বন্ধুকে বললে, ‘দ্যাখো-লুক-লুক এই বাড়িগুলো কেমন যেন নাথিং হয়ে যাচ্ছে। হোয়াই-হোয়াই-’
‘কী জানি মনে হচ্ছে কোনো সুপার-রিয়ালিটি ম্যাজিক শো – দেখি হোয়াটসঅ্যাপ বা ইউটিউবে কোনো-’
‘হ্যাঁ-হ্যাঁ দ্যাখো না – দ্যাখো না। ছিল চার-চারটে মাল্টিকোরিড হয়ে গেল গ্রাউন্ড লেভেল কাউডাংগ কেক – হাউ সুইট!’
পরপর চার দিন। কলকাতা আর আশেপাশে এরকম বাড়ি বসে যাওয়ার খবর। আশঙ্কা-যন্ত্রণা-মৃত্যু কমবেশি সকলেই সন্ত্রস্ত। খবরের কাগজেও আতঙ্কের সংক্রমণ। শুধুই তো অনুমান। প্রথম দফায়, মাল মশলার গোলমাল। যা হয় হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দফায়, অত্যাশ্চর্য ভূমিকম্প। যার হদিস পায় না রিখটার স্কেল! সুতরাং তৃতীয় দফায়, এই প্রথম সাংবাদিকেরা বিপুল ঐক্যমত্যে লিখতে থাকলেন এ এক ভয়ংকর ওয়র অফ্ দ্য ওয়ার্ল্ডস। এইচ.জি. ওয়েলসের সেই কল্পনাই আজ সত্য! কলকাতায় ভিন্ন গ্রহের প্রাণীদের নৃশংস আক্রমণ! অথবা গ্রহান্তরের মেঘনাদের কবলে কলকাতা— এই মেঘনাদ বধের উপায় উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত।
বাঁকুড়া বাজারে সকালবেলায় ভায়রাভাই জ্যোতিষ রক্ষিতের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন, পুরুলিয়া থেকে আসা অধিকারচন্দ্র চাকলাদার। ওই গৃহপ্রপাত নিয়ে কথা তোলা মাত্র জ্যোতিষ তেড়ে এলেন ‘তুমি অত বকচো কী! তুমি ওসব বুঝবে না বটে! ওসব নরম মাটি, এদিকে গঙ্গা, ওদিকে বাদাবন, রিভার বেড, সব মাটি লেদিয়ে গিয়েছে হ্যা! এ তো আর আমাদের পাথরে কাঁকুরে পোক্ত জমি নয়—’
-‘কিন্তু কাগজে যে লিখচে—’
-‘কিছু জানে না ক্রিংকটতারণ বিচক্ষণ জ্যোতিষ মতে রক্ষা পাওয়ার উপায়, ওঃ অমন চোক গোল করে তাকানোর কিছু নেই, তুমি চা দিয়ে কলা খেয়ে তো—’
কথা শেষ হতে পেলো না। সামনের তিনতলা এক জেল্লাদার বাড়ি মিশে গেল মাটিতে। পাথুরে কাঁকুরে মাটি যেন মরা বাড়িটার রক্তে দুর্নিবার লাল!
জ্যোতিষ ঠ্যালা মারলেন ‘কই হে, ওই চা-এর অধিকার-বধিকার ছেড়ে ঘরের পানে ধাওয়া কর’ বটে, চললাম হ্যা, দেকি আমার দালানটাও গেলো কিনা!’
২
বৃক্ষপ্রপাত
অনেক বছর পর কলকাতায় এসে ভালোই লাগছে ডক্টর জি. ডি. বোসের। তিনি একজন চোখের ডাক্তার এবং গবেষক। সম্প্রতি তিনি দৃষ্টিশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংবেদন বা অতি সংবেদনশীলতা গ্রাহী এক পরকলা, সুপার সেনসিটিভ লেন্স তৈরি করে পুরস্কৃত হওয়ার পর মার্কিন মুল্লুক থেকে ফিরেছেন নিরিবিলি বিশ্রামের জন্য। ভবানীপুরে তাঁর পৈত্রিক বাড়ির দোতলায় সপরিবারে থাকেন তাঁর যমজ ভাই ইএনটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ও অধ্যাপক রজদীশ।
মঙ্গলবার বিকেলে সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় বেরিয়েছেন। সবে আগুন দেবেন সিগারেটে, দেখলেন একটা তিনতলা বাড়ি কেমন করে যেন একদম মিলিয়ে গেল মাটিতে। জি.ডি. বিস্মিত। ভীত। লোকজনের চেঁচামেচি কান্না— চিন্তিত মনে কয়েক পা হেঁটে খেয়াল হল তাইতো তাঁর সেই অপটিকো অপটিক্যাল চশমাটা দিয়ে দেখলেই তো হয়!
সিগারেট ধরিয়ে সেই চশমা চোখে দিয়ে পেছোলেন আবার। নাঃ কিছুই নেই! তবে? তবে চশমাটা কাজ করছে না? ওই চশমায় আবার তিনি অভ্যস্ত নন। সুতরাং চশমাটা চোখে একবার হাতে একবার করছেন— তখন হঠাৎ দেখলেন তাঁর দুই পা যেন পাথর। একটা মস্ত বড় গাছ চেপে বসছে আর একটা তিনতলা বাড়ির ওপর। তিনি দেখলেন একটা নয় দুটো তিনটে ওরকম গাছ চেপে বসছে পাশাপাশি দুটো তিনটে বাড়ির উপর। একেবারে মাটিতে মিশে গেল বাড়িগুলো। জি.ডি. চেয়ে থাকতে থাকতেই এক দুই মিনিটের মাথায় দেখলেন কোথাও কিছু নেই। সবই ফাঁকা!
মোটরসাইকেলে দুই দিক থেকে আসা দুই যুবকের কথা এল কানে। ‘ব্যাপারটা কী বলতো? আজ আবার!’
-‘ওফ্ একটু আগে একটা বিরাট পথ অবরোধের খবর পেলাম— সে নাকি এয়ারপোর্ট থেকে একদল মধ্যমগ্রাম—’
‘কী নিয়ে অবরোধ?’
‘থোড়াই জানি, লাক ফেভার করল। ওদিকে জয়িতার বাড়ি— ওকে কল করলাম— জয়িতা ঝটপট গিয়ে যা খবর দিলো— ওঃ সে তো এক্কেরে টক ঝাল মিষ্টিরিয়াস—’
-‘কী?’
-‘সামনে তার এক কিলোমিটার পুরো ফাঁকা এক— এক পিস সিঙ্গল পাবলিক নেই— অথচ মধ্যমগ্রাম মোড় থেকে পেছনে যতটা দেখা যাচ্ছে— সব গাড়ি আটকে! সামনের রোয়ের বাস-মোটর-ট্যাক্সি— স্টার্ট দিয়েও এগোতে পারছে না’
জি.ডি. একটু একটু করে অনুমান করছেন। কোনো কথা বলবার প্রশ্নই নেই। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে। বুঝতে পারলেন, তাঁর চশমায় যা দেখছেন— তা ঠিক। কিন্তু তাকে ধারণ করবেন কেমন করে? বেশ দু-তিন দিন আবারও থাকলেন তার কাজের ঘরে। এবার সমাধান সহজ— কারিগরির ভাগটাই তুলনায় জটিল। চশমায় যদি ক্যামেরার কৃৎকৌশল প্রয়োগ করেন, তবে যা দেখছেন তার ছবি ধরা থাকবে। তাঁর বিশ্বস্ত যন্ত্রবিদ, নারায়ন মূর্তি বেঙ্কটস্বামী আয়ারকে মেল করলেন। ঝড়ের থেকেও দ্রুত বেগে কলকাতায় আসবার জন্য। এরপর প্রায় দশ দিন ছিলো তাঁদের ক্যামেরা চশমা তৈরির পর্ব। বাড়ি দুমড়োনো রান্না অবরোধ মাঝে মাঝে চলছেই।
দুই সপ্তাহের মাথায় জি.ডি. চলে গেলেন চৌঁত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে। রাস্তার পাশে ঘরবাড়ি, দোকান-বাজার আর কিছু বলতে কিছু নেই। তার মধ্যেই এক আধা দুমড়োন, আধা ত্যারছানো চায়ের দোকানের খোঁজ পেয়ে, বসলেন সেখানে। দোকানটাই তার থ্যাঁতলানো মতো মালিককে নিয়ে কুঁকড়ে আছে লজ্জায়। ‘কী দিনকাল যে ছেলো ছ্যার— বাস দাঁড়াচ্ছে – গাড়ি থামচে— চা-কোলডিং-পান-গুটখা ঝটাঝট বিক্কিরি হত—’
-‘এখন?’ জি.ডি. জিজ্ঞেস করলেন।
-‘এখন তো গাড়ি মারি সব ফন্ ফন্ করে চলে যায়— তবে ভগবান আচেন, একটা উপায় হচ্চে—’
-‘কী?’
-‘জানেন না— অবিশ্যি সব খবর তো— জানেন না— এই তো হঠাৎ করে সব গাড়ি পরপর দেইড়ে যায়— এক ঘন্টা দু ঘন্টা’
-‘তাই নাকি? কেন?’ খুব সরল চোখে শুধোলেন হলেন জি.ডি.।
–‘কেন তা কেউ বলতে পারেনে। রাস্তা ফাঁকা— কিন্তু সেই শুনশান হাইরোডে, গাড়িগুলোর যেন চাকায় গেঁটে বাত আর ডেরাইভারদের হাতে নুলো, তখন আবার মানে আমাদেরই আর কি—বিক্কিরি টিক্কিরি— ওই— ওই দ্যাখেন ছ্যার— দ্যাখেন’
জি.ডি. দেখলেন— একটা-দুটো করে গাড়ি থামতে শুরু করেছে। তিনি তাঁর নতুন তৈরি ক্যামেরা কম্বো চশমায় দেখলেন, রাস্তার ওপর নেমে আসছে বড় বড় গাছ— রেনট্রী— যেন বৃষ্টির মতই নামছে ঝাঁকে ঝাঁকে।
৩
সূত্রপ্রপাত
পরপর তিন চার দিন বিভিন্ন হাইওয়েতে ঘুরলেন জি.ডি.। তাঁর যা দেখবার আর ক্যামেরা চশমায় ধরবার ছিল ধরে রাখলেন তাও। কিন্তু কার্যকারণ বুঝতে পারছেন না কিছু। এক রবিবারের সকালে এমনই ঘুরতে বেরিয়েছেন পাড়ার রাস্তায়। দুটো নতুন বাড়ি— দুমড়ে রয়েছে। ফুটপাথে দু-একটা অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছ। চশমাটা চোখে দিলেন তিনি। তাঁদের রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে দেখলেন একটা বড়ো নিম গাছ। একটু আশ্চর্য লাগলো! রজদীশ চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ওই বড়ো নিমগাছটা ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে। তবে? গাছটা কেমন করে এলো? গাছের কাছে গিয়ে হাত দিলেন তার গুঁড়িতে। না হাত ছুঁতে পারছে না! দুই হাত দিয়ে ধরলেন কান্ড— ধরবার চেষ্টা করছেন প্রাণপণ। ‘কী রে গজু? কবে এলি? অমন কচ্চিস কেন? শরীর খারাপ লাগছে?’
বহুকাল পরে ‘গজু’এই ডাকে একটু বিচলিত। তাঁর বাবা ব্রজদীশচন্দ্রের বন্ধু চন্দ্রনাথ তাঁর চাঁদুকাকা! আশি পেরিয়েও বেশ সটান-সতেজ। বাজার করে ফিরছেন। ‘না- চাঁদু কাকা- আসলে এই নিমগাছটা’
-‘কোথায় নিমগাছ? সে তো মরে গেছে, বছর কতক—
-‘ও, হ্যাঁ—’
-‘ওই গাছটা তোর তো খুব ফেভারিট ছিল।’
পুরনো মানুষ, তাঁরা কে কেমন জানেন বুঝতে, শুধোলেন ‘চাঁদুকাকা, একটা নিমগাছ খুব বেশি বয়েসও তো না, হঠাৎ মরে গেলো? কিছু মনে হল না আপনাদের?’
-‘তা দ্যাখ— কত কী-ই তো হয়— এই যে কোভিড— মানুষ মরে গেলো হাজার হাজার— তো একটা বেওয়ারিশ গাছ! হুঁ!’ তারপর আবার বললেন ‘তুই সেই আমেরিকা থেকে এসে এখানে একটা রাস্তার গাছের জন্য অমন হাঁকপাক করিস কেন? দাঁতন করবি? তা বাজারে যা না— ও—’ বলে আবার থেমে, ‘হুঁ— সেই যে ইলেভেনে পড়বার সময় এখানে মাঝখানেক ছিলি, তখন গুপ্তবাবুর মেয়েটা— কী ছাই নাম, মনে আসছে না— তার সঙ্গে তো ওই গাছতলাতেই দেখা টেখা করতি— অ্যাঁ— এখন হঠাৎ এই বুড়ো দামড়া— চুল তো বেশ পেকেওছে—’ তিপান্ন বছরের জি.ডি. হঠাৎই সেই ষোল বছরের ছেলে, দুই সেকেন্ড থতমত ‘না চাঁদু কাকা, ওই নিম গাছের এক্সট্র্যাক্ট্ দিয়ে চোখের ওষুধ— একটা’ বলতে বলতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ‘আপনি আগের মতোই আছেন— একদিন বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসবো।’ বলেই আবার হাঁটতে থাকলেন জি.ডি.।
ঠাকুরদার আমলের ছড়ানো বাড়ি। এক চিলতে ফাঁকা জমিতে এক ফালি বাগান। চশমাটা চোখে দিয়ে দেখলেন, গাঁদা-চন্দ্রমল্লিকা-সন্ধ্যামণি— খুব ঘেঁষাঘেঁষি! এমন তো হবার কথা নয় অন্তত এই কদিন তো এমন তিনি দ্যাখেননি মোটে! আবার ছুঁয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন তাদের। না দেখতে পেলেও ছুঁতে পেলেন না। ‘অ্যাই টিংলু— টিংলু—’ রজদীশের ছেলে, ‘কী হয়েছে কাকু?’
-‘এইখানে বেশ কয়েকটা গাঁদা-সন্ধ্যামণির গাছ’
‘ওঃ তোমার মনে আছে? হ্যাঁ ছিল তো— লাস্ট ইয়ার এরকম বেশ কিছু গাছ— একদম উপড়ে ফেলে দিয়েছি। শুধু পলাশ, পলাশ গাছটা কাটলেও ওর— মানে ওটাকে উপড়ে ফেলা যায়নি। শিকড়টা আছেই— হাউ ফানি না— একটা নন **** গাছের **** রুট—’
এইবার পুরো ব্যাপারটা অনেকটাই স্পষ্ট তাঁর কাছে। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া পর ভাইকে ডাকলেন তিনি। যমজ ভাই, একটা বাড়তি আবেগ থাকেই। তাঁর থেকে চার মিনিটের বড়ো। বাবা ব্রজদীশচন্দ্র, দুই পুত্রের নাম রাখেন রজদীশ আর গজদীশ। নামের মানে বোঝা না গেলেও, ব্রজদীশ নামে, ব্রজ থাকায় এবং রজদীশ নামেও কোনো সমস্যা হয়নি, হতে থাকলো গজদীশের পর্বে। গজদীশ মানে কী এবং কেন, ওই প্রশ্নে বিক্ষত হতে হতে জোর করে তাঁর মামার কাছে, তখনকার মাদ্রাজে চলে গিয়েছিলেন তিনি। একমাত্র ওই নামের কারণে আর কখনও ফেরেননি কলকাতায়। অন্তত পড়তে নয়। বিপুল মনোযোগে পরীক্ষার ফল ভালো করতে করতে চলে যান স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র। এই চার মিনিটের বড়ো- “দাদা”কে এই নিয়ে তিনিও কথা শোনান। আর রজদীশও বলেন ‘হ্যাঁ রে আমার ছেলেও বলে, যদি আমার অমন হাতি মার্কা নাম হত তবে ও-ও তোর ছেলেমেয়েদের মতো বাইরের দেশে থাকতে পারতো! এখন সর্বত্রই তিনি জি.ডি.। ভাইকে বললেন এই গাছ পড়ার ঘটনা, আর দেখালেন তাঁর ক্যামেরা কম্বো লেন্স। বললেন ‘তুই একটু ভালো করে পরীক্ষা করে শব্দ ধরতে পারবি?’
-‘মানে?’
-‘মানে এই গাছগুলো কোনো কথা— কথা মানে তাদের মুভমেন্টে যে শব্দ হয়, তা আলাদা করে মেসেজ দেয় কিনা! চেষ্টা কর তো—’
-‘কিন্তু আমি তো মানুষের কানের ডাক্তার— আ—’
-‘তোর মানুষের কান দিয়েই শোন না— গাছগুলো কোনো কিছু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কিনা—’
-‘হ্যাঁ- হ্যাঁ- বলতে থাক— কোনো কনফারেন্স ডাকে কিনা— বুলেটিন—’
-‘একদম তাই। কাল সকালে বাড়ির এই বাগানটায় তোকে একবার গাছ কিছু দেখাবো— তার সাউন্ডটা ধর। জ্যান্ত কাজ আর ভূতগাছের—’
-‘ঠিক— বুঝতে পারছি কিছুটা— বেশ।’
অবশেষে জি.ডি. একটি বিজ্ঞানী সম্মেলন ডাকলেন। তাঁর বেশ কিছুটা নামডাক আছে। আর সমস্যাটাও এমন যে তাতে সাড়া না দেবার কথাও নেই কোনো। জনা পনেরো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে নিয়ে প্রথম সম্মেলনটি হল। ডক্টর অভিজিৎ বসু বললেন, ‘সমস্যার কারণ তো বোঝা গেল— কিন্তু সলিউশনটা কী—’
-‘এই জন্যই তো আপনাদের সঙ্গে কথা বলা—’
-‘আবার মনে হয় কয়েকজন বোটানিস্ট— আর, আচ্ছা ভাবছি’
ডক্টর প্রাণতোষ মিত্র ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি। ভূতত্ত্ব অর্থাৎ জিওলজিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। বললেন ‘আচ্ছা ওঝাদেরও ডাকলে হয় না—
-‘না না হালকা ভাবে নেবেন না। ঠাট্টা করবেন না। আমরা সবই কি আর জানি!’
-‘আপনি তো ভূ-তত্ত্ব থেকে ভূতত্ত্বে চলে গেলেন।’ বললেন ডক্টর প্রমথনাথ গুপ্ত।
সময় নেই। বাড়ি চ্যাপ্টাচ্ছেই। প্রশাসন জেরবার। অঘোরভূষণ মেমোরিয়াল অডিটোরিয়াম ছোটো। কিন্তু বেশ সব রকম ব্যবস্থা আছে। সেখানেই ডাকা হয়েছে পরের সম্মেলন।
জি.ডি. তাঁর তোলা ছবি আর তাঁর লেন্সের শক্তি সংক্ষেপে দেখিয়ে, বুঝিয়ে চলে এলেন মূল কথায় ‘আপনারা বুঝতে পারছেন কোন ভয়ংকর জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। ভূমিকম্প বা গ্রহান্তরের প্রাণী নয়— মেরে ফেলা গাছ— আজ রিভেঞ্জ নিচ্ছে। সভ্যতার শুরু থেকে গাছ কাটা হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাছ কাটা হলেও তার শিকড়, মানে যা বা যে অংশ মাটির তলায়, তা থেকে যেত বলেই হয়তো, আবার বলছি, হয়তো, তারা প্রেতরূপ পেতো না! কিন্তু গত বছর দশ-বারো যেভাবে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে বা ওষুধ দিয়ে গাছ মেরে ফেলা হচ্ছে তা অত্যন্ত অন্যায়। এই গাছেরাই—’
‘তা মিস্টার জেডি বোস, জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, আপনি জি.ডি. বোস, গজদীশচন্দ্র গাছের ভূত আবিষ্কার করলেন। এতে সমাজের লাভ কী?’ একজন প্রশ্ন করলেন। তখনই আরেকজন ফোড়ন দিলেন ‘দেখুন গাছের প্রাণ থাকলো না গেলো— আছে কি নেই তা নিয়ে কোনও আলাদা মাথাব্যথা তো অকারণ— কিন্তু যা—’
জি.ডি. একটু বিরক্ত হলেও ঠান্ডা মাথায় ‘দেখুন জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেননি— ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রে তার প্রমাণ দেখিয়েছিলেন। আমিও গাছের ভূত আবিষ্কার করিনি সুপার সেনসিটিভ লেন্স-এ তার প্রমাণ দেখালাম। এই সমস্যার মীমাংসা আমাদের সবাইকেই করতে হবে। আমি রজদীশকে, আমার ভাই ডক্টর রজদীশচন্দ্র বোসকে সমস্যাটা বলায় তিনি এই সমস্ত প্রেতবৃক্ষের যে শব্দ আদান-প্রদান তার কিছু ধ্বনি— তাঁর যন্ত্রে ধারণ করেছেন। তা সাধারণ গাছের শব্দের থেকে অনেকটাই আলাদা। একজন বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডক্টর বিজয়গোবিন্দ আপ্তে, এখানে আছেন, তিনি, আচ্ছা তিনিই বলুন।’
ডক্টর আপ্তে বললেন ‘আমি কার্নিভোরাস প্ল্যান্টস, পতঙ্গভুক গাছপালাদেরকে এই গোস্ট্ ট্রীর পাশে বসিয়ে দেখেছি, এই গোস্ট প্ল্যান্টস এলেই এরা কেমন অন্যরকম মুভমেন্ট করে—’
-‘লাফিয়ে গাছ পড়া থামাতে পারে?’
‘না তবে একটা ব্যাপার গত একরাত অবজার্ভ করেছি যে এই গোস্টপ্ল্যান্টের অ্যাপিয়ারেন্স টের পায়। ছোটো ছোটো গাছ গাঁদা-ভিসেনথিরাস- এদের গোস্টকে নিজেদের ডালপালা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে— দুটো অবজারভেশন রেকর্ডেড- থাকতে দ্যায় না।’
-‘ও দিয়ে তো কাজ হবে না ওই কার্নিভোরাস প্ল্যান্টের কি বট অশ্বথ হয়?’
-‘তা বোটানিস্টরা বলবেন কিন্তু এই ট্রী-রেন বা ট্রী-ফল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী?’
কথা চলছেই, নানা রকম। একজন জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু গাছেরা অমন জোট বাঁধলো কেমন করে— কোথায় কোন লোকেশনে—’
-‘অমন হয় না—’
-‘হয়ত – য়ুনিভার্সিটিতে কোর্স চালু করতে হবে—’
-‘আর ততদিনে গাছ চাপা পড়ে অক্কা পাবো, সকলে’
জি.ডি. মনে মনে ভাবলেন, ঠিক ওই পর্যায়টাও বুঝবার আছে।
ওনাদের একদল বললেন, ‘মানুষ বা কুকুর বেড়ালেও ভূত তাড়ানোর কিছু নিয়ম জানি— কিন্তু গাছভূত তো শুনলামই এই প্রথম! আগে প্রবাদ ছিল বট অশত্থ কাটতে নেই, আজকাল তা জানেই বা কে— মানেই বা কে?’
আরেকজন বললেন, ‘তাহলে তো খাওয়া দাওয়া বন্ধ করতে হবে? ধান-গম-আলু-বেগুন গাছেরাও যদি প্রতিশোধ নিতে—’
-‘আচ্ছা এতকাল হয়নি কেন? গাছেদের আবার কোন রেনেসাঁ এলো?’
জি.ডি. বিরক্ত হচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একদল রজদীশকে বললেন, ‘ভাই আবিষ্কার করেছে গাছের ভূত, তা আপনি এখনো তাদের ভাষা আবিষ্কার কত্তে পাল্লেন না? কেমন যমজ ভাই আপনারা?’ আরেকজন বললেন, ‘তা ওই গোস্ট ট্রী বেড়ে বেড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলেই কেন?— এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে এরা কেবল বেঙ্গলেই থাকবে?
-‘এ ও আরেক রকম মনোপলি বুঝলেন না, ওয়েস্ট বেঙ্গল’স ট্রী গোস্ট থিঙ্কস টু-ডে —’
ঠিক এই সময় ধ্রাম্ করে একটা শব্দ। দারোয়ান বললেন ‘স্যার পোর্টিকোটা—’
সকালে চশমা ভাগাভাগি করে দেখলেন, চারটে মাঝারি গাছ নেমে এসেছে পোর্টিকোর ওপর।
-‘আচ্ছা, মূল বাড়িতে না—’
-‘কেন চাপা পড়লে খুশি হতেন?’
-‘ওই ভূতগুলোর বোধ হয় একটু চোখ খারাপ— মিস্টার জি.ডি. ওদেরও একটা চশমার ব্যবস্থা করুন—’
‘এবার থেকে বোধ হয় ওয়াটার প্রুফের মতো ট্রী-ফল প্রুফ কিছু ব্যবহার করতে হবে, বাড়ির ওপরেও ট্রীফল প্রটেক্টার—’
সভা ভেঙে গেল। কত রকম ভূত, গজদীশচন্দ্র সবই শুনছেন। বিরক্ত হলেও, মনে হচ্ছে, এদের সম্মিলিত করে কিছু করা যায় কিনা! ওঝাদের প্রধান প্রমথবিলাস ভট্ট বললেন ‘আচ্ছা মহাভারতে কৃষ্ণার্জুন যে খান্ডব দহন করেছিলেন, অত বড় একটা গণহত্যা— মানে বৃক্ষরাজি – অরণ্য হত্যাকান্ড যে চললো, সেখানে তো কোন ভূতের উপদ্রব হয়নি!’
-‘তো আপনি কী বলতে চান?’
-‘আমার, আমার, আ-মা-র মনে হচ্ছে, এই কৃষ্ণার্জুন নাম নিয়ে চলাফেরা করলে এই গাছভূতদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে—‘
-‘অর্জুনও তো একটা গাছ—‘
-‘ওই তো— বিভীষণ তো রাক্ষস! অন্তর্ঘাত-সাবোটাজ-সাবোটাজই আমাদের রক্ষা করবে— চলুন এবার কৃষ্ণার্জুন নাম নিয়ে ভালোয় ভালোয় ফেরা যাক।’
জি.ডি. দেখলেন সাংবাদিক-ওঝা-বিজ্ঞানী সবাই বিপুল ঐক্যমত্যে সশব্দে কৃষ্ণার্জুন নাম নিচ্ছেন। নিতে নিতে চলে যাচ্ছেন।
পরিপার্শ্বে সমাসীন প্রেতবৃক্ষকুলের অবরুদ্ধ উপস্থিতি, অননুভূত। তাদের তির্যক কঠিন শ্লিষ্ট হাস্যরেখাও দেখতে পেলেন না কেউই।