মুক্ত গদ্য
সুপ্রিয় চৌধুরী
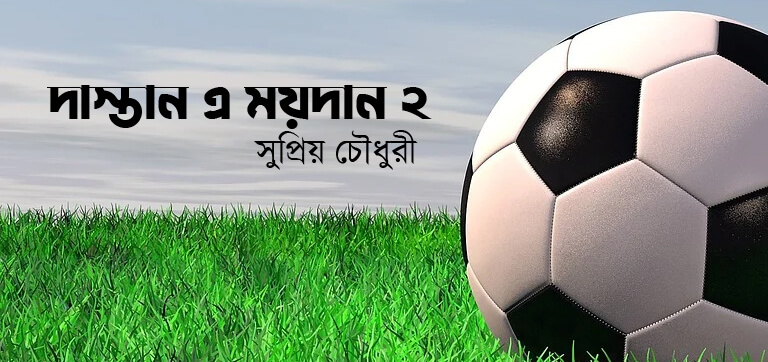
দাস্তান শুরুর আগে।
……………………
বেশ মনে আছে, এই অপার বাংলার গত শারদীয়া সংখ্যাতেই গতবছর লিখেছিলাম ‘দাস্তান – এ – ময়দান’। আসলে তার বহু আগে থেকেই মাথার মধ্যে সুতো পাকাচ্ছিলো ভাবনাটা। সেই ১৯৬৭ সালে বাবা আর মেজোমামার হাত ধরে ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন আরের আই.এফ.এ শিল্ড ফাইনাল দিয়ে মাঠের সবুজ গ্যালারিতে পা রাখা শুরু। সেদিন বছর এগারোর সেই কিশোর ছেলেটার ময়দানি দৌড় থেমেছে এই তো মোটে বছর সাতেক আগে তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এবং পরবর্তীতে যার ফলস্বরূপ অতি আবশ্যক বাইপাস সার্জারিতে যেতে বাধ্য হওয়ার কারণে। তবে মাঠ ছাড়ার পরেও সরাসরি মাঠে মানে কলকাতা ময়দান বা যুবভারতী স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখা সম্ভব না হলেও যোগাযোগটা থেকেই গেছিল খবরের কাগজ আর টিভির দৌলতে। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি এই যে বেহদ লম্বি এক ময়দানি কিস্যাকে আষ্টেপৃষ্টে গায়ে মাখার অভিজ্ঞতা, সে সব নিয়ে একটা কিছু লিখলে কেমন হয়? তার আগে ফেসবুক পেজে দু’চারটে নাতিদীর্ঘ পোস্ট দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু লেখা হয়নি বিষয়টা নিয়ে। ফলে সেই সূদুর আটলান্টা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা অপার বাংলার সম্পাদক শ্রী শুভ নাথের তরফ থেকে যখন তাদের শারদীয়া সংখ্যায় লেখার প্রস্তাব এলো, তখনই মাথার মধ্যে ফের উসকে উঠলো ভাবনাটা। কথাটা সম্পাদককে পাড়তেই অতি সাগ্রহে সাড়া দিলেন তিনি – “লিখুন দাদা, লিখুন! দারুণ হবে ব্যাপারটা। দেশ ছেড়ে প্রবাসে এসেও আমরা, এখানকার বঙ্গ সন্তানরা কেউ কলকাতা ময়দান আর ময়দানের ফুটবলকে ভুলিনি। নিয়মিত টিম করে ফুটবল খেলি এখানেও। এ লেখাটাই ছাপবো আমরা।”
ব্যস! সম্পাদকের গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া মাত্র শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। ময়দানে প্রবল চর্চিত বিষয়গুলো যেমন বিভিন্ন ম্যাচের বর্ণনা, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডানের মত তিন প্রধানের সাফল্য, ব্যর্থতা, গৌরবের ইতিহাস বা ট্র্যাক রেকর্ড নিয়ে যে কিছু লিখবো না সেটা ঠিক করা ছিলো বহু আগে থেকেই। তার বদলে থাকবে ময়দান ও তার ফুটবল সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয় বা ঘটনাক্রম যা তুলনামূলকভাবে চর্চা বা প্রচারের আলোয় আসে না সেভাবে। অথচ যা নিয়ে আম বাঙালির উৎসাহের শেষ নেই। আমার এই ভাবনার প্রতিফলন হিসেবেই অপার বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিবেদনটি। সম্ভবত কিঞ্চিত পাঠক আদৃতও যে হয়েছিল তার প্রমাণ মিললো সম্পাদকের একটি মন্তব্যে। গতবারের প্রতিবেদনের শেষ লাইনে লিখেছিলাম, লেখাটি যদি পাঠক নাম্নী বিচারকদের এজলাসে সানন্দে পাশ করে যায় তাহলে আগামী পুজো সংখ্যায় এখানেই প্রকাশিত হবে ‘দাস্তান – এ – ময়দান : ২’। আমার মেসেঞ্জার পত্রে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে সম্পাদক জানালেন, তারা আমার প্রস্তাবকে সানন্দে অনুমোদন দিচ্ছেন। অতএব ময়দান তথা ময়দানি ফুটবলের তুলনামূলকভাবে কম উল্লেখিত বলা ভালো অ-চর্চিত কিছু বিষয়কে নিয়ে শুরু হচ্ছে ‘দাস্তান – এ – ময়দান : ২’।
কর্মকর্তা
……………………
প্রথমেই এঁরা। এরা মানে ক্লাবের কর্মকর্তা। গালভরা নাম ক্লাব অফিসিয়াল। সর্বাগ্রে যে বিষয়টা খোলসা করে নেওয়া জরুরি সেটা হলো, বিদেশে যেভাবে পেশাদার ক্লাবগুলোর কর্মকর্তারা সবাই আদ্যন্ত পেশাদার অর্থাৎ ক্লাবের মাইনে করা কর্মচারী, আমাদের এই দেশে কিন্তু মোটেই ব্যাপারটা সেরকম না। এ দেশের আধা খ্যাঁচড়া বলা ভালো দো-আঁশলা ফুটবল সিস্টেমে ক্লাব পরিচালনার কাজকর্মগুলো বেশিরভাগটাই চলে সম্পূর্ণ অপেশাদার বা আধা পেশাদার পদ্ধতিতে। এখানে ক্লাবের শীর্ষ কর্তা থেকে শুরু করে পরিচালন সমিতির কেউই কোনরকম পারিশ্রমিক পান না। সেই আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি, এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। ষাটের দশকের এরকমই দুই কিংবদন্তি কর্মকর্তা সম্পর্কে কিছু কথা বলবো এখানে।
এরমধ্যে প্রথমজন শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র গুহ। কলকাতা ময়দান তো বটেই, সারা বাংলার ফুটবল প্রেমীরা একডাকে যাকে চিনতো জে সি গুহ নামে। পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে নিয়ে ষাটের দশকের প্রায় শেষভাগ অবধি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সর্বময় এককথায় একমেবাদ্বিতীয়ম কর্মকর্তা। অত্যন্ত সুপুরুষ, দীর্ঘদেহী আর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। পরিধানে বেশিরভাগ সময়েই শ্বেতশুভ্র ধুতি পাঞ্জাবী। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই ছিলো মানুষটার ধ্যানজ্ঞান। এককথায় যাকে বলে মাঠের মানুষ ছিলেন জ্যোতিষবাবু। প্রতিদিন বিকেলে চলে আসতেন ক্লাব টেন্টে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, এ নিয়মের অন্যথা হওয়ার জো ছিলো না একদিনও, ভুল বললাম, সেনাবাহিনীর আদেশে বছরের ওই পনেরোটা দিন ক্লাব তাঁবুর ছাদ খুলে নেওয়ার সময়টুকু ছাড়া। সর্বদা নিজে টিম নিয়ে মাঠে ঢুকতেন। বসতেন রিজার্ভ বেঞ্চের পাশে আলাদা একটা চেয়ারে। নিজের আলাদা গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই হয়তো বা। ৫০, ৬০, ৭০ দশকে ময়দানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে তাদের বোধহয় সবারই স্মরণে থাকবে ফুটবল সেসময় ছিলো সত্তর মিনিটের। আর খেলা শেষ হওয়ার দশ মিনিট বাকি থাকতে লাইন্সম্যানের হাতের পতাকা যেত নেমে। খেলা তখনও হয়তো ড্র চলছে। আর ঠিক তখনই দেখা যেত ময়দানের সেই চির পরিচিত দৃশ্যটা! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন গুহ সাহেব। উত্তেজনায় লাল টকটকে গৌরবর্ণ মুখখানা! পরমুহূর্তেই শুরু হয়ে যেত সাইড লাইন ধরে অস্থির পদচারণা। “গুহ সাহেব উইঠ্যা পড়সে, এইবার নির্ঘাত গোল হইবো।” দমচাপা উত্তেজনায় নিস্তব্ধ গ্যালারিতে ফিসফাস করতো ক্লাব অন্ত প্রাণ সমর্থকরা। এতে যে সর্বদা কাজ হতো এরকমটা নয় তবে ষাট মিনিটের মাথায় লাইন্সম্যানের হাতের ফ্ল্যাগ নেমে গেলে ওই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এতে সন্দেহ ছিল না কখনোই।
এবার ধীরেন দে মহাশয়। কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দেজ মেডিকেলের অন্যতম কর্ণধার। ইস্টবেঙ্গলে যেমন জে সি গুহ, মোহনবাগানে তেমনই ধীরেন দে। সবুজ মেরুনের হর্তাকর্তা বিধাতা। তবে জে সি গুহর মত ‘মাঠের লোক’ ছিলেন না কখনোই। খেলা শুরুর কিছুক্ষণ বাদে বাছা বাছা সহচরকে সঙ্গে নিয়ে গ্যালারির নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসতেন গম্ভীর মুখে। খেলায় নিজের টিমের হার বা জিত যাই হোক না কেন ওই একইভাবে বেরিয়ে গিয়ে বসতেন ক্লাবের লনে পাতা টেবিলে। নয়তো সটান ঢুকে যেতেন টেন্টের মধ্যে। ধীরেনবাবুর আমলে ক্লাব লনে পাতা ওই টেবিল আর তাঁবুর অন্দরমহল আক্ষরিক অর্থেই ছিলো ‘হাউস অফ লর্ডস’। যেখানে মাঠ আর সদস্য গ্যালারি ‘হাউস অফ কমনস’। অতি বিশেষ কয়েকজন মান্যগন্য ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিলো না হাউস অফ লর্ডসে।
পোশাকআশাকে জে সি গুহ যেমন ছিলেন ষোল আনার ওপর আঠারো আনা বাঙালী, ধীরেন দে ঠিক তার উল্টোটা। বারো মাস পরিধানে থ্রি পিস স্যুট। এমনকি প্রখর গ্রীষ্মের মরশুমেও দামী সামার স্যুট গায়ে চড়ানো থাকতো সর্বদা। ক্লাব তাঁবুতেও নিজস্ব একটা ওয়ার্ডরোব ছিলো তাঁর একাধিক স্যুট রাখার জন্য। ধর্মতলার মোড়ে জে এস মহম্মদ আলী ছাড়া আর কোন দোকানের স্যুট গায়ে চড়ানোর কথা নাকি কল্পনাই করতে পারতেন না তিনি। ফ্লুরিজের ব্রেকফাস্ট আর ফিরপোয় ফাইভ কোর্স লাঞ্চ, ডিনার সবিশেষ প্রিয় ছিল ধীরেনবাবুর। দেশের ঔষধ শিল্পে অন্যতম একটি সংস্থার কর্ণধার হওয়ার ফলে নিজস্ব এবং পরিবারিক সূত্রে নিবিঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল রাজ্য এবং কেন্দ্রে রাজনৈতিক মহলের উঁচুতলায়। যা গঙ্গা পাড়ের ওই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটিকে নানা ধরনের সরকারি আনুকূল্য পেতে সাহায্য করেছিল বলে অনুমান সেসময় তথ্যভিজ্ঞ মহলের অনেকেরই।
আদ্যন্ত বাঙালি জে সি গুহ মহাশয়, অন্যদিকে চলনে বলনে যাপনে পুরোদস্তুর সাহেব মিঃ ধীরেন দে, এই দুজনের মধ্যে অদ্ভুত মিল ছিলো একটি জায়গায়। দুজনেই ক্লাবটা চালাতেন কিঞ্চিত জমিদারি কায়দায় এবং ওরা দুজনেই মনে করতেন খেলোয়াড়রা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মত ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছে সেটাই অনেক, হাতে তুলে যেটুকু দেবো তাতেই খুশি থাকতে হবে। আর এধরনের মানসিকতার জন্য দুজনকে খেসারতও নেহাত কম দিতে হয়নি। জ্যোতিষবাবুকে নাকি সামান্য কিছু পারিশ্রমিক বাড়াতে বলেছিলেন সেসময় লাল হলুদ ডিফেন্সের স্তম্ভ সৈয়দ নঈমুদ্দিন। “হায়দ্রাবাদ থেকে এনে কলকাতা ময়দানে পায়ের নীচে জমি পাইয়ে দিয়েছি। আর কি চাও?” বলে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন জে সি গুহ। অন্যদিকে ধীরেন দে। ময়দানে জনশ্রুতি, সুভাষ ভৌমিকের পারিশ্রমিক কিছুটা বাড়ানোর আর্জি নিয়ে তাকে সঙ্গে করে ধীরেন দে-র ঘরে ঢুকেছিলেন এক সিনিয়ার খেলোয়াড় (পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা)। “স্যার, সুভাষকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে।” কিন্তু কথার শুরুতেই তাল কেটেছিল। “কে সুভাষ? আমি তো সুভাষ বলতে একজনকেই চিনি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস।” চরম ব্যাঙ্গের সুরে মন্তব্য করেছিলেন ক্লাব শীর্ষ কর্তা। বলার সময় নাকি সুভাষের দিকে একবার ঘুরেও তাকাননি তিনি। তাঁদের দুজনের এইজাতীয় উন্নাসিকতার মাশুল দিতে হয়েছিল দুটো ক্লাবকেই। সৈয়দ নইমুদ্দিনের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল লাল হলুদ রক্ষণে। অন্যদিকে ধীরেন দে-র এহেন মন্তব্যের প্রভাব সম্ভবতঃ পড়েছিল সুভাষের খেলার ওপর। গোটা একটা সিজন খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে বিতাড়িত হতে হয়েছিল ক্লাব থেকে। দল বদলে চলে গিয়ে উঠেছিলেন লাল হলুদ তাঁবুতে। তার বিদ্ধংসী ফলাফল যে কতখানি হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়েছিল গঙ্গা পাড়ের ক্লাবটিকে, তার সাক্ষী ময়দানের ফুটবল ইতিহাস।
কর্তাতন্ত্রের বদলনামা
……………………
৭০ দশকের গোড়া থেকে এই চিত্রটা বদলাতে থাকে একটু একটু করে। প্লেয়ারদের পয়সা না দিলে যে তাদের ধরে রাখা যাবে না এটা বুঝে ফেলতে অসুবিধে হয়নি গঙ্গা আর পদ্মা পাড়ের দুই ক্লাবের। একইসাথে ময়দানের আরেক শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মহামেডানেরও। আর এই নতুন চিন্তাভাবনার হাত ধরে ময়দানে চত্বরে প্রবেশ ঘটে পরবর্তী প্রজন্মের। ডঃ নৃপেন দাস, নিশীথ ঘোষ, এরফান তাহের, সুলেমান খুরশিদ, ডঃ প্রণব দাশগুপ্ত, পরবর্তীতে স্বপনসাধন ওরফে টুটু বসু, অঞ্জন মিত্রদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের সবার একটাই বৈশিষ্ট্য। হয় এরা নিজেরা অগাধ টাকার মালিক নয়তো নিজেদের সামাজিক সুনামকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে টাকা জোগাড় করতে সক্ষম।
তবে শুধু টাকা থাকলেই তো হবে না। কারণ খেলোয়াড়দের জগতেও দোলাচল প্রচন্ড। এক ক্লাবে থেকে এ্যাডভান্স নিয়েও আরও বেশি দক্ষিণার বিনিময়ে অন্য ক্লাবে চলে যাওয়া, “এই সিজনে নিশ্চয়ই আপনাদের টেন্টে ঢুকছি।’ জাতীয় ‘পাকা কথা’ দিয়েও শেষ মুহূর্তে পিছলে যাওয়া ময়দানি মানচিত্রে খুবই পরিচিত ছবি তখন। ফলে এইসব দোলাচলে থাকা অনিশ্চিত খেলোয়াড়দের অন্য দল থেকে নিজেদের দলে ভাঙিয়ে আনতে অথবা নিজেদের দলেই ধরে রাখতে বিভিন্ন কলাকৌশলের পাশাপাশি প্রয়োজন হতো পেশিশক্তিরও। আর এই সূত্রেই ময়দানে পা রাখা শুরু পেশিশক্তির কারবারিদের। এরকম তিনজনের কথাই বলবো এখানে।
প্রথমজন মানে দুজন। মানিকজোড় এক জুটি। জীবন চক্রবর্তী আর দীপক দাস ওরফে পল্টু। ময়দানে ‘জীপ’ নামে পরিচিত ছিলেন এই জুটি। ৭০-এর দশকে ইন্দিরা কংগ্রেসি রাজনীতির আঙিনা থেকে উত্থান কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার এই দুই বাহুবলীর। অন্য ক্লাব থেকে ফুটবলার ভাঙিয়ে আনতে বা নিজেদের ক্লাবের খেলোয়াড়দের ক্লাবেই রেখে দিতে জুড়ি ছিলো না দুজনের। এই জীপ জুটির দুটি রোমহষর্ক একইসঙ্গে মজাদার কীর্তির কথা শোনাই এবার।
সে বছর ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানে চলে যাবেন, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন মহম্মদ হাবিব। কলকাতায় পৌঁছেই সবুজ মেরুন তাঁবুতে গিয়ে এ্যাডভান্স নিয়ে নেবেন, কথাবার্তা একেবারে পাকা মোহনবাগান কর্মকর্তাদের সঙ্গে। ফুটবল মরশুম শেষের ছুটি কাটিয়ে হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরছেন শহরে। হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষা করছেন মোহনবাগান কর্মকর্তারা। খড়গপুরে (সম্ভবত) ট্রেন থামতেই দলবলসহ কামরায় উঠলেন জীবন আর পল্টু। দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়ালেন হাবিবের সামনে। এর মধ্যে জীবন, উৎকন্ঠিত গলায় তাঁর অননুকরণীয় পূর্ব বঙ্গীয় ভোকাবুলারিতে বড়ে মিয়াকে বললেন। “কলকাতায় ভয়ংকর দাঙ্গা লাইগ্যা গ্যাছে! তোমার লেইগ্যা আমরা নিরাপদ একখান বাসার ব্যবস্থা কইরা রাখছি। তুমি অহনি আমাগো লগে চলো!” বলেই হাবিবকে একরকম পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে নেমে পড়েছিলেন ট্রেন থেকে। ঘটনার অভিঘাতে হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমুঢ় বড়ে মিয়া, ঠিকঠাক কিছু বুঝে ওঠার আগেই জীপ এ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে এসে পড়েছিলেন স্টেশনের বাইরে। পার্কিং লটে দাঁড়ানো ক্লাব কর্তাদের দুটো গাড়ি। মাঝখানে হাবিব। দুপাশে জীপ। স্টেশন চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল গাড়ি দুটো। এর প্রায় ঘন্টাদেড়েক বাদে হাওড়ায় ঢুকেছিল ট্রেন। ছুটে গিয়ে কামরায় উঠেছিলেন মোহনবাগান কর্মকর্তারা। কোথায় বড়ে মিয়া! ফাঁকা সিট! পাখি ফুড়ুৎ! এভাবেই তুখোড় বুদ্ধি আর কিঞ্চিৎ পেশিশক্তি খাটিয়ে সবুজ মেরুন কর্তাদের টেক্কা দিয়েছিলেন ধুরন্ধর ‘জীপ’।
এই জীপ জুটির মধ্যে জীবন চক্রবর্তীর আরেকটি অনন্য কীর্তির কথা শোনাই এখানে। সেবার লাল হলুদ তাঁবু ছেড়ে সবুজ মেরুন তাঁবুতে গিয়ে উঠবেন, মনস্থ করে ফেলেছেন কৃশানু দে। খুব গোপনে তার প্রস্তুতি চলছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে খবরটা এলো জীবন চক্রবর্তীর কাছে। পাল্টা ঘুঁটি সাজাতে শুরু করলেন জীবন। আর এরপরই ঘটে গেল সেই অভাবনীয় কান্ডটা।
পরদিন ভোরবেলা। নাকতলার বাড়ির দরজা খুলেই চমকে উঠলেন কৃশানুর মা মায়া দেবী। দরজা আগলে শুয়ে আছেন জীবন চক্রবর্তী। কাঁদো কাঁদো মুখ। “মাসীমা, আমি খবরডা পাইসি। রন্টু (কৃশানুর ডাকনাম) মোহনবাগানে যাওনের তাল করত্যাছে। আমি বাইচ্যা থাকতে তো হেইডা হইতে পারে না। এই আমি দরজার সামনে শুইয়া রইলাম। রন্টুরে সঙ্গে না নিয়া নরুম না এইখান থিক্যা। ঘর থিক্যা বাইরাইতে হইলে হেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বুকে পা দিয়া আপনেগো বাইরাইতে হইবো।”
এহেন বক্তব্য শুনে মায়াদেবীর কি অবস্থা হয়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়। ব্রহ্মশাপে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মায়াদেবী “আরে আরে করেন কি! আমার মহাপাপ হবে যে!” বলে হাত ধরে তুলে জীবনকে নিয়ে গেছিলেন ভিতরে। দে বাড়ি থেকে কৃশানুকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলেন জীবন। তারপর সোজা নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন মধ্য কলকাতায় লাল হলুদের এক গোপন ডেরায়। সেবার আর মোহনবাগানের জার্সি পরা হয়নি কৃশানুর।
এবার মীর মহম্মদ ওমর। চাঁদনি, কলুটোলা, মাছুয়া এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ‘আনক্রাউনড কিং’। বিশালদেহী, অতীব সুদর্শন চেহারা। একগাল ঘন চাপদাড়ি। পরিধানে সর্বদা পাঠান স্যুট। মধ্য কলকাতার এক অত্যন্ত অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তান। পরিবারে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। স্বদেশে ও বিদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এমন একটি পরিবারের ছেলে যে কি করে বাহুবলী দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন সেটা সত্যিই এক অপার রহস্য। ৭০ দশকে ইস্টবেঙ্গলে জীবন-পল্টু জুটির উত্থানের পাশাপাশি মহামেডান ক্লাবে প্রবেশ ওমরের, সলমন খুরশিদ নামে এক সুপণ্ডিত, ইতিহাসের অধ্যাপকের হাত ধরে। ক্লাব পাগল এই কর্মকর্তার সবিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন ওমর। এছাড়াও মধ্য কলকাতার দাপুটে এক কংগ্রেস নেতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই বাহুবলী। ফলে ক্লাবে উত্থান হতে থাকে খুব দ্রুত। ১৯৮০ সালে সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সাবির আলি, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, প্রশান্ত ব্যানার্জী সমেত প্রায় পুরো ইস্টবেঙ্গল টিমটাকে ভাঙ্গিয়ে এনে মহামেডান তাঁবুতে ঢোকানোর অন্যতম কুশীলব ছিলেন তিনি। এছাড়াও গোলমেশিন, কালো চিতা চিমা ওকেরিকে প্রথম কলকাতা ময়দানে নিয়ে আসেন এই ওমরই। পরবর্তীতে জীবন চক্রবর্তী ক্ষমতার দৌড়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়লেও পল্টু দাস আর ওমর দুজনেই যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের সচিব তথা শীর্ষকর্তার আসনে বসে অত্যন্ত দক্ষ হাতে এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপে ক্লাব পরিচালনা করেছিলেন।
এহেন ওমর মিয়ার কাছে একবার কিছুটা রুঢ়ভাবেই বকেয়া টাকার দাবী করেছিলেন চিমা। জবাবে মেজাজ হারিয়ে ক্লাব টেন্টে সর্বসমক্ষে চিমাকে ঠাঁটিয়ে এক চড় মেরেছিলেন ওমর। মার খেয়ে ক্লাব লনে দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত হাউ হাউ করে কাঁদছেন অমিত বলশালী কৃষ্ণকায় গোলমেশিন, এ ছবি পরদিন বড় করে ছাপা হয়েছিল প্রায় সককটি স্থানীয় সংবাদ পত্রে। চিমার এই রাগ বা ক্ষোভটাকে কাজে লাগিয়ে পরের বছর কিভাবে তাকে এক ক্লাব কর্তার পার্ক সার্কাসের ডেরা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসছিলেন পল্টু দাস, সেটা নিয়ে বোধহয় আলাদাভাবে একটা টানটান থ্রিলার ওয়েব সিরিজ হতে পারে।
জীবন, পল্টু, ওমর। এই ময়দানি ত্রিভুজটা বোধহয় সম্পূর্ণ হবে না সেটাকে চতুর্ভুজে পরিণত না করলে। তালিকায় চতুর্থ নামটা গজু বসু। মোহনবাগান কর্মকর্তা। জীবন, পল্টু অথবা ওমরের মত পেশিশক্তির জোর বা দাপট কোনটাই ছিলো না। কিন্তু সে অভাবটা পূরণ করে দিয়েছিল ক্ষুরধার মগজাস্ত্র। সেটা প্রমাণ করেছিলেন ৭৭ সালে নিখুঁত পরিকল্পনা সাজিয়ে লাল-হলুদের ক্লাব বয় সুধীর কর্মকার, কর্মকার আর সেসময় ময়দানে আক্রমণ ভাগের সেরা দুই খেলোয়ার সুভাষ ভৌমিক আর মহম্মদ হাবিবকে সবুজ মেরুন তাঁবুতে তুলে নিয়ে গিয়ে। পরবর্তীতে আরও দুবার লাল হলুদ শিবিরকে জোরদার ঝটকা দিয়েছিলেন আরেক ক্লাব বয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর কৃশানু বিকাশ জুটিকে সবুজ মেরুন জার্সি পরিয়ে।
এবার এমন তিনজনের কথা বলবো যাঁরা কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানে শুধু দিতেই এসেছিলেন, বিনিময়ে একটি লাল পয়সাও আশা করেননি কখনো। প্রথমজন নিশীথ ঘোষ। উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল ধনী ব্যবসায়ি পরিবারের সন্তান। একাধিক আয়রন ফ্যাক্টরি আর বাজারের মালিক। ৮০-র দশকে এই নিশীথ ঘোষের আমলেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে জীবন পল্টুর একাধিপত্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা লাগে। সেবছর সুরজিৎ সেনগুপ্তর নেতৃত্বে ক্লাবের নামী ফুটবলাররা প্রায় সবাই দল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও হতোদ্যম হননি নিশীথবাবু। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসেন ইরান থেকে পড়তে আসা দুই ছাত্র মজিদ বাসকার আর জামশেদ নাসিরিকে। মজিদ। অদ্যাবধি এ দেশে খেলতে আসা সেরা বিদেশি ফুটবলার। সঙ্গে জামশেদ। নিখুঁত স্ট্রাইকার। এছাড়াও পুরোনো ক্লাবে ফিরে আসেন বহু যুদ্ধের পোড় খাওয়া তিন নায়ক মহঃ হাবিব, সুধীর কর্মকার ও কোচ পি কে ব্যানার্জি। দল ছেড়ে না যাওয়া মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ মিত্র, তপন দাস, হরজিন্দর সিং, এ ছাড়া আরো কিছু নতুন রিক্রুটকে নিয়ে গড়ে তোলেন একটা সুসংগঠিত দল। ফলও খুব একটা খারাপ হয়নি। ফেডারেশন, রোভার্স, নাগজি, স্টাফোর্ড সহ একাধিক ট্রফি ঢুকেছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে নিশীথবাবুর জমানায়। এহেন নিশীথবাবুর প্রবল ইচ্ছে ছিল খাস বাঙাল অথচ একনিষ্ঠ মোহনবাগানি সুব্রত ভট্টাচার্য ওরফে বাবলুকে অন্তত একবার লাল হলুদ জার্সি পড়ানোর। ময়দানে নিজের একজন অতীব বিশ্বাসভাজনকে দিয়ে ডাকিয়ে এনেছিলেন পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয়। সামনে খুলে দিয়েছিলেন ব্ল্যাঙ্ক চেকের পাতা। “এ্যামাউন্টটা তুমিই ভইরা নাও।” বলে পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে পেনটা বের করে এগিয়ে দিয়েছিলেন সুব্রতর দিকে। নিশীথবাবুর প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মোহনবাগানের ঘরের ছেলে বাবলু। চূড়ান্ত হতাশ হলেও খুশি হয়েছিলেন নিশীথবাবু। ম্লান হেসে বলেছিলেন, “এইরকম স্ট্রেইটকাট কথাই আমি পছন্দ করি। আমি তোমারে সরাসরি অফার করলাম আর তুমিও খোলাখুলি রিফিউজ করলা। আমি খুব খুশি হইলাম তোমার কথায়।” অতঃপর সুব্রতকে বিপুল ভুরিভোজ করিয়ে তবেই বিদায় দিয়েছিলেন। এরকমই ছিলেন মানুষটা। এর অনেক দিন বাদে সেই বিশ্বাসভাজনের মুখে শুনেছিলাম ঘটনাটা। নিশীথবাবুর সাথে পরিচয় ছিলো না। আর তাঁর সেই বিশ্বাসী কর্মকর্তাও প্রয়াত হয়েছেন অনেকদিন। জীবিত একমাত্র সুব্রত ভট্টাচার্য। ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। তবুও একদিন কোথাও সুযোগ হলে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার ইচ্ছেটা রয়েই গেছে।
এবার এরফান তাহের। ৮০ সালে এই মানুষটার হাত ধরেই ফের ঘুরে দাঁড়ানো শুরু মহামেডান স্পোর্টিংয়ের। সে বছরই ইস্টবেঙ্গল থেকে সুরজিৎ সেনগুপ্ত সহ একঝাঁক তারকা ফুটবলারকে ভাঙিয়ে এনে প্রথম চমক দেন তাহের সাহেব। সে চমক থামেনি পরের বছরও। সবুজ মেরুন শিবির ছেড়ে সাদা কালো জার্সি গায়ে চড়ান মোহনবাগানের তিন ‘ক্লাব বয়’ মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু ও প্রসুন বন্দোপাধ্যায়। ১৯৬৭ সালের পর দীর্ঘ ১৪ বছরের ট্রফি খরা কাটিয়ে ১৯৮১ সালে কলকাতা ফুটবল লীগ জেতে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। মীর মহম্মদ ওমর যে তার স্বভাবসিদ্ধ দাপট দেখিয়ে উপরোক্ত তারকা খেলোয়াড়দের তুলে আনতে পেরেছিলেন সেটা প্রধানত তাহের সাহেবের কুবেরের খাজানার উপর ভর করেই। ‘তাহের সাহাব কা তিজোরি (সিন্দুক) অওর উমর মিয়া কা জোশ (দাপট)’ – কথাটা সে সময় প্রবাদ হয়ে গেছিল মহামেডান তাঁবু আর গ্যালারিতে। এককথায় বলতে গেলে পুরোপুরি ক্লাব পাগল মানুষ ছিলেন এরফান তাহের। সম্ভবত ৮৪ সালে দিল্লিতে কোরিয় একাদশকে হারিয়ে ডি সি এম ট্রফি জিতেছিল মহামেডান। ম্যাচ শেষ হওয়া মাত্র ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন ফাইনালে একমাত্র গোলদাতা দেবাশীষ রায়কে। তারপর নিজের সোনা বাঁধানো ওমেগা ঘড়িটা খুলে পড়িয়ে দিয়েছিলেন দেবাশীষের হাতে। এই ছিলেন এরফান তাহের।
তবে এরফান তাহের বা মীর মহম্মদ ওমর, দুজনের পরিণতিটা আদৌ সুখকর হয়নি। এদের মধ্যে তাহের সাহেক, ক্লাবের পিছনে জলের মত টাকা ঢালতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান পরবর্তীতে। কলকাতাকে বরাবরের মত আলবিদা জানিয়ে চলে যান জন্মস্থান কানপুরে (না কি লক্ষ্ণৌ?)। শুনেছিলাম সেখানেই একটা ছোটখাটো ছাপাখানা চালিয়ে দিন গুজরান করতেন মহামেডানের কুবের। তবে কলকাতা ময়দান আজও মনে রেখেছে ক্লাব পাগল দিলদরিয়া মানুষটাকে।
অন্যদিকে মীর মহম্মদ ওমর। বৌবাজারে একটা খুনের মামলায় ফেঁসে শ্রীঘরে যেতে হয়। জামিন পেয়েই পালান দেশ ছেড়ে। আর কোন খবর মেলেনি। পুলিশ প্রশাসনের খাতায় আজও ‘নিখোঁজ’ একদা মধ্য কলকাতা আর ময়দানের এই দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী বাহুবলী!
অতঃপর সেই ‘দ্য ওয়ান এ্যান্ড ওনলি’ টুটু বসু। শুভ নাম স্বপনসাধন বসু। ‘লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন’। বাংলায় বহু পুরোনো সেই প্রবাদটা খাটে টুটু বসুর ক্ষেত্রেও। টুটুবাবু। পারিবারিক সূত্রে বিশাল এক জাহাজ ব্যবসার কর্ণধার। একাধিক অফিস স্বদেশে এবং বিদেশে। মোহনবাগান ক্লাব ধ্যানজ্ঞান মানুষটার। প্রিয় ক্লাবের যে কোন প্রয়োজনে সর্বদা দইয়ের ভাঁর থুড়ি টাকার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত একমেবাদ্বিতীয়ম টুটু বসু। মোহনবাগানের মধুসূদন দাদা। দ্য ফিল্ড মার্শাল অফ গ্রীন এ্যান্ড মেরুন ব্রিগেড। তিনি ক্লাবে পা রাখার আগে লাল হলুদ সমর্থকদের ‘মাইরা ফ্যালাম, কাইট্যা ফ্যালাম’ ধাঁচের কাঠ বাঙাল দাপটের সামনে কেমন মিইয়ে যেত সবুজ মেরুন সমর্থকরা। টুটুবাবুর হাত ধরেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শেখে তারাও। ক্লাবে বিদেশী খেলোয়াড় না খেলানোর শতাব্দী প্রাচীন প্রথা ভেঙে প্রথমবার নাইজিরিয়ান গোল মেশিন চিমা ওকেরিকে মোহনবাগানে সই করান টুটুবাবু। সঙ্গে পেয়ে যান দেবাশীষ দত্ত, অঞ্জন মিত্র, গজু বসুদের মতো একাধিক যোগ্য সহকারীকে। এই টুটু এ্যান্ড কোম্পানির একের পর এক মোক্ষম চালে কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর মত অপরিহার্য খেলোয়াড়দের হাতছাড়া করতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। ইদানীং আই এস এল, স্পনসরশিপ, ইত্যাদির ফলে দলবদলে গুরুত্ব অনেকখানি কমলেও গঙ্গাপাড়ের সবুজ মেরুন তাঁবুতে আজও শেষ কথার নাম স্বপন সাধন ওরফে টুটু বসু। নিশীথ ঘোষ, এরফান তাহেররা অতীত হয়ে গেলেও শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবে আজও চলছে টুটু রাজ।
এর আগেপরেও কলকাতার তিন প্রধানে যে সব কর্মকর্তারা অত্যন্ত দক্ষভাবে এবং স্বকীয় পদ্ধতিতে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ডঃ প্রণব দাশগুপ্ত, দেবব্রত সরকার (নীতু), সৃঞ্জয় বসু, বাবু ভট্টাচার্য, সুপ্রকাশ গড়গড়ি, ইব্রাহিম আলি মোল্লা, সুলতান আহমেদ, ইকবাল আহমেদ, ইসতিয়াক আহমেদ, প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস আর সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে যারা তাদের কর্মকান্ডের জন্য লোকমুখে ও সংবাদ মাধ্যমে অধিকতর চর্চিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে, তাঁদের কথাই আরেকটু সবিস্তারে বললাম এখানে। অতঃপর চলুন, পদার্পণ করা যাক পরবর্তী পর্বে।
রিজার্ভ বেঞ্চের রাজা
……………………
ওঃ! এখনও চোখের সামনে ভাসে সেই ডানকাঁধটা একদিকে হেলিয়ে রাজার মত দাপুটে হেঁটে আসা মেম্বারশিপ গ্যালারির মাঝখানের গেটটা দিয়ে। অথবা উঠে আসা যুবভারতীর টানেলের সিঁড়ি ভেঙে। ঠিক যেন গুহা থেকে বেরিয়ে আসা শিকারি চিতা। পিছনে গোটা লাল হলুদ টিম। ফুটবলাররা মাঠে প্রথম ওয়ার্ম আপটা সেরে ফিরে আসবে। রেফারির বাঁশি শোনার পর আবার ফিরে যাবে মাঠে। রিজার্ভ বেঞ্চে অতিরিক্ত খেলোয়াড় আর কোচের পাশে এসে বসবেন মানুষটা। মিনিট কয়েক বাদেই উঠে দাঁড়াবেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মত! উত্তেজনায় সাইডলাইন ধরে শুরু হয়ে যাবে অস্থির পদচারণা। সেটা খুব তাড়াতাড়ি ওয়াকিং ম্যারাথনে পরিণত হবে। নিজের ক্লাবের বিরুদ্ধে রেফারির প্রতিটি সিদ্ধান্তকে তীব্র চ্যালেঞ্জ জানাবেন পদে পদে। তাঁর চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রেফারিও দশটার মধ্যে কমপক্ষে দুটো সিদ্ধান্ত ভুল নিয়ে ফেলতেন এমনটা হামেশাই দেখেছি। মানুষটার নাম স্বপন বল। ইস্টবেঙ্গল ফুটবল টিমের ম্যানেজার। কর্মকর্তা হিসেবে হয়তো একদম প্রথম সারিতে ছিলেন না কিন্তু স্বপনবাবুর মতো ক্লাব অন্ত প্রাণ মানুষ আর একটিও দেখিনি এই ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মাঠে যাওয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবনে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঝড়জল, দুর্যোগ…প্রতিদিন মোটামুটি দশটার মধ্যে চলে আসতেন ক্লাব তাঁবুতে। রাতে কখন ফিরবেন কোন ঠিক নেই। আসলে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুই ঘরবাড়ি ছিল মানুষটার। ম্যানেজার ছাড়া অসামান্য রিক্রুটারও ছিলেন। সুদূর ঘানায় উড়ে গিয়ে তিনিই তো নিয়ে এসেছিলেন অদ্যাবধি ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া অন্যতম সেরা তিন বিদেশি সুলে মুসা, জ্যাকসন আর ওপোকুকে। জীবনে কোনদিন এমন কোন জামাকাপড় পরেননি যেখানে সামান্য সবুজ বা মেরুনের ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত রয়েছে। “আমায় কাটলেও লাল হলুদ রক্ত বেরোবে।” গর্বের সঙ্গে বলে বেড়াতেন সর্বত্র। প্রাণাধিক প্রিয় ক্লাবের মায়া কাটিয়ে বছরকয়েক হলো অসীম অপার এক মেঘের মাঠে খেলতে চলে গেছেন স্বপনবাবু। যেখানেই গেলেন ওই একইরকম দাপটে থাকবেন, রিজার্ভ বেঞ্চের সম্রাট শ্রী স্বপন বল। এটা একদম গ্যারান্টিড!
দুই প্রিয় বিভীষণ
……………………
শ্রী অজয় শ্রীমানি আর সুবিমল দাশগুপ্ত (ঝন্টু)। এদের মধ্যে প্রথমজন। উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ির সন্তান। একেবারে খাস ঘটি যাকে বলে। কিন্তু কট্টর ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। ফলে সবুজ মেরুন সমর্থকদের চোখে তিনি ছিলেন ঘরশত্রু বিভীষণ কিন্তু লাল হলুদ জনতার নয়নের মণি। ৭০ – ৭৫, ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণযুগে সাফল্যের পিছনে মানুষটার অবদান অপরিসীম। টিম গড়তে নিজের তিন তিনটে বাড়ি বেচে দিয়েছিলেন অজয়বাবু। অথচ এই লাল হলুদ অন্ত প্রাণ কর্মকর্তাটিকে শেষ জীবনে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ক্লাব। সেই তীব্র আক্ষেপ নিয়েই সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন চির ‘ইস্টবেঙ্গলি’ অজয় শ্রীমানি।
বিপরীতে ঝন্টু দাশগুপ্ত। এক্স অলিম্পিয়ান। প্রৌঢ়ত্বেও টানটান মেদহীন চেহারা। পদ অনুযায়ী ক্লাবের হকি সেক্রেটারি হলেও সর্বত্র বিরাজমান। এককথায় মোহনবাগানের ‘জ্যাক অফ অল ট্রেডস’। যে কোন দায়িত্ব ঝন্টুবাবুর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন ধীরেন দে থেকে নিয়ে টুটু বসু, অঞ্জন মিত্ররা সবাই। শতাব্দী প্রাচীন ঘটি ক্লাবে লন, তাঁবু, গ্যালারি, সবার সঙ্গে কথা বলতেন কাঠ বাঙাল ভাষায়, বরিশাইল্যা ভোকাবুলারিতে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তিনিও।
ফুটবলারদের মধ্যেও এরকম তিন ‘ঘরশত্রু বিভীষণ’-এর নাম মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। চুনি গোস্বামী, সুব্রত ভট্টাচার্য আর শান্ত মিত্র। এরমধ্যে প্রথম দুজনকে বহু চেষ্টা করেও লাল হলুদ জার্সি পড়াতে পারেননি ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা। এর উল্টোদিকে কোনদিন মোহনবাগান তাঁবুর ছায়া মাড়াননি খাস ঘটি শান্ত মিত্র। দলবদল, আনুগত্য বদলের এই বাজারে এই নামগুলো একটা দৃষ্টান্ত তো বটেই।
মাঠ করি
……………………
এই লব্জ বলা ভালো পেশাটা সারা ভূভারতে একমাত্র ময়দানে চালু আছে। ময়দানে মানে কলকাতা গড়ের মাঠের কথা বলছি আর কি। ময়দানে যে কোন ক্লাবের একদম শীর্ষ স্তর থেকে নিয়ে এতিপেতি কুচোকাঁচা যে কোন কর্মকর্তাকে জিগ্যেস করুন – “আপনি কি করে?” অবধারিতভাবে উত্তর আসবে – “মাঠ করি।”
এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার, ময়দানের এই মাঠ করিয়েদের মধ্যে যেমন ক্লাবের জন্য গ্যাঁটের কড়ি উজাড় করে দেওয়া নিঃস্বার্থ, ক্লাব অন্ত প্রাণ কর্মকর্তারা রয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে টু পাইস কামিয়ে নেওয়া লোকজনেরও অভাব নেই মোটেই। একদম শীর্ষ স্তর থেকে নীচুতলা, সর্বত্রই এটা সমপরিমাণ সত্য। আর যত বড় ক্লাব, এই ‘টু-পাইস’-এর পরিমা্নটাও সেখানে অনেক বেশি। বিভিন্ন খাতেই এই কাটমানি বা কমিশন কামানোর সুযোগ থাকে। তবে এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি রোজগারের সুযোগ থাকে দলবদলের সময় বিশেষত ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়দের নিজেদের ক্লাবে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে। ওই খেলোয়াড়েরা খাতায় কলমে যে টাকা হাতে পাবেন তার একটি অংশ ঢুকে যাবে যে কর্মকর্তা খেলোয়াড়টিকে রিক্রুট করে এনেছেন, তার পকেটে। ময়দানে আনাচকানাচে ঘুরে বিভিন্ন তথ্যভিজ্ঞ সূত্রে যেটুকু জেনেছি, মোটামুটিভাবে ফুটবলার ৮০%, কর্মকর্তা ২০%, কমবেশি এরকম একটা পার্সেন্টেজের হিসেবে ডিলটা হয়। আর বিদেশি ফুটবলার হলে তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের পরিমাণটা যায় অনেকটা বেড়ে, একইসঙ্গে কাটমানি থুড়ি কমিশনটাও। একসময় বড় রাঘববোয়ালদের না হলেও বেশ কিছু সেজো ছোট কুচোকাঁচা মাঠ করিয়েদের চিনতাম। বিচিত্র এদের জীবন। সকাল থেকে রাত, ঠিকানা ক্লাবের তাঁবু আর গ্যালারি। খাওয়াদাওয়া কেয়ার অফ ক্লাব ক্যান্টিন, অবশ্যই ক্লাবের খরচে। সঙ্গে দেদার সিগারেট, মদ, আনুষঙ্গিক আরও অনেককিছুই। তার ওপর সেই সাবেক কালের বাবুদের মোসাহেবদের মত দুচারজন ভিনরাজ্যের বা ভিনদেশী খেলোয়াড়কে ‘বাবু’ পাকড়াতে পারলে তো আর কথাই নেই। যাকে বলে ‘পাঁচ আঙুল একেবারে ঘিয়ে’। মনে আছে ৮০ সালে কলকাতায় সদ্য আগত দুই বিদেশী ফুটবলার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এক রাতে, শহরের এক নিষিদ্ধপল্লী থেকে। পরবর্তীতে জানা যায় তাদেরকে ওই মধুচক্রের সুলুকসন্ধান বাতলে দিয়েছিলেন এক নেহাতই কুচোকাঁচা মাঠ করিয়ে। বিলক্ষণ কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে। থানা থেকে দুই বিদেশীকে ছাড়িয়ে আনার পর তলব করা হয় সেই কুচো মাঠ করিয়েকে। সর্বসমক্ষে ক্লাব তাঁবুতে তাকে সপাটে চড় মেরেছিলেন এক শীর্ষ ক্লাব কর্তা, “শালা, মাঠে নামার আগেই সোনাগাছিতে খেলতে নামিয়ে দিলি!”
কলকাতা ময়দানে এ ধরনের মাঠ করিয়ে কর্মকর্তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। মুখে বড় বড় বাকতাল্লা সর্বস্ব মাঠ করিয়েদের মধ্যে অন্তত দুজনকে চিনতাম ব্যক্তিগতভাবে। তাদের একজন নিজেকে বম্বের (তখন নাম বম্বেই ছিলো) এক বাঙালি মেগা স্টারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দিতেন। আরেকজনকে ছাড়া নাকি বাইচুং ভুটিয়া বা বিজয়নের মতো সুপারস্টার ফুটবলারকে সই করাতে পাঠাতে ভরসাই পেতেন না ক্লাবের শীর্ষ কর্তারা। বাস্তবে ওই সময়ে কোনদিনই ঘটনাস্থলের ধারে কাছেও দেখা যায়নি তাকে। পরবর্তী সময়ে এই দুজনেই একাধিক জনের টাকাপয়সা মেরে উধাও হয়ে যায় ময়দান থেকে। পরবর্তী খবর অজানা।
বর্তমানে আই এস এল জমানায় ক্লাব ম্যানেজমেন্টের অনেকটাই বিশেষত ফুটবলার ট্রান্সফারের ব্যাপারটা সরাসরি স্পনসরারদের হাতে চলে যাওয়ায়, এ ধরনের মাঠ করিয়ে ক্লাব কর্তাদের বাজার অনেকটাই মরে এেছে সেতবে পুরোপুরি শেষ হয়েছে এমনটা বলা যাবে না কখনোই।
শংকর বাবা, ভাসিয়া, গোবিন্দ সমাচার
……………………
এরাও সবাই এসেছিলেন ভিনরাজ্য মূলতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। অতঃপর হয়ে গেছিলেন খাস মোহনবাগানি নয়তো ইস্টবেঙ্গলি। এদের মধ্যে প্রথম নামটা শংকর। পদবীটা জানা ছিল, ভুলে গেছি এতদিনে। গোটা ময়দান চত্বরে বিখ্যাত ছিলেন শংকর মালি নামে। সেই কোন কিশোর বয়েসে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসে ঢুকে পড়েছিলেন ময়দানের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে। হয়তো বা ক্লাব লনে মালির কাজ দিয়েই জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ক্লাবের ড্রেসিং রুমই হয়ে গেছিল মানুষটার পাকাপাকি ঠিকানা। লাল হলুদ সাজঘরের একচ্ছত্র অধিপতি। শংকর মালি। ফুটবলাররা কে কত নম্বর বুট আর জার্সি পড়বে, এ্যাংক্লেট, হোর্স, নি-ক্যাপ, শিন গার্ড, গ্লাভস, কার জন্য কোনটা ঠিক সময় বুঝে হাতের সামনে এগিয়ে দিতে হবে, কার ম্যাসিওর দরকার…এ সবকিছুর দায়িত্বে একমেবাদ্বিতীয়ম সেই শংকর। ‘ফুটবলাররা একবার লাল হলুল তাঁবুতে ঢুকে পড়লে তার গার্জেনের নাম শংকর মালি।’ – এমনটাই প্রবাদ ছিলো ময়দানে। ফুটবলাররাও চোখ বন্ধ করে ভরসা করতেন তাদের অবিভাবককে। আর এই কারণেই তো সুভাষ ভৌমিকের ‘গুরুদেব’, বড়ে মিয়া হাবিবের ‘ওস্তাদ’ হয়ে উঠেছিলেন মানুষটা। আর সুরজিৎ সেনগুপ্ত তাঁকে ডাকতেন ‘বাবা’ বলে। বছরকয়েক আগে প্রয়াত হয়েছেন লাল হলুদ ড্রেসিং রুমের এই মুকুটহীন রাজা।
শংকরের মতই মোহনবাগান সাজঘরের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন ভাসিয়া মালি। তাঁকে ছাড়া কল্পনাই করা যেত না সবুজ মেরুন ড্রেসিং রুম। ধীরেন দে থেকে টুটু বসু, অঞ্জন মিত্র, গজু বসু হয়ে হালফিলের দেবাশীষ দত্ত, সৃঞ্জয় বসু…সব জমানাতেই কাজ করেছেন একইরকম দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে। অতঃপর একদিন অবসর নিয়ে ফিরে গেছেন নিজভূমে। শেষ তথ্য অজানা।
গোবিন্দ রাজ। শংকর বা ভাসিয়া মালির তুলনায় বয়েসে অনেকটাই ছোট। পদমর্যাদা অনুযায়ী মোহনবাগান ক্লাবের ম্যাসিওর হলেও সক্রিয় ছিলেন অন্যান্য ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে দলবলের সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যেত তাকে। এখনও কি স্বমহিমায় বিরাজমান গঙ্গাপাড়ের ক্লাব তাঁবুতে? জানা নেই সঠিক। ঠিক একইভাবে ভুলে গেছি মহামেডান ক্লাব সাজঘরের সর্বেসর্বা ওই চাচার নামটা। বিহার না উত্তরপ্রদেশ, আদতে কোথাকার একটা বাসিন্দা যেন…আসলে বয়স… স্মৃতিগুলো টুপটাপ ঝরে পড়ে যাচ্ছে মস্তিস্ক নামক প্রকোষ্ঠ থেকে! নামটা কারো মনে থাকলে জানাবেন অনুগ্রহ করে। চির বাধিত থাকবো।
পেটপুজোর ময়দান
……………………
এটা এক্সক্লুসিভলি আপনাদের জন্য। মানে আপনারা যারা যৌবনে স্বদেশ ছেড়ে প্রবাসী হয়েছেন আর কি। আপনাদের মধ্যে যারা ময়দানে নিত্য যাতায়াত করতেন তাঁদের স্মৃতিতে নিশ্চয় থাকবে ময়দানের সেই বিখ্যাত ডান্ডাপানির কথা! একমাত্র কলকাতাতেই যা পাওয়া যায়। একটা ডালাগাড়ির ওপর বসানো জাম্বো সাইজের টিনের ড্রাম। মুখে একটা ঢাকনা লাগানো। ঢাকনার মাঝখানে একটা বড়সড় গর্ত মতো। গর্তর মধ্যে ঢোকানো পিছনে ছ্যাঁদাওয়ালা মগের মত দেখতে একটা পাত্র। মগটার ওপরে লাগানো লম্বাটে একটা টিনের ডান্ডা। ড্রামের মধ্যে ভর্তি স্যাকারিন জল। ডান্ডাটা ঠেলে জলের মধ্যে চুবিয়ে ড্রামের বাইরে বের করে আনলেই তলার ছ্যাঁদা দিয়ে জল বেরিয়ে আসতো। পাশেই খোপে খোপে রাখা গেলাসে গেলাসে ঢেলে একটু লেবু চিপে, বিটনুন বা জলজিরা মিশিয়ে…কোথায় লাগে ওইসব কোক আর পেপসি! নিশ্চয়ই ভোলেননি এসব? ভোলা কি সম্ভব! একইভাবেই যেমন ভোলেননি লজেন্স দিদি যমুনা দাস আর ছোটখাটো চেহারা, তাগড়াই মোচ, ঘটিগরম দুলালদার কথাও। আর কিভাবেই বা ভুলবেন ওই তরুণ ছেলেটির কথা যে সবসময় মাথায় সবুজ মেরুন ফেট্টি বেঁধে মোহনবাগান গ্যালারিতে লজেন্স ফেরি করতো। লজেন্স বলতে মেরুন ঘেঁষা টক ঝাল নোনতা আর সবজে রঙের আম বা লেবু লজেন্স। উল্টোদিকে লজেন্স দিদির বয়ামে সবসময় গাঢ় কমলা (লালের বিকল্প) আর আনারস লজেন্স। আম, লেবু বা টকঝাল লজেন্সের প্রবেশ সেখানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর দুলালদা। ইস্টবেঙ্গল আশিয়ান কাপ জেতার বিনেপয়সায় সবাইকে ঘটিগরম খাইয়ে ঝুড়ি খালি করে তবেই বাড়ি ফিরেছিলেন মধ্যবয়েসী মানুষটি। এছাড়াও ময়দানের সেই বিখ্যাত প্যাটিস! ভেজ – ৫ আর চিকেন – ৮। সাজানো থাকতো কালো রঙের লোহার ট্রাঙ্কে। আট টাকায় চিকেন প্যাটিস! কিভাবে সম্ভব! এই অবিশ্বাস্য কম দামের কারণ বাতলেছিল আমার এক বন্ধু। তার বয়ানে – “আরে শালা, এই চিকেন প্যাটিসের জন্যই তো ময়দানের ইঁদুরগুলো দিনকে দিন কেমন কমে আসছে, সেটা খেয়াল করে দেখেছিস কখনো?” আশাকরি এরপর আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।
অতঃপর আর তিনটে ময়দান ফেমাস কুইজিনের কথা বলেই দাস্তান এ ময়দান : ২ পর্বে ইতি টানবো। এই তালিকায় প্রথমেই আসবে কাস্টমস টেন্টের ফিশ ফ্রাই আর স্টু। চিকেন অথবা ভেজ। শহরের প্রায় সব নামী রেস্তোরাঁ বা কাফেতে খেয়েছি। এদের সবার সাথে সমানে সমানে টক্কর দিতে পারে কাস্টমস টেন্টের এই তিন অমৃতপদ। এরপরই নাম আসবে তালতলা আর আনন্দবাজার টেন্টের সরু চালের ভাত আর কাটা পোনার ঝোলের। যাদের একদা নিত্য আনাগোনা ছিল কলকাতা ময়দানে, আজ জীবিকার দায়ে ছড়িয়ে রয়েছেন নিউ ইয়র্ক, ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া, আটলান্টা, আশাকরি তাদের প্রায় সবারই কখনো না কখনো এইসব হেভেনলি কুইজিন চাখার অভিজ্ঞতা আছে। তাই এবার যখন এ শহরে আসবেন, অনুরোধ একটাই, আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একটিবারের জন্য হলেও নিয়ে আসুন ময়দানে। নিয়ে গিয়ে বসান সবুজ গ্যালারিতে। খাওয়ান কাস্টমস টেন্টের ফিশফ্রাই অথবা যমুনা দিদির লজেন্স, যেটা খুশি। তারা এটুকু অন্তত জানুক যে তাদের বাপকাকাদের কি দুর্দান্ত একটা অতীত ছিলো!
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন
