দুর্গাপূজা
দীপান্বিতা রায়

সময়টা অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক। পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। কলকাতা তখনও শহর হয়ে ওঠেনি। গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি বন্ধুত্ব। তবু সেখানেই চলছে লালমুখো সাহেবদের আনাগোনা। বাকি বাংলার নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় তার কোনও প্রভাব পড়েনি। জীবন চলছিল নিজের নিয়মেই। বর্ধমান জেলার অন্ডালের কাছে দামোদরের গা ঘেঁষে ছোট্ট গ্রাম জগুরবাঁধ। বেশ কয়েকঘর মানুষের বাস। বেশিরভাগই কৃষিজীবী। এছাড়া কামার-কুমোর-জেলে তো আছেই। উগ্রক্ষত্রিয়, হাড়ি, ডোম এই ধরনের নিম্নবর্ণের মানুষও বাস করেন। কিন্তু গ্রামে কোনও ব্রাহ্মণ নেই। সেকালে গ্রামে ব্রাহ্মণ না থাকাটা একটা মহা অসুবিধাজনক অবস্থা বলে গণ্য হত। যে কোনও পূজা-পার্বণে আশপাশের গ্রাম থেকে পুরোহিত ধরে আনতে হয়। সেই ধরে আনার কাজটাও সহজ নয় মোটেই। রাস্তা-ঘাট নেই বললেই চলে। পায়ে চলা পথ আর গরুরগাড়ি ভরসা। এক গ্রামে যদি গিয়ে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ যজমান বাড়ি গেছেন তাহলে হয় সেখানেই থানা গেড়ে দু’দিন বসে থাকো আর নয়তো আবার একবেলার পথ পেরিয়ে অন্যগ্রামে যাও। তাই জগুরবাঁধ গ্রামের মাতব্বররা একসময় ঠিক করলেন এভাবে চলতে পারে না। গ্রামে একঘর বামুন বসানো দরকার। খোঁজ-খবর শুরু হল। শেষ পর্যন্ত নোয়াপাড়ায় বসবাসকারী দুই ভাই হরিনারায়ণ রায় এবং রাজ্যবর্ধন রায় রাজি হলেন নিজেদের বাস্তুভিটে ছেড়ে এই গ্রামে এসে বসবাস করতে। সেই শুরু হল জগুরবাঁধ গ্রামে রায়বংশের পথ চলা।

হরিনারায়ণ আর রাজ্যবর্ধন ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু তাঁদের বংশে শিক্ষার চল ছিল। পূজার্চনার পাশপাশি বিদ্যাচর্চাও করতেন তাঁরা। এই বংশেরই পরবর্তী পুরুষ কেনারাম রায় ছিলেন নামকরা কবিরাজ। পসারও ছিল খুব। গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগী দেখে বেড়াতেন। শোনা যায় একবার মহালয়ার দিন ওরকমই ভিনগ্রাম থেকে রোগী দেখে ফিরছেন। পাল্কি ছিল না। পায়ে হেঁটেই যাচ্ছেন জোর কদমে। আশ্বিনের চড়া রোদ মাথার ওপর। কেনারাম রায়ের তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটু এগোলেই পুকুর। জলপান করবেন বলে সেই পুকুরের দিকে এগোতেই কেনারাম দেখেন পুকুরের ধারে বসে আছে একটি মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী। লালপেড়ে একখানা সাধারণ শাড়ি পরা। গায়ে গয়নাগাটিও বিশেষ কিছু নেই। মুখে ক্লান্তির ছাপ। এরকম নির্জন জায়গায় মেয়েটিকে একলা বসে থাকতে দেখে কেনারাম একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,
“তুমি কে মা? কোথা থেকে আসছ?”
মেয়েটি সেই কথার উত্তরে দশদিকের কোনও একটি দিকে আঙুল তুলে বলে,
“হুই দিক থেকে…।”
“কোথায় যাবে তুমি?”
“বাপের ঘর যাব।”

মেয়েটির উত্তর শুনে কেনারামের সন্দেহ হয়। ছেলেমানুষ মেয়ে। বাপের বাড়ির জন্য মনকেমন করছিল বলে হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। দুর্গাপুর-অন্ডালের ওইসব অঞ্চল তখন জঙ্গলে ঘেরা। ডাকাতের উপদ্রব খুব। মেয়েটি একলা এখানে বসে থাকলে বিপদে পড়তে পারে। তাই কেনারাম বলেন, “ঠিক আছে। আমি তোমাকে বাপের ঘরে পৌঁছে দেব। এখন আমার সঙ্গে চলো। আমার বাড়িতে জল-মিষ্টি খাও। তারপর পাল্কি চড়ে বাপের ঘর যাবে।”
মেয়েটি অনায়াসে কেনারামের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, “তোমার ঘরে যাব? আমাকে নতুন শাড়ি, শাঁখা-পলা দেবে তো?”
ছেলেমানুষ মেয়ের আবদারে মন গলে যায় কেনারামের। তিনি খুশি হয়ে বলেন, “নিশ্চয় দেব। মাকে আমি সাজিয়ে দেব। চলো আমার সঙ্গে।”
কেনারামের পিছু পিছু আসে সেই মেয়ে। বাড়ি পৌঁছে, বারমহলে তাকে বসিয়ে কেনারাম অন্দরে যান গিন্নিকে ডাকতে। কিন্তু নতুন শাড়ি আর শাঁখা হাতে গিন্নি সহ এসে দেখেন কেউ কোথাও নেই। দেউড়ির দারোয়ান অবাক হয়ে বলে, সে কাউকে বেরোতে দেখেনি, বাবুর সঙ্গে কোনও মেয়েছেলেকে ঢুকতেও দেখেনি। হতবাক কেনারাম তখন আবিষ্কার করেন আলতাপরা পায়ের ছাপ গেছে তুলসীমঞ্চের দিকে। মহালয়ার সকালে মা নিজে এসে নতুন শাড়ি, শাঁখা পরতে চেয়েছেন। এর থেকে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! হাতে মাত্র সাতদিন সময়। তবু ওর মধ্যেই সব আয়োজন সেরে ফেলেন কেনারাম। ১৭৭৫ সালের আশ্বিন মাসে শুরু হয় জগুরবাঁধের রায়বাড়ির দুর্গাপুজো।
এ গল্প আমি শুনেছি আমার ঠাকুর্দা শিবশঙ্কর রায়ের মুখে। তিনি ছিলেন এই কেনারামের বংশের পঞ্চম পুরুষ আর আমি সপ্তম। কেনারাম রায়ের শুরু করা সেই পুজো আজও চলছে। সংসারের নানা ডামাডোলে কখনও পুজোর জৌলুস কমেছে। অজন্মা কিংবা বন্যার বছরে আয়োজন কম হয়েছে। নম-নম করে সাজানো হয়েছে উপাচার। আবার যে বছর লক্ষ্মী দু-হাত ভরে দিয়েছেন, মায়ের আরাধনাতেও জাঁক-জমক বেড়েছে। কিন্তু পুজো বন্ধ হয়নি কখনও।

আমার ছোটবেলায় দুর্গাপুজো মানে তাই প্যান্ডেলে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখা ছিল না। স্কুল বন্ধ হত পঞ্চমীর দিন। বাবার অফিস ছুটি হত ষষ্ঠীতে। আমরা স্যুটকেস গুছিয়ে তৈরি হয়ে থাকতাম। আসানসোলের স্ট্যান্ড থেকে বাস ধরা। ঢিকঢিক করে চলত বাস। মাঠ ভরা সবুজ ধানক্ষেতের ওপর থেকে আশ্বিনের বিকেলের আলো দ্রুত মরে আসত। জোনাকি বসানো অন্ধকারের ওড়নায় ঢেকে যেত চারপাশ। জিটি রোডে বাস থেকে নেমে যেত হত বেশ খানিকটা। মোড় পেরোলেই ছাতিমতলা। সুগন্ধ ভরে আছে চারপাশ। বাড়ির কাছাকাছি এলেই চোখে পড়ত হলুদ বাল্বের টিমটিমে আলোর নীচে ঠাকুমা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অপেক্ষায়। ততক্ষণে দুর্গামন্দিরে ঢাক বাজতে শুরু করেছে। কোনওরকমে হাতের জিনিসপত্র ঘরের দুয়োরে নামিয়ে দে-ছুট। বিল্ববরণ শুরু হয়ে যাবে যে।
রাতে শুতাম ঠাকুমার কাছে। পান খেতেন ঠাকুমা। তাঁর গায়ের জর্দা আর দোক্তা পাতার গন্ধের সঙ্গে মিশে যেত বাগানের কামিনী ফুলের সুগন্ধ। ঠাকুমার কাছে শুনতাম তাঁর যৌবনকালের পুজোর গল্প। দাদু চাকরি করতেন বাইরে। পুজোর সময় সবাই মিলে আসা হত গ্রামের বাড়িতে। তখন এরকম বাসরাস্তা ছিল না মোটেই। রেললাইন বসেছে। ট্রেন থামত অণ্ডাল স্টেশনে। ছোট্ট স্টেশন। এপাশে-ওপাশে দুটি কেরোসিনের বাতি ঝোলানো। ছেলে-মেয়ে-পোঁটলা-পুঁটলি সামলে নেমে স্টেশনের বাইরে আসতেই হাঁক শোনা যেত মদন চৌকিদারের,
“কোন্ বাবু আইলেন গো…?”

দাদুরা আট ভাই। তারমধ্যে পাঁচজন থাকতেন বাইরে। পুজো উপলক্ষে আগে-পরে সবাই আসবেন। মদন চৌকিদারের তাই ডিউটি হল সন্ধের আগেই স্টেশনে পৌঁছে অপেক্ষা করা। তারপর লটবহর তুলে নিয়ে রওনা দিত গরুর গাড়ি। ছেলে-মেয়েরা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। দাদু বসেছে সামনে গাড়োয়ানের পাশে। গরুর গাড়ির নীচে ঝোলানো হ্যারিকেনের আলোর বৃত্তটুকু বাদ দিলে চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ছইয়ের ভিতরে ঘোমটা টেনে বসে ঠাকুমা নাকী দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতেন কতক্ষণে রাস্তা ফুরোয়, কতক্ষণে দেখা যায় ঠাকুরদালানের মাথায় ঝোলানো আকাশপ্রদীপের ক্ষীণ শিখা।
যৌথ সংসার তখন। মস্ত বাড়িতে অনেক লোকজন। তার মধ্যে ভালো-মন্দ সবই আছে। একেকজনের এক একরকম মত। তাই নিয়ে মজাও হত নানারকম। অষ্টমী আর নবমীতে যাত্রার আসর বসত। ঠাকুরদালানেরই একপাশে ব্যবস্থা। চিক দিয়ে ঘিরে মেয়েদের আলাদা বসার জায়গা। কিন্তু হঠাৎ ঠাকুমার বড় ভাসুর মানে দাদুদের সবথেকে বড় যে দাদা, তাঁর মনে হল, বাড়ির বউদের যাত্রা দেখতে যাওয়ার দরকার নেই। গোটা গ্রামের লোকজন আসবে, তাদের সঙ্গে বড় বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি হবে। সন্ধে না হতেই তিনি সদর দরজার পাশে একখানা ছোট চৌকি পেতে বসে পড়লেন পাহারা দিতে। এদিকে বউদের তো যাত্রা দেখার জন্য মন আঁকুপাঁকু। কী করা যায়? সমাধান করলেন শাশুড়ি স্বয়ং। মোটা-সোটা ভারী-সারি মানুষটি গিয়ে সেই চৌকিতে বসে ছেলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর বিপুল বপুতে ঢেকে গেল সদর দরজা। গ্রাম দেশে তখন দরজায় আলোর বালাই ছিল না। বউদের বলা থাকল পায়ের নূপুর খুলে চুপিচুপি বেরিয়ে যেতে। একে একে পা টিপেটিপে গিয়ে সবাই বসে পড়ল যাত্রার আসরে। অল ক্লিয়ার বুঝে মাও ছেলেকে বললেন, “এবার ঘরে যা বটু, নয়তো মাথায় হিম পড়ে ঠান্ডা লেগে যাবে। আমি বরং একটু পালাগান শুনে আসি।”

যে কোনও বনেদীবাড়ির পুজোরই নিজস্ব কিছু নিয়ম থাকে। আর সেই নিয়মের পিছনে থাকে নানা গল্প। রায়বাড়ির পুজোও তার ব্যতিক্রম নয়। মা দুর্গা নিজে এসেছেন বাড়িতে। নতুন শাড়ি, শাঁখা-পলা পরতে চেয়েছেন। তাই কেনারাম ঠিক করেছিলেন মা-কে বরণ করে তারপরে শুরু হবে পুজো। সেই নিয়ম কিন্তু এখনও আছে। সপ্তমীর সকালে পুকুর থেকে স্নান করে নবপত্রিকা আসে পাল্কিতে চেপে। মঙ্গলঘট আর প্রদীপ নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়। নবপত্রিকা মন্দিরে এসে পৌঁছলে বাড়ির সধবা মহিলারা পান-সুপুরি-প্রদীপ নিয়ে সেই দোলার চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বরণ করে ঘরে তোলে মা-কে। তারপর শুরু হয় সিঁদুর খেলা। বাড়ির নববিবাহিত মেয়ে-বউরা রীতিমত বেনারসী শাড়ি-গয়নায় সেজে নেমে পড়ে সিঁদুর খেলতে। সপ্তমীর সকালে এরকম সিঁদুর খেলার রেওয়াজ পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও বাড়ির পুজোয় আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।
পুজো মানেই খাওয়া-দাওয়ার নানা ধূম। বৈষ্ণবমতে পুজো। তাই বলির কোনও প্রশ্ন নেই। অষ্টমীর সন্ধিপুজোয় মস্ত একখানা মন্ডা পুরোহিত মশাই দুহাতের চাপে মট্ করে ভেঙে দিয়ে প্রতীকী বলি সেরে নেন। কিন্তু বাড়ির খাওয়া-দাওয়ায় মাছ-মাংসের কোনও কমতি নেই। একসময় নাকি নবমীর দিন গোটা পাঁঠা কাটা হত। মজার ব্যাপার হল সেই গোটা পাঁঠা নিয়ে বাড়িতে একটা ছোটখাটো বিপ্লবও হয়েছিল, যার নেত্রী ছিলেন আমারই ঠাকুমা। ব্যাপারটা একটু বিস্তারে বলি। গোটা একটা পাঁঠা মানে স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি মাংস। তখনকার নিয়ম অনুসারে প্রথমে বাড়ির পুরুষরা খাবেন, তারপর মেয়েরা। প্রতিবারই দেখা যেত ছেলেদের খাওয়ার পর মাংস আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বেচারা মেয়েরা সারাদিন পরিশ্রমের পর শুকনো মুখে ভাতে আলুসেদ্ধ মাখছে। একবার তাই ঠাকুমা আগেই মাথা গুণে রান্নার পর বাটিতে মাংস ভাগ করে রেখে দিলেন। সবার সমান ভাগ। চাইলে অল্পস্বল্প পাওয়া যাবে, কিন্তু ইচ্ছেমত নয়। বাড়ির পুরুষ মহলে তো ব্যাপার দেখে রীতিমত আলোড়ন। কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী মহিলাটিকে সবাই একটু সমঝে চলতেন। তাই কেউ কিছু বলার সাহস পেল না। তারপর থেকে সেটাই হয়ে গেল নিয়ম।

রায়বাড়ির যৌথ পরিবার অবশ্য এখন আর নেই। ১৯৫৭ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা তৈরির সময় সরকার থেকে বসতবাটি, তার আশপাশের জমি, পুকুর অধিগ্রহণ করা হয়। ফলে গ্রাম উঠে আসে আগে ভিটে যেখানে ছিল সেখান থেকে কিছুটা দূরে সরকারের দেওয়া জমিতে। যৌথ পরিবার ভেঙে সবার আলাদা বাড়িও তৈরি হয়। তবে পুজো যেমন ছিল তেমনভাবে নিয়ম মেনেই চলতে থাকে। পুজোর চারদিন বিশাল পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়ার নিয়মও চালু থাকে। সেই ভোজের মেনু কিন্তু বেশ অন্যরকম। রাঢ় বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বহু বছর ধরে যেসব পদ চলে এসেছে সেগুলিই রান্না হয় এ ক’দিন। তালিকায় থাকে শুক্তো, বড়ি দিয়ে কচু-কুমড়োর ঝাল, আলুপোস্ত, কলাইয়ের ডাল, মাছের টক, নারকেলের ডালনা ইত্যাদি। বাড়ির লোকেরা চারদিন পংক্তিভোজনে বসে খুব খুশি মনে খান এইসব পদ। আসলে খাওয়ার থেকেও তো ঢের বেশি আকর্ষণ হল আড্ডা। তাই খেতে বসে হাত শুকিয়ে ওঠে তবু বছর পেরিয়ে দেখা হওয়া ভাই-বোনদের সঙ্গে গল্প যেন আর শেষ হতে চায় না।
বাড়ির পুজো সবসময়ই হয় নিষ্ঠা ভরে, সবরকম নিয়ম-কানুন নিখুঁতভাবে মেনে। মা-কে পরানো হবে একশ-আট বেলপাতার মালা, ঘটের সামনে সাজানো থাকবে আধফোটা পদ্ম, ঘড়ি ধরে সন্ধিপুজো, নবমীতে পূর্ণাহুতি এসবই যে কোনও প্রাচীন পরিবারের মতই আমার বাড়ির পুজোরও নিয়ম। আমি তার বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না। কিন্তু পুজোর এইসব নিয়ম-কানুনের পিছনে সবসময়ই লুকিয়ে থাকে কিছু মানবিক মুখ। যার জন্যই দুর্গাপুজো আমাদের কাছে শুধু ধর্মাচরণ নয় উত্সব হয়ে ওঠে। সেইরকম একটা গল্প শোনাব এবার।
রায়বাড়ির পুজোয় ঢাক বাজানোর জন্য বাঁধা ঢাকি আছে। সেই যখন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা তৈরির আগে জগুরবাঁধ গ্রামে পুজো হত তখন থেকেই বংশ পরম্পরায় মুর্শিদাবাদ থেকে প্রতিবছর তারা আসে ঢাক বাজাতে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাও তাদের জন্য বরাদ্দ করা আছে। বছর পঞ্চাশেক আগের ঘটনা। একবছর ঢাকিদের মনে হয়েছিল, টাকা বড্ড কম পড়ছে। এত কম টাকায় অত দূর থেকে ঢাক বাজাতে আসা পোষায় না। তাঁরা সেবছর আসেননি। ষষ্টীর সন্ধেবেলা অনেক কষ্টে নতুন ঢাকি যোগাড় করে অবস্থা সামাল দিতে হয়েছিল। কিন্তু পরের বছর তাঁরা আবার এলেন। জানা গেল বিগত বছরটিতে নাকি তাঁদের সংসারে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে। গ্রামবাংলার সরল মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মনে হয়েছে, দেবী রুষ্ট হয়েছেন বলেই এমন দুর্গতি। তাই আর পয়সার কথা না ভেবে চলে এসেছেন ঢাক বাজাতে।

বাড়ির মাতব্বররা শুনলেন ঢাকিদের কথা। মুশকিল হচ্ছে পুজোর প্রতিটি খরচ কীভাবে চলবে তা পূর্ব-পুরুষরা নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন। চট্ করে তার থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকিদের টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারোর নেই। ঢাকিরাও সেটা বুঝল এবং মেনেও নিল। কিন্তু সেবছর দশমীর দিনে ঘটল এক মজার ঘটনা। সকালে ঘট এবং নবপত্রিকা বিসর্জন হবে। মন্দির থেকে বেরিয়ে সারিবদ্ধভাবে যাচ্ছে সবাই। ঢাকিও চলেছে ঢাক বাজাতে বাজাতে। হঠাৎ আমার এক দাদু, তাঁর তখন ষাটের বেশি বয়স তো নিশ্চিত, সেই মিছিলের সামনে নাচতে শুরু করলেন। দাদু রসিক মানুষ ছিলেন, ভাল অভিনয় করতে পারতেন। নাচতে নাচতে দাদু প্রতিটি বাড়ির সামনে গিয়ে গিন্নিদের কাছে ঢাকিদের জন্য সাহায্য চাইতে লাগলেন। সে এক অদ্ভূত দৃশ্য। গল্প শুনেছি সে বছর ওই ভাবে নেচে দাদু অনেক টাকা তুলে দিয়েছিলেন ঢাকিদের জন্য। তারা খুশিমনে বাড়ি গেছিল। আর তারপর থেকে সেটাই হয়ে গেল প্রথা। আমার সেই দাদু উমাশঙ্কর রায় অনেকদিন প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এখনও প্রতিবছর বাড়ির একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ দশমীর সকালে মিছিলের সামনে নাচতে নাচতে যান। সবাই এগিয়ে এসে তাঁর হাতে টাকা গুঁজে দেয়। মন্দির কমিটির বরাদ্দ করা অর্থ ছাড়াও এই টাকা দেওয়া হয় ঢাকিদের। এছাড়া বাড়ির সদস্যরা জামা-কাপড়, ওষুধপত্র কিংবা প্রয়োজনীয় আরও নানারকম জিনিস দিয়ে সাহায্য করে ঢাকিদের। ষষ্ঠী থেকে একাদশী বাড়িতেই থাকেন তাঁরা। খাওয়া-দাওয়া করেন সবার সঙ্গে। আসলে এখন তো তাঁরা রায়পরিবারেই অংশ হয়ে গেছেন। দেবীর রোষের ভয়ে নয় ভালোবেসে, মনের টানেই প্রতিবছর নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন মায়ের পুজোয় ঢাক বাজাতে।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন
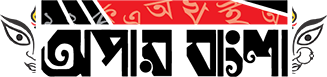
খুব ভালো লাগলো