ঋতা বসু
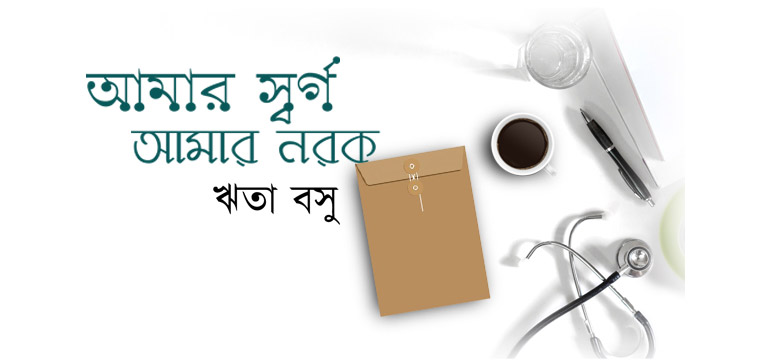
আমার টেবিলের ওপর একটুকরো জ্বলন্ত কয়লার মতো পড়ে আছে গেরুয়া রঙের খামটা। কখন এল? কে রাখল এখানে? কাল সন্ধেবেলা হাসপাতাল থেকে ফিরে টেবিলে বসিনি ঠিকই কিন্তু বিনায়কের সঙ্গে রাতের খাবার তো খেলাম। একবারও উল্লেখ করল না? আশ্চর্য!
এটা রেজিস্ট্রি চিঠি। লেটার বক্সে পড়ে থাকা সাধারণ চিঠি যখন নয় কুঞ্জাম্মাই হয়তো সই করে রেখেছে। হয়তো বিনায়কও জানে না। ভেতরটা এত কাঁপছে কেন? জানতামই তো আসবে। ক’দিন ধরেই অপেক্ষা জমছিল ভেতরে। অবশেষে এসে গেল সেই অন্তিম মুহূর্ত। অন্তিমই বটে। এ তো আর ডাকঘরের রাজার চিঠির জন্য অমলের অপেক্ষা নয় বা বাঁশির সুরও নয় যে চোখে না দেখলেও মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছ—
আহা কবে যেন গাইতাম গানটা— এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি— কী মিষ্টি একটা ব্যাপার ছিল।
বিনায়ক কফি নিয়ে এসে চেয়ারটা টেনে বসতে গিয়েও বসল না। প্রতিদিন সকালের কফিটা ও-ই করে। কাপে ঠোঁট ঠেকানোর আগেই কফির গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ চনমন করে ওঠে। মনে হয় দারুণ রোমাঞ্চকর কী যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। গন্ধটার মধ্যেই তীব্র একটা আকর্ষণ। সমস্ত পরিবেশটাতেই সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। আমরা কলেজ থেকে কফিহাউসে যেতাম শুধু সেই উত্তেজনার আগুনটুকুর জন্য। অথচ বাড়িতে কিন্তু আমাদের চা-ই হত। চা ছিল প্রতিদিনের সঙ্গে জড়িয়ে। খুবই চেনা আপন, সেইজন্যই উত্তেজনাহীন।
ভেবে অবাক লাগে সেই আপনার জিনিসটা খাওয়া দূরের কথা কতদিন চোখেই দেখিনি। পুরোনো জীবনের সঙ্গে খসে গিয়েছে কত চেনা অভ্যেস।
প্রথম প্রথম যখন কফিহাউসে যেতাম আমাদের দলটা বেশ বড়ই ছিল। তারপর শুধু আমরা দু’জন।
সমুদ্র দর্শনের আগেই যেমন গর্জন কানে আসে কফিহাউসেও ঢোকার আগেই সমবেত কোলাহল আছড়ে পড়ত কানের পর্দায়। তারপর সেই মোহিনী গন্ধ। যতক্ষণ থাকতাম মনে আছে সবাই হাসছি, সবাই চেঁচাচ্ছি। সিগারেটের ধোঁয়ায় দূরের মুখগুলো সব আবছা। এই জায়গাটা নাকি কবি লেখকদের আঁতুড়ঘর। আমি সবাইকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতাম। মা-বাবা-দাদাকে নিয়ে আমাদের ছোট পরিবার। পড়েছিও একদম শান্ত, ছোট কনভেন্ট স্কুলে। উলিঝুলি চুল আর রঙচটা পোষাক পরা সবাইকেই ট্যালেন্টেড মনে হত। বাংলা ব্যঙ্গ, শ্লেষ, রস-রসিকতার প্যাঁচ পঁয়জার না বুঝেই হাসতাম এই ভয়ে যেন দলছুট হয়ে না পড়ি। ওখানেই আলাপ নির্বাণের সঙ্গে। তুখোড় বাক্যবাগীশ। সবে মেডিকেলে ঢুকেছে। পড়ুয়া মেয়েরাই ডাক্তারি পড়তে আসত। আমাদের ক্লাসে চান্দ্রেয়ী ছাড়া তেমন ফ্যাশনের ধার ধারত না কেউ। আমি ভাবতাম নির্বাণের পাশে চান্দ্রেয়ীকেই মানায়। অথচ কেন জানি না নির্বাণ আমাকেই বেছে নিল। আজ কারণটা জানি না বললে ভাবের ঘরে চুরি হবে। তখন অবশ্য নিজের সৌভাগ্যে আহ্লাদে আটখানা হয়ে থাকতাম। যতই আমরা আধুনিক হই না কেন পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার চ্যালেঞ্জ নিয়েও মনের গহন গোপন কুঞ্জে পুরুষের পদধূলির দাক্ষিণ্যের জন্য কাঙালপনা লুকিয়ে থাকে দিনের আলোয় না দেখতে পাওয়া তারার মতো।
নির্বাণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এক ধাক্কায় আমার ‘খুকুমনি’ ইমেজটাকে বদলে দিয়েছিল।
এখন হাসি পায় ভাবলে— যখন তাসের ঘরের মতো ঝুরঝুর করে চারপাশ ভেঙে পড়ছিল, চেনা জীবনটা এক ধাক্কায় ঘুরে গিয়েছিল দুশো ডিগ্রি। প্রিয়জনদের আসল মুখগুলোও দেখতে পেলাম মুখোশের আড়ালে তখন বুঝতে পারলাম যারা বোকা তারা চিরকালই বোকাই থাকে। চালাক লোকের থেকে ধার করা আলো বরং বিপজ্জনক খুকুমনিদের ক্ষেত্রে।
সে কথা থাক।
আমার বোকামির কথা বলতে বসলে এক জীবন কেটে যাবে। হচ্ছিল কফি হাউসের কথা— ওখান থেকে যখন ফিরে আসতাম যখন সমস্ত গায়ে চুলে কফি আর সিগারেটের গন্ধ।
কলকাতায় থাকতে দৈনন্দিন জীবনে কফি ছিল না। বাড়িতে দুধ-চিনি দিয়ে মা আর দাদা চা খেত। বাবা খেত চিনি দুধ ছাড়া কালো চা। বাবার প্রতিটা কাজই ছিমছাম স্মার্ট। কালো চা বললাম বটে আসলে কালো নয়, সোনালি মেশানো খয়েরি। সাদা ধবধবে বোনচায়না কাপের তলা পর্যন্ত যেন দেখা যায় চায়ের রঙটা। ঠিক এমনটা না হলে বাবার পছন্দ হত না। কতবার চায়ের কাপ ফিরিয়ে দিয়েছে লিকারের রঙ মনোমত হয়নি বলে। বাবার দেখাদেখি আমিও খেতাম ওইররকম চা। কতরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ছিল চা নিয়ে। দার্জিলিং চায়ের সুগন্ধ আমাদের মনে চোরা স্নবারির জন্ম দিয়েছিল।
বিনায়ক কফির অসীম শক্তিতে বিশ্বাসী। সে আমাকে একটা সিনেমা দেখিয়েছিল— ‘কফি অ্যান্ড সিগারেট’। ছোট ছোট গল্প। কফির কাপ আর সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ঘটনা ঘুরছে বদলে যাচ্ছে দু’টি মানুষের বোঝাপড়া আর জীবন।
আমার জীবনও কত বদলে গিয়েছে। দার্জিলিং চা থেকে আমি এসে গিয়েছি আরাকু কফিতে।
শহর থেকে দূরে আলেপ্পিতে বয়স্কদের জন্য একটা আবাসনে বিনায়কের বাবা থাকেন। ভারি সুন্দর জায়গাটা। বৃদ্ধাশ্রম বলতে আমাদের মনে যে অনাদর অবহেলার একটা ছবি ফুটে ওঠে, এই জায়গাটা মোটেই সেরকম নয়। বিনায়কের বাবার সটান চেহারা। হাফ হাতা শার্ট আর একটা সাধারণ ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা— এর বাইরে কোনোদিন ওঁকে অন্যরকম দেখলাম না। আমাদের বিয়ের ছোট করে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানেও এইভাবেই এসেছিলেন। স্বাবলম্বন কথাটার মানে ওঁকে দেখে আমি নতুন করে শিখেছি। বিনায়কের দেখাদেখি আমিও ওঁকে আপ্পা বলে ডাকি। এই ডাকটা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ‘বাবা’ কথাটার অনুসঙ্গে যে পরিমাণ ঘেন্না-আতঙ্ক আমার মনের গভীরে থাবা গেড়ে বসে আছে তা কল্পনাতীত। ওই শব্দটাই আমার জীবনে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগে। নয়না বিনায়ককে ডাকে আপু বলে।
খুব ইচ্ছে ছিল আপ্পা আমাদের সঙ্গে এসে থাকবেন। স্বীকার না করতে চাইলেও আমি জানি আমার বাপসোহাগী কাঙাল মনটা আঁকড়ে ধরতে চায় ওইরকম কোনো মানুষকে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। চাকরিতে থাকাকালীনই এই জায়গাটা তিনি কিনে রেখেছিলেন সস্ত্রীক থাকবেন বলে। আমি কখনও শুনিনি একমাত্র ছেলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কেউ সাধ করে বৃদ্ধাশ্রমে থাকে। আমি এদের সংসারে আসার আগেই বিনায়কের মা গত হয়েছেন।
বিয়ের পর বিনায়ককে আন্তরিকভাবেই বলেছিলাম উনি আমাদের সঙ্গে এসে থাকুন। বিনায়ক আমার প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে— বাবাকে চেনো না তাই বলছ।
— তুমি যদি নিজের কম্যুনিটির কারওকে বিয়ে করতে তাহলে হয়তো উনি থাকতেন।
দক্ষিণীরা উত্তরের তুলনায় বেশি রক্ষণশীল বলে আমার মনে হয়েছিল। হয়তো এই সিদ্ধান্তটা তারই প্রকাশ।
বিনায়ক বলেছিল— তুমি ভয়ানক সেন্টিমেটাল হয়ে পড়েছ বলে যুক্তিবুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছে। বাবা কবে থেকে এই জায়গাটার ইএমআই দিয়েছে! তখন কোথায় তুমি? কে জানত কোন হতভাগিনী আমার ঘরণী হবে? আমি বোধহয় স্কুলের বেড়াও পার হইনি তখন। বাবার প্রতিটা স্টেপ প্ল্যান করা বুঝলে? ভগবান এলেও তার নড়চড় হবে না।
বিনায়কের কাছে হেরে গিয়ে আমি আরও রেগে যাই। নিজের বাড়ির তুলনায় এদের স্বচ্ছতা, অতি সাধারণ কিন্তু সৎভাবে জীবন কাটানোর অহংকার মনে একটা অসহায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। সে-ও অবশ্য বহুদিন আগের কথা। আগ্নেয়গিরির আগুনবমি বন্ধ হয়ে সে এখন ঝিমোচ্ছে। এই চিঠি কি আবার জাগিয়ে তুলবে তাকে?
এখন বিনায়ক আর আমি দু’জনেই কফির কাপ হাতে চুপ করে বসে আছি। সেই সিনেমাটার মতো একটা গল্প গড়ে উঠছে আমাদের এই কফি টেবিলকে ঘিরে। দু’-চারটে কথা বললেই বিনায়ক স্বস্তি বোধ করবে জেনেও আমি কোনো তাগিদ অনুভব করছি না।
আমাদের দশ বছরের যৌথজীবনে আমি যতটুকু বলেছি ও ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থেকেছে। তার বেশি কখনও জানতে চায়নি।
বিনায়ক ডুবো পাহাড়ের চুড়োটুকু শুধু দেখেছে। তাতেই ওর এত সংকোচ। এখন আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তার থেকে কফির টেবিল ঘিরে যে গল্পটা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে, বোতল থেকে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে আসছে যে ভয়ঙ্কর দৈত্যটা তারই মুখোমুখি হই এবার।
আজ আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে আমার ছ’ বছরের মেয়ে নয়না এসে আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। আমাকে ছুটির দিন ছাড়া পায় না বলে আমার সঙ্গের জন্য ওর মনে তৃষ্ণা জেগে থাকে সবসময়। বিনায়ক হাসপাতাল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত, তাই ওর কাজটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুরু আর শেষ হয়। বলতে গেলে বিনায়কই একসঙ্গে ওর মা ও বাবার ভূমিকা দারুণভাবে পালন করে। শাসন ও আদর দুটোই থাকে। আমার কাছে শুধুই আদর। নয়নাকে যখন দু’হাতে জড়িয়ে ধরি আমার ভেতরটা কাঁপতে থাকে ঝোড়ো হাওয়ায়। হাতের তালুতে আড়াল করা নরম প্রদীপ শিখার মতো নয়নাকে লুকিয়ে রাখতে চাই সব ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে। এমনকি আমার কাছ থেকেও।
কলকাতার সঙ্গে আমার যে কখনও সম্পর্ক ছিল সেটা ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। চোখের ভেতরে আর একটা চোখ এক অতন্দ্র দৃষ্টি মেলে রাখে নেটে আসা খবরগুলোর দিকে— বিশেষ করে চিকিৎসাজগতের খবর। কলকাতার হাসপাতাল ভাঙচুরের খবর থাকে মাঝে মাঝে। ডাক্তারকে মারের ছবিও। একদিন দেখলাম নির্বাণকে ডাক্তারদের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে টেলিভিশনের আলোচনা সভায়। একটু মোটা হয়েছে। চশমা আগেও ছিল। এখন ফ্রেমটা মোটা। নিশ্চয়ই পাওয়ার বেড়েছে। চুল ধূসর আর পাতলা। রংচঙে জামা পছন্দ ছিল নির্বাণের। এখন পরে আছে একটা খুব হাল্কা রং। এটাই এখন পছন্দ, না টেলিভিশনে মুখ দেখাবে বলে, একটা গম্ভীর আলোচনার উপযুক্ত ইমেজ খাড়া করার চেষ্টা— জানি না। ও বরাবরই এসব নিয়ে খুব সচেতন ছিল।
নির্বাণের দিকে তাকিয়ে মনে হল সত্যি অনেকটা পথ আমরা পার হয়ে এসেছি। নিজের মুখটা প্রতিদিন আয়নায় দেখি বলে সময়ের আঁচড় টের পাই না। তবে নির্বাণের অন্য পরিবর্তন যাই হোক না কেন বিজ্ঞের মতো কথা বলার ধরণটা একই আছে। আলোচনা সভায় বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা নানাজন নানা কথা বলছে। নির্বাণ বলছিল— আমাদের কাজ চিকিৎসা। যতদূর সম্ভব প্রাণ রক্ষা, কিন্তু আমাদেরও তো কিছু লিমিটেশন আছে। আমরা তো ম্যাজিশিয়ান নই। এ কথাটা না বুঝলে কিন্তু আমাদের কাজটাই বন্ধ হয়ে যাবে।
— কাজটা সবাই করে না বলেই তো এসব হয়— রাগ চেপে হাসিমুখে বললেন উলটো দিকের প্রতিনিধি।
নির্বাণ শান্ত হেসে ঠান্ডা গলায় বলল— আতঙ্কিত হয়ে থাকলে তো যতুটুকু সার্ভিস দিচ্ছি সেটাও দেওয়া যাবে না।
দোষ স্বীকারের থেকেও ওর গলায় শাসানির সুরটাই যেন শুনতে পেলাম। হাস্যকরভাবে ব্যাঙ্গালোরে আসার আগে আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে গেল। মহত্তম পেশার কর্তব্য সম্বন্ধে জ্বালাময়ী জ্ঞানগর্ভ ভাষণটির প্রত্যেকটা শব্দ আমার মনে গভীর দাগ কেটে বসে আছে— নিজের প্রাণ তুচ্ছ করেও বাঁচাতে হবে রোগীকে। তার পেশা, সামাজিক অবস্থান কিছুই দেখা চলবে না। অন্য সব ফিল্ডের মতো এখানেও আছে প্রলোভন, নানা ফাঁদ। চোখ কান বুজে নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে যেতে হবে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র হিসেবে এতসব কথা মনে রাখলে ওর চলবে না। হয়তো সত্যি আর মনেও নেই।
অ্যাঙ্কর মেয়েটি দু’ আঙুলে একটা পেন ঘোরাতে ঘোরাতে কী বলল তা ভালো করে শোনার আগেই নয়না এসে আমার হাত ধরে টানল।
কোচিতে আমাদের হাসপাতালটাই সবথেকে বড়। তবুও মেট্রোসিটির টেনশনের সঙ্গে তুলনা হয় না। মাঝে মধ্যে ডুব মারলে কারও মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে না।
নয়না তার রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল— বাবা বলছে আজ তোমার ছুটি। হাসপাতালে যাবে না। তাহলে আমাকে নাচের ক্লাসে নিয়ে চলো।
বিনায়ক ধরেই নিয়েছে আমি আজ হাসপাতালে যাব না। নয়নার কথায় মনে হল, না গেলেই তো হয়। আজ না হয় থাকি ওর সঙ্গেই।
ভাগ্যিস ও ছিল। আমি যেন কমলা খামটার থেকে পালাতে পেরে বেঁচে গেলাম। নয়নার নরম নিষ্পাপ হাত আর কলকল কথা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।
— এবার ফ্যান্সি ড্রেসে আমি কিন্তু ডাক্তার সাজব। তোমার স্টেথোটা দেবে তো? আমি একটুও নষ্ট করব না। কী, দেবে তো?
আমি একটু হেসে ওর হাতটা তুলে চুমু খেলাম। আপাতত এটুকুই ওকে শান্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট।
— রোহিনী বলেছে— আগের বার টিচার সেজেছিল বলে প্রাইজ পায়নি। এবার ও স্কেয়ার ক্রো সাজবে। আমাকে চুপিচুপি বলেছে।
— তাহলে তুইও অন্য কিছু সাজ। ডাক্তার হলে কিন্তু প্রাইজ পাবি না। সুসানা আন্টিকে বলব, তোকে অন্যরকম কিছু সাজিয়ে দেবে?
— না। না। আমি সাদা অ্যাপ্রন পরে সত্যিকারের স্টেথো হাতে নিয়ে হাঁটব তোমার মতো। আর কেউ আমার মতো স্টেথো লাগিয়ে হার্টবিট শুনতেই জানে না। সেদিন সবাই আমাকে বলছিল কিনায়ার টেম্পারেচার এসেছে কিনা দেখতে। ওরা ভেবেছে তুমি ডাক্তার বলে আমিও হাফ ডাক্তার হয়ে গিয়েছি। তবে আমি তো ডাক্তারই হব সেটা সবাই জানে।
ওর জগতের পাঁচমিশেলি গল্প শুনতে শুনতে আমার ভেতরটা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যাচ্ছিল। নয়নার সমস্ত অস্তিত্ব থেকে মৃদু সুগন্ধ উঠে আসছিল। বারান্দার ডবলবেড সাইজের দোলনাটায় বসে আরামে চোখ বুজে আসছিল। সামনে ছড়ানো সবুজ জমি। বিনায়কের সঙ্গে যেদিন প্রথম এসেছিলাম ওর বাবা বসেছিলেন এই দোলনাটায়। বারান্দার লাল টুকটুকে মেঝে, একদিকে দোলনা অন্যদিকে সোনার মতো ঝকঝকে বাতিদান সিলিং থেকে ঝুলছে। সীমানা পাঁচিলের ধার ঘেঁসে নারকেল গাছের সারি। আমার মনে হয়েছিল স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে এখানেই।
ব্যাঙ্গালোরের বদলে কোচির হাসপাতালে কাজ নেওয়ায় বিনায়ক আর ওর বাবা দুজনেই খুশি হয়েছিলেন। আর আমার মনে হয়েছিল মনের জ্বালা পোড়া জুড়োবার জন্য এর থেকে ভালো জায়গা আর হয় না।
গেট খুলে সুসানাকে আসতে দেখে নয়না দৌড়ল। সুসানারা পাশেই থাকে। ওদের হোম স্টে-টার খুবই সুনাম। কেরালার ট্র্যাডিশনাল খাবার বানাতে সুসানা সিদ্ধহস্ত। আমাকে বলল— আজ পুট্টু বানিয়েছিলাম, তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম।
আমি পুট্টুর পাত্রটা ওর হাত থেকে নিতে নিতে বললাম— আমিও করেছিলাম কিন্তু এত সুন্দর গন্ধ হয়নি।
— তোমরা অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে করো যে। বাঁশের পাত্রে না বানালে চালের গুঁড়ো নারকেল কোড়ার এই গন্ধটা আসে না।
— সত্যি তোমাকে বাঁধিয়ে রাখতে হয়। মাটির হাঁড়ি, বাঁশের পাত্র এসব আজকাল আর কেউ ব্যবহার করে না।
— করে। তোমরা জানো না। আমরা যারা ট্র্যাডিশনে বিশ্বাস করি তারা সবাই করি।
নাগরিক জীবনের অন্তহীন লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা দেখে ডানাভাঙা পাখির মতো এদের কূলে তরী বেঁধেছি। কত সাধারণ কথা আচরণের মধ্যে দিয়ে এই মানুষগুলো একটু একটু করে আমার মনে শান্তির জল ছিটিয়েছে বলতে পারব না।
পাত্রটা ডাইনিং টেবিলে রেখে এসে সুসানা বলল— একটু পারুথি পাতা নিয়ে যাই তোমার বাগান থেকে। কলকাতা থেকে চারজনের একটা ফ্যামিলি এসেছে। কাল ইডিয়াপ্পাম বানাব। কলাপাতার বদলে পারুথি পাতায় করলে উপকার বেশি।
কী সাধারণ নিষ্পাপ সব সমস্যা আর তার সমাধান। কলকাতার অতিথিদের নিয়ে সুসানা আজ খুবই ব্যস্ত নয়তো আমি ওকে আরও খানিকক্ষণ আটকে রাখতাম। নয়না চলে গেল ওর সঙ্গে নাচতে নাচতে। কলকাতার লোক নিয়ে ওর খুব কৌতূহল। নয়না জানে ওর মা কলকাতায় বড় হয়েছে। ও বাংলা বলতে পারে না। আমার কাছ থেকে কয়েকটা শব্দ আর বাক্য শিখেছে। সেগুলো অতিথিদের বলে বাহবা নিতে ভালবাসে। আমার একেবারে ইচ্ছে ছিল না। মনে হত ওই কয়েকটা শব্দের হাত ধরে যদি উঠে আসে চাপা পড়া অতীত।
এত চেষ্টা করেছি তবু কি ভুলতে পেরেছি কলকাতাকে? এ যেন গর্ভের মধ্যে ভেঙে যাওয়া প্রাণদায়ী জলাধারের সঙ্গে শিশুটিকেও বিসর্জন দেবার ইচ্ছে।
কলকাতার লোক শুনলেই ভেতরটা দুলে ওঠে। আমি কি চিনি? কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কলকাতা থেকে গেস্ট এসেছে শুনলে আমার বুকটা দুরদুর করে উঠত। মনে হত আমাকে দেখলেই তারা চিনে ফেলবে। আমাকে যেন কেউ দেখে না ফেলে সেইজন্য বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতাম।
চিঠিটা পাওয়ার পর মনে হচ্ছে আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি হাজার সূর্যের আলোর মাঝে উলঙ্গ হয়ে। আস্তে আস্তে দোলনা থেকে উঠে পেছন দিকে গেলাম। পেছনেও অনেকটা জমি। তার গা ঘেঁসে ব্যাক ওয়াটার বয়ে চলেছে। বেঞ্চের ওপর বসে থাকিয়ে রইলাম জলের দিকে।
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিনায়কের এই বাড়িটারও শান্তির প্রলেপ দেওয়ার বিশেষ গুণটি আছে। শহরের মাঝে এইরকম ছড়ানো জমি-বাড়ি-বাগান শুদ্ধ বাড়ি যত পয়সাই থাকুক না কেন কলকাতায় আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। এখানে অবশ্য অনেকেরই এমন বাড়ি আছে। বিশেষ করে এই পাড়াটা খুবই পুরোনো। বাসিন্দারা সবাই যত্ন করে ধরে রেখেছে আদি বাসস্থান। বেশ কয়েক বছর হল এর লাভজনক দিকটা নিয়েও সচেতনতা বেড়েছে। কেরালা বরাবরই ট্যুরিস্টপ্রিয় জায়গা। এখন অনেকেই হোটেলের বদলে এই ট্র্যাডিশনাল বাড়িগুলোর হোম স্টে-তে থাকতে পছন্দ করছে।
জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে— কিছু ধরে রেখো না। শুধু বয়ে যাও আপনবেগে। তখনই মনে মনে ঠিক করলাম আমার গল্পটা যা কেউ জানে না সেটা আমি শুধু নয়নাকেই বলব।
কিন্তু সেটা কবে? নিজেরাই যদি গল্পের চরিত্র হই তাহলে সেটার থেকে আলাদা হওয়া যায় না। আর যায় না বলেই সেটা কাউকে বলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই গল্প অন্য যে দু’জন বলতে পারত, তার মধ্যে একজন মৃত। অন্যজন দেশান্তরে। শুধু আমি বসে আছি কী এক অসম্ভবের আশায়।
চোদ্দ বছর মানে যাবজ্জীবন। রাম বনবাসে ছিলেন এতটা সময়। তার সৎমা ভেবেছিল এত দুর্ভোগের পর রাম আর ফিরবে না। সেইজন্যই বোধহয় চোদ্দ বছরের সঙ্গে যাবজ্জীবন মিলেমিশে গেছে। এখন এই বিশেষণটা একমাত্র কারাদণ্ডের সঙ্গেই সত্যি। বাকি সবকিছুর সঙ্গে যাবজ্জীবন কথাটা বেমানান। আমি যাবজ্জীবন তোমাকে ভালোবাসব বা যাবজ্জীবন আমার বৃদ্ধ মা-বাবার দায়িত্ব পালন করব—শুনলেই মনে হয় মিথ্যে কথা।
গত চোদ্দ বছর আমি মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিলেও কারাদণ্ড ভোগ করেছি অন্যভাবে। ছিলাম সংসার অনভিজ্ঞ বছর চব্বিশের এক সদ্য তরুণী। আজ ভরা সংসারে একজনের স্ত্রী, তার সন্তানের মা, কর্মজগতে ব্যস্ত, প্রায় চল্লিশের পোড় খাওয়া এক মানুষ। চোদ্দ বছর ধরে ফেলে আসা যে পথটা একটু একটু করে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সেই কাদা-ছাইমাখা পথে আবার হাঁটতে হবে আমার সবথেকে ভালোবাসার, সবথেকে ঘেন্নার মানুষটার জন্য।
তিনি আমার বাবা।
সবাই বিশেষ করে মেয়েরা মায়ের কাছেই সবকিছু চায়। মায়ের হাতে সমাধান না থাকলেও মাকেই জানানো হয় প্রথমে। এটাই নিয়ম। আমাদের সংসারে উলটো। মা-দাদা-আমি— তিনজনেরই চাইবার জায়গা একটাই— বাবা। ছোটবেলায় চেম্বার থেকে ফিরে গল্প বলে ঘুম পাড়াত বাবা। কারওরই মনে হত না ক্লান্ত লোকটার বিশ্রাম দরকার। আরও পরে স্কুলের প্রথম দিন, পেরেন্ট টিচার মিটিং, পুজোর পোশাক, সিনেমা দেখা, বাইরে খাওয়া— সমস্তই বাবার উপস্থিতে গমগম। আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে উপস্থিত থাকাটা যেন বাবার নিজেরই প্রয়োজন। আহ্লাদ-আদরে এমন অকর্মণ্য হয়েছিলাম যে আমাদের হয়ে চিন্তাভাবনার ভারটুকু পর্যন্ত বাবার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছিলাম।
বাবাই ঠিক করেছিল দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং আর আমি ডাক্তারি পড়ব।
আমার কথা ভেবেই বোধহয় চেম্বারের ওপরটা ভাড়া নিয়ে সাত বেডের একটা ডে কেয়ার ক্লিনিক খুলল বাবা। তিনতলায় থাকেন বাড়িওয়ালা জেঠু আর জেঠিমা। বাবার সঙ্গে আমাদের পুরো পরিবারকে যে কী ভালবাসতেন জেঠুরা সেটা বলে বোঝাতে পারব না।
কিছুদিন পর থেকেই মা রোজ জিজ্ঞেস করত— ক’টা রুগী হল?
কত লাভ হচ্ছে মার শুধু সেটুকু জানারই উৎসাহ।
থ্যাংকস টু মেয়েমানুষের শরীর। কতরকম ঘিনঘিনে আধিব্যাধি যে লেগে থাকে— তার ওপর আছে অবাঞ্ছিত গর্ভ। কচিকাঁচা মেয়ে থেকে পোড় খাওয়া বিবাহিত। এছাড়া মা ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টি তো আছেই।
আমি তখন জয়েন্টের জন্য টিউশন নিচ্ছি। নিজেকে প্রায় ডাক্তার বলেই মনে হয়। সুপারিন্টেনডেন্ট অমলা চক্রবর্তীর সঙ্গে বাবার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কেসগুলো বোঝার চেষ্টা করি। শরীরের সমস্যা যত, মনের সমস্যাও তত। একদিন একটি বৌকে দেখলাম শুকনো মুখে অমলাপিসির ঘরে বসে আছে। আমি অভ্যেসমতো ঢুকতে যেতেই পিওন রাজেশ আটকাল— জরুরি আলোচনা হচ্ছে। পরে এসো।
খুব মানে লাগল। কিছুদিন বাদে আমিই তো বসব বাবার চেয়ারে। গটমট করে ভেতরে ঢুকে গেলাম। অমলাপিসি আমাকে দেখে বিরক্ত হলেও প্রকাশ না করে বৌটিকে বলল— এখন তবে আসুন। যে ওষুধগুলো দেওয়া আছে ওগুলোই চলুক। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলব।
বৌটির সিঁথিতে বাসি সিঁদুরের দাগ। শাড়িটার সস্তা চকরা-বকরা নকশায় যা দাম, তার থেকে দামি দেখানোর চেষ্টা। হাতের ব্যাগ পায়ের চটি— সবগুলোরই খুব দুঃখী চেহারা বৌটারই মতো। তার গলাটাও ওইরকম ক্লান্ত, বিষণ্ণ। বলল— আজ দেখা হলে ভাল হত। তারপর শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে আর হবে না।
অমলাপিসি বুঝদারের মতো ঘাড় নেড়ে বলল— জানি তো। কিন্তু আজ বসে থাকলে ফিরতে তোমার রাত হয়ে যাবে।
— তা হোক। আজই সুবিধে— বৌটির গলা একই রকম ঝাপসা।
সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম— শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতে পারবে না কেন? ওর বরকে নিয়ে আসবে।
আমার তখন নবীন বয়স সবুজ মন। সম্পদে সংকটে প্রেমময় বুঝদার প্রেমিক স্বামীর কল্পনা খুবই জীবন্ত। অমলাপিসির কথায় তাল কেটে গেল— আরে সেখানেই তো সমস্যা। দুটো মেয়ে। আর মেয়ে চায় না। ছেলে হচ্ছে না বলে সবাই ওকেই দুষছে। বরটা তো পারলে এখনই আর একটা বিয়ে করে। এদিকে আবার প্রেগন্যান্ট। মেয়েটা বাচ্চা রাখতে চায় না। বলে আবার মেয়ে হবে। আমাদের ডাক্তারবাবুর এদের ওপর খুব সিমপ্যাথি।
— ছেলে না হলে বাবা কী করবে? ওটা তো কারও হাতে নেই।
— ডাক্তারবাবু ওদের দু’জনকেই একসঙ্গে কাউন্সেলিং করবেন তাই পরে আসতে বলেছেন। এদিকে আমাদের একজনকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে? এত সময় কোথায় আছে বল?
এত গর্ব হল বাবার জন্য যে আমার বুকটা টনটন করে উঠল।
দেখ দেখ করে বাবার ক্লিনিক একটা ছোট নার্সিংহোমে দাঁড়িয়ে গেল। দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমেরিকা গেল এমবিএ পড়তে। আমার নাম করে মার শাড়ি গয়না কেনা খুব বেড়ে গেল।
বাবা কখনও টাকা পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেয়নি বলে আমাদেরও ‘লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন’ এইরকমই একটা মনোভাব ছিল। সমস্ত আগাম প্রয়োজনের কথাও বাবা ভেবে রাখত আমাদের আগেই। ভারি গর্ব হত বাবার জন্য। ভাবতাম যাদের এমন বাবা নেই তারা বেচারা।
দাদা বাইরে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার জয়েন্টের রেজাল্ট বেরোল। নির্বাণের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জয়েন্টের টিউশনে। ও যে মেডিকেলে চান্স পাবেই তা নিয়ে কারওর সন্দেহ ছিল না। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম বাবার জোরে।
বাবা বলত— তুই শুধু পড়াশোনা করে যা। বাকি ভাবনা আমার।
সেইজন্য আমি জানতাম আমরা একসঙ্গে একই কলেজে পড়ব। রেজাল্টের আগেই নির্বাণকে নিয়ে বাবার নার্সিংহোমে এসেছিলাম। এত দূরে চলে এসেছি বলেই এখন প্রত্যেকের কথার ভেতরে যে আরও কথা ছিল সেগুলো বুঝতে পারি। আসলে অমোঘ বলে কোনো কিছু হয় না। জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গেই সবকিছু পরিবর্তনশীল। যদি আজ আমি ওখানেই থাকতাম, যা যা ভাবা হয়েছিল সব যদি সেইভাবেই ঘটত তাহলে তাহলে আজ আমাকেও হাতড়ে হাতড়ে মানে খুঁজতে হত না।
নির্বাণ নার্সিংহোমটা দেখতে দেখতে কেমন স্বপ্নালু হয়ে উঠেছিল— আমি আর তুমি মিলে আরও বড় করব একে। একেবারে মডার্ন করে ফেলব।
সব দেখা হলে পর বাবার চেম্বারে বসে কোল্ড ড্রিংক খেতে খেতে নির্বাণ বিজ্ঞের মতো বাবাকে বলল— আস্তে আস্তে সব পেশেন্টস হিস্ট্রি কম্পুটারাইজড করে ফেলুন। অনেক সুবিধে হবে।
বাবা মৃদু হেসে বললেন— অনেকটা করা হয়। তবে দেখো, এটা তো একটা ব্যবসাও বটে। নিজে যখন যোগ দেবে বুঝতে পারবে কোথায় কতটা জল মেশাতে হবে।
নির্বাণের কতটা আগ্রহ কীসের জন্য, বাবার ব্যবসায় কতটা জল কতটা দুধ এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মত তুখোড় মাথা আমার কোনোদিনই ছিল না। নয়তো বীনাপানির ব্যাপারটা থেকে অন্তত আমার কিছুটা আঁচ করা উচিত ছিল। সে অবশ্য আরও অনেক পরের কথা।
সেদিন আমরা জেঠুদের তিনতলায় জেঠুদের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলাম। জেঠু আমাদের দু’জনকে দুটো দামি কলম দিয়ে বলেছিলেন— এখন থেকেই ভিজিট দিয়ে বুক করে রাখলাম। তোদের ভরসাতেই আছি।
জেঠিমা দারুণ সব রান্না করতেন। বরাবরের মতো দেখা হলেই কিছু না কিছু রান্না গুছিয়ে আমার হাতে দিয়ে দিতেন। সেদিনও দিতে দিতে বললেন— জানিস না তো একদিন কী কাণ্ড— বসিরহাট থেকে আসা একটা বৌয়ের মরা ছেলে হয়েছে। কী আছাড়ি পিছাড়ি কান্না তার।
আহা রে, খুব কষ্ট হল।
জেঠিমা বললেন— সেই মেয়েকে কেউ বোঝাতে পারছে না— বলে মরা ছেলের মুখ না দেখে নড়বে না। নাকি স্বপ্নে দেখেছিল সেই মুখটাই কি না মিলিয়ে নেবে।
— তো দেখালে না কেন?
— পাগল নাকি? জন্মাবার আগেই যে মরা, সেই মুখ মায়ের দেখতে নেই। ওর আত্মীয়স্বজন স্বামী বুঝিয়ে পারে না। শেষে তোর বাবা এসে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল তবে সেই মেয়েকে বাড়িতে নেওয়া গেল।
নির্বাণ খুব বুঝদারের মতো বলল— অশিক্ষিত পেশেন্ট নিয়ে কাজ করার সুবিধে-অসুবিধে দুই-ই আছে।
আমার তখন সন্তানহারা মায়ের বেদনা বুঝবার মন বা সময় কোনোটাই নেই। জেঠিমার কাছে শুনে কয়েক মুহূর্তের খারাপ লাগা তৈরি হয়েছিল— ওইটুকুই। জেঠিমাও গোটা ঘটনাটার নাটকীয়তায় বিহ্বল উত্তেজিত। অতএব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ান্তরে যেতে অসুবিধে হল না।
রেজাল্ট বেরোল যথাসময়ে। দেখা গেল কলকাতার কলেজগুলোতে আমার হবে না। নির্বাণের সঙ্গে এক কলেজে হল না ভেবে মন খারাপ হলেও নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম অন্য রাজ্যে বা জেলায় যেখানেই হোক চলে যাব।
পাড়ার বেকার ছেলেদের রক থেকে মন্তব্য উড়ে আসতে লাগল মাঝে মাঝেই।
— কাঁদে না খুকুমণি। বাবা ঝাঁ চকচকে হোমিওপ্যাথি চেম্বার বানিয়ে দেবে।
— খুকুমণির বে’তে সাদা কোট আর স্টেথো দেব আমরা চাঁদা তুলে।
কোথায় কত টাকা ঢেলে বাবা ভর্তির পথ সুগম করেছিল জানি না। নির্বাণের সঙ্গে একই কলেজে আমারও হয়ে গেল। এইবার কিন্তু আমার মনে হয়েছিল বাবার ওপরে আমি অযথা চাপ সৃষ্টি করছি। নির্বাণকে সে কথা বলায় ও বলেছিল— এই টাকা তুমি অনায়াসেই শোধ করে দিতে পারবে।
আমাদের নার্সিংহোম, বাবার পসার প্রতিপত্তি আমার থেকেও নির্বাণকে বেশি স্বস্তি দিয়েছিল।
কোনো সমস্যা ছাড়াই চার বছর হাওয়ায় উড়ে গেল। চারপাশে কত সংকট। আমাদের অন্য সতীর্থরা যখন অনিশ্চয়তায় ভুগছে আমার চারপাশে তখন শুধুই সুখ আর আনন্দ। এর সবটুকু কৃতিত্ব অবশ্য বাবারই পাওনা।
একবার ছুটিতে বাবা আমাকে আর নির্বানকে দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের ভবিষ্যৎ আস্তানা। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত আবাসনে তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট। বাবা বলল— হায়ার স্টাডিজ শেষ করতে করতে তোমাদের চেম্বারও রেডি হয়ে যাবে। নার্সিংহোম তো রইলই।
নির্বাণ কলকাতাতেই এমডি-তে চান্স পেয়ে গেল। আমাকে বলল— তোমার জন্যই আমি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করতে পারছি। নয়তো আমার বাড়ির যা অবস্থা, পড়াশোনা ফেলে আমাকে চাকরি খুঁজতে হত।
আমাদের সবার মতো নির্বাণও ক্রমশ বাবানির্ভর হয়ে উঠছিল। আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই জানতাম কোনো একসময়ে আমরা দু’জনেই বিদেশে যাব। বাবাই সে সব পথ মসৃণ করে রাখবে। আপাতত আমার আর পড়াশোনা ভালো লাগছিল না। নির্বান যত খুশি পড়াশোনা করুক, আমি ইন্টার্নশিপ শেষ করে বাঁধা সময়ের চাকরী করব সেটাই আমার ইচ্ছে।
আমি ইন্টার্নশিপ শুরু করলাম দক্ষিণে। যথারীতি বাবারই ব্যবস্থা, বাবারই সিদ্ধান্ত।বাবা বলল— দু’-তিন বছর বাইরে থাক। সেটাই ভালো হবে।
মাঝে মাঝেই চলে আসতাম কলকাতার টানে। এখন মনে হয় এক-একবার এক-একটা ঘটনা ঘটছিল আমার চোখের সামনেই। কিন্তু আমি যেন জেগে ঘুমোচ্ছিলাম। বীনাপাণির ঘটনাটাও সেইরকম।
আমাদের আবাসনের পেছন দিকে যেখানে পাম্পঘর ইত্যাদি আর যত হাবিজাবি জিনিসের মেলা সেখানে কেয়ারটেকার নারায়ণ ছাড়া আর কেউই যেত না। সেখানেই তার ছোট্ট কোয়ার্টার। নারায়ণের বাড়ি উড়িষ্যার বর্ডারে কোন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে। কাছেপিঠে স্কুল নেই বলে ছেলেকে এখানে এনে রেখেছিল। বছর দশেকের রোগা জিরজিরে ছেলেটা খাকি প্যান্ট সাদা জামা পরে পিঠে ব্যাগ নিয়ে কাছেই একটা কর্পোরেশন স্কুলে পড়তে যেত। সেই সময়েই কখনও দেখেছি। চোখে না পড়লে জানতেও পারতাম না পেছনদিকে একটা ছোট ছেলে থাকে। প্রায় অশরীরীর মতো নীরব ছিল তার অস্তিত্ব। ছেলেকে নিয়ে নারায়ণ বছরে একবার একমাসের জন্য দেশে যেত।
তারপর কবে যে সে খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে, সঙ্গে ভাইকেও দেখাশোনা করার জন্য মেয়েকে নিয়ে এল আমরা কেউ জানতেও পারিনি। আমার অবশ্য আপন ভুবনের বাইরে কিছু জানার ধৈর্য, ইচ্ছে, সময়, সহানুভূতি কোনোটাই ছিল না।
আমার আর নির্বাণের তখন থেকে থেকেই নির্জনতা দরকার হয়। সারাদিন একসঙ্গে কাটানোর পর চুমু খাওয়ার জন্য আমরা আবাসনের পেছন দিকে এসেছিলাম বলে বীনাপাণিকে দেখতে পেয়েছিলাম। দু’হাঁটু জড়ো করে তার ওপর মুখ রেখে বসেছিল। পনেরো-ষোল বছর বয়স। হাতে সিটি গোল্ডের চুড়ি। চুল বিনুনি বাঁধা। আমাদের দেখে মুখ তুলে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল খুব আস্তে আস্তে। অত বিষণ্ণ মুখ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম— তুমি কে?
— বীনাপাণি।
— নারায়ণের মেয়ে?
মেয়েটি শুধু ঘাড় নাড়ল।
— তোমার ভাই কোথায়?
— স্কুলে।
— তুমি যাও না স্কুলে?
মেয়েটি নেতিবাচক ঘাড় নেড়ে ঘরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নির্বাণ বলল— এরা ছেলের জন্য করে কিন্তু মেয়ের এডুকেশনের ব্যাপারে সিরিয়াস নয়।
সেদিন চুমু খাওয়াটা কেন জানি জমল না। আমি মেয়ে বলেই বোধহয় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বীণাপাণির গভীর বিষণ্ণতা আমার নিরেট আত্মসুখী মনের দেয়ালে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল।
তারপর বীণাপাণির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।
তিনমাস বাদে আবার কিসের একটা ছুটিতে এসে দেখি নারায়ণ ঘন ঘন বাবার সঙ্গে দেখা করছে। কী বিষয়ে কথা তা বুঝতে পারছি না তবে সে যে খুবই চিন্তান্বিত তা বোঝা যায়। কেন জানি না মনে হল এর সঙ্গে বীনাপাণির সম্পর্ক আছে। শুধু কৌতূহলবশতই গেলাম একদিন পেছনদিকে। দেখি বীনাপাণি শুয়ে আছে পেছন ফিরে। শরীরটা আরও রোগা তা সত্ত্বেও কোমরের কাছের ফোলা ভাবটা চোখে পড়ল। বুকটা কিরকম যেন ধকধক করছিল। রাতে বাবাকে বললাম— বাবা বীনাপাণি প্রেগন্যান্ট?
বাবা আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল— তুই চিনিস নাকি ওকে?
— হ্যাঁ গতবার যখন এসেছিলাম তখন দেখা হয়েছিল।
— আর বলিস না। নারায়ণ সাতকাজে ব্যস্ত। নিজেরটা কোনোরকমে চালিয়ে নিতে পারে কিন্তু ঘাড়ের ওপর কচি ছেলে, তার স্কুল, টিফিন, খাওয়া-দাওয়া। তাই বাড়ি থেকেই বলল মেয়েও পড়ুক এখানে আর বাপ-ভাইয়েরও দেখভাল করুক। সেই মেয়ে কোথায় কার সঙ্গে মিশে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। মাঝখান থেকে নারায়ণ পড়েছে বিপদে।
— নারায়ণের বিপদ কেন?
— বাহ, বাড়িতেও তো পাঠাতে পারবে না এই অবস্থায়। দেশ গাঁয়ে বদনাম হয়ে যাবে না?
আমি খুব আশ্চর্য হয়ে বললাম— ব্যাপারটা খুবই আনফরচুনেট ঠিকই, কিন্তু এই অবস্থায় পাঠাবে কেন? অ্যাবর্শন করে দাও।
— করা যাচ্ছে না।
— কেন?
— বেশ অ্যাডভান্স স্টেজেই ধরা পড়েছে। তারপর শরীরের যা অবস্থা—
বাবা কথা শেষ করতে চাইছিল তাড়াতাড়ি।
— তাহলে ছেলেটাকে ধরে বিয়ে দিয়ে দাও— আমিও নাছোড়বান্দা ।
— মুশকিল হল মেয়েটা মুখ টিপে আছে। কারওর নাম বলছে না।
— তাহলে কী করবে এখন?
— যতটা পারি ওষুধপত্র দিয়ে চাঙ্গা রাখছি। ভালো খাওয়া-দাওয়া যেন করে, সেই জন্য নারায়ণকে টাকা দিয়ে একটু সাহায্য করছি, বাচ্চাটা হলে পর কোন অ্যাডপশন সেন্টারে দিয়ে দেব। ও দেশে ফিরে যাবে। ঘটনাটা কেউ জানবে না। সময়মতো বিয়ে-থা হয়ে যাবে। এর বেশি আর কী করতে পারি বল।
বাবার জন্য গর্বে আনন্দে বুকের মধ্যে ছলছল করছিল। এমন যার বাবা তার আর চিন্তা কী?
সেবারই নার্সিংহোমে অমলাপিসির বদলে বেশ কেতাদুরস্ত একটি মেয়েকে দেখলাম অফিসে। বাবা বলেনি কেন এত বড় কথাটা?
বাবাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলল— অমলা নিজেই আর কাজ করতে চাইল না। সুগারে শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছিল। আমিও দেখলাম নার্সিংয়ের জন্য অন্য লোক রেখে কম্পিউটার জানা লোক হলে ভালো। পাপিয়া কাজ করছে দু’ মাস হয়ে গেল। ভালোই করছে।
বাবার কাছে অমলাপিসির ফোন নম্বর চাইলাম।বাবা বলল— অমলা ভাইয়ের কাছে ভিলাই চলে গেছে। নতুন নম্বর নিয়ে ফোন করবে বলেছিল। করেনি এখনও।
— আশ্চর্য! কী করে এখন কনট্যাক্ট করবে?
আমার কীরকম যেন অদ্ভুত লাগছিল।
বাবা বলল— ভাবিস না। তোর বিয়ের সময় গোয়েন্দা লাগিয়ে ধরে আনব।
হো হো করে বাবার প্রাণখোলা হাসির তোড়ে অস্বস্তির কাঠকুটো উড়ে যায়। তবে নার্সিংহোমের নতুন মেয়েটার মতো এবারই বাবার হাতে প্রথম বিপত্তারিণীর লালসুতো আর গ্রহদোষ কাটানোর আংটি দেখি।
কাঁচা আম কচকচ করে চিবিয়ে খেলে দাঁতটা কেমন টকে থাকে কিছুক্ষণ। বলার মতো নয় কিন্তু চিবোতে গেলে প্রতি মুহূর্তে জানান দেয়। আমার অবস্থা ঠিক সেরকম। বাবাকে অন্যরকম লাগছে, কিন্তু সেটা এত সূক্ষ যে একেবারেই বলার মতো নয়। মাকে একটু বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম—নার্সিংহোমে পাপিয়া বলে নতুন যে মেয়েটা জয়েন করেছ দেখেছ?
— হ্যাঁ। বাড়িতে তো এল বেশ ক’বার।
— কেমন মেয়েটা?
— তোর বাবা তো বলে বেশ ভালো।
— অমলাপিসি না থাকায় অসুবিধে হচ্ছে না?
— অসুবিধে হচ্ছে না নিশ্চয়ই।
মা শাড়ি গয়নার বদলে আরও কোনো দামি জিনিস হারাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। অমলাপিসি যেন জাস্ট উবে গেল।
রিসেপশনের পাপিয়ার সঙ্গে অমলাপিসির নিরুদ্দেশ হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে বলে একটা কূট সন্দেহ বিষ ছড়াচ্ছিল আমার মনের গোপন কোণে। ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল পাপিয়ার আগমন আমাদের জন্য শুভ হতে পারে না।
কিন্তু বীনাপাণির ঘটনাটাও তো মিথ্যে নয়। সেই দিলদরিয়া উদার দয়ালু মানুষটা তো একই আছে। একদিন এমনি কৌতূহল বশতই গেলাম পেছন দিকে। বীনাপাণি ভাইয়ের সঙ্গে বাইরে বসে একই বাটি থেকে মুড়ি খাচ্ছিল। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কেমন আছ? ঠিকমতো খাচ্ছ-টাচ্ছ তো?
বীনাপাণি কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি আরও কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করলাম। কেন জানি না ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব, নিদেন কথাবার্তা বলার মত একটা জায়গায় আসতে খুব ইচ্ছে করছিল।
বীনাপাণি ঘরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে আমার দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে যে পরিমাণ ঘেন্না মিশেছিল তা যদি আমাকে স্পর্শ করত আমি পুড়ে শেষ হয়ে যেতাম।
কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না আমার ওপর ওর এত বিদ্বেষ কেন?
বীনাপাণির কথা আমি কারওকে বলতে পারিনি। শুধু মনের মধ্যে এক নিদারুণ অস্বস্তি আমাকে থেকে থেকে আনমনা করে দিত। পাতলা মেঘের মতো একটা ভাবনা মনের মধ্যে ভেসে যেত—বীনাপাণির এই অবস্থার জন্য কে দায়ী? বাবা যা বলল সেটাই পুরো সত্যি? তাহলে আমার ওপর এই বিদ্বেষের কারণ কী? বাবা কি কোনোভাবে জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে?
সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপরের মনটা সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠত— পাগল হয়েছ নাকি যে এইসব উল্টোপাল্টা ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ?
নিজের মনকে চোখ ঠেরে রাখতাম। যদি সেই মুহূর্তেই ঘটনার তলায় ডুব দিতাম তাহলে সত্যটা অনেক আগেই জেনে যেতাম।
বীনাপাণির ঘটনাটা যদি উড়িয়েও দিই পাপিয়ার ঘটনাটা কিন্তু লেগেই রইল আমার সঙ্গে।
এদিকে বাড়িতে সব কিছুই কিন্তু ঠিকঠাক। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একই রকম মাথা ঘামানো। মাকে কখনওই বাবার সচিব সখী মনে হয়নি। প্রিয় শিষ্যাও নয়। লীলা সহচরী হিসেবে কেমন ছিল তা সন্তান হিসেবে আমার জানার কথা নয়। আমার মনে হত বাবা মাকে বাচ্চা মেয়ের মতো ট্রিট করেছে বরাবর। নির্বাণ বা আমার সঙ্গেও যতটা সিরিয়াস ছিল, মা তার ধারে-কাছেও আসে না। মা যেন স্ত্রী নয়, আবদার করার একজন, বাবা যেটা প্রচণ্ড উপভোগ করত। এখন মনে হয় আমার পরিচিত কারওকে মার মতো শাড়ি ও গয়না নিয়ে এত উন্মত্ত হতে দেখিনি। প্রাণহীন সোনালী ধাতুর আদর দেখে মনে হত তারা যেন জ্যান্ত। ওগুলো যে খুব শিল্পসম্মত ছিল এমন নয়। ভারি মোটা ওজনদার গয়নার দিকেই মার ঝোঁক ছিল। শাড়িও তা-ই। আমার কেনা আরামদায়ক নিষ্প্রভ রঙের শাড়িগুলো দেখে মা নাক সিঁটকে বলত— দেখে মনে হচ্ছে সাতবাসি পুরোনো কাপড়।
— কিন্তু হাত দিয়ে দেখ, কী আরাম। সাধে অত দাম নিয়েছে? গরমেও পরতে পারবে। সিল্ক তো শীতে ছাড়া পরা যায় না।
— দুর, যদি দেখামাত্রই কেউ দামটা না বুঝল তাহলে আর মজা কী?
আমার দাদুর বাড়ি গরিব না হলেও বড়লোক ছিল না। গৌরবর্ণা সুন্দরী মেয়ের বিয়ের বাজারে দর চড়া বলেই ডাক্তার পাত্র পেতে অসুবিধে হয়নি। দাদুর একটা কথা আজ খুব মনে পড়ে— আরে ডাক্তার বাড়িতে বসে প্রেসক্রিপশন লিখলেও পয়সা পায়।
কোনও মহৎ পেশার মানুষের সঙ্গে দাদু মেয়ের বিয়ে দেননি। দিয়েছিলেন নিষ্ক্রিয় থাকলেও রোজগার হবে এমন নিশ্চিন্ততার সঙ্গে। মার মনেও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সেটা চারিয়ে গিয়েছিল। তাল তাল সোনা হয়ে সেই নিশ্চিন্ততা মার লকারে বিরাজ করত। পরিবার অন্ত প্রাণ বাবারও তাতে অগাধ প্রশ্রয় ছিল।
এখন মনে হয় এই সময়টাই ছিল বাবার জীবনের সবথেকে ভালো, সবথেকে নিশ্চিন্ততার সময়। নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের শেষ উজ্জ্বলতার সময়টুকু।
দাদা বিদেশে স্বনির্ভর। বাবা টাকা পাঠানোর দায়মুক্ত। আমার কর্মজীবন শুরু হতে আর দেরি নেই। উপযুক্ত মানুষও অপেক্ষা করছে পাণিগ্রহণের জন্য। সেই গর্ব আনন্দ ফুটে বেরোত বাবার কথায়। বাবার প্র্যাকটিস ফুলেফেঁপে উঠেছে। মা আরও বেশি পতিব্রতা। স্বামীর কল্যাণ কামনায় পুজোআচ্চা বেড়ে গিয়েছে দ্বিগুণ।
হাসি পায় ভাবলে। মা বলত বটে বাবার জন্য। আসলে এগুলো সবই নিজের জন্য। আমাদের চারপাশ যেন এইভাবে একইরকম থাকে তার জন্যই তো যত দৈবশক্তির পায়ে মাথা কোটা, সোনার তুলসীপাতা, রূপোর বাঁশি আরও কত কিছু।
ছুটির শেষ দিন বাবা আমাদের নিয়ে গেল একটা খুব ফ্যান্সি রেস্তোরাঁয়। ভালো লাগার সঙ্গে বুকের মধ্যে বিষাক্ত সাপটা মাথা তুলছিল— আমার সাদাসিধে বাবা জানল কী করে এই জায়গার কথা? মনে হচ্ছে আগে অনেকবার এসেছে। মা-ও তো আমারই মতো প্রথম এল। তাহলে কার সঙ্গে এসেছিল?
না থাকতে পেরে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম। বাবা বলল— আমার এক পেশেন্ট বাচ্চা হওয়ার পর এখানে ট্রিট দিয়েছিল। তখন থেকে ভেবে রেখেছি, তুই এলে নিয়ে আসব। খুব ভুল হল। নির্বাণকেও বললে হত।
সেই চিরচেনা বাবা। নিজের নোংরা মনটার জন্য নিজেকে চড় লাগাতে ইচ্ছে করে। রেস্তোরাঁর বাইরে তারাভরা আকাশের নীচে আমরা তিনজন দাঁড়িয়েছিলাম। বসন্তের মন কেমন করা বাতাস বইছিল। আমি হঠাৎ বাবাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললাম। বাবা কী বুঝল কে জানে— কোনও কথা না বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখল শান্ত হওয়া পর্যন্ত, যেন দিশেহারা নৌকোটাকে শক্ত করে ধরে পাড়ে নিয়ে এল।
তখনও জানি না এটাই শেষ রাত— আমাদের শান্ত সুখী জীবনটা এরপরই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এভাবে বাবাকে আর কোনোদিন পাব না।
দুপুরে হাসপাতাল ক্যান্টিনে কোনোরকমে দুপুরের খাওয়া সারি। রাতের খাওয়া বাড়ির ডাইনিং টেবিলে বসে আরাম করে খাই। যেখানে পিজিতে থাকি, সেই মাসিমার তখন টিভি টাইম। সেই সময় বাংলা চ্যানেলে কলকাতার যত খবর তার সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির অধঃপতন নিয়ে গলাবাজি— ঠিক মনে হয় কলকাতাতেই বসে আছি। সারাদিন বিজাতীয় ভাষার মধ্যে কাটাবার পর এই সময়টার জন্য আমিও মুখিয়ে থাকি। সব ছাপিয়ে বাংলা ভাষা যেন কানে মধু ঢেলে দেয়।
রাত্রিবেলা নির্বাণের সঙ্গে কথা হয়। বেশিরভাগই কাজের কথা। প্রেমপর্ব এত লম্বা হলে যা হয়। রোমাঞ্চর বদলে অভ্যেসটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।
এইরকম এক দিনে টিভিতে ব্রেকিং নিউজে দেখি হরিনাভির কোন একটা নার্সিংহোম থেকে অমলাপিসিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। সংবাদ পাঠিকা চূড়ান্ত নাটকীয়ভাবে বারবার করে যা বলছে তা হল এই নার্সিংহোমের ভারপ্রাপ্ত অমলা চক্রবর্তীকে বাচ্চা পাচার চক্রের একজন মূল চাঁই হিসেবে গ্রেপ্তার করা হল। এই নার্সিংহোম চোরাই বাচ্চাদের আড়ত। এখান থেকে উনিশটি সদ্যোজাতকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর পেছনে আরও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত আছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এই কথাগুলোর সঙ্গে অমলাপিসির মুখ ঢাকা ছবিটা বারবার দূর থেকে ছুটে এসে টিভির পর্দায় চড়া মিউজিকের সঙ্গে আছড়ে পড়ছে। আমার বুকের মধ্যে থেকেও একটা আওয়াজ উঠছে। ভয়ংকর ঘুর্ণি তুলে গুমগুম শব্দে পাড় ভেঙ্গে ছুটে চলেছে মরণ স্রোত।
ভাগ্যিস টিভির পর্দার ভয়ঙ্কর খবরটা ওঁদের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তাই আমার আচমকা উঠে পড়া কেউ লক্ষ্য করলেন না।
আসার সময় শুনলাম মাসিমা বলছেন— এদের জানোয়ার বললে জানোয়ারকে অপমান করা হয়।
ঘরে এসেই বাবাকে ফোন করলাম।
— এ কী শুনছি? অমলাপিসি এমন নোংরা কাজ করতে গেল কেন? তুমি কিছু টের পাওনি? মিথ্যে বললে কেন ভিলাইয়ে ভাইয়ের কাছে আছে?
বাবা একদম উড়িয়ে দিল— বলল আমাকে যা বলেছে আমি তাই বলেছি। ও তারপর কার খপ্পরে পড়েছে, কী করেছে, আমি কী করে জানব বল?
— তুমি কি দেখা করবে একবার? অমলাপিসি এরকম জঘন্য ক্রাইম করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না। কেউ ওকে ফাঁসাল না তো?
— পাগল হয়েছিস? আমি যাচ্ছি না ওর মধ্যে। আচ্ছা রাখি রে জরুরি অপরেশন আছে দুটো। চিন্তা করিস না। খবরে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলে হয়তো ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়।
বাবার কথাগুলো হাতে নিয়ে আমি বসেই রইলাম। পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র নিয়ে এগিয়ে আসা পরীক্ষক যতক্ষণ আমার টেবিলে না আসছেন একটা অসহায় অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আমি অন্ধকার ঘরে সেই কঠিন মুহূর্তটার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।
পরদিন হাসপাতালে বাড়িতে জরুরি অবস্থার কথা জানিয়ে মেল করে সোজা চলে গেলাম এয়ারপোর্টে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে তৎকালে টিকিট কেটে চলে এলাম কলকাতা। বাবা আমাকে দেখে মাথার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলল— তুই সত্যি একটা পাগলি।
বাবার কথাবার্তা আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। মা-কে হাঁকডাক করে আমার প্রিয় জিনিস বাজার করাবার কথা মনে করাল। আর আমাকে বলল— তুই এসেছিস এটা খুবই প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ। ভাগ্যিস টিভি নিউজ দেখলি, নয়তো আসতিস না। ক’দিন থাকবি?
— দেখি।
— তুই এসেছিস নির্বাণ জানে? এর মধ্যে আমার সঙ্গে ওর কথা হয়েছে। পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর। খুব ব্যস্ত।
আমি চুপ করে রইলাম। এখন মনে হচ্ছে এভাবে চলে আসাটা খুবই হঠকারিতা হয়েছে। নির্বাণকে বললেই এই শেষ মুহূর্তে ছুটি নেবার কুফল সম্বন্ধে একগাদা জ্ঞান শুনতে হবে।
অপ্রস্তুত হেসে বাবাকে বললাম— কী জানি হঠাৎ মাথায় পোকা নড়ে উঠল। কালই চলে যাব।
— দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল।
বাবা বেরিয়ে গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম— বাবাকে একটু শুকনো লাগছে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছে?
মা নতুন কেনা গয়নাটা দেখাতে দেখাতে বলল— ক’দিন খুব ব্যস্ত। রুগীর প্রেশার বেড়েই চলেছে।
আমার অবস্থা যেন খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর। পরশপাথরের সঙ্গে উপমাটা ঠিক হল না জানি। কিন্তু কী করব? এ ছাড়া আর কিছু মনে এল না। কী যে খুঁজছি জানি না, কোথায় পাব জানি না। কেবল মনে হচ্ছে এই নিস্তরঙ্গ পর্দার ওপারে কি যেন আছে। আমি শুধু তার বিজাতীয় সংকেত পাচ্ছি। যার মানে আমি নিজেই জানি না।
কোনও মানেই হয় না, তবু মা-কে জিজ্ঞাসা করলাম— নারায়ণের মেয়ে কেমন আছে জানো?
ভেবেছিলাম মা অবাক হয়ে আমাকেই জিজ্ঞেস করবে— কার মেয়ে? নারায়ণের আবার মেয়ে আছে নাকি?
আমাকে অবাক করে মা বলল— ছেলে হতে গিয়ে সে তো প্রায় যায় যায়। নারায়ণ কান্নাকাটি করছিল বলে জানলাম। সেই মেয়ে নাকি বাপের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চায় না আর। চাকরি করে ছেলে মানুষ করবে গোঁ ধরায় তোর বাবা নতুন নার্সিংহোমে তার কাজ ঠিক করে দিয়েছে। বাপ অনেক সাধাসাধি করেও আনতে পারেনি।
— বাচ্চাটা কোথায়? তাকে নিয়ে তো আর চাকরি করতে পারবে না।
— আপাতত একটা হোমে আছে। পাঁচবছর হলে নিজের কাছে নিয়ে আসবে। নারায়ণ তো বলল ছুটির দিনে গিয়ে ছেলের সঙ্গে কাটিয়ে আসে।
আবার নিজের গালে চড় কসালাম। বাবা আর কত পরীক্ষা দেবে?
ঠিক পাঁচদিন পর ভোর বেলা ফোনটা এল। মা-র হাউমাউ কান্না চিৎকার থেকে আমি এটুকু বুঝলাম কিছুক্ষণ আগে পুলিশের এক বিরাট দল বাচ্চা পাচার কেসের সঙ্গে বাবার যোগ আছে সন্দেহ করে বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার আর কিছু ভাবার সময় ছিল না। হাতব্যাগ নিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে।
তারপরের কয়েকটা ঘণ্টার কথা আমার সত্যি মনে নেই। মাত্র কয়েক দিন আগে বাবার বলা কথাগুলো মাথার মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছিল। মিথ্যে, সব মিথ্যে। আমার বাবা এমন হতেই পারে না। এতদিনের সুনামধারী একজন ডাক্তার, যার বেশিরভাগ রোগীই হল গ্রামগঞ্জ থেকে আসা গরীব মানুষজন। যার কাজই হল শিশুকে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে মা-বাবার মুখে হাসি ফোটানো সে কেন এমন কাজ করবে? নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে। অমলাপিসির চক্রান্ত নয় তো?
বাড়িতে ঢোকামাত্র মা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। মার এরকম আলুথালু চেহারা আমি কোনোদিন দেখিনি। মা ফিসফিস করে বলল— হ্যাঁরে গয়না-টয়নাগুলোকেও গ্রেপ্তার করবে নাকি রে? কোথায় লুকোবো এত? টাকাগুলো পুড়িয়ে ফেলি চল—।
ভালো করে মার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল চোখগুলো খুব বেশিরকম জ্বলজ্বলে। গালের পেশিগুলো কাঁপছে তিরতির করে। হাতের তালু ঠান্ডা ভিজে।
এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে টিমটিমে আশার আলোটা জ্বলছিল আলমারি, লকার, তোষকের মধ্যে আরও নানা লুকোনো জায়গায় গয়নার স্তূপ, সোনার বিস্কুট আর টাকার পরিমাণ দেখে সেটা এক দমকায় নিভে গেল। যত সফল ডাক্তারই হোন না কেন সোজা পথে এই পরিমাণ সম্পদ জড়ো করা সম্ভব নয়।
বাবাকে তো সাদাসিধেই দেখেছি বরাবর। কবে থেকে এমন ভয়ঙ্কর নেশা পেয়ে বসল তাকে? একটা ছবিতে দেখেছিলাম কোণঠাসা এক ড্রাগকিং সপরিবারে পালাচ্ছিল। শিশুকন্যাকে শীতের হাত থেকে বাঁচাতে নিরুপায় হয়ে টাকার বান্ডিল জ্বালিয়ে ঘর গরম করছে। আমাদের উষ্ণ রাখার জন্যই কি এত আয়োজন?
দিশাহারা হয়ে ফোন করলাম দাদাকে। সে বলল— জানি না তুই কী করে ম্যানেজ করবি— তোর পক্ষে ডিফিকাল্ট বুঝতে পারছি কিন্তু আমাকে আর ফোন করিস না। আমি নিজেই এখানে পা রাখার জন্য যথেষ্ট স্ট্রাগল করছি, তার মধ্যে এসবের সঙ্গে কানেকশন বেরোলে শেষ হয়ে যাব।
রত্নাকরের পাপের ভাগী নই— এই ভেবে দায়িত্ব এড়াতে পারলাম না। থানায় গেলাম। হয়তো তখনও ভাবছিলাম কোনও মিরাকল ঘটবে।
ডিউটিতে থাকা অফিসার বললেন— মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। জামিন হবে না। আপনার বাবাই তো মেন অ্যাকিউজড। সলিড সব প্রমাণ। এ যা কেস, চোখ বুজে বলা যায় যাবজ্জীবন হবেই।
সেই প্রথম শুনলাম এই হাড়হিম করা কথাটা।
ঘরে-বাইরে সব সমস্যার সমাধানে যে বাবা ছিল মুশকিল আসান, এই কঠিন সংকট কালে তার চেহারাটাই দেখতে পেলাম না। তখনও ভাবছি বাবার সঙ্গে দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা গাইড করবে বরাবরের মতো। কোথাও নিশ্চয়ই একটা ভুল হচ্ছে। ঠিকমতো চিন্তা করার শক্তিও আমার ছিল না। মাথার মধ্যে তালগোল পাকানো কথা ঘটনা ছবি তাঁতের মাকুর মতো ছোটাছুটি করছিল।
এত কাছে ছিলাম বলেই কি কিছু চোখে পড়েনি? গতবার অকারণ সন্দেহে মিছিমিছি কষ্ট পেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে পাপিয়ার সঙ্গে অ্যাফেয়ারটাই হল না কেন এর বদলে?
বাড়ি ফিরে মাথা ঠান্ডা করে সবার আগে নির্বাণকে ফোন করলাম। কিছুতেই ফোন লাগল না। নির্বাণের মা থাকেন ওর দাদার সঙ্গে শিলিগুড়িতে। বাবার নতুন নার্সিংহোম শুরু হবার প্রথমদিন নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য দাদা-বৌদি এসেছিল। সেই একবারই দেখা। নির্বাণের সঙ্গেও বাড়ির যে খুব যোগাযোগ আছে এমন নয়। হঠাৎ মনে হল নির্বাণকেও আমি তেমন চিনি না। সত্যিই তো, এই ফোন নম্বর আর কয়েকটা উপহার ছাড়া সে যে আমার জীবনে ছিল তার কোন চিহ্নই নেই আমার কাছে। আমি কোনোদিন তার ঠিকানায় যাইনি। সে-ই এসেছে বরাবর। কাগজে টেলিভিশনে এতবার করে বাবাকে দেখাচ্ছে নির্বাণ জানে না হতেই পারে না। তা সত্ত্বেও যখন সে আসেনি, নিজে থেকে ফোন পর্যন্ত করেনি তখন বুঝতে হবে তার ছিঁড়ে গিয়েছে।
সেদিন শরীর মনের ক্লান্তিতে আর ভাবার দম ছিল না। পরদিন নিজের মনকে চোখ ঠেরে আশা-আশঙ্কায় দুলতে দুলতে আবারও চেষ্টা করলাম। ফোনটা একইভাবে নিথর হয়ে রইল। এবার বুঝলাম আমার নম্বরটা ব্লক করে দিয়েছে। নির্ভর করার দ্বিতীয় মানুষটিও উবে গেল রাতারাতি।
শেষ ভরসা হিসেবে জেঠুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ঘিনঘিনে ছোঁয়াচে রুগীর ভয়ে জেঠুরা দরজাই খুলল না।
নীচে নার্সিং হোমের দুটো ফ্লোর সিল করা। কয়েকটা পুলিশ গুলতানি করছে।
বরাবর শুনে এসেছি আমি পিতৃমুখি কন্যা। আমার মুখ দেখেই কি এরা বুঝে যাবে আমিই ডা. বেরার মেয়ে? ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর? বলবে এর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, শখ আহ্লাদ, এত ফুটানির ডাক্তারি পড়া— সব বাচ্চাবেচা টাকায়?
বাড়িতে মা আরও অসংলগ্ন, আরও বেসামাল। ঘর সামলাব না বাইরেটা দেখব ঠিক করতে পারছিলাম না। বাবার নামে যা কিছু, সব সিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে আমার ও মার নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও লকারগুলো তখনও পর্যন্ত ঠিকঠাক থাকায় অসুবিধে হয়নি।
প্রচুর টাকা দিয়ে একটা উকিল ঠিক করেছিলাম। কেবল মনে হচ্ছিল বাবা একবার জামিন পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
কেসের দিন কালো ভ্যান থেকে একে একে নামল পাপিয়া, অমলাপিসি, বাবা ও আরও কিছু অচেনা লোক। বাবাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল বাচ্চা হারানো মা-বাবার দল। পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিজেরাই শাস্তি দেবার জন্য তৈরি। প্রবল গোলমালের মধ্যে পুলিশের দল কোনোরকমে দলটার হাত থেকে বাবাদের বাঁচিয়ে কোর্টরুমে ঢোকাল।
জাজ কী বলবেন জানি না— সেই ক্রুদ্ধ হতাশ মানুষগুলোর কান্না জড়ানো ছিটকে আসা কথা থেকে দিনের আলোর মতো সত্যিটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।
বাবার পেশেন্ট ছিল এরা। ডাক্তারবাবু প্রায় বিনেপয়সায় চিকিৎসা করে এদের কাছে দেবতা হয়ে উঠেছিল। সেই জন্য মরা বাচ্চার কথা এরা অবিশ্বাস করেনি। সেইসব বাচ্চাকে প্রচুর টাকায় বিক্রি করা হয়েছে নিঃসন্তান দম্পতিদের কাছে। আরও অন্য কোনও ঠিকানায় গেছে কিনা তদন্তসাপেক্ষ। হরিনাভির নার্সিং হোমে অমলাপিসি চুরি করা বাচ্চাদের দেখাশোনা করত। সদ্যোজাতদের আর একটু বড় দেখিয়ে ক্রেতাদের ধোঁকা দেবার জন্য নানা ওষুধ আর ইঞ্জেকশন। পাপিয়া অনলাইনে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।
এই দলের সঙ্গে কাঠগড়ায় ছিল আর একটা লোক যাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তার নাম শুনলাম শিরীষ তলাপাত্র। সে মোটে ডাক্তারই নয়। বাবাকে নানাভাবে সাহায্য করত। তারপর বাবারই পরামর্শে সে একসময় ডাক্তার সেজে বসিরহাটে একটা ছোট ক্লিনিক খুলল। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের থেকে ঝকঝকে আর জরুরি পরিষেবা মিলত বলে ধীরে ধীরে সেটা একটা বড়সড় নার্সিংহোম হয়ে উঠেছিল। এটিও বেনামে আমার বাবারই নার্সিং হোম।
ভয়ংকর সব তথ্য। বিচারক কঠিন মুখে বললেন— যাবজ্জীবনও যথেষ্ট নয় এদের জন্য।
কেউই জামিন পেল না। পরবর্তী শুনানি তিনমাস পর।
বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়। মা ছিল নিজেকে নিয়ে আহ্লাদে গলে থাকা আত্মসুখী এক মানুষ। আচমকা মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে গেলে এইসব মানুষেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। মাকে একা এখানে কার জিম্মায় রেখে যাব? এর থেকে মা বিধবা হলে ভাল হত। আমার কাজটা সহজ হত।
উকিল বলল, দেখুন আমি আপনাকে মিথ্যে আশা দেব না। যেভাবে জাল গুটিয়ে এনেছে কোনওভাবেই জামিন পাবার সম্ভাবনা দেখছি না। বাইরের আলোও আর দেখবেন কিনা সন্দেহ।
— মানুষ তো খুন করেও ছাড়া পায়— আমি শেষ চেষ্টা করি।
— সে যদি প্রমাণ না হয়। বিপক্ষ যদি দুর্বল হয়, বেনিফিট অফ ডাউট পেতেই পারে— এখানে তো সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আদালত ছাড়ান দিলেও পাবলিক পিটিয়ে মেরে ফেলবে। উনি জেলের ভেতরেই সেফ।
উকিলও হাত ঝেড়ে ফেলল।
তখনও পর্যন্ত আমার মনের ভেতরে তিরতির করে করুণাধারা বয়ে যাচ্ছিল। আহা, কী করে জেলের ভেতরে চোর-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে রাত কাটাবে? কী খাবে? পরিচ্ছন্নতা নিয়ে পিটপিটে বাবা প্রাকৃতিক কাজগুলোই বা কী করে করবে? এই মানুষটা কত লোকের উপকারও তো করেছে তার কি কোনও দাম নেই? বাবার সুকৃতীর যদি কিছু জোর থাকে তার কাছে মাথা নত করে প্রাণপণে একটা মিরাকল প্রার্থনা করছিলাম।
কোর্ট কাছারি থেকে মন সরিয়ে এবার মায়ের দিকে মন দিলাম। একজন থেকেও নেই। আর একজন আধখানা। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধই থাকে সারাদিন। বন্ধ দরজার ওপারের দুনিয়া নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না।
দুপুর থেকে বেজায় গুমোট। দলা দলা কালো মেঘ আমার কালো ভাবনাগুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। এইরকম বর্ষাদিন মানে সেলিব্রেশন— হইচই, খিচুড়ি, ইলিশ মাছ, অগুনতি কুশনের মাঝে ডুবে গিয়ে বই পড়া গান শোনা— কবে হত এসব? পূর্বজন্মে কি?
মাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের চলার পথটির চেহারা কেমন হবে ভাবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম গেটের ধারে বীনাপাণি। মনে হল আপনজন কাউকে দেখলাম। এ অন্তত বাবার উজ্জ্বল দিকটার পরিচয় পেয়েছে। ওর কাছে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে হল, কিন্তু যাব কিনা সেটাই ঠিক করতে পারছিলাম না। ওর চোখের ঘেন্নার দৃষ্টিটা আমি আজও ভুলিনি। শেষে মনের জড়তা কাটিয়ে নীচে গেলাম। বাবার বিষয়ে অন্তত একটা ভালো শব্দের জন্য আমার ভেতরটা তৃষ্ণায় কাঁপছিল। সেই খড়কুটোটার জন্যই দৌড়োলাম। ততক্ষণে বীনাপাণি চলে যাওয়ার জন্য রাস্তা পেরিয়ে ওদিকের ফুটপাথ ধরে হাটতে শুরু করেছে। যদিও বারবার পেছন ফিরে দেখছে। কাউকে খুঁজছে, নাকি কারওর থেকে পালাচ্ছে, সেটাই বুঝতে পারছি না। আমি এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম। দূর থেকে বুঝতে পারিনি, কাছ থেকে দেখলাম কীরকম বদলে গিয়েছে বীনাপানি। ওর মুখের সেই গ্রাম্য সরলতা আর নেই। খুব টাইট অন্তর্বাস পরলে যা হয়, ব্লাউজের ছড়ানো গলার ওপর দিয়ে ঠেলে উঠেছে বুক। ব্লাউজটারও দু কাঁধ পিঠের কাছে জানালার মত ফুটো। হাত আর পায়ের নখে রঙ।
বীনাপাণি একটা মোচড় দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল— তুমি? কী মনে করে? বাবার ব্যবসাটা ধরতে এয়েচ?
বীনাপানির মুখে ওইরকম নিষ্ঠুরের মতো কথা শুনে আমার সমস্ত আশা ভরসা দপ করে নিভে গেল। গত তিন-চার দিনের টানা অনিয়ম, অনিদ্রা ও টেনশনে আমার শরীরটা হঠাৎ যেন জবাব দিল। মাথা ঘুরে পড়েই যেতাম যদি না বীনাপাণি ধরে ফেলত। কয়েক মুহূর্ত ঝাপসা অন্ধকার। জ্ঞান ফিরতে দেখি আমি বাস স্ট্যান্ডের বেঞ্চে বসে আছি আর বীনাপাণি তার খাবার জলের বোতল থেকে আমার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে। ভাগ্যিস বর্ষাদুপুর বলে রাস্তায় লোক নেই।
বীনাপাণির বোতলটা চেয়ে নিয়ে জল খেলাম এক ঢোঁক। উঠতে গিয়ে মনে হল হাত পায়ে জোর নেই। বীনাপাণি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে— কী যেন বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর গলাটা একটু নরম করে জিজ্ঞেস করল-নিজে নিজে যেতে পারবে না রাস্তা পার করে দেব?
— পারব। কিন্তু একটু বসে থাকতে ইচ্ছে করছে।
তারপর দীন কাঙালের মতো বীণাপাণিকে অনুনয় করে বললাম— তুমিও একটু বোসো না বীনাপাণি—বসবে?
একটু ইতস্তত করে সে বসল আমার পাশে। দু’জনে বসে রইলাম চুপচাপ। তারপর সে-ই প্রথম কথা বলল— তুমি সত্যি কিছু জানতে না?
— কী ব্যাপারে?
— ন্যাকা— নরম ভাব মুছে গিয়ে বীনাপাণি আবার খরখরে— তোমার বাবা গো বাবা। ইনি ছাড়া আর কে আছেন কতা বলার?
এত কিছু সামলেছি শুকনো চোখে এখন এই অনাত্মীয় অশিক্ষিত মেয়েটার কথায় ভেঙে গেল পলকা জলাধার। হু হু করে স্রোতের মতো বয়ে গেল বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা, অপমান, প্রত্যাখ্যান একসঙ্গে কত কিছু। একটু সামলে নিয়ে বীনাপাণিকে বললাম— আমি কিচ্ছু জানি না। এখানে এসে সব শুনেও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কী করে হল এমন?
— আমিও বিশ্বাস করেছিলাম। সবার কাছে শুনতাম ডাক্তারবাবু দেবতা। সে যে আসলে দানো তা জানব কেমন করে? অবিশ্যি কে নয়? তোমার বাবা, আমার বাবা—
তারপরে বীনাপাণির কাছে যা শুনেছিলাম তাতে এটা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম আমার থেকেও দুঃখী, আমার থেকেও কপালপোড়া কেউ আছে। আমার আর কিছু না থাক, শিক্ষা আছে। নাকে না কেঁদে নিজের জীবনটা নিজে গড়ে তোলার মতো ক্ষমতা আছে। একেবারে কপর্দকশূন্যও নই। একটু কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। সত্যি বলতে কি, বীণাপাণির গল্পটাই আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল।
বাবা-ভাইয়ের খাওয়ার কষ্ট বলে উড়িষ্যাঘেঁষা গণ্ডগ্রাম থেকে বীনাপাণি কলকাতায় এল বাবার সংসারে। গ্রামের স্কুলে সে এইট পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর আরও দূরে যেতে হবে বলে পড়া ছেড়ে ঘরেই বসেছিল। বিয়ে তো দিতেই হবে, তার আগে স্বামী-ছেলের সুবিধের কথা ভেবে বীনাপাণির মা তাকে পাঠাল কলকাতায়। কলকাতায় নানা জিনিস শেখার স্কুল আছে। কাজকর্ম সামলে সেরকম কোন স্কুলে ভর্তির কথাও হয়েছিল।
বীনাপাণি একঘেয়েভাবে টানা বলে যাচ্ছিল। ওর গলায় কোনো ওঠাপড়া ছিল না। ঠিক এইভাবেই সে আমাকে তার জীবনের বীভৎসতম জঘন্যতম ঘটনাটা বর্ণনা করেছিল— একদিন দুপুরে বাবা ঘরে খেতে এসে আমাকে রেপ করল। তারপর থেকে রোজ। ভাই তখন ইস্কুলে থাকত। আমি শুধু কানতাম। আমার কাছে ফোন নাই, রাস্তাঘাট চিনি না। এই নরক থেকে উদ্ধারের কোনও রাস্তাই জানি না। কবে ভাইয়ের ছুটি হবে, কবে বাড়ি যাব, গিয়েই বা কী হবে, আমার কতা কি কেউ বিশ্বেস যাবে? এসবই ভাবতাম সারাদিন।
বীনাপানির কথাগুলো আমার কান পুড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি বললাম— আমাদের কারওকে বললে না কেন? পুলিশে গেলে না কেন?
— তোমাদের কারোকে কি চিনি? তোমরা কেমন লোক, আমাকে ঘরে তুলবে কিনা— তারপরে তো বাপের ঘরেই ফিরতে হত। তাছাড়া এর মধ্যে পেটও হয়ে গেল।
বাপ গিয়ে ধরল ডাক্তারবাবুরে। মিথ্যা করে অন্য লোকের নামে দোষ দিল। আমারে পরীক্ষা করতে নিয়ে গেল ক্লিনিকে। আমি ডাক্তারবাবুর পায়ে ধরে বললাম— আমারে বাঁচাও বাপের হাত থেকে। বাচ্চাটা খসিয়ে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। তোমার কেনা হয়ে থাকব। তখনও যদি ফিরতাম আমার একটা গতি হত। কিন্তু সে পিশাচও আমারে ছাড়ল না। বাপেরে বলল— আমার শরীল ভাল নয়। দেরি করে এনেছ। এখন খসাতে গেলে বিপদ আছে। ওষুধপত্র দিল, টাকা দিল। বাপ আমারে বলল— বাচ্চাটা হলেই দেশে পাঠিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু বাচ্চাটা দিয়ে দেবে অনাথ আশ্রমে। টাকা দেবে। তোর ভালো ঘরে বিয়ে দেব। কেউ বুঝবেনি।
শুনতে শুনতে আমি শিউরে উঠছিলাম। বললাম— তোমার ভাই ছিল তো?
— ছিল তো। বাবা ওরে বললে, দিদির পেটে জল হয়েছে। কারোরে বলিস না। ভাইটা কী বুঝল কে জানে। সে একেবারে চুপ মেরে গেল।
সেইজন্যই বীণাপাণির চোখে অমন দৃষ্টি ছিল। জীবন ওকে নিয়ে যে নিষ্ঠুর খেলা খেলছিল তাতে অসহায় ঘেন্নায় ওর নির্বাক হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।
এখন ওর একঘেয়ে সুরে গুনগুন করে সেই ভয়ংকর কাণ্ডের বিবরণ শুনতে শুনতে মনে হল বীনাপাণি গীতার সেই সুখে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হয়ে থাকার আপ্তবাক্যটা সত্যি সত্যিই নিজের জীবনে আত্মস্থ করেছে আর সেভাবেই নিজের জীবনতরীটি বেয়ে চলেছে।
আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল সে কিন্তু নির্বিকারভাবেই বলে যাচ্ছিল— আমি বুজলাম ইহকাল পরকাল সব গেল। সবই যখন গেল, বাবারে বললাম— বাচ্চাটারে দিবনি। হাগাব, মোতাব, দুধ খাওয়াব। নিজের বলতে থাকুক ওই রক্তের দলাটা।
বাবা বললে— পাগল হইছিস? সবার মুখে কালি দিতে চাস? নিজে কী খাবি তার ঠিক নাই, বাচ্চা পালার শখ। ডাক্তারবাবুর দয়ার শরীল। যা বলছে তাই করতে হবে। তাতে সবার মঙ্গল।
একদিন কাকপক্ষী ডাকার আগে বাপে আমারে রেখে এল বসিরহাটের নার্সিংহোমে। সেখানে নানা জায়গা থেকে বাচ্চা হতে আসা মেয়েদের দেখলাম। একটা হোম থেকে এসেছিল বিন্দু। সুখ-দুঃখের কথা কইতাম। সে বলেছিল— এই নিয়ে দু’বার এলাম। তোরেও এখান থেকে নিয়ে যাবে হোমে। যার কেউ নেই তার জন্য স্বনিভ্ভর হোম আছে। খাওয়া দাওয়া পাবি। শাড়ি, বেলাউজ, কাজল লিপস্টিকও। আর মাঝে মাঝে নার্সিংহোম। তুইও আসবি আবার, কিন্তু বাচ্চা পাবি না কোনদিন। আমি লাইন করে রেখেছি। এইবার পালাব। খদ্দের যদি বসাবই তবে আর মিনি মাগনা নয়। নিজের ইচ্ছেয় পয়সা নিয়েই বসাব।
আমি বললাম— বাবা বলেছে বাচ্চাটা হয়ে গেলে আমারে দেশে পাঠায়ে দেবে।
বিন্দু গা মুচড়ে বলে— দেখ কী হয়।
বাচ্চা হবার সময় কী সব সমিস্যে হল। ডাক্তারবাবু বলল— আমার কাঁকাল নাকি ছোট। শরীল পাকেনি পুরো। পেট কাটতি হল। অনেক রক্ত গেল। শরীল খুব দুব্বল। উঠতি পারি না খেতি পারি না। বাপেরে বললাম— মার কাছে যাব।
বাপ ঝামড়ে উঠে বলে— পেটে সেলাইয়ের দাগ নিয়ে কোন মুখে যাবি? এমনি এমনি হত তো নে যেতাম।
বিন্দুর কথাই ঠিক হল। ওখান থেকে হোম। কতরকম মেয়ে যে দেখলাম। ডাঁশা মেয়েগুলোর আদর আছে। ভালো খাওয়াদাওয়া, পাউডার পমেটম। রাত বিরেতে নানারকম লোক আসে। কখনও আবার গাড়ি আসে। চালাকচতুর মেয়েগুলো বাইরে থেকে ঘুরে আসে।
মরার কথাও ভেবেছি অনেকবার। সাধ্যে কুলোয়নি গো। বিন্দু বোঝাত— মরবি কেন? তুই মরলে কার ক্ষতি? তোর নিজের জন্মদাতা তোকে রেয়াত করেনি। ওদের মুখে লাথি মেরে নিজের জীবন নিজের মতো চালাবি। নিজের গতর বেচা টাকায় খাবি। কার কী বলার আছে?
শরীল যদ্দিন সারেনি দাঁতে দাঁত চিপে রইলাম। তারপর পালালাম বিন্দুর সঙ্গে। ওদের সঙ্গেই আছি এখন ইছাপুর কারখানার পেছনে। যা করি নিজের ইচ্ছেয়।
— মাকে খুলে বললে না কেন সবকিছু।
— একদিন ফোন করেছিলাম। মা বলল— বাপের কাছে সব শুনিচি। কার সঙ্গে লটঘট করে পেট বাঁধিয়ে ঘর ছেড়েছিস আমি আর কিছু জানতে চাই না। আমার কাছে তুই মরা। খবরদার এদিকে আসবি না।
— তো এতদিন বাদে হঠাৎ এখানে এলে কেন?
— টিভিতে দেখলাম ডাক্তারবাবুরে পুলিশ ধরেছে। ভাবলাম আমার বাপটাই বা বাদ যায় কেন? তখন সাহস হয়নি, এখন থানায় গেলে কেউ অবিশ্বেস করবেনি। পেটের কাটা দাগ দেখাব। ডাক্তারবাবু একন গত্তে পড়েছে। পুলিশের কোঁৎকা খেলে বাপ বাপ বলে সব স্বীকার যাবে। এখানে এসে মনে হল বাপ জেলে গেলে মা-টা না খেয়ে মরবে। ভাইটার পড়াশুনা বন্দ হবে। গুন্ডা-বদমাশ হয়ে যাবে শেষে। আমার তো যা গেছে, তা তো আর ফিরবেনি। এদের জীবনটা ছাই করি কেন? তাই কেউ দেখে ফেলার আগেই—
বীনাপাণি কথা শেষ না করেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল— যাই। বিন্দুরাও এসেছে। শেয়ালদায় রথের মেলা বসেছে। সেখেনে যাব সবাই মিলে।
যাওয়ার আগে আমাকে সে একখানা মোক্ষম কথা বলে গেল— দিদি আমি কিন্তু এখন বেশ ভালোই আছি। তুমিও এই পিচেশগুলোর কথা ভুলে ভালো থাকার চেষ্টা করো। তোমার পেটে বিদ্যে আছে, তোমার ভয় কী?
হাজার চেষ্টা করেও যা হচ্ছিল না অশিক্ষিত বীনাপাণির কথায় তা হল। এক দমকায় মনের ধুলোবালি উড়ে গেল। সত্যিই তো, বীনাপাণির তুলনায় আমি তো ভাগ্যবান। আমাদের জীবনটা যদি একটা স্কেল হয় সবসময় দেখা যায় আমার নীচে আরও কত মানুষ। আমার বাবার অপরাধের সীমা নেই কিন্তু বীনাপানির বাবার মতো আত্মজার হাড়মাংস চিবিয়ে তো খায়নি। তারপরেও বীনাপাণি রথের মেলায় যাচ্ছে। তারপরেও মা-ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় নিজেকে দূরে সরিয়ে নিল কেমন শান্তভাবে।
ঘ্যানঘ্যানে কান্না মুছে ফেলে বাস্তবের দিকে তাকালাম। মা-কে এখানে রাখা যাবে না। টাকা-পয়সা যতদূর সম্ভব ট্রান্সফার করলাম আমার আর মার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। বাবার নামে যা কিছু ছিল সেগুলো আর নার্সিংহোম ক্লিনিক সব লাল ফিতের ফাঁসে বন্দি। আমার অবশ্য দরকারও নেই সেসবের।
ভালোবাসার কলকাতা নরক হয়ে উঠেছিল। থানায় জানালাম— চাকরি ফেলে এভাবে আর থাকতে পারছি না। আসলে আমি পালাতে চাইছিলাম দূরে, বহু দূরে। যেখানে কেউ আমাকে বাবার মেয়ে বলে চিনবে না। পিতৃমুখী মেয়ে শুনেছি সুখী হয়। আমি বিশ্বাসও করতাম কথাটা। এখন মুখটা ক্ষতবিক্ষত করে বদলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।
থানায় ঠিকানা রেখে কাজের জায়গায় ফিরলাম মাকে নিয়ে। নতুন বাড়িতে নতুন পরিচয়ে মাকে নিয়ে শুরু হল অন্য জীবন। বীনাপাণি ঠিকই বলেছিল— পেটে বিদ্যে থাকলে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সবথেকে বড় অবলম্বন। বিদ্যে নামক পরম ধনটি পেয়েছি বাবারই দয়ায়। সেটা মনে করেও অসহায় রাগে ধিকিধিকি পুড়ত ভেতরটা।
খাওয়া পরার চিন্তা আমার ছিল না। কিন্তু ভুলে থাকার জন্য কাজই ছিল একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। যতদিন মা ছিল, আগের জীবন কলকাতা এদের ভুলতে চাইলেও ভোলা যেত না। মা-ই হঠাৎ হঠাৎ এমন সব কথা বলে বসত ভেতরটা ঝনঝন করে উঠত। ক্রমশ অবস্থা আরও খারাপ হল। মাকে বাড়িতে আর রাখা গেল না। না চাইলেও শেষপর্যন্ত অ্যাসাইলামেই দিতে হয়েছিল। ওখানে গিয়েও আর বেশিদিন বাঁচেনি। আমিও ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে আরও দূরে কোচি চলে এলাম।
নির্বাণ যেমন একধাক্কায় দূরে মিলিয়ে গিয়েছিল তেমনই আস্তে আস্তে কাছে এল হাসপাতাল ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকা কেরালারই মানুষ বিনায়ক। ওকে যতটুকু বলেছি ততটুকু শুনেই সে আমাকে বলেছিল— তোমার চোখের তলায় সবসময় জল টলটল করছে দেখতে পাই। কোনও একটা গভীর কষ্ট তোমাকে সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমি জানি না পারব কিনা। তবে খুব চেষ্টা করব।
বিনায়ক আর নয়নার জন্য আমি আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছি। শুধু জানতাম একদিন ডাক আসবে। সেদিন আমার অগ্নিপরীক্ষা।
বিনায়ক ধরেই নিয়েছে আমি বাবাকে আনতে যাব। কী হয়, যদি না যাই? যদি দাদার মতো আমিও হাত ঝেড়ে ফেলি? বাবার মুখোমুখি না হওয়ার মতো আরাম আর কিছুতে নেই। কী বলব নয়নাকে? এই তোমার দাদু। জঘন্য অপরাধ করে জেল খাটছিল এতদিন। উফ! ভগবান কেন আমি জন্মালাম বাবার মেয়ে হয়ে?
বিনায়ক স্টিয়ারিংয়ে বসে অপেক্ষা করছে আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে বলে।
নয়নাকে যাতে একা থাকতে না হয়, তাই সুসানা কাল রাত থেকে আমাদের বাড়িতেই আছে। বিনায়ক এয়ারপোর্ট থেকে ফিরলে কাজকর্ম সেরে বাড়ি যাবে। আমি খোলা জমি পেরিয়ে সারা বাড়ি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাকওয়াটারের মুখোমুখি একলা ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম।
এখানেই বাবা থাকবে। আমার কাছে কিন্তু দূরে। আমার ভালোবাসা আর ঘেন্নার মধ্যে।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন


অসাধারণ লাগলো ঋতা বসু র লেখা উপন্যাসটি।
ঋতা বসু সুলেখিকা।
নিছক গল্প উপন্যাস নয়, সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা তার গল্পের মোড়কে নানান ভাবে বলেন তিনি।
এই উপন্যাসেও সেই রকম একটি বিষয় তার বলিষ্ঠ
লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ্যে এনেছেন।
খুব ভালো লাগলো । লেখিকাকে সাধুবাদ।