নলিনী বেরা
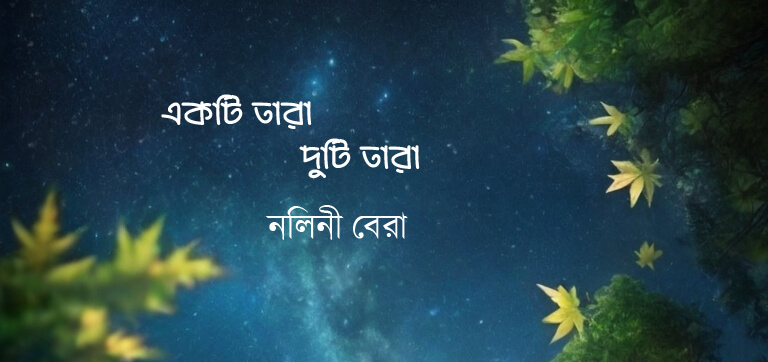
আচমকা আমাদের বাবা ধুলো পায়ে কোত্থেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বলে বসলেন, ‘এখানে আর একদণ্ডও থাকাটা নিরাপদ নয়, আঁকাড়া বিপদ চারধার থেকে ধেয়ে আসছে ধাঁই ধাঁই করে। সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে এক্ষুনি পালাতে হবে। কই, ডাক তোর মাকে।
জানি বাবার মা-অন্ত প্রাণ, তাই বলে আমি ও আমার বোন নাকফুঁড়িও তাঁর কাছে কম নই। কখনও পিঁপড়ের ডিম বা ‘কুরকুট পটম’, ডিমওয়ালা ‘ডিমাল কাঁকড়া’ কী খঙ্গা-বঙ্গা ধরে আনলে ঘরের কাছে এসে প্রায় রাস্তা থেকে বাবা হাঁক পাড়তেন, ‘কই রে নাকফুঁড়রি, কই রে নীলুয়া! ডাক তোর মাকে!’ ডাক শুনে আমরাও ঘর থেকে দৌড়ে বেরুতাম।
কখনও কখনও খলুইভরতি করে নিয়ে আসেন লাল লাল চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল কোঁড়ল ‘চুটিয়া’ বা ইঁদুরের বাচ্চা। অবশ্য আমাদের থেকেও চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল কোঁড়ল চুটিয়ার বাচ্চা আমাদের মায়ের খুব প্রিয়।
কাঁচায় কচমচিয়ে চিবিয়ে খেতে তিনি যে কী ভালোই না বাসেন! খেতে খেতে তাঁর মুখের কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে আর আমরা হি হি করে হাসছি, মা-ও হাসছেন, আহা! সে কী তাঁর মা কালীর মতো হাসি!!
সেই মাকে এখন খুঁজতে বেরিয়েছি। মা কোথায় আর যাবেন যা দিনকাল – এই বড়জোর বাঁধগোড়ার জলে গেঁড়ি-গুগলি, শুশনি কি ঘোড়াকানা শাক তুলছেন।
আঁকাড়া বিপদের আঁচ আমরা ছোটরাও একটু একটু করে টের পাচ্ছিলাম। কেননা দিনেদুপুরে অযথা জমির আলে-আবডালে হঠাৎ হঠাৎ ঢিস্ ঢিস্ করে ধুলো উড়ছিল, রাত- বিরেতে জঙ্গলে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছিল মট্ মট্ করে। অকালে ভুস্ ভুস্ করে ‘খতখানা’ থেকে বেরিয়ে আসছিল ফিনফিনে ডানাওয়ালা শালুইপোকা।
বর্ষার শালুইপোকা বালিখোলায় মুচমুচে ভেজে খেতেও ভারি সুস্বাদু। কিন্তু অসময়ের পোকামাকড় খেতে তিতকুটে লাগছে, আমরা মুখে পুরেই ছিঃ থুঃ করে ফেলে দিচ্ছি।
দূরের পিচ রাস্তায় জঙ্গল ভেদ করে ছোটদের যাওয়াও এখন বারণ, অচেনা কারা যেন সেখানে অষ্টপ্রহর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে! সন্ধ্যা হতে না হতেই টিপিক্ টিপিক্ করে ‘বাঘযুগনি পোকা’-র সঙ্গে জ্বলে উঠছে ঘন ঘন সত্যিকারের টিপালাইটের আলো, দু-ব্যাটারি তিন ব্যাটারি এমনকি পাঁচ ব্যাটারির টর্চ।
বেড়ে গেছে ‘রি-রি-আঁ’ পোকার ডাকও। রাত যত বাড়ে, বাড়তে থাকে একটানা ভয়ঙ্কর রিঁ রিঁ আওয়াজ। থেকে থেকে ভদভদিয়ে গাছ থেকে, টাঁড়- টিকর থেকে উড়ে উঠছে কয়ের- কপতি টিয়া-হরিয়ালের ঝাঁক।
ঘরে দোরে রাস্তায় ঘাটে টাটকাটাটকি মরে পড়ে থাকছে ‘বাগাডুলু’ ‘পতনি’ কেঁচো-কেন্নো-ক্যাঁকলাস’, ‘ঘরঘুন্নি’।
অথচ বেশ তো, ভালোই তো চলছিল সম্বৎসর!
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের রুখাশুখা দিনগুলোয় ঝাঁটি কুড়োতে পাতা ছিঁড়তে জঙ্গলে যাওয়া, এর তার গায়ে ঢলতে ঢলতে হল্লা করে যাওয়া। একা নয়, দঙ্গলে মিলে যাওয়া।
জষ্টিমাস খরার মাস, জাম-জামরুলের কাল। ঢুঁড়লে আলু-তুঙা, নানাবিধ ফলমূলও পাওয়া যায়। তাছাড়া শিকার, ধামসা-মাদল-চেরপেটি বাজিয়ে – ‘টি-লি-ঙ ডু-বু-ল ডু-বু-ল’। কাঁড়াল কোঁড়ল পাখির বাচ্চা, ঝিঁকর-খেড়িয়া-বরহা, ঢ্যামনা-গোই-গোধি শিকার করতে জঙ্গলে যাওয়া।
এসময় কতই ফলপাকুড় – পিয়াল-ভুড়রু আম-জাম-বেল কচড়া-কুসুম – খাও রে! ছড়াও রে!!
আষাঢ়ে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলেই অজস্র ‘ছাতু’ – সরুবালি বড়বালি, কুড়- কুড়িয়া কাড়হান ঝালুয়া হলদে ভণ্ডা সাদা ভণ্ডা, শালপোঙড়া-পোয়াল।
পরাং তমাল কুবাই নদীতে আষাঢ়-শ্রাবণে ‘ঝোপ’ এলে শোল বোয়াল পুঁটি দাঁড়িকিনি চ্যাঙ গোড়ুই খঙ্গা বঙ্গা কাঁকড়ার অভাব হয় না।
ধানপাকা, ধানকাটার মরশুমে খেতভরতি তো ধানের ‘টুঙ’! আর আছে ধানখেতের আলের গাঢ়হায় ইঁদুর, ইঁদুরধান।
আমি আর আমার বোন “খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তাহারি” করে খুঁজতে থাকি ধানের টুঙ আর আমার বাবা আমার মা খন্তা দিয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে গর্তের মুখে ধোঁয়া দেন, ধোঁয়ায় থকোবকো হয়ে বেরিয়ে আসে জোড়া-ইঁদুর।
জোড়া ইঁদুর ধরা পড়লে অতঃপর খন্তা দিয়েই খান খান করা হয় জমির আল। উদ্ধার করা হয় ইঁদুরধান আর মায়ের অতি প্রিয় সেই লাল লাল চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল কোঁড়ল ‘চুটিয়া’ অর্থাৎ ইঁদুরছানা।
ফাগুন, চোত তো মধুর মাস। মহুল গাছে গাছে মধু, লাটাপার খাঁজে খাঁজে মধুর চাক। মহুল কুড়োনোর ধুম পড়ে যায় তল্লাট-কে-তল্লাট।
পোহাতারা উঠল কি উঠল না – তাই দেখতে ঘর-বাহির করতে করতেই রাত ভোর করে দেন আমাদের মা-কাকি-ঝিউড়ি-বউড়িরা। রাত থাকতে থাকতে আগেভাগে না গেলে যে মহুল কুড়িয়ে সাফা করে দেবে চোর-চুরনীরা!
আখের খেত আর আমাদের কোথায়? মহুলের রস জ্বাল দিয়েই তো আমাদের গুড় করা, গুড় খাওয়া।
বনকাল্লা-বনকুঁদরী-বনকাঁকড়ো, চেঁকা-ঘলঘসি-নাহাঙা-সরন্তি-শুশনি – জঙ্গলে আনাজপাতি-শাকপাতা তো আছেই আর আছে চোত-বোশেখের ‘কেঁদ্’ পাকা, কেঁদুগাছের ফল।
যতখুশি খাও রে! দাও রে!! বাকিটা ঝুড়িতে ভরে খালা খালা করে বেচতে কামহার-কুমহার-হাটুয়া পাড়ায় যাও রে!!! মা-কাকিমারা পাড়ায় বে- পাড়ায় যান ঝুড়িতে আঁচল চাপা দিয়ে। খদ্দেররা দেখতে চাইলে সামান্য একটু আঁচল সরিয়ে দেখান – শালপাতার খালায় ভরা গণ্ডা গণ্ডা করে সাজানো হলদে রংয়ের গোল গোল পাকা কেঁদফল।
-আহা, ফল তো নয়, যেন অমৃত! বিনিময়ে চাল তো নয়, খুদ। নচেৎ দু-চার গণ্ডা পয়সা। ওই-ই ঢের।
তবু তো মন্দের ভালো এসব ছিল। ছিল, ছিল। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে কে জানে কোথায় পালাতে হবে!
সত্যি সত্যিই বাঁধগোড়ার জলে ঘোড়াকানা শাক তুলছিলেন মা।
ঘোড়ার কানের মতো লম্বা লম্বা শাক, নীল রংয়ের ফুল। তারউপর হেথা হোথা বক বসে আছে দু-চাট্টা, যেন বা সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে, বকফুল।
কাছে গিয়ে মাকে বললাম, ‘মা! মাগো!! বাবা বলল আর একদণ্ডও এখানে থাকাটা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়, সব ছেড়ে ছুড়ে এক্ষুনি পালাতে হবে।’
মায়ের যেন সবকিছুই জানা ছিল। একটাও কথা না বলে এতক্ষণের তোলা কোঁচড়ের সবকটা শাকপাতা জলেই ফেলে দিয়ে ঘরের দিকে দৌড়ুলেন।
আর এসময়ই ঝিটকার জঙ্গলে অজানা অচেনা ভয়ঙ্কর আওয়াজে ডানা ফেটিয়ে একসঙ্গে ভদভদিয়ে উড়ে উঠল অজস্র টিয়া-হরিয়াল চড়ৈ-চটি।
আমরাও দৌড়োনোর গতি বাড়িয়ে দিলাম।
হাতে আর একমুহূর্তও সময় নেই, বাবা তাড়া দিচ্ছেন, আমরা যাহোক তাহোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।
কী-ই বা ছিল আমাদের! ওই তো একটা পাতার কুঁড়িয়া, মাটির ‘তুঁবাঘর’। মায়ের মাথায় একটা গাঁটরি, হাতে একটা কলসি। কী-ই জানি কী আছে কলসিতে।
শীতের মরশুমে ইঁদুর ধরার প্রাক্কালে দেখেছি ওই কলসিটারই মুখে খড় গুঁজে ভিতরে ঘুঁটের আগুন জ্বেলে ইঁদুরের গর্তের মুখে ধোঁয়া দিতে। খড়ের ডাঁটি বেয়ে গাবানো উসুম উসুম ধোঁয়া দিকভ্রান্ত না হয়ে সোজা চলে যায় গর্ত বরাবর ইঁদুরের বাসায়।
হয়তো ভবিষ্যৎ ইঁদুর-শিকারের লক্ষ্যেই ধোঁয়া দিতে মা ওটা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন।
বাবার কাঁধে বস্তা, হাতে খন্তা – চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে আগে আগে হেঁটে চলেছেন। তারপরে মা, মায়ের পিছনে বোন, বোনের পিছনে আমি।
বোনের মাথায় ‘রোল’ করে বাঁধা ছেঁড়াফাটা একটা খেজুরপাতার চাটাই। এ যাত্রায় চাটাইটা নিতে বারণ করেছিলাম, বোন কথা শোনেনি। সে নাকি খোলা ‘মেঘপাতাল’-এর
নিচে রাতের বেলা ওই চাটাই পেতে শুলেই কত নতুন নতুন তারা দেখতে পায় – ‘সাতভায়া’ ‘দধিভারিয়া’ ‘কালপুরুষা’ –
আমার হাতেও ‘টুইলা’ ও ‘সাতনলা’। ‘টুইলা’ হল বাজাবার আর ‘সাতনলা’ হল পাখি ধরবার যন্তর। এক এক করে সাত-সাতটা নল, সবার শেষে সরু তীরের ফলা-গোঁজা-নল।
মগডালে বসে থাকে কপতি কী গোবরা চড়ৈ কী ক্যারকেটা, হয়তো বসে বসে ঝিমোয়। তখনই লতাপাতা ডাল-আবডালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে সন্তর্পণে চালিয়ে দিতে হয় ‘সাতনলা’।
পাখি টেরও পায় না আচম্বিতে সে কখন সাতনলার ফলায় বেঁধা হয়ে যায়! পাকা ফলের মতো থুপ্ করে মাটিতে পড়ে যায় নচেৎ ফলায় গাঁথা হয়ে ডানা ঝাপটায়।
এমন এমন যে অস্ত্র তাকেই বা ফেলে যাই কী করে? হ্যাঁ, প্রিয় ‘টুইলা’-র সঙ্গে ‘সাতনলা’টাও নিলাম।
ঘর ছাড়ার আগে আগে আমাদের ঘরে ‘কাঁটাদুয়ারি’ করতে এত বিপদের মধ্যেও বাবা কিন্তু ভুললেন না। কোত্থেকে ‘ভাবুর’ গাছের কাঁটাডাল এনে দুয়ারের মুখ কাঁটা দিয়ে আটকে দিলেন।
যাতে করে ‘ঝাঁটিয়া কুঁদরা’ ‘গিয়ান’ ‘গোমুহা’ ‘কালপুরুষা’-র মতো অপদেবতার ছায়া না পড়ে ঘরে।
ঘর ছাড়ার আগে আমার ও বোনের কান কামড়ে কী একটা ছাল কোমরে গুঁজে দিয়ে বাবা বললেন, ‘এবার নির্ভয়ে চল!’
আমরা চলতে শুরু করলাম। শুধু কি আমরা? আমাদের গ্রামের ঘর-ঘর। ওই তো হাঁসুদের পরিবার, বড়ভদ্র-ছোটভদ্রদের লোকজন, বস্তা কাঁধে কালিপদ- বধিরাম, গাঁটরি মাথায় হারানির মা কালমণি, বেজু-কাঁদরির বাপ শরাবন।
কারুর মুখে কোনও রা নেই, কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাও করছে না, ‘কোথায় যাচ্ছ গো?’ জিজ্ঞাসা করলেও সঠিক উত্তর দিচ্ছে না, যাচ্ছে উত্তরে তো বলছে দক্ষিণে। কে জানে কী আছে কার মনে!
দু-পা যাওয়ার পরেই অস্থির হয়ে উঠল বোন নাকফুঁড়ি। উসখুস করছে – সে নাকি তার দামি জিনিস ফেলে এসেছে।
‘কী জিনিস রে? কী জিনিস?
‘আরশি-কাঁকই।’
মা জানতে চাইলেন, ‘কোথায় রেখেছিলি?’
‘ভুগড়াঘরের খাঁজে।’
বাবা বললেন, ‘আগে নিজে বাঁচ তারপর আরশি-কাঁকই।’
বাবার কথা শুনে ভারি কষ্ট হল। বেশ বুঝতে পারছি বোন নাকফুঁড়ি ফনফনিয়ে বাড়ছে, তার এখন আয়নায় মুখ দেখা দরকার।
বাবাকে বললামও, ‘যাই একছুটে নিয়ে আসি?
বাবা কড়া নিষেধ করলেন, ‘ন্না, ঘরে কাঁটাদুয়ারি হয়ে গেছে, আর এখন যেতে নেই।’
গ্রামের মানুষজন নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকদূরের নিরাপদ গ্রামের আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি চলে যাচ্ছে। যাদের আছে তারা তো একটা দিশা নিয়ে আশায় বুক বেঁধেই যাচ্ছে, যাদের কেউ কোথাও নেই, দিশাহারা, তারাও পালাচ্ছে।
যেমন আমরা।
এর-তার মুখে কত গ্রামের নামই তো শুনি – গিধিঘাটা, দলদলি, কেন্দাপাড়া, ভুলাভেদা, চিল্কিগড়, কেঁদুয়াসোল, কাদাসোল, কলাইমুড়ি, কিয়া-বনি, পিংবনি, আরও অমুক-তসুক।
যতদূর জানি এসব গ্রামে আমাদের তিনকুলের কেউ জানাচেনা আত্মীয়-কুটুম্ব একজনাও নেই। আশপাশের গ্রামে মায়ের বাপের বাড়ির, বাপের বাপের বাড়িরও সব মরে হেজে সাফা!
বড় রাস্তার দিকে কিছুদূর এসে বোন নাকফুঁড়ি আচমকা জিজ্ঞাসা করল, ‘বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?’
বাবা কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ চলার পর আমিও জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা?’
বাবা এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘যেদিকে দুচোখ যায়।’
ঝাঁটিজঙ্গলের ভিতর দিয়ে সুঁড়িপথ, দুধারে লহ লহ করছে আঁটারি গাছের ডগ্। আমি আর বোন ডগ্ ছিঁড়ে মুখে পুরছি, চিবোচ্ছি। ঢোঁক গিলছি। কষা কষা অম্লমধুর স্বাদ। মুখের ভিতরটা জলে ভরে যাচ্ছে।
এতক্ষণ পরে মা যেন বুকের ভিতর থেকে কথা বলে উঠলেন, ‘যেখানে মেঘপাতালে দেখবি গোল হয়ে চিল ঘুরছে, ঘুরছে তো ঘুরছে, সেখানে জানবি জলের জন্য চিল কূঁয়া খুঁড়ছে। আমরা সেই দিশমেই যাচ্ছি রে ধন!’
মায়ের কথামতো তারপর থেকেই আমরা দু ভাইবোন মাঝেমধ্যেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। আকাশও যেন শুনশান, চিল তো চিল, একটা ঢেপচু পাখিরও দেখা নেই – যে কীনা অনবরত ‘ভু-ই-চু-ঙ্’ ‘ভু-ই-চু-ঙ্’ করে মাকুর ফিতার মতো এ-মাথা সে-মাথা উড়ে ঘুরে বেড়ায়।
বড় রাস্তা এসে গেল। খাকি পোশাকের পুলিশ সব, হাতে বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছে। দেখামাত্রই আমরা খানিকটা পিছু হটে লাটাপাটার ভিতর লুকিয়ে পড়লাম।
আমাদের মা কিন্তু অকুতোভয়, বাবার হাত টেনে ধরে বললেন, ‘ডরপেল-কার মতন এখন লুকালে চলবে? মাথা সোজা করেই হাঁটো!’
বাবার ভারি ভয় – যদি আনসাটকা সন্দেহ করে ‘জিহলখানা’-য় পুরে দেয় পুলিশ? পুলিশ আমাদের সত্যি সত্যিই থামিয়ে দিল।
‘কোথায় যাচ্ছ?’ জিজ্ঞাসা করল।
উত্তর না দিয়ে খালি চোখ পিট্ পিট্ করছেন বাবা, কথা আটকে গেছে তাঁর। মা এগিয়ে এসে বললেন, ‘কোথায় আর যাবেন? ঘরে যাচ্ছি।’
‘কোথায় গিয়েছিলে?’
মায়ের চটজলদি উত্তর, ‘কুটুমবাড়ি।’
‘কী আছে পুটলিতে? কলসিতে?’
আর তর সইছিল না পুলিশদের, পোঁটরাপুঁটলি নিজেরাই খুলে ফেলল।
কলসিটা কিছুতেই হাতছাড়া করছেন না মা, ভিতরের জিনিস মুঠোয় এনে দেখাচ্ছেন, আমরাও উঁকি মেরে দেখছি, কী জিনিস দেখি! দেখি!!
শুকনো মহুল আর ছালছাড়ানো ভাজা তেঁতুলবীচি।
এতক্ষণে বুঝলাম কেন যখের ধনের মতো কলসিটা আগলে রেখেছেন মা -ওই তো আমাদের পেটের ভাত! মহুল আর তেঁতুলবীচি সেদ্ধ।
গরম জলে ফুটে ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়ে যায় শুকনো মহুল আর ছাল-ছাড়ানো পোড়া তেঁতুলবীচি। তখন কোনটা মহুল কোনটা তেঁতুলবীচি চেনা-ই দায় হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার মা জানেন বেছে বেছে সেদ্ধ তেঁতুলবীচি খেতে আমি কতটা ভালবাসি।
পুলিশ ওই এক মুঠোতে সন্তুষ্ট হল না। বলল, ‘উসিসে ফায়দা নেহি হোগা, বিলকুল লোটা দো!’
পুরোটাই ঢালতে হল। পেটের অন্ন অতটা হেলাফেলার নাকি? রাস্তার বালি-কাঁকরে মা কিছুতেই ঢালতে রাজি হলেন না। বোনের ছেঁড়া চাটাই পেতে তবে ঢাললেন।
সব দেখেশুনে পুলিশ আমাদের ছেড়ে দিল। আর আমরাও মায়ের কথা মতো কুটুমবাড়ি ছেড়ে নিজেদের ঘরের দিকে হেঁটে যেতে লাগলাম।
বাবার মুখে কোনও কথা নেই, মা-ও চুপ। আমরা অনবরত হেঁটে চলেছি। হেঁটে চলেছি, হেঁটে চলেছি, হেঁটে চলেছি। খালি যা আমি আর নাকফুঁড়ি মাঝে মাঝেই পথের দুধারের লতাপাতা ছিঁড়ে মুখে পুরছি, কখনও ঢোঁক গিলছি, কখনও ছিঃ থুঃ করে ফেলে দিচ্ছি।
আমরাও চুপচাপ, কথা তেমন বলছি না। আসলে কথা বলার ইচ্ছাটাই যেন মরে আসছে ধীরে ধীরে।
এভাবে আরও কতদূর যেতে হবে – সে হয়তো বাবা জানেন, কিন্তু বাবার ভাব-গতিক দেখে মনে হচ্ছিল সেটুকুও বাবার জানা নেই।
এসময়টা ‘কচড়া’ ‘কুসুম’-এর দিন – অথচ ধারে কাছে কোথাও একটা কচড়া কি কুসুমগাছ দেখা যাচ্ছে না, এদিকে কুসুমের নামে জিভে জল এসে যাচ্ছিল।
অগত্যা মাকে বললাম, ‘চাট্টি তেঁতুল ‘মুজি’ দাও না মা, খাই!’
মা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ‘চ, কোথাও একটুক বসি।
একটা চল্লাগাছের তলায় আমরা বসে পড়লাম, বাবা বিরক্ত হলেন, তবু আমাদের দেখাদেখি বেজার মুখ করে বসেও পড়লেন।
চল্লাগাছ ওই তো আরেকটা – এত যখন চল্লাগাছ, কাছে পিঠে নির্ঘাত গাঁ-গঞ্জ আছে। বেছে বেছে ভাজা ছাল ছাড়ানো তেঁতুলবীচি চিবোতে চিবোতে সেকথা বাবাকে বললামও।
বাবা যেন খুশি হয়ে বললেন, ‘ঠিকই ধরেছিস, ‘ঠিকই ধরেছিস, এদিকটায় কাদাসোল বাঁদরিসোল কলাইমুড়ি বাবুইবাসা চাঁপাসোল’ -বলে বাবাও তেঁতুলের বীচি সহ একমুঠো কাঁচা মহুল চিবিয়ে খেলেন।
আমরা ফের ট-ঙ-স ট-ঙ-স করে হাঁটতে লাগলাম।
গাঁ-গেরাম তো আছে কিন্তু লোকজন কোথায়? একটা লোকও তো নেই! নেই, নেই। ঘরের দরজা জানলা – সব হাট করে খোলা, চৌকাঠের পাল্লাগুলো যেন এখনও ঠির্ ঠির্ করে নড়ছে, যেন এইমাত্রই ‘গিরিহা’ ঘর ছেড়ে হুট্ হাট্ বেরিয়েছে, এক্ষুনি এক্ষুনি ফিরে আসবে।
চোখে পড়ল দু-চাট্টা মুরগি টিঁ টিঁ করে চরে বেড়াচ্ছে, কয়েকটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। আমাদের দেখে আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল, তবে আমাদের কাছে দৌড়ে এল না, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই ল্যাজ নাড়ছে।
কোথাও গরু ডাকল – হা-ম্বা!! একটা নয়, আরও কয়েকটা। বাবা বললেন, সব ছেড়ে ছুড়ে লোকজন পালিয়েছে। গেরামটা মাহাত মহাজনদের। কতবার এ গেরামে দিতে এসেছি গরুর গাড়ির ‘আরা’ ‘ধুরিকাঠ’ ‘জুয়াল’ লাঙ্গলের ‘ঈশ্’। গ্রামের মাথায় একটা পাতকুয়া, ঘড়রিতে এখনও লাগানো আছে দড়ি-বালতি। বোন নাকফুঁড়ি আর আমি দৌড়ে গেলাম – যদি একটু জল পাওয়া যায়!
বাবা হাঁকড়ে উঠলেন, ‘খ-ব-র-দা-র!!’
আমরা হাত গুটিয়ে ফিরে এলাম। বাবা কেন যে নিষেধ করলেন বুঝতে পারছি না। অথচ তেঁতুলের বীচি চিবিয়ে ‘টাকরা’ শুকিয়ে যাচ্ছে আমার।
মা বললেন, ‘হাঁটতে থাক, সামনে কত নদীনালা সায়র বাঁধগোড়া পাবি।’
সত্যি সত্যিই আমরা একটা নদী পেলাম। মরাহাজা হাড় জিরজিরে নদী, এখানে জল তো সেখানে চাপড়া চাপড়া ঘাস-পাথর। আমরা আঁজলা ভরে জল খেলাম।
‘কী নাম, বাবা?’
বাবা বললেন, ‘জঙ্গলের ভিতর বাস অত নদীনালার নাম কি আর জানি? শুনেছি ‘টাঙ্গাই’ কি ‘তমাল-টমাল’ হবে।’
বোন আচমকা জিজ্ঞাসা করল, ‘বাবা, আরও কদ্দূর যেতে হবে?’
উত্তর দিতে না দিতেই কাছে পিঠে কোথাও ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল, জঙ্গলের ভিতরে কি ওধারে আগুনের হলকা উঠল।
আমরা দৌড়ুতে থাকলাম – রিটপিটে দৌড় – দৌড় দৌড় –
দৌড়ুতে দৌড়ুতে মা একজায়গায় থুপ্ করে আচমকা বসে পড়ে বললেন, ‘কার খাই না ধারি যে অমন পড়ি-কি-মরি দৌড়াব?’
বোন আর আমি বুঝতে পারলাম – মা আর পারছেন না। বাবাও ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে ফেললেন, ‘আর তো সামান্যই!’
আমরাও জেনে উল্লসিত হলাম, যাক আর ক-পা হাঁটলেই আমরা তাহলে ভয়ের মুল্লুক পেরিয়ে যাব!
ফের ট-ঙ-স ট-ঙ-স হাঁটা। একই তো আবহাওয়া গাছপালা রাস্তাঘাট, বাবুই ঘাসের চাষ। বেলা প্রায় হেলে পড়েছে।
তফাতের মধ্যে এই যা – এখানে ডুবকাডুংরিতে গরু চরছে। গরুর গলায় ঠরকা বাজছে, ঠ-র-ক্! ঠ-র-ক!! তবে লোকজনের এখনও দেখা নেই, গরুবাগালরাই বা কোথায়?
দেখতে দেখতে একটা লোক সাঁক্ করে সাইকেল চালিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল, তার সাইকেল ক্যারিয়ারে গাদাগুচ্ছের ডুমুরগাছের পাতা, বোধকরি ছেড়ী-ছাগলের জন্য।
লোকটা সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে গেল কিন্তু একটাও কথা বলল না আমাদের কারোর সঙ্গে। তাহলেও তবু তো অবশেষে একটা গ্রামে আসা গেল যে গ্রামে অন্তত একটা মানুষ আছে, তার নিজস্ব কতকগুলো ছেড়ী-ছাগল আছে।
একটা নয়, অনেক মানুষেরই দেখা মিলল, আমাদের বাবাও তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়বাড়ি খুঁজে পেলেন। আমি আর বোন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বললামও, যাক তাহলে আমাদেরও আত্মীয় কুটুম্ব আছে!
বাবার সম্পর্কে মাসতুতো ভাই মোটামুটিভাবে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়া মানুষ। সাইকেলে চেপে ঘুরে ঘুরে কেঁদুপাতা ও বাবুইদড়ির কারবার করেন, সাইকেলের ক্যারিয়ারে এখনও বাঁধা বাবুইদড়ির বান্ডিলই তার প্রমাণ।
গলায় জোর আছে তবু যেন কথা বলছেন বাবার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে। মা আর বোন ততক্ষণে ঝিউড়িবউড়িদের সঙ্গে ভিতর ঘরে, একলা আমি দু-পা এদিক সেদিক হেঁটে বেড়িয়ে গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখছি।
তেঁতুলতলায় এক ন্যাড়ামুণ্ডি আমারই বয়সী ছেলে এসে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, ‘আমার নাম দামু, তোর?’
আমিও নাম বললাম।
‘আমাদের গেরামের নাম চিচুরগেড়িয়া, তোদের?’
গ্রামেরও নাম বললাম।
‘তোরা কোন পার্টি? আমরা…’
দৌড়ে ফিরে এলাম কোনও উত্তর না দিয়ে। বাবাকে বললাম। বাবার মাসতুতো ভাইকেও।
তিনি দ্রুত তেঁতুলতলায় ঘুরে এসে হাসতে হাসতে বললেন, ‘ও দামু, হাবাগোবা, আধ‐ পাগলা – কিন্তুক ভালো ‘আলি’ খেলে, যা না দু-দান ওর সঙ্গে খেলে আয়!’
‘আলি’ তারমানে কাচের নানা রংয়ের গুলি, গুলিখেলা দিয়ে আঙুলের ‘টিপ’ পরীক্ষা। কত খেলেছি! তাবলে এখানে কাচের গুলি নয়, ভেলা ফলের কালো কালো বীচি।
এখন এই চারধার আঁধার করে আসা ঝুঁজকো বেলায় আর ‘আলি’ খেলতে মন গেল না। এতদিন মাঝে মধ্যে ‘কুরথি-সিজা’ খেয়েছি, কিন্তু কুরথির ডাল? আজ আমাদের কুটুমবাড়িতে সেই কুরথির ডাল দিয়ে শুকনো ভাত খাচ্ছি। দু-এক গ্রাস খেয়েছি কি খাইনি, দরজায় দমাদ্দম লাথি পড়ল, কে বা কারা বাবার মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িটাই যেন ভেঙে দিচ্ছিল। আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল চালে – দাউ দাউ!!
খাওয়া ফেলে কোনও মতে গাঁটরিগুঁটরি নিয়ে আমরা ফের উদ্বাস্তু হলাম, দৌড়ুলাম। শুধু কী আমরা? বাবার দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ির লোকজনেরাও।
দৌড়ুতে দৌড়ুতে দলছুট হয়ে গেলাম আমরা। তাঁরা তো যাবেন তাঁদের আত্মীয়ের বাড়ি, দূরদূরান্তের কোনও এক নির্দিষ্ট গ্রামে কিংবা টাউনে। আমাদের আর কোনও আত্মীয়কুটুম্ব নেই, যাওয়ার জায়গাও নেই।
বাবা ফের মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বলে বসলেন, ‘অভাগা যেদিকে চায় সাগরের জলও শুকায়। যেদিকে দুচোখ যায় দৌড়া!!’
আমরা ঝাঁ ঝাঁ রাতে সাপখোপ পোকামাকড় মাড়িয়ে দৌড়ুতে লাগলাম। আমার পদে পদে আশঙ্কা হচ্ছিল – মা না থুপ্ করে বসে পড়ে বলে বসেন, ‘কার খাই না ধারি যে অমন পড়ি-কি-মরি দৌড়াব?’
আসলে আমরা কুরথির ডালভাত যাহোক করে দু-এক গ্রাস মুখে পুরলেও মা যে আমার এক খাবলও মুখে দেননি! পুরুষদের খাওয়া শেষ হলে তবেই না মেয়েদের খাওয়া শুরু হবে!
পিছনে দাউ দাউ আগুন, মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ। আমরা ঠিক করতে পারছি না যে-পথে গিয়েছিলাম সে-পথেই ফিরে আসছি কী?
আমার কেবলই মনে হচ্ছিল হাবাগোবা আধপাগলা দামু কী আঙুল উঁচিয়ে সেই তাদেরও জিজ্ঞাসা করছে – ‘তোমরা কোন্ পার্টি?’
যাওয়ার রাস্তায় ফিরে আসা আর তো নিরাপদ নয়, বাবা বললেন, ‘নাহ্, আমরা কাঁটাপাহাড়ী সিজুয়ার দিকেই যাচ্ছি।’
কোথায় সিজুয়া, কোথায় কাঁটাপাহাড়ী আমার জানা নেই। বোন নাকফুঁড়িও অস্থির হয়ে বলে উঠল, ‘আর পারছি না বাবা! কাঁটাপাহাড়ী-ঝাঁটাপাহাড়ী থাক, ওই জঙ্গলেই চল-অ। আমার যে দমে ঘুম পাচ্ছে বাবা।’
অগত্যা আমরা বাকি রাতটুকু কাটাতে জঙ্গলে ঢুকলাম। জঙ্গল, জঙ্গল। গাছ- পালার আড়ালে একটা টিকরোল ভুঁই দেখে আমরা আস্তানা গাড়লাম।
মাথার উপর গাছপালহার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারাভরা ‘মেঘ- পাতাল’, এক-দু’টুকরো ভাসমান ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ। তারমধ্যেই মাঝেমাঝে একটি-দুটি তারা হারিয়ে যাচ্ছিল।
সেদিকে চোখ পড়ামাত্রই বোন নাকফুঁড়ি সিলোক বলে উঠল –
“একটি তারা দুটি তারা
কোন্ তারাটি আরাঝারা।
আন্ দেখি গ’ কাঁড়বাঁশটা
বিঁধে দিব ভুরভুরাটা।”
আমরা কেউই কিছু বললাম না। চারধারে ঝোপেঝাড়ে রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা ডাকছে, ডাকছে মানে? যেন তাদের বুক-পেট ফাটিয়ে ডাকছে।
কোত্থেকে দু-চাট্টা ধরে এনে মাটিতে গুঁজে দিল নাকফুঁড়ি। অর্ধেক মাটিতে, অর্ধেক উপরে, তারমধ্যেও শুঁড় নেড়ে নেড়ে বিরামহীন ডেকে চলেছে ‘রিঁ-রিঁ-আঁ’ পোকাগুলো -রিঁ-ই-ই-ই! রিঁ-ই-ই-ই!!
নাকফুঁড়ি ঘোষণা করল, ‘আজ থাক, কাল তোদের বিয়ে দেব।’
তারপর সে তার ছেঁড়া চাটাই পেতে শুয়ে শুয়ে আকাশের নতুন নতুন তারা আবিষ্কারে মেতে উঠল, মুখে তার সেই সিলোক – “একটি তারা দুটি তারা কোন্ তারাটি আরাঝারা” –
বাবা খন্তা-হাতে চারপাশটা ঘুরে ভালো করে দেখে এলেন। সর্ সর্ করে শুকনো মড়মড়ে পাতার উপর বুকে ভর দিয়ে চলে যাচ্ছে রাতের ‘লতা’, হুপ্ হুপ্ করে মাঝেমধ্যেই ডেকে উঠছে বন্য নিশাচরের দল। বনমোরগ ‘বাঙ’ দিচ্ছে দূরে কোথাও, ট্র্যাঁ ট্র্যাঁ করে পাখি ভদকালো গাছের মগডালে।
মা কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন! এবার নাকফুঁড়িও ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা আর আমি জেগে, থেকে থেকে খন্তার খুপ্ খুপ্ আওয়াজ পাচ্ছি। একসময় সে আওয়াজও থেমে গেল, বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমিও।
ভোরের দিকে মায়ের আর্তচিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখি খন্তা-হাতে বাবা লাটাপাটা ভেঙে দৌড়ুতে দৌড়ুতে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছেন।
আর একমুহূর্তও দেরি না করে আমিও বাবার পিছু পিছু দৌড়ুতে শুরু করলাম।
আমাদের পরিবারের আমরা সাকুল্যে চারজন একসঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম। এখন আমরা তিনজন।
গতকাল রাতে কে বা কারা এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে বোন নাক- ফুঁড়িকে। তন্ন তন্ন করে সারা জঙ্গল ঢুঁড়েও আমরা তাকে আর খুঁজে পেলাম না।
তার ফেলে যাওয়া খেজুরপাতার ছেঁড়া চাটাইটা জঙ্গলেই পড়ে থাকল, কেউ আর তার উপর শুয়ে তারা ভরা রাতে ‘মেঘপাতাল’-এ ‘কালপুরুষা’ ‘দধিভারিয়া’ ‘সাত-ভায়া’-র মতো নতুন নতুন তারা খুঁজবে না।
‘রিঁ-রিঁ-আঁ’ পোকাগুলো অর্ধেক মাটিতেই পোঁতা থাকল, পোঁতাই থাকল, ঘটা করে তাদের বিয়ে দিতে নাকফুঁড়ি নামের কেউ আর থাকল না।
দুপুর গড়িয়ে আড়বেলা পর্যন্ত আমরা সেখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম – যদি সে ফিরে আসে, যদি সে আসে!
বাবার চোখদুটো খোসা ছাড়ানো পাকা কুসুমফলের মতো লাল, একটাও কথা বলছেন না। মা থেকে থেকে কঁকিয়ে কেঁদে উঠছেন। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল বোন যেন এসেই বলবে, ‘আরও কদ্দূর যেতে হবে বাবা?’
সব মায়া কাটিয়ে আমরা ফের রওনা দিলাম পোঁটরাপুঁটলি নিয়ে। কোথায় এসেছিলাম, এখন কোনদিকে যেতে হবে – তা জানা নেই, আর তার যেন দরকারও নেই।
বাবা এগিয়ে চলেছেন, মা হাঁটতে পারছেন না, মাকে জড়িয়ে ধরে ধরে হাঁটছি।
হাঁটছি, হাঁটছি। টাঁড়-টিকড় বন-বাদাড় পেরিয়ে। দুয়েকটা গ্রাম যে চোখে পড়ছে না তা নয়, পড়ছে পড়ছে, তবে জনমানুষশূন্য, খাঁ খাঁ।
মাটির ভুগড়া, কোনটায় বা পলিথিন শিট চাপা দেওয়া। দরজা হাট করে খোলা, নচেৎ ঝিঁজরি দেওয়া। যে কেউ দরজা না ভেঙে ঢুকতে পারে ভিতরে।
ভিতরে ঢুকে চুরিচামারি করার লোকও যেন আর অবশিষ্ট নেই। বাড়ির মাচানে ভুয়াঙ লাউ ফলেছে, কুঁদরি মাচায় কুঁদরি পেকে লাল হয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে, কাঁচা কুঁদরি তুলে ‘ভাতে-সেদ্ধ’ বা তরকারি করে কে আর খাবে?
পাতকূয়ার ঘড়রিতে লটকানো দড়ি-বালতি পড়ে আছে যেমনকার তেমন। দেখেই আমার মনে পড়ে গেল বোন নাকফুঁড়ির কথা, ছুটে সেই জল খেতে যাওয়া আর বাবার নিষেধের কথা।
সেবার নিষেধ মেনে ফিরে এলেও এবার যেন জেদি মোরগের মতো ঝুঁটি ফুলিয়ে দৌড়ে গেলাম, বোনও যেন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। কূয়ায় বালতি ধাসিয়ে জল তুলে জলও খেলাম।
বাবাও নিষেধ করলেন না, তাঁর যেন আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না।
একটা খাল পড়ল। খালপাড়ে ডুবকাডুংরিতে গরুমোষ চরছে। কিন্তু সঙ্গে ভাঙা-ছাতা-লাঠি-ধারী সচরাচর দেখা যায় এমন কোনও গরুবাগাল কাড়াবাগালকে দেখা গেল না।
আমরা খাল পেরিয়ে মোরাম রাস্তায় উঠে এলাম। এখন ডাইনে যাবেন না বাঁয়ে যাবেন ঠিক করতে না পেরে বাবা খানিক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে ‘আড়বেলা’-র অবস্থান দেখে ডানদিকেই হাঁটতে লাগলেন।
হাঁটছি, হাঁটছি।
কখনও মনে হচ্ছে সামনের দিক থেকে কেউ আসছে, কখনও মনে হচ্ছে কেউ পিছন পিছন আসছে।
দুধারে জঙ্গল, তবে জঙ্গল খুব গাঢ় নয়, রাস্তার ধারে ধারে দু-দশটা বড় বড় গাছ, তার তলায় তলায় আঁটারি-চুরচু-পড়াশের ঝাঁটিজঙ্গল। কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল – রাস্তা কাটা!
বাবা ফের মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বলে উঠলেন, ‘এই যা!!’
আসলে ধন্দে পড়ে গেছেন তিনি – কোনদিকে কারা? এগোলে ভালো, না পিছোলে ভালো? আমাদের জড়িয়ে ধরে বাবা সামনের দিকেই হাঁটতে লাগলেন।
হাঁটছি, হাঁটছি।
রাস্তার উপর একটা আস্ত গাছের গুঁড়ি ফেলা। রাস্তার তেমাথা কি চৌমাথার মোড়ে মাঝেমাঝেই দেখা যায় ধানের তুষসহ হাঁড়ি ভাঙা, ডিমের খোসা, সিঁদুরগুঁড়ো, সিঁদুরটিপ।
তারমানে কেউ ‘তুকগুণ’ ‘ছাড়ান’ ‘নিমছা’ করেছে।
রাস্তা পার হতে গিয়ে আমরা মোড়টা না ডিঙিয়ে খানিকটা ঘুরপথে হেঁটে যাই। বাবাও তাই করলেন। গাছের গুঁড়িটা না ডিঙিয়ে আমরা ঘুরপথে হেঁটে ফের রাস্তায় উঠলাম।
এখন নাক বরাবর হাঁটা। হাঁটছি, হাঁটছি। কখনও মনে হচ্ছে আশপাশে কেউ নেই। সুনসান, সুনসান। পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কে বা কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে, হাঁটছে চলছে, লাটাপাটা তো নড়ছে সড়্ সড়্ করে। কে জানে – ‘খেড়িয়া’ না ‘বরহা’!
বাবা এই সময়টায় ফের মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বললেন, ‘চোখ কান খোলা রেখে হাঁটো!’
আমি চারপাশটা চন্ মন্ করে দেখতে দেখতে হাঁটছি, মায়ের অত দেখাদেখি নেই, বললেন, ‘ছাড়্ ত! ধর্মের রাস্তায় হাঁটছি – ডর কী? মায়ের ডরভয় নেই, সদ্য সন্তানহারা জননীর কাছে ডর-ভয়ের চেয়ে শোকই তো বড়। মা এখনও মাঝে মাঝেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠছেন। বেলা আড় হয়ে ঢলে পড়লেও হঠাৎ যেন নিভু নিভু চারধারটা জ্বলে উঠল দপ্ করে। তারমানে জঙ্গল শেষ হল। জঙ্গল শেষ হতেই দেখা গেল বেশকিছু লোকজন রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় এক-দুমাইল তফাতে। হাতে তাঁদের কাঁড়-কাঁড়বাঁশ-টাঙ্গি-বল্লম-তাবলা-বুড়িয়া।
মুখে চিৎকার করে হাত-পা নেড়ে কীসব বলে চলেছেন। বাবা থমকে দাঁড়ালেন, ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ‘পিছনটা একবার দ্যাক্ রে নীলুয়া !!’
দেখলাম বন্দুক-হাতে তাক্ করে খাকি আর তার উপর ছাপকা ছাপকা রংয়ের পোশাক পরা কাতারে কাতারে পুলিশ! এর মধ্যেই কোথাও একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হল, একসঙ্গে কত যে গোলাপায়রা ডানা ফট্ ফটিয়ে উড়ে উঠল!!
একটা, তারপর আরও একটা আওয়াজ! কা-ন-ফা-টা!!
আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি থমকে। বাবা বোধহয় তড়পে উঠলেন রাগে, তার চোখদুটো লাল, আরও লাল হয়ে উঠল। তারপর খন্তা-হাতে কেন যে হঠাৎ দৌড়ে গেলেন সামনের দিকে এখনও বুঝতে পারছি না!
একমুহূর্তও গেল না, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বাবা। মা আর আমি দৌড়ে গেলাম বাবার কাছে, বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছি, আমাদের উপর দিয়েই ডাইনে-বাঁয়ে গুলি চালাতে চালাতে দৌড়ে গেল খাকি আর ছাপকা ছাপকা পোশাক পরা লোকগুলো।
মাটির কলসি ভেঙেচুরে রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল শুকনো মহুল আর ছালছাড়ানো তেঁতুলবীচি। তারউপর ভারী বুটের সরকারি ছাপ্পা লাগল।
এখন ওই, ওই তো বাবার দেহ, একটা ইস্কুলঘরের সামনে একটা বেঞ্চিতে শোয়ানো। তাঁর কাছে যাবার আর এখন আমাদের অধিকার নেই।
মাঝেমধ্যেই মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করার জন্য আর আমাদের কেউ থাকল না। বাবা এখন পুরোপুরি ওঁদের সম্পত্তি। ‘ফটো-খিঁচা’ মেসিনে এখন ঘন ঘন কত ছবি উঠছে বাবার!
আমরা বড় গরীব ছিলাম, গরীব হয়ে গেলাম আরও।
এরমধ্যেই পুলিশ এসে আমার হাফ-পেন্টুলের পকেট হাঁতড়েছে দু-দুবার। তল্লাসি করে দু-দুটো শুঁড় জড়ানো লোহার মতো শক্ত ‘রিঁ-রিঁ-আঁ’ পোকা পেয়েছে। কে জানে কাল রাতের বেলায় কখন পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল নাকফুঁড়ি!
‘টুইলা’ আর ‘সাতনলা’ তো ছুঁড়ে ফেলে এসেছি সেই ‘বহিন-খাকী’-র জঙ্গলে!
একসঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম আমরা চারজন। বাবাও চলে গেলেন, বোনও। মুখে গাঁজলা তুলে জ্ঞান হারিয়েছেন মা-ও।
এতক্ষণে মরে গেছেন কি বেঁচে আছেন – জানি না।
মা পড়ে আছেন রাস্তায়, ঠিক রাস্তায় নয়, রাস্তার একধারে। আমিই টেনে এনেছি এদিকে, পাছে রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ চলে আসা গাড়িঘোড়া – কাঠের ধুরিওয়ালা লোহার মুখপাত বসানো দুচাকার গরুর গাড়ি তো নয়, বনের ভিতর পিচরাস্তার উপর দিয়ে গিড়্ গিড়্ করে আসতে আসতে গাড়োয়ান ঘুমিয়ে থাকলেও অবলা জীবদুটি রাস্তায় কাউকে পড়ে থাকতে দেখলে তক্ষুণি থমকে দাঁড়ায়!
আর এখন যা অবস্থা এসব অঞ্চলে গরুর গাড়ি আসাটাই ঝকমারি, কখন কোথায় ফেঁসে যাবে কীভাবে! যা আসছে সব বুঝি মিলিটারি গাড়ি বুম্ বুম্ করে।
এই তো একটু আগে গেল একটা, এখন আরেকটা। এমন ভাবে হুঁকরে আসছিল যেন তালজ্ঞান ভুলে চড়ে বসবে মায়ের উপর! আমি উপুড় হয়ে শুয়ে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলাম মাকে।
এই আমার মা, মুখে এখন বুজকুড়ির মতো গাঁজলা উঠছে ফেনা ফেনা। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি আমি, মাঝেমাঝে হাতের আঙুল বুলিয়ে গাঁজলা মুছে দিচ্ছি আর বুকের উপর কান চেপে শুনছি – ধুকপুকানিটা আছে কীনা?
আছে, আছে।
কেঁদ্ কি কুরকুট্ নিয়ে হাটে গিয়েছেন, জিনিস বেচে কিনে এনেছেন চাল-নুন-ডাল, সেইসঙ্গে মিষ্টি পান একটা।
পান চিবোতে চিবোতে ঠোঁট লাল করে ফেলেছেন, কোত্থেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মায়ের দুহাঁটু জড়িয়ে ধরে, আমরা দু ভাইবোন আবদার ধরেছি, ‘দাও না গো মা পান, খেয়ে ঠোঁট লাল করি।’
মা মুখ থেকে চিবোনো পান তার জিভের ডগায় নিয়ে একবার আমার মুখের সামনে, একবার বোনের মুখের সামনে ধরে লোভ দেখাতেন, ধরতে যেই আমরা হাত বাড়াতাম, অমনি মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিতেন সুড়ুৎ করে।
আসলে প্রথম প্রথম কৌতুক করতেন মা, অবশেষে চর্বিত পান মুখের ভিতর থেকে বের করে ভাগ করে দিতেন আমাদের মধ্যে।
তবে ওই যে, যখন লাল লাল চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল কোঁড়ল চুটিয়ার বাচ্চা কচমচিয়ে চিবিয়ে খেতেন, ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ত রক্ত, তখন চর্বিত ভগ্নাংশ চাওয়া তো দূরঅস্ত্, আমরা দূরে দূরেই থাকতাম আর বলতাম, ‘তুমি কী গো মা!’
তাতেও মায়ের হিন্দোল নেই, ওই শুধু হি-হি করে মা কালীর মতো হাসি।
আমাদের জঙ্গলে একপ্রকার আলু আছে, যার নাম ‘পানআলু’। হয়তো আলুলতার পাতা দেখতে পানের মতোই, তাই পানআলু। সেই পানআলুর পাতা চুন-খয়ের সহকারে আমি আর বোন কতদিন চিবিয়ে দেখেছি – ধুর! কোথায় পান আর পানআলুর পাতা?
ছিঃ থুঃ! ঠোঁট লাল তো হলই না, উল্টে গোটামুখ বিস্বাদে ভরে গিয়েছিল। আমাদের কিত্তি দেখে মায়ের সেদিন কী মুচকি মুচকি হাসি আর গান –
“আলুপতর কি পান হেইব।
পরদেশরে কি মন রহিব।।”
ঠোঁটের কষ বেয়ে চর্বিত পানের রস নয়, লাল লাল চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল কোঁড়ল চুটিয়ার রক্তও না, মায়ের মুখ দিয়ে এখন সাদা সাদা বুজকুড়ির মতো গাঁজলা উঠছে।
ঢুঁড়লে এই জঙ্গলেও কী আর পানআলুর দেখা মিলবে না? মিললেও চুন-খয়ের মিশিয়ে তার পাতা চিবোনোর আর দোসরা পাওয়া যাবে না। একা একা চিবোলেও কে আর তাই দেখে মুচকি হেসে গেয়ে উঠবে – ‘আলুপতর কি পান হেইব?’
না না। আলুর পাতা কখনও পানপাতা হবে না, বিদেশও কখনও স্বদেশ হবে না, মন ‘রহা-রহি’ তো পরের কথা!
রাস্তায় একটা লোক নেই, সুনসান। সুনসান, সুনসান। অথচ একটু আগে – ওই তো ওই, ওই যেখানে শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করে আছে আঁটারি লতা, রাস্তার দুধারে নেমে গিয়েছে মোরাম রাস্তা, হেলা-বটগাছের তলায় একটা জনশূন্য ভাঙা গুমটি – সেখানেই টাঙ্গি-বল্লম কাঁড়-কাঁড়বাঁশ তাবলা-বুড়িয়া নিয়ে কাতারে কাতারে লোক রাস্তা ঘিরে ধরে দাঁড়িয়েছিল!
ফুট্ ফাট্ ফুটুস্ ফাটাস্! কীসব শব্দ হল, জাঁতাকলে পড়ে বেঘোরে একটা লোক মরল, আর মুহূর্তেই সব ভোঁ-ভাঁ, নিমেষে হাওয়া!!
লোক অবশ্য আছে অদূরে ইস্কুলঘরের আনাচেকানাচে, ওই যেখানে কাঠের বেঞ্চিতে শোয়ানো রয়েছে বাবার দেহ। তবে ঝলকে ঝলকে ফটো-তোলা-মেসিন তাক করে ফটো-খিঁচা-মানুষগুলো আর নেই, বেলা থাকতে থাকতে যে যার সরে পড়েছে।
বেলাও পড়ে আসছে, বেলা এখন ঝিরিঝিরি। কখন খসে যাবে টুঙ্ করে! নিঃসাড় হয়ে আসছে বনজঙ্গল, বড় বড় গাছ, গাছতলার ঝোপঝাড়, লাটাপাটা। থেকে থেকে ওই যা দুটো-একটা ‘পাখ’ ডাক দিয়ে যাচ্ছে ঘরে-ফেরানির।
ডাক শুনলেই বুঝা যায় – সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাদের গ্রামের বাঁধগোড়ার জলে হিলহিলে হাওয়া যখন বিলি কাটে, জলের কিনারে দুয়েকটা কুচো বক কি কাদাখোঁচা জলপিপি কি কয়ের-কপতি যখন একপায়ে দাঁড়িয়ে এক পা তুলে গলা ফুলিয়ে গলার সাদা অংশ কাঁপিয়ে “ক-য়ে ক-ক” “ক-য়ে ক-ক” করে ডাক দেয়, তখন বুঝি বৈকি সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরি নেই।
আজ আবার সন্ধ্যা নামবে, রিঁ-রিঁ করে বিরামহীন ‘রিঁ-রিঁ-আঁ’ পোকা ডাকবে, রাত গাঢ় হবে, গেল রাতের মতো বোন নাকফুঁড়ি আজ তো আর ঘুমের জন্য বায়না ধরবে না, রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা ধরে এনে মাটিতে গুঁজে রেখে পরের দিন প্রত্যুষে কেউ আর বিবাহের উদ্যোগ করবে না, বাবা ঘুমন্ত, মা-ও তো ঘুমিয়েই আছেন।
আজ আবার খাবার জুটবে না। এতদিনের সঞ্চয় যা মা আঁকড়ে রেখেছিলেন ওই মাটির কলসিতে, ভাজা ও খোসা ছাড়ানো ‘তেঁতুল মুজি’ আর শুকনো মহুল দানা, তা তো ভেঙে ছত্রখান, এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তায়! তারউপর কত যে গামবুট, মোটরগাড়ি, মিলিটারি ভ্যান – গেল এল! আরও কত আসবে যাবে!! কত যে সরকারি শিলমোহরের ছাপ্পা পড়ল, আরও কত পড়বে!!!
সে যা হয় হোক, এখন কোথাও একটু জল পেলে হয়! মাথায় চোখেমুখে জলের ছিটা দিলে তবে যদি মায়ের জ্ঞান ফিরে!
জলের আশায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছি -ধারেকাছে কোথাও কী একটা বাঁধগোড়া নেই? জল ছিল্ ছিল্ পুকুর? গহম বাঁধ, রিলিফ বাঁধ? কিংবা, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে, কেঁদ-কুসুমের গাছতলা দিয়ে, জইড়তল-বড়তল পেরিয়ে বহন্তি কোনও খাল? এমনকি মরাহাজা কোনও নালা?
জঙ্গলে পাতা ছিঁড়তে ঝাঁটি কুড়োতে গিয়ে ঠা-ঠা খরায় গলা ‘শঁসালে’ জল না পাই, আমরা আঁটারি লতার ডগ্, শালের ডগাল্ চিবোই।
এখন আমি নাহয় – কিন্তু মা? অথচ এই মানুষটাই আমাদের তেষ্টা পেলে অথবা জলের কথা উঠলে একদা বলতেন, ‘যেখানে দেখবি গোল হয়ে চিল ঘুরছে, ঘুরছে তো ঘুরছে, সেখানে জানবি জলের জন্য চিল কূঁয়া খুঁড়ছে। সেখানে গেলে জল পাবিই পাবি।’
মায়ের কথামতো বড় বড় গাছের মাথার ফাঁকফোকর দিয়ে মেঘপাতালের দিকে চোখ তুলে দেখছি – যদি ঘুর্ ঘুর্ ঘুরন্তি চিলের ঘুরে ঘুরে কোনও কূঁয়া খোঁড়ার হাল-হদিস খুঁজে পাই!
কিন্তু হায়! বেলা আড় হয়ে যে অস্তাচলে ঢলে পড়ছে তার মায়ের কোলে, এখন আর চিল কোথায়? সব তো কূঁয়া খুঁড়তে খুঁড়তে ‘থকে’ গিয়ে নেমে পড়েছে খালেবিলে, নদীধারের বট পাকুড়ে!
ইস্কুলবাড়ি যখন, ধারেকাছে কোথাও একটা-দুটো গ্রাম আছেই আছে। গ্রামে মানুষ-জন না থাকে না-ই থাক, কুঁয়ো তো আছে, আছে কুঁয়োয় ধাসাবার দড়ি-বালটিন –
বাবার আর বাধা কোথায়? ‘আয় নাকফুঁড়ি আয়’! মাকে ফেলে রেখেই যাব ভাবছি জল আনতে, জল আনার পাত্র না পাই গলায় জড়ানো গামছাটাই ভিজিয়ে চবচবে করে আনব।
উঠে দাঁড়ালাম – তাহলে যাই? যাচ্ছি! পরক্ষণেই মনে হল, না, ন্না। আমার
অনুপস্থিতিতে কেউ বা কারা যদি এসে ফের তুলে নিয়ে যায় মাকে? তখন? তারবেলা?
ছেড়ে যেতেও ভয়, ছেড়ে যেতেও মায়া! অথচ একটু জল না হলে যে –
একটা ‘গ্যাজর’, তারমানে লাল তেলতেলে বুনো বিছা, ওই, ওই তো রাস্তার ওপার থেকে ছুটে আসছে এপারে, ঠিক মায়ের দিকেই! অঙ্গভঙ্গি ঠিক সাপের মতোই, মাঝেমাঝে ফণা তোলার ন্যায় সামনের শুঁড়দুটি উপরে তুলছে।
হাতে অস্ত্রও নেই যে গ্যাজরটাকে মেরে ফেলব, বাপের হাতের ‘খন্তা’-ও তো বাজেয়াপ্ত। অগত্যা গ্যাজরের যাত্রাপথ থেকে মাকে বগলদাবা করে কিছুটা সরিয়ে আনলাম। গ্যাজর সর্ সর্ করে সরে যাচ্ছে তার মতোই।
গ্যাজরের জায়গায় এবার একটা বিষধর সাপও তো আসতে পারে? হ্যাঁ, আসতে পারে বৈকি। আংকুড়া বাংকুড়া ‘লতা’ – সবাই তো জঙ্গলেরই জীব।
যদিও জঙ্গল ছাড়িয়ে আমরা এখন জঙ্গলের শেষ মাথায়, তবু তাদের বিচরণে বাধা কোথায়? সাপনিধনের লাঠি বানাতে ডকাগাছের একটা আস্ত ডালকে ভেঙে ফেললাম মড় মড় করে। আর এসময়ই দূরে-অদূরে কতকগুলো কুকুর ডেকে উঠল একসঙ্গে!
ইস্কুলঘরের সামনে টহলদারি মিলিটারি পুলিশ শূন্যে ক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল। একজন তো দৌড়ে এল আমাদের কাছে! আবার কী হাফ-পেন্টুলের পকেটে, অস্থানে-কুস্থানে তাঁরা হাঁতড়াতে শুরু করবে?
তার আগেই আমি আমার হাফ-পেন্টুলের ‘পাকিট’-এ হাত রাখলাম। বোন নাকফুঁড়ির গুঁজে দেওয়া ‘রিঁ-রিঁ-আঁ’ পোকাদুটি আছে তো ঠিক?
ফেলেই দিয়েছিল পুলিশটা পকেট হাঁতড়ে, আমি আবার কুড়িয়ে জড়ো করে গামছার সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছি। আহা, কী শক্ত পোকাদুটির শিংজোড়া! একদম যেন লোহার তারের পারা!
‘কৌন হো তুম?’ লম্বা বন্দুক-হাতে পুলিশ লোকটা জিজ্ঞাসা করল। ভাবলাম বলি, ‘ওই যে ইস্কুলঘরের সামনে বেঞ্চিতে শুয়ে লোকটা, যাঁর এতক্ষণ ছবি তোলা হচ্ছিল ফটাফট, যাঁকে তোমরা হয়তো বুদ্ধি করেই বলে বেড়াচ্ছ বেওয়ারিশ ‘লাশ’ – ওই আমার বাবা। আর গুলি খেয়ে লোকটা মারা গেলে তাঁর মৃত্যুতে সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে মুখে গাঁজলা তুলে পড়ে আছেন যে – তিনিই আমার মা।’
কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। কারণ মায়ের মুখেই শুনেছি – “সবু পরব ত আসে ভালা ঘুরি-ন-ঘুরি যে বাবু হো, মানুষ ম-রলে নাহি আওয়ে।”
কিংবা, “আঙটি-ভাঙা পিতল-ভাঙা স-বই জুড়া যায়, মানুষ মরিলে দিদি নাই গ জুড়া যায়।”
তারমানে, এ বছরের পূজা-পরব পরের বছর ঠিকই ঘুরে আসে, কিন্তু মানুষ একবার মরে গেলে সে আর ফিরে আসে না। ভাঙা আংটি ভাঙা পিতলকাঁসা সবই মেরামত করা যায়। তাবলে মরা মানুষকে মেরামতি করে ফের বাঁচিয়ে তোলা যায় না।
ইস্কুলঘরের সামনে বেঞ্চিতে বরাবরের জন্য যে শুয়ে আছে, তাকে তো আর জাগানো যাবে না। সে আর ‘বাবা’ নয়, সে এখন মড়া, মুর্দা। কাঁহাতক তাকে ‘বাবা’ পরিচয় দিয়ে হুট্ মুট্ উটকো বিপদে পড়া !
তাই চুপ থাকলাম।
‘হিঁয়া ক্যায়া করতা?’
দেখতেই তো পাচ্ছ! ফের চুপ।
মিলিটারি লোকটা নিচু হয়ে মাকে ঘাঁটাঘাঁটি করে বলল, ‘বিমারী হ্যায় ক্যায়া?’
তাও চুপ। তার ভাষা হয়তো বুঝতে পারছি না বলে অন্য কাউকে ডেকে আনতে চলে যাচ্ছিল সে। আর থাকতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে তার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেঁদে কঁকিয়ে উঠে বললাম, ‘মায়ের জন্য একটুক জল দাও না গো!’
এবারে আমার ভাষা ওই হয়তো বুঝল না, পা ছাড়িয়ে চলে গেল সদম্ভে। একটু বাদেই এল আরেকজন।
একটুবাদেই কী আর, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে। রিঁ-রিঁ-আঁ পোকাও ডাকতে শুরু করেছে। পাশের জঙ্গলে মাঝে মাঝেই পাখ-পাখালি ভদকাচ্ছে।
তাহলে, গত রাতের মতো আরেকটা রাত আসছে! মায়ের অবস্থা যে-কে-সেই। অদূরে ইস্কুলঘরের সামনে কাঠের বেঞ্চিতে শোয়া বাবার অবস্থাও যেমনকার তেমন।
‘আছা ভালা’ কী করবে ওরা বাবার রোগা-প্যাটকা দেহটা নিয়ে? পয়সা খরচ করে পোড়াবে? না, গাড়হা করে পুঁতে দেবে মাটিতে?
ধুর!! অত কী আর করবে! হয়তো রাতের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেবে জঙ্গলে, শিয়াল-শকুনে টানাটানি করে খাবে, কে আর দেখছে! কে কার বাবা, কে কার স্বামী – বেওয়ারিশ মড়া ছাড়া বা কী!!
একসঙ্গে অনেকগুলো হ্যাজাক ধরানো হল ইস্কুলঘরে। মিলিটারি পুলিশদের একজন তো এ-লাইট সে-লাইটের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে খালি বাতাস দিচ্ছে। এখান থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ইস্কুলঘরের ভিতর টেবিলের চারধারে বসে ওরা কীসব খাচ্ছে! দেখাদেখি খিদে পেল আমারও। সে তো পাবেই, সেই কবে কুরথি ডালের সঙ্গে একমুঠো ভাত খাওয়া। তাও তো আধ-খাওয়া! মা এখন ক্ষুধা-তেষ্টার বাইরে, আমি তাঁর বুকের উপর ফের কান পেতে শুনছি – ধুকপুকানিটা আছে কীনা?
“ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্” – আছে । “ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্” – আছে, আছে!!
আমি পরম নিশ্চিন্তে মায়ের পাশটিতে শুয়ে এখন ভাবছি – সেই আমাদের গ্রামের উত্তরে মাঝুডুবকার জঙ্গলের ভিতরে ঝাঁটিবুদা কেটে তৈরি করা ডাহি জমিনে সেবার কুরথির বীজ বুনেছিল যুধিষ্ঠির কুমহার, সবুজ শুঁড় তোলা কুরথি লতিতে ক্ষেত ভরে গিয়েছিল কানায় কানায়, এমনকি ক্ষেতের চারধারে আলের উপর দিয়ে হাঁটতে চলতে কুরথি লতির শুঁড় এসে দুপায়ে জড়িয়ে যায়। অগত্যা পায়ে মাড়িয়ে দুমড়াতে মুচড়াতেই যেতে হয়। কারণ ওই তো আমাদের গ্রামে যাবার একমাত্র রাস্তা!
ক্ষয়ক্ষতির বহর দেখে আমাকে ডেকে ঝানু চাষী যুধিষ্ঠিরই বলেছিল, ‘বাবু রে, পাহারা দে! তোকে দু-মান কুরথির ডাল খাওয়াব!’
রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে কড়া পাহারাও দিয়েছিলাম আমি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে দু-মান কুরথির ডাল দিয়েছিল মাকে।
দু-মান অর্থাৎ দু-কুনকে বা দু-টোপা। ক্ষেতের কাঁচা ফলও খেয়েছিলাম খুব – দুধ ভরে আসা কাঁচা কুরথিরও যে কী স্বাদ! ক্ষুধা-তেষ্টা দুই-ই একসঙ্গে মিটে যায়।
কুরথি ডালের দুধ ভরে আসা কাঁচা দানাশস্যে এখন ক্ষুধা ও তেষ্টা মেটানোর স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বন্দুকের বাঁটের গুঁতো খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল চট করে।
মায়ের বুকের কাছে উবু হয়ে বসে দু-হাঁটুতে থুতনি গুঁজে জুলু জুলু চোখে চেয়ে থাকলাম পুলিশটির দিকে। আমার ও মায়ের শরীরে টর্চের আলো ফেলে হিন্দিতে নয়, আমাদের ভাষাতেই বলল, ‘ওঠ!’
বলামাত্রই আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকটাও তৎক্ষণাৎ আমার হাফ-পেন্টুলের পকেট হাঁতড়ে বের করে আনল সেই গামছার সুতোয় বাঁধা রিঁ-রিঁ-আঁ পোকার বাণ্ডিলটা। জিজ্ঞাসা করল, ‘এসব কী?’
বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, ‘রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা।’
পুলিশটা গর্জন করে উঠল, ‘হো-য়া-ট? রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা – তারমানে?’
শহরবাজারের মানুষরা হয়তো রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা চেনে না, চেনে না – এখন কী করে তাকে রিঁ-রিঁ-আঁ পোকার মানে বুঝাব ভাবছি।
কোনও কিছু বিষাক্ত পোকা ভেবে তার আগেই জিনিসটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল লোকটা। অবশ্য খুব দূরেও না, আমার পায়ের কাছেই।
জ্বলন্ত টিপা-লাইটের আলোয় চটজলদি কুড়িয়ে এনে ফের পকেটে পুরলাম। আর কী আশ্চর্য! এসময়ই কীনা গাবগুবি গাছের ঝোপেঝাড়ে একসঙ্গে হাজারটা রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা পোঁদ ফেড়ে ডেকে উঠল “রিঁ-ই-ই-ই রিঁ-ই-ই-ই” করে!!
উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, ‘বাবু গ, ঔই ওই ডাকছে পোঁদ ফেড়ে রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা! আনব ধরে? মিলিয়ে দেখবেন?’
ফের গর্জন করে উঠল লোকটা, ‘চো-ও-প! ও তো ঝিঁ ঝিঁ পোকা’।
মাথা নামিয়ে দুহাতের আঙুল মটকাতে মটকাতে বললাম, ‘তাহলে তাই, আমরা তো বলি-’
পুলিশটা বলল, ‘ফের পকেটে পুরলি যে? এ দিয়ে কী করবি?’
বললাম, ‘অষুধ।’
‘কার?’
মাকে দেখিয়ে বললাম, ‘আমার মায়ের’।
মায়ের কথায় একটু যেন নরম হল লোকটা। জিজ্ঞাসা করল, ‘কী হয়েছে তোর মায়ের? কই, ডাক তোর মাকে!’
“কই, ডাক তোর মাকে”, “কই, ডাক তোর মাকে” – মুহূর্তে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মাথাটা। ঠিক একদিন আগে এইরকমই একটা কথায় আমরা ঘর ছেড়েছিলাম।
আমাদের বাবা ধুলো পায়ে কোত্থেকে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করে বলে বসেছিলেন, ‘এখানে আর একদণ্ডও থাকাটা নিরাপদ নয়, আঁকাড়া বিপদ চারধার থেকে ধেয়ে আসছে ধাঁই ধাঁই করে। সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে এক্ষুনি পালাতে হবে। কই, ডাক তোর মাকে!’
বললাম, ‘মায়ের হুঁশ নেই। ডাকলেও আর উঠছে না!’
শশব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ে মায়ের নাড়ি দেখল লোকটা। আঁতকে উঠে বলল, ‘আরে তাই তো!’
ততক্ষণে আরও চার-পাঁচজন মিলিটারি পুলিশ – পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ – চার-দিকেই বন্দুক তাক করে মহড়া দিতে দিতে আমাদের কাছে এসে গেল।
তাদের মধ্যে একজন বলল, ‘মতলব, উঁহাপে যো মুর্দা আদমী, ইহলোগ উসীকা লেড়কা অউর জেনানা আছে?’
কে জানে কী বলল! আমি তো ফেঁসে যাবার আশঙ্কায় ও মায়ের সেই – “সবু পরব ভালা ঘুরি ঘুরি আওয়ে মানুষ মরলে নাহি আওয়ে” – গানের ধুয়ো ধরে মাথা নাড়লাম, না না।
বাঙালি পুলিশটা জিজ্ঞাসা করল, ‘তবে আসছিস কোত্থেকে? যাচ্ছিসই বা কোথায়?’
এখানেও সেই মায়ের বুলি, ‘গিয়েছিলাম কুটুমবাড়ি যাচ্ছি নিজেদের বাড়ি।’
কিন্তু নিজেদের বাড়ি বলে কোন্ গ্রামের নাম করব? ত্যামন নিরাপদ গ্রামনামও তো আমার জানা নেই। চটজলদি মুখে এসে গেল বাবার মাসতুতো ভাইয়ের গ্রামনামটা।
বললাম, ‘যাচ্ছি চিচুরগেড়িয়া।’
সঙ্গে সঙ্গে একাধিক গলায় আওয়াজ উঠল, ‘উরিব্বাস!! খতরনাক জায়গা। উধর আভি আভি মৎ যা না!’
তখনও আমাদের ফেলে রেখেই চলে গেল পুলিশগুলো।
ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মা তো ঘুমোচ্ছেনই। আসলে না ঘুমিয়ে আমাদেরই বা উপায় কী? অবশেষে, রাত তখন কত হবে কে জানে, বেদম আওয়াজ করে একটা গাড়ি এসে থামল।
মাকে ওরা ধরাধরি করে গাড়িতে তুললও। মায়ের পিছু পিছু গিয়ে গাড়ির ভিতরে উঁকি মেরে দেখছি – বাবাও সাদা কাপড়ে দড়িতে বাঁধাছাঁদা হয়ে শুয়ে রয়েছেন। মাকেও তাঁর পাশাপাশি রাখা হল।
বাইরে মাটিতে তখনও আমি দাঁড়িয়ে, গাড়ি ছেড়ে দিল হুট্ বলতে! চলন্ত গাড়ির পিছনে কাঁদতে কাঁদতে পড়ি-কি-মরি দৌড়ুচ্ছি আর পুলিশ বাবারা হো হো করে হাসছে।
ভুখা পেটে প্রায় আধ ক্রোশটাক দৌড়েছি, গাড়িটা থামল। ডালা খুলে আমাকেও তুলল। ও, তাহলে এতক্ষণ!
গাড়ির ভিতর ধাতস্থ হয়ে দেখলাম – না, সবকটা কাঠ-কাঠ মুখ, কেউ একটা কথাও বলছে না। বাবার ঢাকা মায়ের আ-ঢাকা মুখ দেখে যাচ্ছি, দেখতে দেখতে ভাবছি – এরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ‘জিহলখানা’-য়?
‘জিহলখানা’ বা জেলখানাকে বাবার বড্ড ভয় ছিল, মা কিন্তু অকুতোভয়। একসময় তেড়িয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, ‘আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জিহলখানায়?’
কাঠ-কাঠ গুরুগম্ভীর মুখগুলো হেসে ফেলে উত্তর দিল, ‘না, হাসপাতালখানায়।’
বুঝতে পারছি, রাতের অন্ধকারে মিলিটারি পুলিশের গাড়িটা ঘনজঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। কে জানে কোথাকার জঙ্গল!
মাঝে মাঝে গাড়ির আওয়াজকে ছাপিয়েও জঙ্গলের ভিতর থেকে আচমকা একটা-দুটো অচেনা আওয়াজ উঠে আসছে, অনেকটা হনুমানের ডাকের মতো, “হু-উ-প-!”
হনুমানও হতে পারে আর নয়তো জঙ্গলের ভিতরে কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকছে। গাড়ির ছুটন্ত গতিতে সে ডাক কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে, ঠিক বুঝে ওঠা কঠিন।
এক ঝটকায় মনে পড়ে গেল বোন নাকফুঁড়ির মুখটা! এতক্ষণে ছাড়া পেয়ে সে-ই হয়তো ঠোঁট বিদুর করে কাঁদছে, আর কখনও “মা” কখনও “বাপু” বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে। “নী-ই-লু-উ” “নীলুয়া রে-এ-এ-এ” বলে কী আর ডাকছে না?
ডাকছে, ডাকছে।
বন্দুকধারী মিলিটারি পুলিশগুলোর নিরেট মুখের উপর চোখ বুলিয়ে হাঁটুতে রাখা আড়াআড়ি হাতের ভাঁজে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চাপা-গোঙানির মতো ডুকরে কেঁদে উঠলাম।
চোখের লোর কী আর হাতের ‘আড়’ মানে? কাঁদছি অঝোরঝর, অঝোরঝর, কিন্তু তারা কেউ ভ্রূক্ষেপও করছে না।
আমরা একসঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম চারজন। বাবা গেলেন, বোনও। মুখে গাঁজলা তুলে জ্ঞান হারিয়েছেন মা। এখন ওই তো, একজন মরা একজন না-মরা মানুষ পাশাপাশি শুয়ে!
মাঝেমধ্যেই গাড়িটা ঘোঁচ্ করে আটকে যাচ্ছিল, যতবারই আটকাচ্ছে ততবারই খালি মনে হচ্ছিল – এইবুঝি তারা পিঠে সপাটে বুটের লাথি মেরে আমাকে না ফেলে দেয়!
কিন্তু না, গাড়ি থামছিল অন্য কারণে। কখনও বিষধর ‘লতা’ ব্যাঙ কি পাখির কাঁড়াল কোঁড়ল বাচ্চা খেয়ে নধর গতরে লদোপদো করে রাস্তা পার হচ্ছিল ধীরে-সুস্থে, কখন বা ভুঁড়াশিয়াল অতি দ্রুত গতিতে।
গাড়ির জানলার ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটা-দুটো গাছের ডাল হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে আসছিল গাড়ির ভিতর। কুড়চি কি আঁটারি, পড়াশ ঝাঁটির ডাল – যেন কতকালের চেনা, চেনা-চেনা মানুষ।
হাত ধরে গালের উপর চেপে রাখছি। চেপে রাখা কী যায়? সে তো হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সর্ সর্ করে!!
শিরশিরানি হাওয়া ঠোঁটে লেগে ঠোঁট কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। বুঝতে পারছি – শীত আসছে! শীত আসছে!!
বুঝতে পারছি – আর কিছুদিন বাদেই শীতের ‘জাড়’-এ আমার ঠোঁট ফাটবে,
ঠোঁট ফেটে ‘মামড়ি’ উঠবে। মামড়ি-ওঠা ফাটা-ঠোঁটে ঝাল তরকারি কি খাসি মাংসের ‘জ্যুস্’ খেতে গেলে – আহা রে কী কষ্ট! কী কষ্ট!!
খালে, বুড়বুড়ি ঝর্ণায়, নদীতে নাইতে গিয়ে বালিতে, আর নয়তো হাঁসা-পাথরে ঘষে ঘষে ফাটা ঠোঁটের মামড়ি ছাড়াব।
মামড়ি ছাড়ানো ফাটা ঠোঁটের ফাটায় ফাটায় রক্ত। রক্ত মুছে তার উপর মা কাঠি দিয়ে বড়ো আদর করে লাগিয়ে দেবেন কুড়চি গাছের ‘ক্ষীর’, গাঢ় দুধের মতো। ঠোঁট ফাটা কদিনেই ঠোঁট ছেড়ে “বাপ” “বাপ” বলে পালাবে!
আর মা তো বেঁচেই আছেন। এই তো একটু আগে ইস্কুলের জঙ্গলের ধারে রাস্তায় পড়ে থাকা মায়ের বুকে কান চেপে ধরে – তার ধুকপুকানি টের পেয়েছি। এখনও কী উঠে গিয়ে আরেকবার কান চেপে ধরে দেখব?
না, তার আর দরকার কী? ওরা তো বলেইছে, নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালখানায়। সেখানে বড় বড় ‘ডাগতর’ আছে, বিনা পৈসার ওষুধ আছে, চোখ-না-ফোটা লাল লাল কাঁড়াল কোঁড়ল চুটিয়ার বাচ্চা না থাক, ভাতটা রে দুধটা রে – সব নামী দামী খাবার আছে। মা আমার দুদিনেই ‘টেনকে’ উঠবেন।
মা না হয় বেঁচে আছেন, তাই হাসপাতালখানায় ডাগতরের কাছে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু বাবা? তবে কী বাবাও বেঁচে আছেন – ধুলো পায়ে কোত্থেকে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে মাথার উপর হাত ঘুরিয়ে সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিত করা সেই লোকটা?
ওরা ঘুমোচ্ছে, হাতে ধরা বন্দুকের উপর ঠেস দিয়ে। কেউ কেউ গাড়ির গদিতে ঠেস দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আরামসে। ঘুম নেই একফোঁটা আমার চোখে। রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা ডাকছে – রিঁ-ই-ই-ই রিঁ-ই-ই-ই!!
যেন ‘নাইকুণ্ডুল’-এর মূলও নাড়িয়ে দিচ্ছে, কী ‘পোঁদ-ফাটা’ ডাক ! আমার বিরক্ত লাগছে। একে গাড়ির ডাক, একটা তো নয় সামনে আরও দু-দুটো, তার উপর অতিরিক্ত রিঁ-রিঁ-আঁ পোকার ডাক।
সর্ সর্! রিঁ-ই-ই-ই-রিঁ!!
একটু ফাঁকা, জঙ্গল যেন পাতলা হয়ে আসছে। এইমাত্র চলে গেল একটা ‘বাবোই’ ঘাসের ক্ষেত। বাবোই ঘাসের ক্ষেত যখন গেল, ধারেকাছে তখন নিশ্চয় মাহাতোদের গ্রাম আছে, আছেই।
মাহাতোরাই তো বেশি বেশি বাবোই ঘাসের চাষ করে, আর হাত মসকে মসকে রাস্তার ধারে বাবোইয়ের দড়ি পাকায় তাদের ঘরের বুড়োবুড়িরা, তাদের বেটাবেটিরা।
গাড়ি আরেকটু গড়াতেই ঝোপঝাড় লাটাবুদার ভিতর দিয়ে দেখা গেল রাস্তার ধারে ধারে পোঁতা খুঁটির মাথায় বিজলী বাতি জ্বলছে। বিজলীর আলোয় একঝটকায় একটা গাঁ-গেরস্তি, একটা-দুটো টালির বাড়ি, টিনের বাড়ি, এমনকি পাকা বাড়ি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে।
কে জানে এখন কত রাত, আজ ক ঘড়ির ‘জন’, এখনও তো বিজলীর আলোটুকু বাদ দিলে জঙ্গলের গায়ে-মাথায় কালো কালো হাঁড়ির পারা অন্ধকার! ‘জন্’ না থাকলেও একটা ‘মরা’ আলো থাকে, আজ সেটুকুরও বড়ো অভাব!
গাঁ যখন, নিশ্চয় মানুষজনও আছে, ঘুমোচ্ছে, নাকি আমাদের গ্রামের মতোই ‘গাঁ-উজাড়’ করে সবাই ভাগল-বা?
আমাদের সঙ্গেই তো ঘর ছেড়েছিলেন হাঁসুরা, বড়ভদ্র ছোটভদ্ররা, হারানির মা কালামণি, কালীপদ-বধিরামরা, কাঁদরুর বাপ শরাবণরা।
কে যে কোথায় ‘কুটুমবাড়ি’ যাবার নাম করে ‘গাপ্’ হয়ে গেল রাস্তায়! কী করছে এখন মন্মথর বেটা পাড়রু, গুরভার বেটা চৈতন, আর চিনিবাসের বেটা বিনন্দ?
পাড়রু, চৈতন, বিনন্দ আর আমি – মাঠেঘাটে ডুবকাডুংরিতে সাপকাটি-চিহড়-বান্দীর জঙ্গলে ‘কাঁড়-কাঁড়বাঁশ’ ‘টুইলা-সাতনলা’ নিয়ে কোথায় কোথায় না ‘ঢুণ্ডে’ বেড়াতাম!
পালাতে গিয়ে তারাও কী আমাদের মতো হাতেনাতে ধরা পড়েছে? তাদেরও বাপেরা কী আমার বাপের মতোই আনসাটকা গুলি খেয়ে মারা পড়েছে?
কাঠবেঞ্চিতে শুইয়ে রেখে তাদের বাপেদেরও কী অমনি ধারার ফটাফট্ ফটো খিঁচা হয়েছে? তাদের মায়েরাও কী আমার মায়ের মতোই জ্ঞান হারিয়ে মুখ থেকে বুজ্ বুজ্ করে গ্যাঁজলা তুলেছে?
এখনও মরে নাই, যেকোনো সময় টাটকাটাটকি মারা পড়বে?
সেবার তিন বন্ধুতে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম এমনি একটা মাহাতোদের গ্রামে, ‘শুগনিবাসা’-য়। আমি ছিলাম ‘গোল-কীপার’।
গোলে ওপক্ষ এত বেশি বেশি করে বল ঠেলছিল যে, বল ধরতে ধরতে আমার দু-হাঁটুর ছাল গেল ‘ছড়ে’! রক্ত বইছিল দর্ দর্ করে।
চারধারে রুগড়ি ভরা টাঁড়-টিকর, মাঝের ডুংরিতে বলখেলা, বল খেলার মাঠেও রুগড়ি রগ্ রগ্ করছে, তবে মাঝে মাঝে ‘জুরগুঁড়া’ – ওই যাকে ‘বাবুঘরের’ ছা- ছানারা বলে ‘চোরকাঁটা’।
কিন্তু ‘পেনাল্টি-এলাকা’-র ভিতর জুরগুঁড়ার একটা ঝাড়ও ছিল না যে, হাঁটু মুড়ে বল ধরতে ‘সুসার’ হবে।
আচমকা আমার রক্ত-ঝরা হাঁটু দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে দু-দুটো ‘উরুমাল’ নিয়ে দৌড়ে এল এক মাহাতো ‘বিটি’ -মাহাতোদের এক সুন্দরী তরুণী কন্যা!
আমার দু হাঁটুতে পটাপট্ দু-দুটো উরুমাল বেঁধে দিয়ে দু-গালে ফটাফট্ দু-দুটো ‘কিস্’ খেয়ে আনন্দে-উত্তেজনায় পাগল হয়ে বলতে বলতে গিয়েছিল – “হিপ্ হিপ্ হুর্ রে!!”
সেবার সাত-সাতটা ‘সিওর’ গোল বাঁচিয়ে আমরাই তিন গোলে জিতেছিলাম কীনা! পাঁড়রু হাফ-ব্যাক থেকে দৌড়ে এসে আমার কানে কানে বলে গেল, “তোর কী ভাগ্য রে নীলু!”
আজও তুই এসে দেখে যা পাঁড়রু, আমার কী ভাগ্য!! আমি গাড়ি চড়েছি। যে সে গাড়ি তো নয়, মিলিটারিদের গাড়ি।
ভোটের সময়ে গাঁয়ে আসা ভোটবাবুদের গাড়ি নয় যে, গাড়ির ধূলাধূসর গায়ে হাত দিলেও ডেরাইভার খেঁকিয়ে বলে উঠবেন, ‘খোকা, হাত দিসনে, ‘হরেন’ খারাপ হয়ে যাবে।’
কিংবা, ‘টায়ার পাঙচার হবে।’
শুধু মাঝে মাঝে, এঁরা আমাকে গাড়ি থামিয়ে ঠেলে ফেলে দ্যান রাস্তায়, রাস্তায় আমাকে ফেলে তাঁরা তাঁদের গাড়ি অল্পবিস্তর চালিয়ে দ্যান জোরে, জোরে। পড়ি-কি-মরি ছুটতে ছুটতে আমিও গাড়ির পিছন-পিছন ধাওয়া করি, হায়! হায়!! আমার মা-বাবা যে রয়ে গেলেন গাড়িতে?
রঙ্গ-তামাশাই। রঙ্গ-তামাশা সেরে তাঁরা ফের আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে নেন ডেকে। তবু, তবু আশঙ্কা একটাই, খেলা খেলতে খেলতে, খেলার মহড়া দিতে দিতে, কখন যে মিলিটারি পুলিশের গাড়িটা আমাকে বাড়তি ‘আবর্জনা’ ভেবে খেলাচ্ছলে ফেলে রেখেই ছুট দেবে, আর কখনও থামবে না।
অথবা, দুই গাড়ির মাঝখানে ফেলে লোকগুলো উপর্যুপরি গুলি ছুঁড়ে আমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে, যেমনটা করেছে আমার বাবাকে!
কিছু কিছু কুকুর আছে, ছুটন্ত গাড়ি দেখলেই “ভুক্ ভুক্” করে, শুধু “ভুক্ ভুক্” করা নয়, কোনও কোনও কুকুর ছুটন্ত গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতেও থাকে, শুধু ছোটা তো নয়, কখনও কখনও গাড়িকে ছাপিয়েও তার গতিবেগ বেশি হয়ে যায়।
সে তখন টাল সামলাতে সামান্য এগিয়ে যায়। পরক্ষণেই পিছিয়ে আসে, এসেই ড্রাইভারের দরজা বরাবর, যাত্রীদের দরজা বরাবর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বিকট চিৎকার করে তাকে, তাদেরকে কামড়াতে চায়, আচড়াতে যায়।
রাস্তার নেড়ীকুকুর যেমন তেমন, জঙ্গলের জঙ্গলী ‘আদড়া’ কুকুর হলে তো কথাই নেই, আঁচড়ে কামড়ে একশা করবে, টুঁটি কামড়ে ধরবে।
হয়তো মাহাতো গ্রামের কোনও একটা কুকুর, আর নয়তো জঙ্গলের জীব – আচমকা দৌড়ে এসে “ভুক্ ভুক্ ভু-উ-উ-উ” করে, মনে হল, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল।
চিৎকার বাড়ল বৈ কমল না। হঠাৎই একটা গুলির আওয়াজ!
কুকুরটা যেন শূন্যে লাফ দিয়ে “ভু-উ-উ-উঙ-ঞ-চ্” চিৎকার করে উঠে আছড়ে পড়ল মাটিতে, আওয়াজটাও একেবারে থেমে গেল।
আমাদের গাড়ির ঘুমন্ত মিলিটারি লোকগুলো ঘুমে প্রায় এর-তার গায়ে ঢলে পড়ছিল, গুলির আওয়াজে আচমকা জেগে উঠে গুলির কারণ জেনে নিয়ে হাসল, ‘অঃ ইসিলিয়ে?”
বলেই ফের চোখ বোজার আগে কটমট করে তাকাল আমার দিকে, যেন এটা আবার কোত্থেকে এল?
কেউ কেউ বিড়ি-সিগারেট মুখে দিয়ে দাঁতে চেপে প্যান্টের পকেটে ধুলো ঝাড়ার মতো থাপ্পড় মেরে মাচিস বের করে বিড়ি-সিগারেট ধরাল। তারপর হুস্ হাস্ টেনে ধোঁয়ার রিং বানিয়ে আমারই মুখের দিকে পাঠিয়ে মুচকি হাসল।
তারমধ্যে আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘ক্যায়া? নিঁদ আতা নেহি? লেট্ যাও বস্! আভি ভি আসপিটাল করীব দূর বা!’
আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমোবার ভান করে চোখ বুজলাম।
ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ধীরে ধীরে চোখ খুলে পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছি – ওই তো মা, ওই তো বাবা!
দুজনেই সাদা থান-কাপড়ে মোড়া, অবশ্য মায়েরটা গলা অব্দি। তারমানে মা এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু বাবারটা মুখ-কান ঢাকা, বাঁধাছাঁদা। এমনটা দেখেছিলাম ওই যখন আমাদের গ্রামের তিলোচাঁদকে সাপকাটির জঙ্গলে বাঘ না বাঘারুলে কামড়ে গলার টুঁটি প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিল! গ্রামের লোকেরা তাঁকে ধরাধরি করে দড়ির খাটিয়ায় শুইয়ে গলায় তিলো- চাঁদের বউয়ের পুরাতন শাড়ি পেঁচিয়ে কাঁধে তুলে দোলাতে দোলাতে নিয়ে গিয়েছিল সাপ-ধরা ‘হেল্থ্ সেন্টার’-এ। দুদিন তিনদিন ছিলেন, তাও বাঁচানো গেল না। তাঁকে যখন গ্রামের লোকেরাই ফের খাটিয়া করে নিয়ে এল, তখন তাঁর সারা অঙ্গ, এমনকি কান, মাথা, মাথার চুলও নতুন থান-কাপড়ে মোড়া ছিল, গলার কাছেও কাপড়ের একটা প্যাঁচ ছিল।
বাবার সঙ্গে তাঁর সাদা থানকাপড়ের একটু উনিশ-বিশ আছে। কেননা, বাবার গলায় কাপড়ের কোনও গেরো নেই। এমনি এমনিই কপাল অব্দি বিছানো, এমনকি মারার চুলগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে!
তবে কী বাবা আমার এখনও বেঁচে আছেন? ‘হে-ই বড়ামথান! হে-ই বাবা কালুয়াষাঁড়!! বাঁচিয়ে দে তুই রোগাভোগা বাসটাকে, মা-টারও হুঁশ ফিরিয়ে দে! দে বাবা, দে!!’
ওরা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে হ্যাঙলার মতো হাঁ-করে, যেন কতকাল ঘুমোতে পায়নি। বনেবাদাড়ে লাটায়পাটায় কখনও বন্দুক ঘাড়ে, কখনও বন্দুক তাক করে হাঁটা।
হাঁটা, হাঁটা। কখনও পায়ে এসে জড়ায় চিহড় চুরচু ‘হাতিবাঁধি’-র লত্, কখনও খরিস্ চন্দ্রবোড়া শিয়রচাঁদা রাতভিতের ‘লতা’।
জড়াতে জড়াতে ছাড়াতে ছাড়াতে হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে ঘুম কী আর আসে? এলেও ঘুমের ‘ডগ্’-টা মুচড়ে ভেঙে দিতে হয়।
এখন গাড়িতে চড়ে বেশ দুলতে দুলতে যাওয়া, হাঁটা তো নয়, না-ঘুমের-ক্ষতি ঘুমিয়ে যতটা পারা যায় পূরণ করা।
ওরা ঘুমোচ্ছে, হাতে-ধরা বন্দুকের উপর ঠেস দিয়ে, কেউ কেউ নাক ডাকাচ্ছে “ঘ-ড়-র-র-র-র্…ঞশ্চু” করে।
মাঝে মাঝেই বন্দুকে রাখা হাতের মুঠিটা কারোর কারোর আলগা হয়ে যাচ্ছে, বন্দুকটা পড়ে যাচ্ছে দেখে ঘুমের ঘোরেই ফের যেন আঁকড়ে ধরছে, আরও জোরসে।
কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হাতের মুঠো থেকে একটা বন্দুক খসে পড়ল ঠিক আমার নাকের ডগায়, বন্দুকের মাথার ‘ছুরি’-টা ঠক্ করে লাগল আমার কপালের মাঝ-খানে!
আমি জাপটে বন্দুকটা হাত-মুঠোয় ধরে অবিকল তাঁদের মতোই বসে থাকলাম। খালি গা, কোমরে বাঁধা গামছা, মরা রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা পকেটে, হাফ-পেন্টুলের বন্দুকধারী ‘পল্টন’।
কিন্তু সে আর কতক্ষণ! যার বন্দুক সে তড়াক্ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে কেড়ে নিল বন্দুকটা। ‘রীতিমতো পজিশন’ নিয়ে আমার বুকের কাছে যন্তরটা ঠেকিয়ে তার সে কী কায়দা! কী আস্ফালন!!
অন্যেরা জেগে উঠে রগড় দেখে বলল, ‘চল্ রহা ক্যায়া?’
আস্ফালনকারী বন্দুকবাজ হেসে উত্তর দিল, ‘এ লেড়কা মেরা রাইফেল হাইজ্যাক্ কিয়া।’
কেউ যেন বলল, ‘মাও বা? কিতনা উমর?
তারাই দেখেশুনে সাব্যস্ত করল, ‘করীব্ আঠার-উনিশ সাল তো হোগাই।’
তাদের কথা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছিলাম না, বুঝার কথাও নয় আমার! যদিও আমার ঠিক বয়স এখন ষোল।
অবশেষে তারা গাড়ি থামালো। মিলেজুলে সবাই বলল, ‘উও লেড়কা লোগকো ফিন্ উতার দেও।’
আবার আমাকে নামিয়ে দিল ওরা। অবশ্য তারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে নামল। রাস্তার ধারে একজন বন্দুক উঁচিয়ে তাক্ করে দাঁড়াল, আরেকজন তার বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে ‘পিসাব’ করল ছর্ ছর্ করে।
একজনের পালা শেষ হলে আরেকজন।
আমার ক্ষুধাতেষ্টা নেই, সব মরে গিয়েছে কখন! তবু তো ‘পিসাব’ পায়। রাস্তার এধার-ওধার নয়, মাঝখানে দাঁড়িয়েই আমি হুড়্ হুড়্ করে পিসাব করলাম, করছিও।
আর ওরা হো হো করে হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল! সেই বলে না – “কার ঘরে ডিঁগা ডিঁগা, কার ঘরে ডাল মুরগা। কেরকেটা পড়েছে ফাঁদে, মাছ-রাঙা ডাঙায় কাঁদে?”
আমার মা মর-মর, বাপ মরে গিয়েছে, বোন হারিয়ে গেছে-আমি মরছি শোকে। আর ওরা মজা মারছে। পেচ্ছাপ করতে করতেই গাড়ির পিছন পিছন দৌড়ুচ্ছি।
এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। কে জানে আজ ক ঘড়ির ‘জন্’, ক ঘন্টা পরে চাঁদ উঠেছে? বনেজঙ্গলে ‘জন’-এর ওঠাওঠি দেখেই তো রাতের বেলা সময়ের হিসাব হয়। পূর্ণিমার পরের দিন উদয়ের একঘন্টা পরে চাঁদ ওঠে, তাই ‘একঘড়ির জন’।
এই কদিন তো সব হিসাব তালগোল পাকিয়ে গেছে। নচেৎ মা আঙুলের ‘কড়’ গুনে গুনে ‘জন’-এর হিসাব রাখেন। ঘরের দেয়ালে রেখ্ কেটে কেটে অমাবস্যা-পূর্ণিমা দিন-ক্ষণ মাস- বছরের অঙ্ক কষেন।
আহ্ মা, মাগো!!
জঙ্গল এখানে পাতলা, আঁটারি লতার শুঁড়গুলি, ডগগুলি নড়ছে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পেচ্ছাপের জলে রাস্তায় আঁকিবুকি কাটতে কাটতে দৌড়ুচ্ছিলাম, গাড়ির গতিবেগও ততটা প্রবল ছিল না, বরঞ্চ কমে আসছিল ক্রমশ।
আমার ধারণা, আগের বারের মতোই ওরা আমাকে ফের গাড়িতে তুলবে, কিছুতেই ফেলে যাবে না, আমাকে নিয়ে তারা টুকচার রগড় করছে, এই যা।
জঙ্গলের ওদিকে কোথাও অসময়ে একটা মোরগ ডাকল। তারমানে ধারেকাছে একটা লোকালয় আছে, আবার পরক্ষণেই মনে হল – ‘বন-খুকড়া’-ও হতে পারে।
আর ঠিক এসময়ই আমার ভয় ধরল – যে কোনও মুহূর্তে ওরা আমাকে গুলি করবে, গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে আমার ‘ধুকপুকি’-টা!
একবার আমাদের গ্রামের ধারে ঝিটকার জঙ্গলে বাবার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ‘খেড়িয়া’ শিকারে এসেছিলেন পুলিশে কাজ করা ডাইনটিকরির খাঁদুকর্তা। সঙ্গে একটা দো-নলা বন্দুক আর দুদুটো পাঁচ-ব্যাটারির ‘টিপালাইট’।
টিপালাইট সে এক মজার গ্যাঁড়াকল। নাকি আঙুল ছোঁয়ালেই ধোঁয়াধার আলো, আর সে-আলো ‘খেড়িয়া’ বা খরগোশের চোখে পড়লে তারও নড়ন চড়ন ‘নট’।
একটা টিপালাইট আমার হাতে, আরেকটা বাবার – ডাইনটিকরির জঙ্গলে আমরা ‘ফোকাস’ ফেলছি আড়াআড়ি।
অকস্মাৎ একটা খেড়িয়ার বাঁ চোখে পড়ল আমার হাতের আলো, ডান চোখে বাবার। খরগোশটা সামান্য লাফিয়ে উঠে, ‘চিঁড়রা’ অর্থাৎ কাঠবিড়ালীর মতো সামনের দুপা জড়ো করে বোধহয় প্রাণভিক্ষাই চেয়েছিল।
এমনসময় খাঁদুকর্তার বন্দুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল তার ধুকপুকিটা! হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে বাইরে এসে মাটিতে পড়ে লাফাচ্ছিল ‘ব্যাঙটুনি’-র মতো।
সেই পাপেই হয়তো আজ গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল বাবার ধুকপুকিটাও! এখন কী এবার আমার পালা? অথচ খাঁদুকর্তা তো দিব্যি বেঁচে আছেন বহাল তবিয়তেই!
পালাব কী? ডাইনে-বাঁয়ে, পিছনে – যে কোনও দিকেই যদি দৌড়ায় লাটাপাটা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, ভালুকঝোড়-ঝিঁকরঝোড়, বরা বা শিয়ালঝোড়ের ভিতর দিয়ে, মিলিটারি পুলিশগুলোর সাধ্য কী পিছু পিছু দৌড়ে আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে?
তবে ওই একটাই ভয় – পিছন থেকে যেকোনও মুহূর্তে দেখামাত্রই বন্দুকের ঘড়া টিপে “ফ্যাত্” করে গুলি মেরে দেবে পিঠে! আমাকে আর তাদের দরকার কী? আমি তো অতিরিক্ত, ফালতু একটা!
কিন্তু আমার বাবা-মা? তাঁরা যে এখনও পাশাপাশি শুয়ে পড়ে আছেন গাড়িতে? কথার কথা, একজন না হয় ‘মরা’, আরেকজন তো ‘অ-মরা’। তারবেলা?
আর না-দৌড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপচাপ, দেখি-ই না ওরা কী করে? এখন তিন-তিনটে গাড়িই আমার সামনে। আমাদের গাড়িটা মনে হল গতি কমিয়ে সামনে না গিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে আসছে।
ওরা ভেবেছে কী – জঙ্গলের মাঝখানে আমাকে গাড়িতে তুলে ফের গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে হেনস্থা করবে? কীরকম হেনস্থা – বনে-বিভুঁইয়ে একলা পড়ে থাকলে আমাকে বাঘে-হুঁড়ারে ভালুকে-ল্যাকড়ায় খেয়ে ফেলবে?
দিনের পর দিন অনাহারে থেকে খেতে না পেয়ে কাঠ হয়ে শুকিয়ে মরব? আর তাছাড়া, ‘বনপার্টি’-রা এসে আমাকে কুড়িয়ে পেয়ে তাদের দলে ভিড়িয়ে ‘গাপ্’ করে দেবে?
আহা, ওরা তো আর জানে না, ভাদুতলা-শালবনি-আসনবনি-পিংবনি-কাঁটাবনি-জামবনি, বেলপাহাড়ি-কাঁকরাঝোড়-কাঁটাপাহাড়ী-বাঁশপাহাড়ি, তপোবন-কমলা-সোল-পাঁচকাঁহানিয়ার জঙ্গলে বাঘ তো বাঘ, একটা বাঘারোল-হুঁড়ার-ল্যাকড়াও পাওয়া যাবে না, ওই বড়জোর একটা-দুটো বরহা-ঝিঁকর-খেড়িয়া কী খেঁকশিয়াল।
ভালুকেরও আজকাল আকাল! ভালুকওয়ালা – অবশ্য একটা-দুটো নাকে দড়ি বেঁধে খেলাতে নিয়ে আসে, তাও তো কালেভদ্রে!
তবে “হুপ্! “হুপ্!!” – বিস্তর হনুমান আছে বৈকি এ দিগরে! কখনও বটগাছের ঝুরি ধরে দোল খাচ্ছে, কখনও ডুমুরগাছে –
পাকা ডুমুর যত না পেড়ে খাচ্ছে, তার থেকে ছড়াচ্ছে বেশি গাছতলে। ওই, ওই -যেখানে জঙ্গলের মাথায় চাঁদোয়ার মতো চাঁদের আলো ফুটেছে, আলোও মনে হচ্ছে ধোঁয়া, ধোঁয়া, ধোঁয়া -সেখানে “হুপ্” করে একটা আওয়াজ উঠল! ওই আরও দুটো – “হুপ্! হুট!!”
বাবুরা, জঙ্গলে খাবার-দাবারের অভাবের খোঁটা দিচ্ছ, বলি, তাহলে শোনো –
বৈশাখ-জষ্ঠি-আষাঢ় – ফলপাকুড় কুড়োবার পাতা ছিঁড়বার
মাস। কেঁদ-কুসুম-কচড়া-বেল-কোঁৎবেল-ভেলা-ভুড়রু-জাম-
জামরুল-আম-পঁড়স-খেজুর-বৈঁচি গাছ থেকে পাড়ো আর খাও।
শালপাতা ছিঁড়ে থালা বানাও দোনা বানাও। আর কেঁদপাতা
বিড়িপাতা। তোলো, বাণ্ডিল করো, শহর- বাজারে চালান দাও।
‘সাতনলা’ ‘লাটাচুলী’ ‘কাঁড়-কাঁড়বাঁশ’ নিয়ে শিকারে যাও,
‘দিশম্ সেঁদরা’-য় কয়ের-কপতি-গুঁড়ুর-ট্যাঁসা-কেরকেটা-চড়ৈ-চটা-
বনি-গুয়েবনি শিকার করো। খঙ্গা-বঙ্গা-ঢ্যামনা-গোঈ-গোধি-
গেঁড়ি-গুগলি-খেড়িয়া-বরহা – যত পারো ধরো।
রিমঝিম করে জঙ্গলে ঝড়িয়া-বরষা হলে জলে ভিজে
মাটি ‘বতর’ হয়। বতর মাটিতে পুঙ পুঙ করে ‘ছাতু’ ফোটে।
শালপোঙড়া, সরুবালি, বড়বালি, কুড়কুড়িয়া, কাড়হান, পরব
ছাতু, সাদা ভণ্ডা, লাল ভণ্ডা।
আলু-তুঙা হয় – পানআলু খামআলু চুরচু আলু, আঁউলা-
বাঁউলা। চিরোল চিরোল পাতা গজায়, চ্যাঁকা-শুশনি-সরন্তি-
ঘোড়াকানা-ঘলঘসি শাক লহ্ লহ্ করে, লই-লতিতে থোঁকা
থোঁকা ফুল হয়, ফল হয় -বনপুঁই-বনকাল্লা-কুঁদরি-কাঁকড়ো।
শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে ‘জনার’ গাদর হয়, মকাইয়ে
পাক ধরে। জঙ্গলের ভিতরে খাল-নদী-ঢড়হা-কংসাবতী-সুবর্ণ
রেখা-ডুলুঙ-কুবাই-তমাল-পারাং-শিলাবতী – সব ভরাজলে টই-
টম্বুর।
খল্ বল্ করে ওঠে শোল-মাগুর-চ্যাঙ-গোড়ুই, অল্প
জলে ছির্ ছির্ করে পুঁটি-দাঁড়িকিনি-চাঁদা-ধানাহূলু। বিলে-
বাতানে বাঁধগোড়ায় কাঁদরে জলের ধারে নরম মাটিতে
কাঁকড়া তার অতগুলো দাঁড়ায় আঁকিবুকি কাটে, গর্তে ঢুকে
জলে বুজ্ বুজি তোলে। বুজ্ বুজি দেখে গর্তের পাশে ‘গজাল’
গুঁজে দিলেই ডিমাল কাঁকড়া বেরিয়ে আসবে চাপে পড়ে।
তখন মারো রে, ধরো রে।
কার্তিক-অঘ্রাণ-পৌষ – ধানকাটা ধান তোলার কাল।
শুখা মরশুম। ঠোঁট ফাটে, গায়ে খড়ি ফোটে। যার ধান সে
কাটে, সেই তোলে। আমাদের আর কি! ধান-কাটা-ন্যাড়া-মাঠে
পড়ে থাকা যা ধানের শিষ। ধানের ‘টুঙ’ কুড়াই আমরা “খুঁজে
খুঁজে নারি। যে পায় তাহারি।”
ধানবিলের ‘হিড়’ কেটে ইঁদুরের ‘গাড়হা’ থেকে ‘ইঁদুরধান’
যেটুকু পাই, সে তো পাই, তারসঙ্গে পেয়ে যাই ছোটো ছোটো লাল
লাল চোখ-না-ফোটা কাঁড়াল কোঁড়ল চুটিয়ার বাচ্চা। মা তো
আমার সেসব গোটা গোটা মুখে পুরে কাঁচাই কচমচিয়ে চিবিয়ে
খান! তাঁর দুঠোঁটের কষ বেয়ে তখন কাঁচা লোহু ঝরে।
আর, মাঘ-ফাগুন-চোত্ তো মধুর মাস। মহুলগাছে
মধু, চাক-ভাঙা-মধু -খাও রে, বেচো রে, মদ ‘চুয়াও’ রে!!
তবে হ্যাঁ, আজকাল জঙ্গলে ‘বনপার্টি’ – এক সমস্যা বটে! বহিন
নাকফুঁড়িকে কী ‘বনপার্টি’-রাই গাপ্ করেছে?
পিছোতে পিছোতে গাড়িটা আমার সামনে এসে ‘ব্রেক্’ কষল। হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল বন্দুকধারী মিলিটারিরা। আমাকে পাকড়াও করে বলল, ‘ক্যা, ভাগনেকো লিয়ে মতলব্ কিয়া?’
আমি ‘হাঁ’ ‘না’ – কিছুই বললাম না। তবে হাত চাপাচাপিতে টানাহ্যাঁচড়ায় বুঝলাম – এ পর্যন্ত তাদের কাছে ‘ফালতু আবর্জনা’ ছিলাম, এতক্ষণে ভারি ‘দরকারি’ হয়ে গেলাম।
তারা টেনে হিঁচড়ে আমাকে গাড়িতে তুলল, ‘চুপচাপ বৈঠ্ রহো! নেহি ত আঁখি বনধ্ কর্ লেট যাও!
আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে বসলাম – এখন ভারি তো দরকারি হয়ে পড়লাম! তবে কী এরা বাবা-মাকে হাসপাতালখানায় পৌঁছে দিয়ে আমাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে ‘বনপার্টি’-র লোক সন্দেহ করে জমা রেখে আসবে ‘জিহলখানা’-য়?
জিহলখানাকে বাবার বড়ো ভয় ছিল। আমিও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। এত জোরে জোরে কাঁপছি যে, দু হাঁটুতে ঠক্কর লেগে খট্ খট্ আওয়াজ উঠছিল।
এক বন্দুকধারী তার বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার হাঁটুতে সামান্য আঘাত করে বলল, ‘হিলতি কিঁউ রে? জাড়া লাগতি হ্যায় ক্যা?’
তাহলে বনের রাস্তা ‘ফুরাঁইল’, এতক্ষণে শেষ হল। ওই তো বনধার! ঝোপঝাড় লাটাপাটা আর নেই, ছাড়া ছাড়া একটা-দুটো গাছ।
বড় বড় গাছ, শাল-আসন গাছই হবে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় খুঁটির উপরে বিজলী বাতি জ্বলছে। “গিড়্ গিড়্ দাগিন্ গেঁদা” – যেন মরা খুঁটির মাথায় আলোর ফুল ফুটেছে!
ফুল, ফুল।
পলাশ, সুরগুঁজা, ধাতকি, কুড়চি, আঁটারির ফুল তো নয়, এ ‘হৈল বিলাইতি ফুল’, আলোফুল। তার কবে যে এজাতের ফুল আমাদের গাঁ-গেরাম-ঝিটকার জঙ্গলে ফুটবে? জঙ্গল ধব্ ধবাবে?
রাস্তার চলমান-বিজলী-আলো গাড়ির ভিতরে এর-তার মুখে পড়ে চকিতে ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুখগুলো কিন্তু যেমনকার তেমন, নির্বিকার। ঘুমে এখনও ঢুলছে।
এত আলো, এত আলো, বোধকরি কোনও শহর-বাজার এসে গেল! তারমানে তো হাসপাতালখানাও এসে গেল। হাসপাতাল যখন তখন ‘জিহলখানা’-ও আর দূরে নয়।
আমার হাঁটু-ঠকঠকানি কমল তো না, বরঞ্চ বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল। কে জানে কোন্ শহর! রাস্তায়, রাস্তার বিপরীতে ট্যাক্সি গাড়ি মোটরগাড়ি, সাইকেল-রিক্সা-ভটভটি, এমনকি বাসগাড়িও যাচ্ছে আসছে।
ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। পাতার ঝুপড়ি, কুঁড়িয়া ঘর, বাঁশ বা শালরলার ভুগড়া ঘর তো নয়, সব বড় বড় পাকাঘর। রঙ-করা, কোন-কোনটা চুনের মতো ধবধবে সাদা। কোথাও বা ঠাকুরথান, মন্দির।
লোকজনও দেখা যাচ্ছে – ওই, ওই তো একজন। সাইকেলের ‘রড’-এ প্রায় শুয়ে পড়ে পেডেল করছে। ঝাড়গাঁ না মেদিনপুর? আমাদের কাছেপিঠে ওই দুটো শহর-বাজারের নামডাকই তো আছে।
তা বাদে আছে বটে ‘সাপধরা’ আর ‘চাঁদাবিলা হেল্থ সেন্টার’। কিন্তু কোথায় চাঁদে আর মেনি বান্দরের –
কটা ঘন্টা বাজল। একটা নয়, একসঙ্গে অনেকগুলো। ঢং ঢং ঢং ঢং…!!
‘হাটুয়া’ ছা-ছানাদের ইস্কুলে এমনিতরো ঘন্টা বাজে। কিন্তু সে তো রাতের বেলা নয়, দিনমানে। তবে কী এখন এখানে ‘রাত-ইস্কুল’ চলছে?
আমাদের গ্রামেও একটা রাত-ইস্কুল ছিল। ছিল, ছিল। সেখানে যতসব বুঢ়হা-বুঢ়হিরা পড়ত। হারানি-বেজু-বঢ়কয়-হাসনমণি-কাঁদুরারা। পাঁড়রু চৈতন বিনন্দ আর আমিও ক’মাস ঢুকেছিলাম বড়দের সঙ্গে।
আন্দাজে আন্দাজে, কখন বা অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে ‘জন’-এর উদয় দেখে একঘন্টা অন্তর অন্তর বাজানো হত ঘন্টা -ঢং ঢং!!
পড়াশোনা না হোক, ছাত্রসংখ্যা যত নগন্যই হোক, ঘন্টাটা কিন্তু বাজত ‘ঘড়ি’ ধরে ধরে। আসল কথা কি, লেখাপড়া করতে নয়, ঘন্টা বাজাতেই যেন কেউ কেউ যেত রাত-ইস্কুলে।
ঢং ঢং!!
সে ঘন্টাধ্বনিও আর নেই, সে রাত-ইস্কুলও আর নেই। তবে ঘন্টাটা এখনও আলবাৎ আছে। গোলাকার পিতলের চাকতি, দড়িবাঁধা। আরেকটা কাঠের মুগুর। ‘ঘড়ি’ ধরে ধরে কাঁদরুর বাপ শরাবণ এখনও কী ঝড়িয়া কী বর্ষায় ঘন্টা বাজান – ঢং ঢং ঢং ঢং!!
আর বাজবে না – কেননা তিনিও তো ‘কাঁটাদুয়ারি’ করে বেরিয়ে এসেছেন ঘর ছেড়ে। তাঁর ঝুপড়িতেই তো বসত ‘রাত-ইস্কুল’।
রাত-ইস্কুলে আরেকটা কাণ্ড হত। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ‘শীতলামঙ্গল’ যাত্রা-পালার মহড়া। সে-যাত্রাপালা গাওনা হত পৌষসংক্রান্তি অর্থাৎ মকরের দিন রাত্রে।
সকালে মকরস্নান, শীতলাথানে ঘট-আনয়ন, দেহুরির পূজাপাঠ, তারপর তো বলিদান। ‘খুকড়া বলি’ ‘পাঁঠাবলি’। অবশেষে বলির মাংস, পিঠাপুলি আর মদ-হাঁড়িয়া খেয়ে খলা-আঙনায় গড়াগড়ি। রাতে –
‘শীতলামঙ্গল যাত্রা’। সারা বছর ধরে তার মহড়া চলত ওই রাত-ইস্কুলেই। আমি, পাঁড়রু, চৈতন আর বিনন্দ – ‘নাচুনী’ সেজে প্রথমে ‘গরাম দ্যাবতা’-র বন্দনা করতাম। সেই বন্দনাগীত এখনও মনে আছে –
“এহি বাটে আসুছন্তি গাঁয়ের গ্রাম।
উত্তর-দক্ষিণ পূরব-পশ্চিম।।
তার নামে সঞ্জিয়া যোগাই মুই রে।
এহি বাটে আসুছন্তি মা যে শীতলা।।
রুগিনী-যুগিনী-ওলাওঠা বুড়ি।
বসন্তকুমারী-চামডলিয়া বুড়ি।।
তার নামে সঞ্জিয়া যোগাই মুই রে।।”
ঘন্টাধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না, থেমে গিয়েছে। রাস্তায় লোকজন বাড়ছে, বাড়ছে আলোর ঝলকানি। কথাবার্তাও। মাহাতো-কথা শোনা যাচ্ছে। ওই তো দুজন সাইকেল আরোহী পাশাপাশি যেতে যেতে এ-ওকে বলছে, “ধূর্ ব! কালে ল্লে বইল্যে আসছিন্ ঐ একেই কথা ন, তার কে শুনছে!”
সাইকেলবালা কাল থেকে কাকে যে কী কথা বলে আসছে, আর যাকে বলা সে যে কেন শুনছে না – জানা গেল না, জানা গেল না।
‘আছা ভালা, ‘হাসপাতালখানা’ আর ‘জিহলখানা’ কী কাছাকাছি এসে গেল?’ আমার চোখ-কান চারধারটা গোগ্রাসে গিলে চলেছে, শুনে চলেছে। আর, ততই হাঁটুজোড়াটার ঠক্ ঠকানি বাড়ছে তো বাড়ছেই।
এর আগে কোনওদিন তো ভুলেও শহর-বাজারে আসিনি! হাত দিয়ে দুহাঁটুর মাঝখানে ‘ইয়ের’ জায়গাটা দেখলাম – কেমন যেন ‘ভিজা’ ‘ভিজা’ লাগছে! তবে কী আমি মুতে ফেলেছি ভয়ে?
এতটাই ডরপুক্? এতটাই ডরপেলকা?
অনর্গল ঘন্টা বাজাতে বাজাতে একটা লাল রংয়ের মস্ত গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে হুঁকরে ছুটে গেল। মায়ের কথা বাপের কথা, যাবতীয় ভানাচিন্তা এখন মাথা থেকে উধাও।
উধাও, উধাও।
ওই তো একটা দোকান, পানবিড়ির দোকান কী? ওই, ওই তো আরেকটা!! সাঁক্ সাঁক্ করে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে দোকানপাট। সরন্তি রাস্তাঘাটের আলো এসে চোখে মুখে বিঁধছে, ঝলকাচ্ছে।
জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে লাটায়পাটায় গাঁদারগুঁদুর অন্ধকারে এমনিতেই আমাদের চোখের পাতা পিট্ পিট্ করে, আর এ তো আলোরইবানবন্যা!
ভালো করে তাকাতেও পারছি না। সে না হয় চোখ বুজেই থাকলাম। কিন্তু, কিন্তু – এরপরেও ‘কিন্তু’ আছে – চোখ বুজে কান ঝুলিয়ে বালুতে মুখ লুকালেই কী আর ‘খেড়িয়া’-র ধুকপুকিটা রক্ষা পায়?
ওদিকে খাঁদুকর্তার ছোঁড়া ‘ছড়রা’ যে পিঠে এসে লাগল বলে! “রোজ রোজ ঘুঘু তুই খেয়ে যাস ধান। আজ ঘুঘু তোর বধিব পরাণ।”
অবশেষে গাড়ি এসে থামল। এই তাহলে হাসপাতালখানা? না, জিহলখানা? বড় বড় বাড়ি, কত বড় বড় ঘর! কত কত গাড়ি! হেথা হোথা খুঁটিতে ঝুলছে কত বড় বড় আলো। আলোর চারধারে ধোঁয়া ধোঁয়া, তার চারধারে অজস্র ‘নিরঘুইন্না পোকা’!!
কী পোকা? ‘সালোই’ না ‘বাদৈল্যা’? – ওই যারা ভড়্ ভড়্ করে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পরে পরেই খতখানা থেকে, নোংরাজবরার গাদা থেকে ভুস্ ভুস্ করে বেরিয়ে এসে উড়তে থাকে।
সারা আঙনাময় ডানা মেলে উড়েঘুরে বেড়ায়। ফিনফিনে ডানা, সামান্য ওড়া-ঘোরা করলেই খসে যায়। তখন থুপ্ করে মাটিতে পড়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।
মাটিতে পড়লেই গিনা-বাটি-তাটিয়ায় কুড়াও রে, বালির খলায় ভাজো রে, কুড় মুড় করে খাও রে!! চালভাজার মতো খেতেও তো মন্দ না।
তা ঝড়িয়া-বরষার দিন তো গত হয়ছে কবেই ! এমন অসময়ে ‘বাদৈল্যা’ পোকা বা আসবে কোত্থেকে? ওসব নিরঘুইন্না ‘পাদুরা’ পোকাটোকা হবে।
আগের গাড়িদুটো একটু আগেই হাসপাতাল না জেলখানা চত্বরে ঢুকে পড়েছিল। তাদের ব্যস্ততা ভারি। গাড়ি থেকে নেমেই ছট্ ফট্ করছে। গামবুট পায়ে খট্ খট্ আওয়াজ তুলে একবার এদিকে আসছে, একবার সেদিকে যাচ্ছে।
আমাদের গাড়িটা ঢুকে পড়তেই তারা চারধার থেকে ছেঁকে ধরল! ততক্ষণে আমার বুঝি হয়ে গেছে! ‘ঝরণ’ তো শুরু হয়েছিল একটু আগেই, এবার তবে বাঁধভাঙা অঝোরঝরে নেমে পড়বে?
আমাকে টানাহিঁচড়ান করে নামিয়ে নিয়ে চালান করে দেবে জিহলখানায়? কিন্তু না, গাড়ির পিছনের ডালা খুলেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমার মাকে নামিয়ে নিতে।
বুঝলাম, তবে জিহলখানা এ নয়, হাসপাতালখানাই হবে নিশ্চয়। বাঁধাছাঁদা হয়ে গাড়িতেই পড়ে থাকলেন বাবা, মাকে ওরা সযত্নে নামিয়ে রাখছে।
দুজন মিলিটারি পুলিশ হাসপাতালের অন্দরে ঢুকে পড়ল শশব্যস্ত হয়ে, হয়তো ডাক্তারের খোঁজে। পরক্ষণে বেরিয়েও এল, তাদের পিছন পিছন এল হাসপাতালেরই দুজন লোক, হাতে তাদের খাটিয়ার মতো সাদা কাপড়ের দোলনা। মাকে এবার ধরাধরি করে দোলনাতে তোলা হবে।
গাড়ির ডালা খুলে ওরা যখন ধরাধরি করে মাকে নামাচ্ছে, ধরাধরি নামানামিতে ভারি ব্যস্ত, তখনই, বলতে কি তারও আগে চোখের নিমেষে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলাম আমি!
যত আলো তত অন্ধকার। যেখানে যেখানে আলো পড়ছে, সেখানে সেখানে ‘ফিন্-ফোটা-জ্যোৎস্না’-র মতো আলোয় আলোময়। কিন্তু যেখানে একফোঁটাও আলো পৌঁছাতে পারছে না, সেখানে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার।
তারউপর ঝাঁকড়া শালগাছের ছায়া পড়েছে, পড়েছে ‘পাকা ঘর’-এর ছায়া। হাসপাতালখানার চৌহদ্দিতে তো অভাব নেই শালগাছের, অভাব নেই পাকা ঘরেরও।
কত কত গাছ! কত কত পাকাঘর!! বনজঙ্গলের মতো মাঝে মাঝে রাতের পাখ, রাতচরা পাখি গাছে গাছে ভদকাচ্ছে, ‘কহরাচ্ছে’।
উপরের ঘরের ঝুরকায় ঝুরকায় আলো জ্বলছে, আলো জ্বলছে নিচের ঘরগুলোয়ও। কিন্তু যে ঘরে আলো নেই সে ঘরে এক ঘর কালো হাঁড়ির অন্ধকার।
তারমধ্যে কোথাও একজায়গায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়ে আছি, ধরা পড়লেই দৌড়ুব রিটপিটে দৌড় – দৌড় – দৌড় –
ওদের জনাকতক মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালখানার বড়বাড়ির ভিতরে ঢুকল। হুটোপুটি করে ঢুকছে, যেন তাদের হাতে ফালতু ফালতু নষ্ট করার মতো অত সময় নেই।
যে কজন মিলিটারি পুলিশ বাইরে খামোখা দাঁড়িয়েছিল, তিনজন ড্রাইভার বাদে তারাও সব ভিতরে ঢুকে পড়ল।
তিন ড্রাইভার একজোট হয়ে এখন সিগারেট খাচ্ছে, খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে কাশছে
গলায় ‘গয়ের’ তুলে। কথা বলছে, কথা বলছে – কত কী কথা!
‘কৈ? ডেরাইভার বাবুরা ত হামাকে লিয়ে অ্যাকটা কথাও বলছে নাই?’
বিস্মরণ হয়ে গেছি বাবুদের? অতিরিক্ত, ফালতু। ফালতু, ফালতু। ফালতু একটা লোককে কারই বা অত মনে রাখার দরকার? সেই বলে না “কোথাকার কে, দুটো আমড়া ভাতে দে?”
হাসপাতালের গেটের ধারে বাজারের রাস্তায় এখনও লোক-চলাচলের বিরাম নেই। আর হাসপাতাল যখন সময় অসময় নেই-রুগী নিয়ে রুগীর লোকজন তো আসবেই, আসছেও।
বোধকরি হাসপাতালে যাঁরা ডিউটি করেন, তাঁদের কেউ কেউ ডিউটি সেরে এখন হাসপাতালখানা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ওই, ওই তো একজন -সাইকেলে চড়ে গেট পার হচ্ছেন। পরনে কুঁচি দেওয়া শাড়ি, ফুলহাতা সাদা সেমিজ, মাথায়ও কী সাদা ফেট্টি বাঁধা?
দিঙ্ দিঙ্ করে আমার মনে পড়ে গেল বহিন নাকফুঁড়িকে। হাত চলে গেল সুড় সুড় করে হাফ-পেন্টুলের পকেটে।
সুতোয় বাঁধা সেই দুটো ‘রিঁ-রিঁ-আঁ পোকা’! ‘বর-কইন্যা’।
পকেটের বাইরে এনে অন্ধকারেও আঙুলে টিপে টিপে দেখছি, আর অমনি একটা সাদা বিল্লী ঝুপ্ করে নামল আমার মাথার উপর দিয়ে মাটিতে। আচমকা আমাকে দেখতে পেয়ে মিঞ মিঞে গলায় ডেকে উঠল, “মি- ঞা-ওঁ!!”
আমিও ফিস ফিস করে উত্তর দিলাম, ‘হঁ হঁ, ডাক! ডাক রে নাকফুঁড়রি! ‘ভাই’ বলে ডাক বহিন!! তোর ভাই এখন মস্ত ফাঁদে পড়েছে।’
মিলিটারি পুলিশগুলো বন্দুক-হাতে গট্ মট্ করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে। নেমেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। টর্চ লাইট জ্বেলে বোধ করি আমাকেই খুঁজছে!
তাহলে এতক্ষণে মনে পড়েছে তাদের – অতিরিক্ত, ফালতু লোকটাকে? তাদের ভাষায় কী যেন বলাবলি করছে!
একবার তো বলল – ‘ঢেঁডরি, কাঁহা গৈল বা!’
কে ‘ঢেঁডরি’ কী ‘ঢেঁডরি’ – কিছুই তো বুঝতে পারছি না!
‘ঢেঁডরি’ বলল, না তার অন্যকিছু – কে জানে! তারা টর্চের ফোকাস ফেলে ফেলে সামনের সারা মাঠটা ঢুঁড়ছে, শালগাছগুলোর উপরও তল্লাশি চালাচ্ছে।
কিন্তু আমি তো দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছি একটা অন্ধকার ঘরে, পেট তাবুড় দিয়ে শুয়ে আছি একটা খোঁদলে।
টিপালাইটের ফোকাস এলেও পিছলে যাবে উপর দিয়ে। জানি জানি, একবার আমার হদিস পেলেই হয়! বুটের লাথিতে পিঠের ছালচামড়া ফাটিয়ে ছাড়বে। তারপর হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাবে ‘জিহলখানা’-য়।
আমাদের গাড়িটা বাবাকে নিয়েই বেরিয়ে গেল সাঁৎ করে, দেখলাম। হয়তো তারা যাবে আরও কোন বড় হাসপাতালখানায়। সঙ্গে গেল ক’জন বন্দুকধারী মিলিটারি।
বাকি বন্দুকধারীরা আপাতত খোঁজাখুঁজি ছেড়ে একজায়গায় জড়ো হয়ে বোধকরি যুক্তি করছে, ফন্দি আঁটছে তল্লাশি আরও কী করে জোরদার করা যায়!
নাকি, একটা অতিরিক্ত, ফালতু লোককে খোঁজাখুঁজির আর কি দরকার বলে হাল ছেড়েই দিচ্ছে মিলিটারি লোকগুলো – ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবু ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি, কেঁপে যাচ্ছি।
খোঁদলের ভিতর থেকে মুণ্ডুটা সামান্য উঁচু করে দেখছি – জোড়া জোড়া পা, জোড়া জোড়া গামবুট হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, পায়ের ফাঁকে ফাঁকে এই আলো, এই অন্ধকার।
আমার হাফ-পেন্টুলের তলায় দু’পায়ের ফাঁক দিয়ে প্রায় গড়িয়ে পড়া জলের ধারাকে দাঁতে-দাঁত কামড়ে কোনও মতে আটকে রেখেছি, কিন্তু সেই বলে না – “হাগা না মানে বাঘা?”
যেই জোড়া জোড়া পায়ের হাঁটাচলা শুরু হল এধার ওধার, মনে হল গামবুট পরা লোকগুলো এগিয়ে আসছে এদিকেই, তখন আমার ‘দমে’ হয়ে গেল!!
না, মিলিটারি পুলিশগুলো এদিকে এলই না, ওরা ওদিকে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ধুপ্ ধাপ্ শব্দ করে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছেড়েও দিল।
এখনও উঠে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছি না, কেননা আরেকটা মিলিটারি গাড়ি তো আছে। আছে, আছে। তবে তার লোকগুলো আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, যে যেমন গাড়িতে উঠে আলো না জ্বেলে চুপচাপ বসে আছে গাড়িতেই।
তার কারণ, তাদেরও তো ভয়ডর আছে – অন্ধকারে আড়ালে আবডালে কখন কে কোথায় ঘাপ মেরে, বলা তো যায় না – সুযোগ এলেই ‘ফ্যাৎ’ করে –
খানিকটা মরীয়া হয়েই উঠে দাঁড়িয়েছি, গামছা দিয়ে পা-জাঙ মুছছি, হঠাৎ হেডলাইট জ্বেলে একটা গাড়ি ফিরে এল।
বাবাকে নিয়ে যে-গাড়িটা বেরিয়ে গিয়েছিল, সেইটা? নাকি একটু আগে যেটা রওনা দিয়েছিল, সেটা?
ঠিক বুঝতে পারছি না। বিদ্যুদ্বেগে ফের খোঁদলে সটান শুয়ে পড়লাম – “নিচে হল্ হল্ উপরে তুলসীর জল!” সেই অবস্থায় কাছিমতুল্য ঘাড়টা ঈষৎ উঁচু করে দেখছি -দুজন মিলিটারি পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে এল গট্ গট্ করে।
একজনের কাঁধে বন্দুক, হাতে ধরা কী একটা প্যাকেট। আরেকজন বন্দুক তাক করে তার পিছন পিছন। ওই যে ওই – বলা তো যায় না –
সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই হাতে-প্যাকেট-ওয়ালা পুলিশটা কাকে যেন হাঁক দিল! বাপ রে, সে কী বাজখাঁই গলা!! তারউপর সে-ডাক পাকাঘরের ভিতর ঠোক্কর খেতে খেতে আরও যেন বড় হল, যেমনটা হয় আমাদের ‘তিলকমাটিয়া হুড়ি’-তে।
‘তিলকমাটিয়া হুড়ি’ – সেও তো এমন চার-পাঁচটা পাকাঘরেরই সমান উঁচু। সাইকেলে যাও আর হেঁটেই যাও – ধার ঘেঁষে যেতে যেতে যদি কখনও হাঁক দাও “স্যা-ঙা-ৎ হে-এ-এ-এ”, তবে সে-হাঁক তিলকমাটিয়া হুড়ির গায়ে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে তোমার কাছেই ফিরে আসবে “স্যা-ঙা-ৎ হে-এ-এ-এ”, আর তুমি ঠিক শুনবে “-আ-ছি- হে-এ-এ-এ!!”
এ এক মজার গ্যাঁড়াকল!
হুঁকরাতে হুঁকরাতে দুটো গাড়িই চলে গেল, আমারও বুকের উপর থেকে চাপিয়ে-দেওয়া-দেড়মনী পাথরটা কে যেন সরিয়ে নিল!
বা, তাও-ও নয়। এক ‘ঘরোয়ালী’ আজরাতে ‘ঠেকা-চাপা’ দিয়ে রেখেছিল একটা ‘খুকড়া’-কে কাল সকাল হলেই কেটেকুটে খাবে বলেই! তো, সকালে কী মনে করে ঠেকাটা উল্টে দিয়ে ঘরোয়ালী বলল, “যা চরেঁ খা!” অমনি খুকড়া-মোরগ ডানা ফেটিয়ে ‘আড়িশ’ ভেঙে উড়ে উঠেই পগার পার!!
আমারও হল সেই অবস্থা। ধড়ফড়িয়ে উঠে হাত পায়ের ‘আড়’ ভেঙে গলায় গামছা জড়িয়ে রগড়াতে রগড়াতে অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়ালাম।
হাসপাতালে লোকজন এখনও ঢুকছে বেরুচ্ছে। কেউ সাইকেল টেনে নিয়ে ছুট্ লাগাচ্ছে, কেউ হয়তো পায়ে হেঁটে ঢুকছে ধীরে ধীরে।
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সাদা শাড়ি সাদা হাত-জামা, মাথায়ও সাদা রঙের কুঁচি-দে-ও-য়া টুপি। ‘এড়ি’তে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হয়ে কাকে যেন খুঁজছেন, কাকে যেন! কাকে? হাতে একটা প্যাকেট?
যাকেই খুঁজুন, যাই ত, যাই! গলায় গামছা জড়িয়ে রগড়াতে রগড়াতে গেলামও।
দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই যে, সি.আর.পি.এফ-এর গাড়িতে কী তুই ছিলি?’
‘হাঁ’ বললে কী হবে আর ‘না’ বললেই বা কী হবে -টুকচার ভাবলাম। তারপর মাথা নাড়লাম।
ফের জিজ্ঞাসা ‘গাড়িতে যে রুগী ছিল, সে তোর কে হন?’
স্বীকার করব কি করব না? সহসা মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, ‘হঁ, আমার মা ছাড়া আবার কে? মা-ই বঠে ন্ন!!’
সোন্দরী মহিলা, মনে ত লয় ‘ডাগতর’, আর নাহলে নার্স। বললেন, ‘কচি রে, তোর মায়ের ‘স্ট্রোক’ হয়েছে। বাহাত্তর ঘন্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না!’
স্টোক? কে জানে ওটা কী রোগ? আর বাহাত্তর ঘন্টা? তাই বা কে জানে ক’দিনে?
আমি আর কী বলি? ঘাড়-মাথা নিচু করেই আছি।
সহসা ‘দিদিমণি’ আমার হাতে একটা প্যাকেট, সেই যে সেই প্যাকেটটাই গুঁজে দিয়ে বললেন, ‘এই নে, ধর! সি.আর.পি.এফ. খাবার দিয়ে গেছে তোর!’
আমি হামলে পড়ে প্যাকেটটা নিলাম। খাবার? আহা রে, খাওয়া হয়নি কতকাল!! সেই তো কবে, কুরথির ডাল –
হ্যাঙলার মতো প্যাকেট খুলে গবাগব্ খেয়ে চলেছি – ডিম, পাঁউরুটি। রুটি, তরকারিও আছে। আছে, আছে। ‘দিদিমণি’ তখনও দাঁড়িয়ে।
খাবার মুখে পুরে ‘চাভলাতে চাভলাতে’ জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আর আমার বাবা?’
‘কে তোর বাবা?’
‘কেন, মায়ের ‘সঙে’ একগাড়িতেই তো ছিলেন?’
রীতিমতো চিৎকার করে উঠলেন ডাগতর দিদিমণি, ‘তবে যে ওরা বলল – বেওয়ারিশ লাশ?’
‘বে-ও-য়া-রি-শ লা-শ? তা-র-মা-নে?’
কিছুই বুঝলাম না। ফের জিজ্ঞাসা করলাম, ‘বাবা এখন কোথায়?’
‘মর্গে।’
‘স্বর্গে? না, মর্ত্যে?’ – কী বলল? বলল কী? ঠিকঠাক বুঝতেও পারলাম না। ‘দিদিমণি’ তো খটাখট্ আওয়াজ তুলে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলেন উপরে, ‘স্বর্গেই’।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন
