নবকুমার বসু
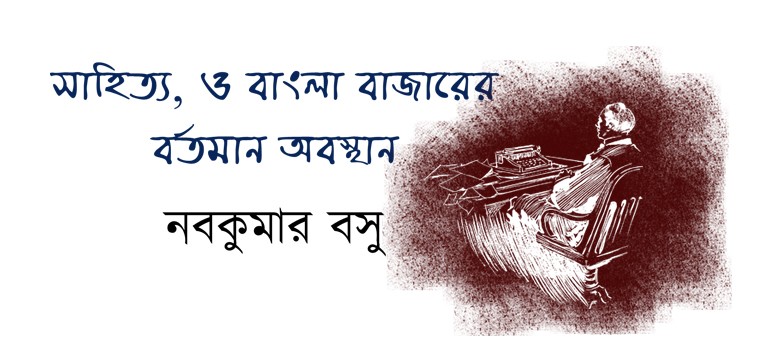
সাহিত্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস কিংবা দীর্ঘদিন যাবৎ সাহিত্যচর্চা করলেই যে সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য, তার তুল্যমূল্য বিচার, বিষয় নির্বাচন, গঠনপ্রক্রিয়া… ইত্যাদি অবলম্বন করে নিবন্ধ রচনার দায়বদ্ধতা অনুভূত হবে, এমন কোনো কথা নেই। দায়িত্বের কথা তখনই মনে আসে, যখন এই মাধ্যমের সঙ্গে ঘর করতে করতে নিজেরই অনুভূতির তলদেশ কিছু বলার কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসতে চায়। ব্যক্তি বিশেষে এই অনুভূতির অস্তিত্ব নিয়েও কথা উঠতে পারে। এমন অনেক সাহিত্যকার আছেন, যাঁরা জীবনের কয়েকটি দশক ধরে নাগাড়ে সাহিত্য রচনা করেই গেছেন কিংবা লিখে গেছেনও বলা যায়। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এমনকিছু বলার বা প্রকাশের আবেগ, দায়বদ্ধতা অনুভূত হয়নি (নাকি সময় পান নি), যা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
তবে কিনা সাহিত্যে নিবেদিত অনুসন্ধিৎসা মনন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠে আসে এই প্রসঙ্গে। সেটি এই যে, যে বিষয়, যার চর্চা, যার সঙ্গে জীবনযাপন… হয়তো জীবিকা নির্বাহ-ও এবং যে কর্ম করার জন্য কেউ কখনও মাথার দিব্যি দেয় নি অথচ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মতো পবিত্র-ঐকান্তিক-অনিবার্য আগ্রহে জীবনের অংশ করে নেওয়া, তার সম্পর্কে আমার কোনো বলার কথা অনুভূতির তলদেশে জমবে না, তা কি খুব স্বাভাবিক?
স্বাভাবিক না। কেননা সাহিত্য ভাবনার জগত ও দৃষ্টি থেকে উৎসারিত। যে ভাবুকের মন এই দুইয়ের অধিকারী তিনিই সাহিত্যিক। সাহিত্যের যে কোনো শাখার কথাই বলা হোক, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-রম্যরচনা… এমনকি নাটকরচনা বা নাট্যসাহিত্য রচনায় প্রাথমিক শর্ত এই দুটি জিনিস, ভাবনা ও দৃষ্টি। আর ভাবনা এবং দৃষ্টি যেটা করে, তা হচ্ছে, বাইরে থেকে যা কিছু আমরা আহরণ করি, মনের ভেতর ঢুকে, তা আর এক নতুন জগত সৃষ্টি করে। সেই নতুন জগত বা জগতের নতুনত্ব-ই প্রকাশিত হয় আমাদের লেখায়… সাহিত্য বাইরের জগতের সঙ্গে তখন তাকে আর মেশানো যায় না। তার কারণ, ভাবনা আর দৃষ্টি ওই দুই উপকরণের সঙ্গে নীরবে এবং নিভৃতে আরও একটি যে ব্যাপার ক্যাটালিস্ট বা উদ্বোধকের মতো মিশে যায়, তারই নাম অনুভূতি।
সুতরাং যা দাঁড়াল, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অলক্ষ্যে যে ত্রয়ী ক্রিয়াশীল, তারা হল, ভাবনা, দৃষ্টি ও অনুভূতি। এমনভাবেও বলা যায়, ভাবনা ও দৃষ্টির উপকরণকে অনুভূতির আঁচে উপযুক্তভাবে পরিপাক করতে পারলে, (ক্ষীর-শর্করার মিশ্রণকে যেমন আগুনের উত্তাপ সহকারে) সাহিত্যের সন্দেশ বানিয়ে তোলা যেতেও পারে।
এই কর্ম করতে করতে আগুন কিংবা আঁচের কোনো প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ অনুভূতির কিছুমাত্র কি সাহিত্যিক মননের তলদেশে জমা পড়ে না! তাকে ‘বলার কথা’ বলব, নাকি অভিজ্ঞতা, নাকি বয়সের ভারসঞ্জাত বকবকানি, সে কথা আলাদা, কিন্তু কিছু সঞ্চিত যে হবেই, তা এমনকী এই অধীনও টের পেয়েছে। আর পেয়েছে বলেই আজ সাড়ে চার দশকের ওপর চর্চার অধিকারে কিছু লিপিবদ্ধ করাকে প্রগলভ্তা বদলে দায়বদ্ধতা বলেই মনে করছি।
এই কথার সূত্রেই তাহলে উপরোক্ত একটি মন্তব্যের কিঞ্চিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এমন কিছু লেখক-সাহিত্যিক আছেন, যারা নিজের যাপিত জীবনের একটি দীর্ঘ সময় ধরে প্রভূত লেখালিখি করেছেন, গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তা সে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যও হয়তো। তারপরেও তাহলে সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের কোনো বক্তব্য নেই কেন?
এই প্রশ্নের দুটি উত্তর হয়।
প্রথম উত্তরটি এইরকম মানুষদের সারস্বত সাধনায় কৃতবিদ্য এবং সম্মানীয় করে তোলে এবং সেই উত্তরটি হচ্ছে, তাঁরা তাঁদের লেখা এবং রচনার মধ্যেই তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত বোধ ও ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এমনভাবেই যে, আলাদা করে ভাবনার তলদেশ থেকে উৎসারিত হওয়ার আর কিছু ছিল না।
দ্বিতীয় উত্তরটিকেও আমাদের গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। সেই উত্তর হচ্ছে, সেই লেখকবৃন্দ যাঁরা বছরের পর বছর ধরে পাতার পর পাতা লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যে না আছে কোনো সাহিত্য ভাবনার ব্যাখ্যা। না আছে পরবর্তীকালে অন্য প্রবন্ধ নিবন্ধের মধ্যেও সাহিত্যরচনা ও বোধ সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ তাঁরা শুধু লিখেছেন। হয়তো গল্প, উপন্যাসের বইও হয়েছে। এ প্রশ্ন করা শোভন হবে কিনা বলতে পারি না যে, সেইসব রচনা কতখানি সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। গল্প-উপন্যাসের বই মাত্রই সাহিত্য হয়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই। আষাঢ়ে গপ্পো লেখারও লোক আছে। আবার বটতলার বইয়েরও লেখক আছে। এ হেন লেখক আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। সম্ভবত লেখক হওয়ার তাড়না এবং প্রবণতা ইদানীং যে-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাইতে এই দ্বিতীয়-উত্তর সম্প্রদায়ের লেখকের সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে। অসংখ্য বই প্রকাশিত হওয়া এবং আমার মতো প্রবাসী লেখকেরও আজকাল অনেক বই উপহার পাওয়ার ঘটনায় এই “শুধু লেখক” সম্প্রদায় সত্যটির প্রমাণও পাওয়া যায়। গাদাগাদা বই পড়ে থাকে এবং ধুলো জমে।
খ্যাতিমান প্রয়াত লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য ওই ‘শুধু লেখক’দের লেখা ও বই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে। শ্যামলদা ওইসব বইয়ের ও লেখার তুলনা করতেন কাগজের ঠোঙা-র সঙ্গে। বলতেন, ওসব লেখার ভবিষ্যৎ হচ্ছে, চালডাল বা মুড়ি চিঁড়ে চিনি বা মশলার ঠোঙা। অস্বীকার করব না, এহেন লেখক, বই এবং ঠোঙার সন্ধান আমরা পেয়েছি। সত্যি বলতে কি তেমন লেখকদের সংখ্যা যে নেহাৎ নগণ্য নয়, তা আমরা অনেকেই জানি।
অথচ এই বাস্তবতার পাশাপাশি আর একটা কথাও খুব সত্যি যে, মানুষের হৃদয়ের আকুলতা কিন্তু অনেক কিছু না ভেবেই নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য ছটফট করে। সেই প্রকাশ, যে আকুতি, নাম বা গঠনের মাধ্যমেই হোক, ভালমন্দ যাই হোক, আসলে সেইটাই হচ্ছে সাহিত্যের আবেগ।
আর একথা তো অনস্বীকার্য যে আবেগ অথবা ইমোশন ব্যতিত সাহিত্যকর্ম কেন, কোনো সৃষ্টিধর্মী কাজই হয় না। কিন্তু বিচার করার দরকার হয়, সেই হৃদয়ের আকুলতা আর আবেগের মধ্যে, প্রকাশের সময়, কতটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। কে করে সেই বিচার? সাহিত্য ক্ষেত্রে পাঠক ছাড়া আর কে! এবং পাঠক তা করেন সচেতন না হয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই সামঞ্জস্যকে আমরা আকুলতা আর আবেগের ভারসাম্যও বলতে পারি, যা জন্ম দেয় সাহিত্যের।
কিন্তু শুধু কি তাই? না। রচনাশক্তির নৈপুণ্য – শেষপর্যন্ত সাহিত্যকে পাঠযোগ্য ও ভাবনার উপযুক্ত করে তোলে। আসলে কথা থেকেই কথা বাড়ে, এক কথা থেকে এসে পড়ে আরও পাঁচ কথা।
এই যে ‘রচনাশক্তির নৈপুণ্য’ কথাটা লিখলাম, ভেবে দেখুন তো মাত্র দুটো শব্দের মধ্যে কি বিপুল ব্যাখ্যার আকাশ থেকে যাচ্ছে। সাহিত্যক্ষেত্রে রচনাশক্তির নৈপুণ্য বলতে তো সবই এসে পড়ে। বিষয় ভাবনার কথা ছেড়ে দিলেও, নেহাৎ উল্লেখ করার জন্যই বলি, এই নৈপুণ্যেরই অন্তর্গত হচ্ছে, বাক্যগঠন, বাক্যের মধ্যে টেন্স্ এবং ভয়েস-এর ব্যবহার, সংলাপ, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা… কতটা দিতে হবে কিংবা হবে না, ফ্ল্যাশব্যাকে-এর ব্যবহার, পরিচ্ছেদ ভাগ… সবকিছুই কি এসে যাচ্ছে না, যা একটি রচনাকে নিবিড় নিয়ন্ত্রণের সাহিত্য করে তোলে। আর তা যদি সত্যিই হয়, ভেবে দেখবেন, সাহিত্যকর্ম তখনই সফল হয়, যখন তা যথেষ্ট সমসাময়িক হয়েও, একইসঙ্গে অতীতকে অস্বীকার করে না, বরং মনে পড়ায়, এবং ভবিষ্যৎকে স্মরণ করার জন্য ইঙ্গিতবাহী হয়ে থাকে।
এর পরের কথাটাই হচ্ছে প্রকাশ।
কাব্য হোক, সাহিত্য-শিল্প যাই হোক, প্রকাশের মধ্যে দিয়েই যে তার চরিতার্থতা, এটুকু বোঝা এবং উপলব্ধির জন্য কোনো অতিরিক্ত মেধার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু সাহিত্য সংক্রান্ত নিবন্ধে আমাদের তা উল্লেখ করতে হবে দুটি কারণে। এক হচ্ছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। আর এক হচ্ছে, প্রকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠককে আর একটু সচেতন এবং উদ্বুদ্ধ করতে। কেননা, যে যাই বলুক, কবি লেখক সকলেরই লক্ষ্য আসলে পাঠক সমাজ। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যসম্পর্কিত তাঁর এক রচনায় লিখেছিলেন, “… নীরস কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে…”। সুতরাং আসল কথাটা হচ্ছে, যে কোনো রচনাই লেখকের নিজের জন্য না… তিনি প্রকাশ করতে চান অন্যের জন্য… কেননা প্রকাশের আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যত নিজেকে প্রকাশ করা যায়, যতই নিজের অস্তিত্ব দৃঢ় হয়ে ওঠে।
এখন তো না হয় প্রকাশের আগ্রহ এবং প্রকাশ মাধ্যম নিয়ে ছেলেখেলা করার যুগ এসেছে। সে কথায় আমরা পরে আসব। কিন্তু যারা সেই ছেলেখেলাটা করে, তাঁদের অবগতির জন্য শুধু মনে করিয়ে দেব যে, একদিন নিজেকে প্রকাশের জন্য এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ কী না করেছে! সম্রাট অশোক, তাঁর নিজের কথাগুলো আগামী দিনের জন্য, কালের জন্য পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে দিয়েছিলেন। কেননা পাহাড় অনন্তকাল ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর যুগের পর যুগ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে – ওখানে কিছু লেখা, কিছু ভাবনার, কিছু কথার প্রকাশ আছে বলে।
সত্যিই তো! আজ কোথায় সেই সম্রাট অশোক, কোথায় সেই পাটলিপুত্র… কত পাঠান-মোগল-রাজপুত-বর্গিরা দাপিয়ে গেল ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে… দিনে দিনে বদলে গেল দেশ, তার সভ্যতা, সংস্কৃতির কত মিশ্রণ ঘটে গেল। কিন্তু পাথরের গায়ে খোদাই করা সেই লিপি রয়ে গেল কাল থেকে কালান্তরে… একদিন লিপি থেকে উদ্ধার হল ভাষা-ও। আর হাজার বছর আগেকার এক সম্রাটের নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছা প্রাণিত হল।
না, অশোকের শিলালিপির সেইসব ভাষ্য যে সাহিত্য তা নয়।
কিন্তু বহু অতীত থেকেই মানুষের নিজেকে প্রকাশের আকাঙ্খা কত তীব্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু যে লেখার মধ্যে তাই বা কেন? মূর্তি, ছবি, মন্দির, ভাস্কর্য … এসব নির্মাণও কে সেই একই কথা বলে না! আর এই সবেরই উদ্দেশ্য একটাই। মানুষ আন্তরিক হয়ে বেঁচে থাকতে চাইছে আরও মানুষের মধ্যে।
কিন্তু এই চাওয়ার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য চাওয়া ও অস্তিত্বে তফাৎ আছে।
একটা ব্যাপার বুঝতে হবে যে, সাহিত্য রচনা করতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও, সেটাই সব নয়। সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন কিন্তু ভাব… ভাবের বস্তু ও বিষয়। জ্ঞান আসলে চিরপরিবর্তনশীল এবং সেই কারণেই ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানের কথা, যেমন – পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। একথা একবার জানা হয়ে গেলে নতুন করে আর জানার দরকার হয় না। কিন্তু ভাব আর ভাবের কথা যতবারই বলা যায়, তা প্রতিভাত হয় বিভিন্ন মাত্রায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় – সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, এটা জ্ঞান। কিন্তু সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য হচ্ছে ভাবের বস্তু। জ্ঞানের প্রসার দরকার হয়। ভাব হচ্ছে সৃষ্টির জিনিস। সেই সৃষ্টির ব্যাপারে এবং তার প্রতিষ্ঠাতেই সাহিত্যিকের পরিচয়… ভাবকেই একজন লেখক তাঁর রচনায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাকে বলা হবে ভাবপ্রকাশ। আর সেই প্রকাশ যখন সর্বজনীন মুগ্ধতার দ্যোতক হয়, তা সাহিত্য হিসেবেও স্থায়িত্বে চিহ্নিত হয়।
আর ঠিক এই উপলব্ধি থেকেই বেরিয়ে আসে আর একটা কথা। সেটা হচ্ছে, বাস্তবের সত্য, জীবনের সত্য এবং প্রত্যক্ষতার সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের তফাৎ আছে। আবার রবীন্দ্রনাথ কোট করে বলছি, “… সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না…”। আবার তার অর্থ এই নয় যে, সাহিত্যের সত্যটা সত্য নয়। সুতরাং দুটোই সত্য, কিন্তু সাহিত্যের সত্য তার প্রকাশের গুণে অথবা বৈচিত্রে প্রকৃত সত্যের চেয়েও অন্যরকম একটা অনুভূতি সঞ্চার করে। সাহিত্য ছাড়াও অন্য শিল্পমাধ্যম, যেমন ভাস্কর্য বা চিত্র শিল্পও একই কথা বলে।
একটা ব্যাপার শুধু আমাদের বুঝে নিতে হবে।
এই যে আগের প্যারাগ্রাফে ‘অন্যরকম একটা অনুভূতি’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছি। ওই অনুভূতিটাই হচ্ছে আর্ট। ব্যাপারটা সূক্ষ্ম। কিন্তু যে কোনো শিল্পচর্চা করতে গেলেই, ওই সূক্ষ্মতাটুকুই শিল্পীর আসল পরিচয়। ওটুকু না থাকলে চলে না। লেখকের ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে, ওই অনুভূতি এবং তার সঠিক অথবা অমোঘ প্রকাশ, দুই মিলে তাঁকে সাহিত্যিক করে তোলে। এই কথাটাই ঘুরিয়ে বললে, এভাবে বলা যায় যে, সাহিত্যিক তথা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে, ভাবের বিষয়বস্তুকে ভাষায়, অন্তরের জিনিসকে বাইরের এবং সমকাল ও ক্ষণকালের বিষয়কে চিরকালের করে তোলা। সেটা করে ওই সূক্ষ্ম অনুভূতি।
এতো কথা বলার পরে, সাহিত্য ব্যাপারটা কী – এ সম্বন্ধে একটু ধারণা নিয়ে আমরা ক্রমশ বিষয়ান্তরে যাব।
সাহিত্য শব্দটা এসেছে ‘সহিত’ শব্দ থেকে। সহিত মানে আমরা জানি – সাথে বা সঙ্গে ইত্যাদি। অর্থাৎ শব্দরূপ বা ধাতুরূপ যদি বিচার করা যায়, তাহলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটা সম্পর্ক কিংবা মিলনের ব্যাপার আছে বোঝা যায়। এবং তাকে আর একটু ব্যাখ্যা করতে বলা যায়, এই মিলনটা কিন্তু শুধু ভাব-ভাষা-বই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। সাহিত্যের মিলন হচ্ছে সেই মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে (বা সাথে বা সহিত) বর্তমানের এবং দূরের সঙ্গে কাছের। তার মানে হচ্ছে, সাহিত্য হচ্ছে সেই বাঁধন এবং মাধ্যম যা সবরকম যোগাযোগ এবং সম্পর্ক রক্ষা করে অন্য মানুষ, অন্য সময় ও দেশের সঙ্গে।
নিবন্ধের এই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে, পাঠকদের (জানি না ক’জন হতে পারেন) একটি তথ্য জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি। তা হচ্ছে বর্তমান লেখক খ্যাতিমান নন, কিন্তু যেটুকু তাঁর পরিচয়, তা গল্প-উপন্যাস এর রচয়িতা হিসাবে।
তাহলে ‘অপার বাংলা’-র এই বিশেষ সংখ্যায় হঠাৎ তিনি নিবন্ধ রচনায় আগ্রহী হলেন কেন! কী কারণে?
প্রথম কারণটি অবশ্যই সম্পাদকের অনুরোধ। সম্ভবত তিনি কিঞ্চিৎ বৈচিত্রের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন, এবং সাহিত্যিকের নিবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কিতই হবে, যা তাঁদের পত্রিকারও উপযুক্ত, সেই অনুমান থেকেই অনুরোধ।
দ্বিতীয় কারণটির উত্তর দেওয়ার দায় অবশ্যই এই অধীনের, কেননা তিনি সম্মত হয়েছেন এই নিবন্ধ রচনা করতে। কারণের একটি প্রাথমিক সূত্র একেবারে গোড়াতেই দিয়েছি, যে, দীর্ঘদিন সাহিত্যচর্চা করতে করতে, এই বিষয়ে নিজের কিছু ‘বলার কথা’ ভেতরে ভেতরে জমে ওঠাই স্বাভাবিক এবং তা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছেটাও স্বতঃস্ফূর্ত।
এইবার তাঁর সঙ্গে আর একটু ব্যাখ্যাও যোগ করব।
সাহিত্যচর্চা এবং ভাষাচর্চা প্রায় কাছাকাছি এবং প্রায় একইরকম কাজ হলেও, তার মধ্যে ইচ্ছে করলে একটু অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাপারটা দেখা যায়। সত্যি বলতে কি, সাহিত্যচর্চা বিষয়টা খুবই বড় এবং সীমাহীন এবং তারমধ্যে মানুষ, সভ্যতা, সমাজ সংস্কৃতি… সবকিছুর পৃথিবীব্যাপী সামগ্রিকতা মিশে রয়েছে।
কিন্তু ভাষাচর্চা বিষয়টিকে ইচ্ছে করলে আমরা একটু সীমাবদ্ধ করেও ভাবতে পারি… যেহেতু আমাদের চর্চার মাধ্যম হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমার নিবন্ধ রচনার আগ্রহ এবং রাজী হওয়ার অনেকটা কারণ কিন্তু ওই বাংলাভাষার কারণেও… অর্থাৎ কিনা সাধারণভাবে আলোচনাসূত্রে নানান কথার অবতারণা হলেও, বর্তমান নিবন্ধে কিন্তু আমরা বাংলাভাষা, সাহিত্য ও তার চর্চা নিয়েও কথা বলব। আর এই সত্যটাও বোঝার কোনো অসুবিধা নেই যে, ******* সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার বদলে যখনই আমরা শুধু বাংলা সাহিত্য আলোচনার দিকে মুখ ফেরাব, স্বাভাবিকভাবেই তখন ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও কিছুটা সংকুচিত হয়ে আসবে।
বিশেষ করে বাংলাভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে কথা বলা, আলোচনার আগ্রহ কেন, সেই বিষয়েও আলোকপাত করব।
প্রথমকথা তো অবশ্যই বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং যে কোনো ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারেই আমরা সর্বাপেক্ষা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করব, তাই নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। তবে বাঙালি মাত্রই তাদের মাতৃভাষা বাংলা হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং তাদের প্রকাশ মাধ্যম-ই বা কী হবে, আমরা জানি না। কিন্তু বাংলাভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের আমরা অবশ্যই ‘বাঙালি’ বলব।
ভাষা এবং সাহিত্যচর্চা করতে গেলেই দুটি ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হয়। সৌন্দর্যবোধ এবং সংযম। সুতরাং চর্চা যেখানে বাংলা নিয়ে, সেখানেও প্রতিটি পদে আমাদের দেশ, বাঙালিয়ানা, প্রকৃতি, সংস্কৃতি… সবকিছুর নিরিখেই ওই দুটি ব্যাপার স্মরণ করতে হবে বারবার, কিন্তু বাঙালি হয়েও যাঁরা দেশ-ভাষা-সংস্কৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা উদাসীন, তাদের বাঙালি তক্মা যদি থেকেও থাকে, তা সত্ত্বেও অন্তত সাহিত্য বিষয়টা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য, কেননা ভাষাগত সৌন্দর্য এবং ভাষাগত সংযমের বিষয়টা কিছুতেই তাঁদের মাথায় ঢুকবে না। ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের হয়তো সাহিত্যে ওই দুটি শর্তের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো সম্ভব হবে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে তাদের ভূমিকা কী এবং কতখানি, তা তারা ধরতে পারবে না। এবং এই কথাটা বিশেষভাবে মনে আসার কারণ, আমরা প্রবাসী বাঙালি এবং সাহিত্যচর্চা, ভাষাচর্চা করে থাকি নিয়মিত সেইজন্যই। প্রসঙ্গটির সামান্য আর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
এটা বিশেষ করে আমাদের বঙ্গসন্তানদের এক অনিবার্য প্রবণতা যে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর বসবাস অর্থাৎ ভূগোল-কে ছড়িয়ে দেওয়া। একদিকে আমরা বলি, পৃথিবী এখন কত ছোট হয়ে গেছে। আর একদিকে, লেখক যদি ইংল্যান্ড আমেরিকায় থাকেন, তাঁকে বলা হয় – প্রবাসী লেখক। শুধু তাই বা কেন! একটা সময় এমনকী বিহার-এর ভাগলপুর, মুঙ্গের, ছোটনাগপুরের বাসিন্দা হিসাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-কেও বলা হতো প্রবাসী বাঙালি লেখক। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড আমেরিকা সত্যি তো প্রবাস-ই বটে!
কথা হচ্ছে এই তক্মাটা কারা দেয় এবং কেন? সচেতনভাবেই কি, নাকি অবচেতন মনের হীনমন্যতার কারণে!
নাহ্ একটা সময়ে লেখক নামের পূর্বে এই অতিরিক্ত বিশেষণ বসানোর জন্য বাঙালির অন্তত কোনো হীনমন্যতা ছিল না। বরং প্রবাসী বিশেষণে কৃতী বঙ্গসন্তানকে একটু বেশি শ্রদ্ধেয় আসনে বসাবারই উদ্যোগ টের পাওয়া যেত। এবং সেটা দিতেন তৎকালীন পত্র-পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক থেকে শুরু করে সাধারণ পাঠকপাঠিকারাও। এই দেওয়ার পেছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল, তা হচ্ছে, নিজের দেশ (বাংলা), জাতি ও ভাষার জন্য অনিবার্য দুর্বলতা। সেখানে এমনকী ধর্মেরও কোনো পৃথক ভূমিকা ছিল না। আর একটা কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে, সারস্বতচর্চা করা সম্মানীয়জনকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাবার মতো মানসিক উদারতা। লেখালিখি, সাহিত্যচর্চা করা, শিল্পসংস্কৃতির চর্চা যে এলেবেলে, আটপৌরে, কাঠখোট্টা, হাটুরে-ফড়ে-ফেরেব্বাজ-চোরজোচ্চোরদের কাজ নয়, তারজন্য শিক্ষা-রুচি-বোধ-দর্শন-ভাবনার দরকার… মানুষ হিসেবে তাদের একটু অন্যরকম হতে হয়, এই ব্যাপারটা সাধারণ লোকজন বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই তাঁদের অন্য চোখে দেখতেন।
এমনকী প্রবাসী লেখক-সাহিত্যিকদের প্রতি দেশের মানুষের একটা কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল।
পাঠকপাঠিকা, সম্পাদকমণ্ডলী ভাবতেন, মানুষটা নিজের কাছে, প্রয়োজনে, ব্যবসায় বা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রবাসে থাকলেও নিজের ভাষার প্রতি দুর্বলতা এবং শ্রদ্ধা ত্যাগ করেননি, যে কারণে লেখালিখি করেন মাতৃভাষায়। এছাড়াও বাঙালি পাঠক ভাবতেন, লেখক প্রবাসে আছেন বলেই, তাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা দূরদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে এং সেখানকার মানুষ-জীবনযাপন-প্রকৃতি-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে জীবন ও সমাজের আয়না। সেই আয়নায়, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, প্রতিফলনের মাধ্যমে পাঠকরা অনেক কিছু দেখতে পান, জানতে পারেন।
সাম্প্রতিক কালে, আর্থসামাজিক বিবর্তনের ফলে মানুষের মানসিকতা বদলে গেছে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে… এমনকী মূল্যবোধও। বিশেষ করে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে একটা সবজান্তা ভাব এসেছে, সেটা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়। আমার তো মনে হয় আমরা দীর্ঘকাল বিদেশবিভূঁইয়ে জীবনযাপন করছি বলেই, যেন বেশ দূর থেকে, পাখির চোখে দেখার মতো, নিজের দেশ ও জাতিটাকে আরও ভালভাবে দেখার সুযোগ পাই। আর টের পাই, বাঙালির পরিবর্তনগুলো কেমন হয়েছে। খুব সত্যি কথা বললে, বলতে হয় – পরিবর্তনের ইতি থেকে নেতিবাচক দিকগুলোই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকট হয়েছে।
ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালিদের একটা “কলার ওল্টানো”র মতো আচার আচরণ টের পাওয়া যেত। এমন একটা ভাব ছিল বাঙালির, যে আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরাই পণ্ডিত, আমরাই জ্ঞানী-গুণী-বোদ্ধা। আমরা বিহারীদের মেড়ো ও খোট্টা, ওড়িয়াদের উড়ে, দক্ষিণীদের তেঁতুল, গুজরাটিদের গুজু, তামিলদের রাবণ… ইত্যাদি বলে উপহাস করতাম। উনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিংশশতাব্দীর কয়েকটি দশক পর্যন্ত সত্যি সত্যিই উন্নতজাতি হিসেবে বাঙালির তো একটা গরিমা এবং পরিচিতি ছিলই। কিন্তু তারপর? সেই অতীত পরিচয় ভাঙ্গিয়েই, এবং প্রত্যক্ষভাবে নিজেরা পলিটিকস্ ছাড়া অন্যকিছু না করে, চায়ের কাপে তুফান তুলে, অন্যের সমালোচনা করে, ফাঁকি মেরে, টুকলি করে, পরিশ্রম না করে… নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করেছে। এবং সর্বাঙ্গীণ সর্বনাশের সূচনা হয়েছে তখন থেকে।
একটু একটু করে বোঝা গেছে, দেশের মধ্যেই ক্রমশ রাজ্য এবং জাতি হিসেবে ধারাবাহিক অবনতি হয়ে চলেছে বাংলা ও বাঙালির। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃতি- ব্যবসা-যানবাহন-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক- উন্নয়ন-সামাজিকতা- রাস্তাঘাট- জলসম্পদ-সবুজায়ন-উড়ান-চিকিৎসা- দেশের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ… প্রত্যেকটি শাখায় বাঙালিরা একমাত্র ‘মুখে মারিতং জগত’ ছাড়া, কোনো দিকেই উন্নতি করতে পারে নি। বরং আগের দিনে যে গরিমা ছিল, ক্রমশ তা-ও অপহৃত হয়ে চলল। যুক্তফ্রন্ট সরকার কম্প্যুটার ঢুকতে দেয় নি সময়মতো এবং প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইংরিজি সরিয়ে দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। তখন থেকে ছাত্ররা অন্যরাজ্যে পড়তে এবং চাকরি করতে গেছে। আর অসুস্থ মানুষ চিকিৎসার জন্য ছুটল চেন্নাই-ভেলোর-মুম্বাই… সেই ধারাবাহিকতা আজও চলছে।
মস্তান- রংবাজ- তোলাবাজ-ঘুষখোরদের আবাসভূমি হতে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ। তারমধ্যে জন্ম নিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। বাঙালি আবেগে ভাসল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, সমগ্র বাঙালিজাতির চেতনা এবং বঙ্গসংস্কৃতি সেই ঘটনায় কতটা প্রভাবিত আর উপকৃত হয়েছিল বা হয়েছে, ভাবতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকের ধ্বস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থার মধ্যে নতুন শতাব্দীর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন যে কোনো শুভ বার্তা বহন করে নিয়ে আসেনি। বিগত একটি দশকেই তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে গেলছে। ঘুষ-দুর্নীতি-চোরাকারবার-মিথ্যাচার- সত্যের কণ্ঠরোধ-কৃতীজনকে অস্বীকার অপমান এবং চাটুকারদের স্বীকৃতি, রাজনীতিকে ধনী এবং ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার… এসবই পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙালির বৈশিষ্ট্য আর পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আর এইসব পরিবর্তন ও মানসিকতার প্রবল প্রভাব পড়েছে আমাদের তথাকথিত কালচার ও সাহিত্যের ওপরে। পড়াটাই স্বাভাবিক। কেননা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক পরিবর্তন, মূল্যবোধ যেদিকে যাবে, মানুষের প্রতিক্রিয়া ও প্রকাশও সেইদিকে যাবে। একটু আগে সাহিত্যকে সমাজের আয়না বলেছি। সুতরাং এখনকার যে বাংলা সাহিত্য, তারমধ্যে পরিষ্কারভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে বিস্মৃত, বিপন্ন, বিধ্বস্ত, মূল্যবোধহীন, গভীরতাহীন, লম্পট মানসিকতা। নেহাৎ দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতিত, যারা এই চর্চা এবং ব্যবসায় আছে, তারাও তো এই সমাজ ও পরিস্থিতির প্রোডাক্ট্।
যাই হোক, বাঙালি লেখকদের প্রবাসী বিশেষণে চিহ্নিতকরণের প্রসঙ্গেই আরও কিছু কথা এসে পড়ল… সম্ভবত যেসব কথা থেকে বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সম্পর্কিত সাম্প্রতিক অবক্ষয়েরও একটা ধারণা পাওয়া যাবে। প্রবাসী ছাপ্পা দিয়ে অনেক উৎকৃষ্ট রচনা এবং কৃতী লেখককে বাংলা সাহিত্য জগত ইদানীং দূরে সরিয়ে রাখার উদ্যোগ নেয়। তাঁদের লেখায় দেশের জীবনযাপনও মানসিকতা সম্পর্কে সমালোচনা, স্পষ্টোচ্চারণ দেশের সাহিত্য মাফিয়ারা সহ্য করতে পারে না। কথায় কথায় বলে ফেলেন, ওঁরা তো প্রবাসী… দেশের সম্যক অবস্থা জানবেন কোত্থেকে!
তখন কিন্তু দেশের সাহিত্য কারবারিরা মনে রাখেন না – পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে! যাক সে কথা।
সাহিত্যে অবক্ষয়ের ধারাবাহিকতা আরও বেশি দেখি ফেসবুক বা ফেবু সাহিত্য নামে গজিয়ে ওঠা নতুন মাধ্যমের প্রকাশে। শুধু ফেবু লেখার মধ্যেই না, অতঃপর তার মন্তব্যধারার মধ্যেও। প্রথমত খুব বিরল ব্যাতিক্রম ছাড়া, ফেবু-সাহিত্য যে নেহাতই হালকা, তাৎক্ষণিক, অগভীর, শস্তা, বানানো এবং দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যম ও উদ্যোগ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিষ্কার বোঝাই যায়, পত্রপত্রিকায় জায়গা ও সুযোগ না পেয়ে, নাম কেনার জন্য কিছু অযোগ্য লোক, নারীপুরুষ নির্বিশেষে, এই মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছে। এই মাধ্যমে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, বিচার বিবেচনা নেই। সুতরাং হাবিজাবি, এলোমেলো কিছু কথা… কিছু আবেগ, কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাদিকে গল্প-কবিতা-নিবন্ধ… যা ইচ্ছে বলে তুলে দেওয়া হয়।
তারপর এসব লেখক-লেখিকার মূল্যায়ন হয় লাইক-কমেন্ট-এর মাধ্যমে।
সেও এক বিচিত্র আয়োজন। বোঝা যায়, কিছু কিছু লোকের পেটোয়া অর্থাৎ ফিট করা মন্তব্যকারী বা মন্তব্যকারিণী থাকে, যারা অক্লেশে ওই ফেবু রচনার প্রবল প্রশংসা করে যায়। দারুণ, অসাধারণ, অসাম, সুপার্ব, অপূর্ব… ইত্যাদি কতরকম বিশেষণে যে বিশেষ কিছু কিছু রচয়িতার লেখার জন্য মন্তব্য বর্ষিত হয়, দেখে অবাক হতে হয়। কিন্তু ওই … সব ব্যাপারটাই মাত্র কিছুক্ষণের। তারপরেই শেষ। ভুঁইফোড় লেখক, ভুঁইপটকার মতো তার স্থায়িত্ব।
আর এক শ্রেণির লেখকও ইদানীং চিহ্নিত হচ্ছে বাংলাসাহিত্যে। এরা হচ্ছে টুকলিবাজ। ইংরিজিতে যাকে প্লাগিয়ারিজম বা বাংলায় আত্মসাৎ করা বলে, এরা হচ্ছে তাই। অন্যের লেখা থেকে টুকে বা চুরি করে এরা নিজের নামে চালায়। এই মূহুর্তে এরকম কিছু লেখক-লেখিকা যে বাংলা বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা এমনকি আমার মত প্রবাসীও জানে। এই বিষয়ে দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা বেশ একটা কঠোর এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যখনই কোনো টুকলি করা গল্প, রচনা ধরা পড়েছে, তখনই ওই পত্রিকা দপ্তর থেকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই সব লেখক-লেখিকার কোনো রচনা আর কোনোদিনই ওই হাউজের কোনো কাগজে ছাপা হবে না। কিন্তু অনেক টুকলি তো ধরাও পড়ে না। আসল কথা হচ্ছে, মানসিকতার অবনমন। যে নিজে যা নয়, সে নিজেকে তার থেকে বেশি করে দেখাতে চাইছে। দেখাতে গিয়ে ধরাও পড়ছে, কিন্তু তার তো লাজলজ্জা নেই। কথা আছে, ‘দুর্জনের নাহি লাজ, নাহি অপমান / সুজনকে এক কথা মরণ সমান’ কিন্তু সুজনের বড় অভাব।
আর কৃতী হতে চাওয়া এজাতীয় লোভী, মূর্খ, যশোপ্রার্থীদের মানসিকতায় সুযোগ নিতে বাংলাবাজারে নেমে পড়েছে একদল ধূর্ত ব্যবসায়ী, তারা কখনও আবার নিজেদের সম্পাদক – প্রকাশক বলেও পরিচয় দেয়… অনেকক্ষেত্রে তাদের একটি পত্রিকা এবং প্রকাশন সংস্থাও থাকে। এরা রীতিমত ভাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে, ওইসব যশোপ্রার্থীদের লেখা এবং বই ছাপিয়ে দেয় তাদের সংস্থা থেকে। একটা চুক্তি থাকে – কতটাকায় কত বই তারা ছাপিয়ে দেবে… এবং লেখক নিজেই তা বিক্রির দায়িত্ব নেয়… যদিও আসলে তা শেষপর্যন্ত জঞ্জালের মতো বিলি করতে হয় অনিচ্ছুক পাঠকদের কাছে। শস্তায় লেখক-সাহিত্যিক হতে চাওয়ার এহেন উদাহরণ বাঙালি ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে কজন আছে জানি না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বাজারে এখন ভুরি ভুরি – একথা আর চেপে রাখা যাচ্ছে না।
মুশকিল হচ্ছে অশিক্ষিত, অসাধু সাহিত্য ব্যবসায়ী এবং যশোপ্রার্থী, দুর্নীতিগ্রস্ত, লোভী লেখকদের দাপটে, প্রকৃত সাহিত্যবোধসম্পন্ন, মননশীল, চিন্তাশীল, শান্ত-ভাবুক-সচেতন লেখকরা হয়ে পড়ছেন প্রান্তবাসী। মাত্র দেড়শ বছর আগেও আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের এমনই একটা দশা ছিল, যে মানুষের বিশ্বাস ছিল না বাংলাভাষা কোনোদিন আন্তর্জাতিক স্তরে, শ্রদ্দেয় ভূমিকায় উঠে আসতে পারে। রাজা রামমোহন রায় প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত দিক থেকে বঙ্গদেশকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যাকে এখনও আমরা বলি বাংলার নবজাগরণ বা বেঙ্গল রেনেসাঁস। সমাজনীতি – সাহিত্য – রাজনীতি – ভাষা … বাংলাদেশের আধুনিকতা নির্মাণে এমন কোনো দিক নেই যার সূত্রপাত রামমোহন করেন নি। অতঃপর হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কৃতী ও খ্যাতিমান, বিবেকসম্পন্ন বঙ্গসন্তানরা বাংলা গড়ার জন্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন।
তার মধ্যে বিশেষভাবে ভাষা ও সাহিত্য (বাংলা)কে উপযুক্ত মর্যাদায়, গৌরবশালিনী করে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর প্রবল প্রতিভা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে। তারপরে পুরোধা হিসাবে এলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। অবশ্যই আরও অনেকে ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কল্লোলযুগের লেখক কবিবৃন্দ – সহ নজরুল-জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-প্রবোধকুমার… প্রমুখ ছিলেন। তারপরেই প্রায় কাছাকাছি সময়ে এলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর। তাঁদের ধারাপ্রবাহ অস্তমিত হতে হতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ধ্বজা উড়িয়ে আবির্ভূত হলেন প্রবল প্রতিভাবান সমরেশ-কালকূট। হ্যাঁ আরও ছিলেন তো বটেই… নরেন্দ্র – রমাপদ – সন্তোষ – বিমল – জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ। কিন্তু মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন স্বনাম ও ছদ্মনামে সমরেশ-কালকূট যিনি উভয়নামেই যতটা কৃতী ততটাই খ্যাতিমান। কিন্তু তারপর?
কোথায় যেন বাংলাসাহিত্য একটু থমকে যাওয়ার মতো অবস্থায় কাল গুনছে। সুনীল প্রয়াত হয়েছেন দশবছর আগে। শ্যামল চলে গেছে আরও আগে, তাঁদের সময়ের কেউ কেউ অস্তমিত হয়েও এখনও রয়েছেন। তাঁদের পরের দশকের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের লেখক সাহিত্যিক তো প্রায় নেই বললেই চলে। যা দু-তিনজন আছেন, তাঁদের মধ্যে বাণী বসুকে সম্ভবত সঠিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানই ব্যবহার করে নি। অবশ্য বাংলা সাহিত্যজগতে আনন্দবাজার ছাড়া আর সেরকম প্রতিষ্ঠানই বা কে! তাদের সম্পর্কে যা-ই বলা হোক, এখনও তারাই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেউ কেউ তাঁদের সম্পর্কে বাজারি পত্রিকা ইত্যাদি তক্মা দিলেও, বাস্তবতা এই যে, ওই হাউজের পত্রপত্রিকায় লেখার জন্য নির্বাচিত লেখক-লেখিকার পরিচিতি অন্তত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর কে টিকে থাকবেন বা থাকবেন না, সেটা নির্ভর করবে তাদের রচনার ওপর। এমন বেশ কয়েকজন লেখক আছেন, যাঁরা দেশ-আনন্দবাজার পত্রিকায় অনেক সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু কৃতী সাহিত্যিকের ভূমিকায় নিজেকে সম্মানীয় চিহ্নিত করে নিতে পারেন নি। কিন্তু অনেকেই পেরেছেন।
বাংলা সাহিত্যে (পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই। বাংলাদেশের সাহিত্যজগতের কথা এখানে আনছি না।) এরপরেই এসে পড়েছিলেন। সত্তর দশকের একগুচ্ছ লেখক, যাঁরা এখনও সৃষ্টিশীল… দুএকজন চলেও গেছেন। এঁদের মধ্যে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর, ভগীরথ মিশ্র, নবকুমার, ঝড়েশ্বর, স্বপ্নময়, (প্রয়াত সুচিত্রা) কিন্নর রায়, নলিনী… নিয়মিত লেখেন। এঁদেরও বয়েস বসে নেই। সুতরাং স্থায়িত্বের দৌড়ে শেষপর্যন্ত কতজন টিকে থাকবেন সময় বলবে। একজন, দুজন জায়গা করে নিচ্ছেন তারপরেও। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় হয় নি। তাছাড়া প্রচুর বেনোজল মিশে গেছে… এইসব আশি নব্বই দশকের লেখকদের মধ্যে। ঝাড়াই বাছাই হতে সময় লাগবে।
তবে একটা কথা ঠিক। সাহিত্যজগত কখনই বদ্ধ জলাশয় হয়ে থাকতে পারে না। হয় জোয়ার, নয়তো ভাঁটা কোনো একটা দিকে তাকে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যজগত যে সমরেশ-কালকূট এ এসে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলা যায় না, হয়তো আপাত নিস্তরঙ্গতার তলদেশে কোনো অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু তা অগ্র নাকি পশ্চাতে, বোঝা যাচ্ছে না এখনও। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। কিন্তু সেটা যে সামাজিক মাধ্যমে ঢাক পিটিয়ে আর আত্মপ্রচার করে হবে না, তা নিয়ে কোনোও সন্দেহ নেই। বরং কিছু পরিচিত লেখকের এই অসম্ভব বোকা বোকা, শস্তা আত্মপ্রচার তাদের ক্ষতি করে বলেই মনে হয়। অথচ এই প্রবণতা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এক গভীর অসুখ মনে হচ্ছে – নিজেই নিজের লেখা সম্বন্ধে বলে বেড়াচ্ছে – দারুণ, ফাটাফাটি! দেখে শুনে মনে হয়, এরা সাহিত্যচর্চা না করে ঝালমুড়ি, চানাচুর বিক্রি করেন না কেন!
আসলে সাহিত্যের বিচারশক্তি জন্মাতে সময় লাগে। তার বিকাশও হয় দেরিতে। তাড়াহুড়ো করে এবং অতি প্রগলভ্ হয়ে নিজেকে প্রকাশ ও খ্যাতিমান করতে গিয়ে অনেকেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। সাহিত্যের মধ্যে মিতাচারণ, শৃঙ্খলা আর প্রাজ্ঞতা না থাকলে কখনই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। মত্ততা যেমন আনন্দ নয়, তেমন সংযমই সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করে এবং সাহিত্যিককে সতত এসব কথা স্মরণ রাখতেই হবে।
আজ জনসংখ্যার নিরিখে আমাদের বাংলাভাষা পঞ্চম আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু সত্যোচ্চারণ করলে আমরা কি বুকে হাত রেখে বলতে পারি, ওই স্বীকৃতি প্রকৃত অর্থে কতখানি সম্মানিত করেছে আমাদের পৃথিবীর কাছে! কতটা গৃহীত হয় আমাদের সাহিত্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে? সামান্য… অতি সামান্য। কখনও যদি পরিচিতি স্বীকৃতির জন্য দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবে, তাহলে সেই সাহিত্য বা রচনাকে অন্তত ইংরিজিতে অনুবাদ করার দরকার হয়। কিন্তু কে করবে সে অনুবাদ? তেমন অনুবাদক কোথায় যিনি, বাংলা ছাড়াও ইংরিজি, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ বা জার্মান ভাষা জানেন! তাহলে আমাদের সাহিত্যের স্বীকৃতি-ই বা হবে কি করে?
মাঝখান থেকে অতি শস্তা, ফালতু, নেহাৎ এলেবেলে দুএকটা প্রান্তিক স্বীকৃতি যদি একটা দুটো গল্প বা রচনা অনুবাদের মাধ্যমে জুটে যায়, আমাদের আটপৌরে বাংলা সাহিত্যজগত তাই নিয়েই লম্ফঝম্ফ শুরু করে দেয়। কিছু কুয়োর ব্যাঙ সমালোচক তাই নিয়ে ফেবুতে লিখতে শুরু করে দেয় – আসল ব্যাপারটা না জেনেই। অনেক সময়, প্রতিযোগিতা বা স্বীকৃতি বা পুরস্কৃত হওয়া নয়, অনুদিত রচনার জন্য সৌজন্য প্রকাশকেই কেউ কেউ পুরষ্কার প্রাপ্তি বা বিরাট স্বীকৃতি বলে প্রচার শুরু করে দেয়। বহু অজ্ঞ বাঙালি পাঠক তাইতে হুজুগে মাতেন। কিছু বলার নেই নেহাৎ সহ্য করা ছাড়া। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগেই বলেছিলেন, “… বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মানলাভের ভাষা নহে, অর্থোপার্জনের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা…”। আজ পঞ্চম আন্তর্জাতিক ভাষার সম্মানিত স্বীকৃতির পরেও, আমরা মাতৃভাষার আবেগ ছাড়া আর কী সম্মান, স্বীকৃতি পেয়েছি? এই প্রশ্নের সামনে স্তব্ধ ও মূক হয়ে আরও কতদিন আমাদের বসে থাকতে হবে, সে উত্তর জানা নেই।
তবে কিনা সাহিত্যে নিবেদিত অনুসন্ধিৎসা মনন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠে আসে এই প্রসঙ্গে। সেটি এই যে, যে বিষয়, যার চর্চা, যার সঙ্গে জীবনযাপন… হয়তো জীবিকা নির্বাহ-ও এবং যে কর্ম করার জন্য কেউ কখনও মাথার দিব্যি দেয় নি অথচ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মতো পবিত্র-ঐকান্তিক-অনিবার্য আগ্রহে জীবনের অংশ করে নেওয়া, তার সম্পর্কে আমার কোনো বলার কথা অনুভূতির তলদেশে জমবে না, তা কি খুব স্বাভাবিক?
স্বাভাবিক না। কেননা সাহিত্য ভাবনার জগত ও দৃষ্টি থেকে উৎসারিত। যে ভাবুকের মন এই দুইয়ের অধিকারী তিনিই সাহিত্যিক। সাহিত্যের যে কোনো শাখার কথাই বলা হোক, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-রম্যরচনা… এমনকি নাটকরচনা বা নাট্যসাহিত্য রচনায় প্রাথমিক শর্ত এই দুটি জিনিস, ভাবনা ও দৃষ্টি। আর ভাবনা এবং দৃষ্টি যেটা করে, তা হচ্ছে, বাইরে থেকে যা কিছু আমরা আহরণ করি, মনের ভেতর ঢুকে, তা আর এক নতুন জগত সৃষ্টি করে। সেই নতুন জগত বা জগতের নতুনত্ব-ই প্রকাশিত হয় আমাদের লেখায়… সাহিত্য বাইরের জগতের সঙ্গে তখন তাকে আর মেশানো যায় না। তার কারণ, ভাবনা আর দৃষ্টি ওই দুই উপকরণের সঙ্গে নীরবে এবং নিভৃতে আরও একটি যে ব্যাপার ক্যাটালিস্ট বা উদ্বোধকের মতো মিশে যায়, তারই নাম অনুভূতি।
সুতরাং যা দাঁড়াল, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অলক্ষ্যে যে ত্রয়ী ক্রিয়াশীল, তারা হল, ভাবনা, দৃষ্টি ও অনুভূতি। এমনভাবেও বলা যায়, ভাবনা ও দৃষ্টির উপকরণকে অনুভূতির আঁচে উপযুক্তভাবে পরিপাক করতে পারলে, (ক্ষীর-শর্করার মিশ্রণকে যেমন আগুনের উত্তাপ সহকারে) সাহিত্যের সন্দেশ বানিয়ে তোলা যেতেও পারে।
এই কর্ম করতে করতে আগুন কিংবা আঁচের কোনো প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ অনুভূতির কিছুমাত্র কি সাহিত্যিক মননের তলদেশে জমা পড়ে না! তাকে ‘বলার কথা’ বলব, নাকি অভিজ্ঞতা, নাকি বয়সের ভারসঞ্জাত বকবকানি, সে কথা আলাদা, কিন্তু কিছু সঞ্চিত যে হবেই, তা এমনকী এই অধীনও টের পেয়েছে। আর পেয়েছে বলেই আজ সাড়ে চার দশকের ওপর চর্চার অধিকারে কিছু লিপিবদ্ধ করাকে প্রগলভ্তা বদলে দায়বদ্ধতা বলেই মনে করছি।
এই কথার সূত্রেই তাহলে উপরোক্ত একটি মন্তব্যের কিঞ্চিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এমন কিছু লেখক-সাহিত্যিক আছেন, যারা নিজের যাপিত জীবনের একটি দীর্ঘ সময় ধরে প্রভূত লেখালিখি করেছেন, গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তা সে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যও হয়তো। তারপরেও তাহলে সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের কোনো বক্তব্য নেই কেন?
এই প্রশ্নের দুটি উত্তর হয়।
প্রথম উত্তরটি এইরকম মানুষদের সারস্বত সাধনায় কৃতবিদ্য এবং সম্মানীয় করে তোলে এবং সেই উত্তরটি হচ্ছে, তাঁরা তাঁদের লেখা এবং রচনার মধ্যেই তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত বোধ ও ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এমনভাবেই যে, আলাদা করে ভাবনার তলদেশ থেকে উৎসারিত হওয়ার আর কিছু ছিল না।
দ্বিতীয় উত্তরটিকেও আমাদের গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। সেই উত্তর হচ্ছে, সেই লেখকবৃন্দ যাঁরা বছরের পর বছর ধরে পাতার পর পাতা লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যে না আছে কোনো সাহিত্য ভাবনার ব্যাখ্যা। না আছে পরবর্তীকালে অন্য প্রবন্ধ নিবন্ধের মধ্যেও সাহিত্যরচনা ও বোধ সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ তাঁরা শুধু লিখেছেন। হয়তো গল্প, উপন্যাসের বইও হয়েছে। এ প্রশ্ন করা শোভন হবে কিনা বলতে পারি না যে, সেইসব রচনা কতখানি সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। গল্প-উপন্যাসের বই মাত্রই সাহিত্য হয়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই। আষাঢ়ে গপ্পো লেখারও লোক আছে। আবার বটতলার বইয়েরও লেখক আছে। এ হেন লেখক আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। সম্ভবত লেখক হওয়ার তাড়না এবং প্রবণতা ইদানীং যে-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাইতে এই দ্বিতীয়-উত্তর সম্প্রদায়ের লেখকের সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে। অসংখ্য বই প্রকাশিত হওয়া এবং আমার মতো প্রবাসী লেখকেরও আজকাল অনেক বই উপহার পাওয়ার ঘটনায় এই “শুধু লেখক” সম্প্রদায় সত্যটির প্রমাণও পাওয়া যায়। গাদাগাদা বই পড়ে থাকে এবং ধুলো জমে।
খ্যাতিমান প্রয়াত লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য ওই ‘শুধু লেখক’দের লেখা ও বই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে। শ্যামলদা ওইসব বইয়ের ও লেখার তুলনা করতেন কাগজের ঠোঙা-র সঙ্গে। বলতেন, ওসব লেখার ভবিষ্যৎ হচ্ছে, চালডাল বা মুড়ি চিঁড়ে চিনি বা মশলার ঠোঙা। অস্বীকার করব না, এহেন লেখক, বই এবং ঠোঙার সন্ধান আমরা পেয়েছি। সত্যি বলতে কি তেমন লেখকদের সংখ্যা যে নেহাৎ নগণ্য নয়, তা আমরা অনেকেই জানি।
অথচ এই বাস্তবতার পাশাপাশি আর একটা কথাও খুব সত্যি যে, মানুষের হৃদয়ের আকুলতা কিন্তু অনেক কিছু না ভেবেই নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য ছটফট করে। সেই প্রকাশ, যে আকুতি, নাম বা গঠনের মাধ্যমেই হোক, ভালমন্দ যাই হোক, আসলে সেইটাই হচ্ছে সাহিত্যের আবেগ।
আর একথা তো অনস্বীকার্য যে আবেগ অথবা ইমোশন ব্যতিত সাহিত্যকর্ম কেন, কোনো সৃষ্টিধর্মী কাজই হয় না। কিন্তু বিচার করার দরকার হয়, সেই হৃদয়ের আকুলতা আর আবেগের মধ্যে, প্রকাশের সময়, কতটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। কে করে সেই বিচার? সাহিত্য ক্ষেত্রে পাঠক ছাড়া আর কে! এবং পাঠক তা করেন সচেতন না হয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই সামঞ্জস্যকে আমরা আকুলতা আর আবেগের ভারসাম্যও বলতে পারি, যা জন্ম দেয় সাহিত্যের।
কিন্তু শুধু কি তাই? না। রচনাশক্তির নৈপুণ্য – শেষপর্যন্ত সাহিত্যকে পাঠযোগ্য ও ভাবনার উপযুক্ত করে তোলে। আসলে কথা থেকেই কথা বাড়ে, এক কথা থেকে এসে পড়ে আরও পাঁচ কথা।
এই যে ‘রচনাশক্তির নৈপুণ্য’ কথাটা লিখলাম, ভেবে দেখুন তো মাত্র দুটো শব্দের মধ্যে কি বিপুল ব্যাখ্যার আকাশ থেকে যাচ্ছে। সাহিত্যক্ষেত্রে রচনাশক্তির নৈপুণ্য বলতে তো সবই এসে পড়ে। বিষয় ভাবনার কথা ছেড়ে দিলেও, নেহাৎ উল্লেখ করার জন্যই বলি, এই নৈপুণ্যেরই অন্তর্গত হচ্ছে, বাক্যগঠন, বাক্যের মধ্যে টেন্স্ এবং ভয়েস-এর ব্যবহার, সংলাপ, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা… কতটা দিতে হবে কিংবা হবে না, ফ্ল্যাশব্যাকে-এর ব্যবহার, পরিচ্ছেদ ভাগ… সবকিছুই কি এসে যাচ্ছে না, যা একটি রচনাকে নিবিড় নিয়ন্ত্রণের সাহিত্য করে তোলে। আর তা যদি সত্যিই হয়, ভেবে দেখবেন, সাহিত্যকর্ম তখনই সফল হয়, যখন তা যথেষ্ট সমসাময়িক হয়েও, একইসঙ্গে অতীতকে অস্বীকার করে না, বরং মনে পড়ায়, এবং ভবিষ্যৎকে স্মরণ করার জন্য ইঙ্গিতবাহী হয়ে থাকে।
এর পরের কথাটাই হচ্ছে প্রকাশ।
কাব্য হোক, সাহিত্য-শিল্প যাই হোক, প্রকাশের মধ্যে দিয়েই যে তার চরিতার্থতা, এটুকু বোঝা এবং উপলব্ধির জন্য কোনো অতিরিক্ত মেধার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু সাহিত্য সংক্রান্ত নিবন্ধে আমাদের তা উল্লেখ করতে হবে দুটি কারণে। এক হচ্ছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। আর এক হচ্ছে, প্রকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠককে আর একটু সচেতন এবং উদ্বুদ্ধ করতে। কেননা, যে যাই বলুক, কবি লেখক সকলেরই লক্ষ্য আসলে পাঠক সমাজ। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যসম্পর্কিত তাঁর এক রচনায় লিখেছিলেন, “… নীরস কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে…”। সুতরাং আসল কথাটা হচ্ছে, যে কোনো রচনাই লেখকের নিজের জন্য না… তিনি প্রকাশ করতে চান অন্যের জন্য… কেননা প্রকাশের আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যত নিজেকে প্রকাশ করা যায়, যতই নিজের অস্তিত্ব দৃঢ় হয়ে ওঠে।
এখন তো না হয় প্রকাশের আগ্রহ এবং প্রকাশ মাধ্যম নিয়ে ছেলেখেলা করার যুগ এসেছে। সে কথায় আমরা পরে আসব। কিন্তু যারা সেই ছেলেখেলাটা করে, তাঁদের অবগতির জন্য শুধু মনে করিয়ে দেব যে, একদিন নিজেকে প্রকাশের জন্য এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ কী না করেছে! সম্রাট অশোক, তাঁর নিজের কথাগুলো আগামী দিনের জন্য, কালের জন্য পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে দিয়েছিলেন। কেননা পাহাড় অনন্তকাল ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর যুগের পর যুগ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে – ওখানে কিছু লেখা, কিছু ভাবনার, কিছু কথার প্রকাশ আছে বলে।
সত্যিই তো! আজ কোথায় সেই সম্রাট অশোক, কোথায় সেই পাটলিপুত্র… কত পাঠান-মোগল-রাজপুত-বর্গিরা দাপিয়ে গেল ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে… দিনে দিনে বদলে গেল দেশ, তার সভ্যতা, সংস্কৃতির কত মিশ্রণ ঘটে গেল। কিন্তু পাথরের গায়ে খোদাই করা সেই লিপি রয়ে গেল কাল থেকে কালান্তরে… একদিন লিপি থেকে উদ্ধার হল ভাষা-ও। আর হাজার বছর আগেকার এক সম্রাটের নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছা প্রাণিত হল।
না, অশোকের শিলালিপির সেইসব ভাষ্য যে সাহিত্য তা নয়।
কিন্তু বহু অতীত থেকেই মানুষের নিজেকে প্রকাশের আকাঙ্খা কত তীব্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু যে লেখার মধ্যে তাই বা কেন? মূর্তি, ছবি, মন্দির, ভাস্কর্য … এসব নির্মাণও কে সেই একই কথা বলে না! আর এই সবেরই উদ্দেশ্য একটাই। মানুষ আন্তরিক হয়ে বেঁচে থাকতে চাইছে আরও মানুষের মধ্যে।
কিন্তু এই চাওয়ার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য চাওয়া ও অস্তিত্বে তফাৎ আছে।
একটা ব্যাপার বুঝতে হবে যে, সাহিত্য রচনা করতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও, সেটাই সব নয়। সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন কিন্তু ভাব… ভাবের বস্তু ও বিষয়। জ্ঞান আসলে চিরপরিবর্তনশীল এবং সেই কারণেই ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানের কথা, যেমন – পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। একথা একবার জানা হয়ে গেলে নতুন করে আর জানার দরকার হয় না। কিন্তু ভাব আর ভাবের কথা যতবারই বলা যায়, তা প্রতিভাত হয় বিভিন্ন মাত্রায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় – সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, এটা জ্ঞান। কিন্তু সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য হচ্ছে ভাবের বস্তু। জ্ঞানের প্রসার দরকার হয়। ভাব হচ্ছে সৃষ্টির জিনিস। সেই সৃষ্টির ব্যাপারে এবং তার প্রতিষ্ঠাতেই সাহিত্যিকের পরিচয়… ভাবকেই একজন লেখক তাঁর রচনায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাকে বলা হবে ভাবপ্রকাশ। আর সেই প্রকাশ যখন সর্বজনীন মুগ্ধতার দ্যোতক হয়, তা সাহিত্য হিসেবেও স্থায়িত্বে চিহ্নিত হয়।
আর ঠিক এই উপলব্ধি থেকেই বেরিয়ে আসে আর একটা কথা। সেটা হচ্ছে, বাস্তবের সত্য, জীবনের সত্য এবং প্রত্যক্ষতার সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের তফাৎ আছে। আবার রবীন্দ্রনাথ কোট করে বলছি, “… সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না…”। আবার তার অর্থ এই নয় যে, সাহিত্যের সত্যটা সত্য নয়। সুতরাং দুটোই সত্য, কিন্তু সাহিত্যের সত্য তার প্রকাশের গুণে অথবা বৈচিত্রে প্রকৃত সত্যের চেয়েও অন্যরকম একটা অনুভূতি সঞ্চার করে। সাহিত্য ছাড়াও অন্য শিল্পমাধ্যম, যেমন ভাস্কর্য বা চিত্র শিল্পও একই কথা বলে।
একটা ব্যাপার শুধু আমাদের বুঝে নিতে হবে।
এই যে আগের প্যারাগ্রাফে ‘অন্যরকম একটা অনুভূতি’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছি। ওই অনুভূতিটাই হচ্ছে আর্ট। ব্যাপারটা সূক্ষ্ম। কিন্তু যে কোনো শিল্পচর্চা করতে গেলেই, ওই সূক্ষ্মতাটুকুই শিল্পীর আসল পরিচয়। ওটুকু না থাকলে চলে না। লেখকের ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে, ওই অনুভূতি এবং তার সঠিক অথবা অমোঘ প্রকাশ, দুই মিলে তাঁকে সাহিত্যিক করে তোলে। এই কথাটাই ঘুরিয়ে বললে, এভাবে বলা যায় যে, সাহিত্যিক তথা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে, ভাবের বিষয়বস্তুকে ভাষায়, অন্তরের জিনিসকে বাইরের এবং সমকাল ও ক্ষণকালের বিষয়কে চিরকালের করে তোলা। সেটা করে ওই সূক্ষ্ম অনুভূতি।
এতো কথা বলার পরে, সাহিত্য ব্যাপারটা কী – এ সম্বন্ধে একটু ধারণা নিয়ে আমরা ক্রমশ বিষয়ান্তরে যাব।
সাহিত্য শব্দটা এসেছে ‘সহিত’ শব্দ থেকে। সহিত মানে আমরা জানি – সাথে বা সঙ্গে ইত্যাদি। অর্থাৎ শব্দরূপ বা ধাতুরূপ যদি বিচার করা যায়, তাহলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটা সম্পর্ক কিংবা মিলনের ব্যাপার আছে বোঝা যায়। এবং তাকে আর একটু ব্যাখ্যা করতে বলা যায়, এই মিলনটা কিন্তু শুধু ভাব-ভাষা-বই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। সাহিত্যের মিলন হচ্ছে সেই মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে (বা সাথে বা সহিত) বর্তমানের এবং দূরের সঙ্গে কাছের। তার মানে হচ্ছে, সাহিত্য হচ্ছে সেই বাঁধন এবং মাধ্যম যা সবরকম যোগাযোগ এবং সম্পর্ক রক্ষা করে অন্য মানুষ, অন্য সময় ও দেশের সঙ্গে।
নিবন্ধের এই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে, পাঠকদের (জানি না ক’জন হতে পারেন) একটি তথ্য জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি। তা হচ্ছে বর্তমান লেখক খ্যাতিমান নন, কিন্তু যেটুকু তাঁর পরিচয়, তা গল্প-উপন্যাস এর রচয়িতা হিসাবে।
তাহলে ‘অপার বাংলা’-র এই বিশেষ সংখ্যায় হঠাৎ তিনি নিবন্ধ রচনায় আগ্রহী হলেন কেন! কী কারণে?
প্রথম কারণটি অবশ্যই সম্পাদকের অনুরোধ। সম্ভবত তিনি কিঞ্চিৎ বৈচিত্রের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন, এবং সাহিত্যিকের নিবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কিতই হবে, যা তাঁদের পত্রিকারও উপযুক্ত, সেই অনুমান থেকেই অনুরোধ।
দ্বিতীয় কারণটির উত্তর দেওয়ার দায় অবশ্যই এই অধীনের, কেননা তিনি সম্মত হয়েছেন এই নিবন্ধ রচনা করতে। কারণের একটি প্রাথমিক সূত্র একেবারে গোড়াতেই দিয়েছি, যে, দীর্ঘদিন সাহিত্যচর্চা করতে করতে, এই বিষয়ে নিজের কিছু ‘বলার কথা’ ভেতরে ভেতরে জমে ওঠাই স্বাভাবিক এবং তা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছেটাও স্বতঃস্ফূর্ত।
এইবার তাঁর সঙ্গে আর একটু ব্যাখ্যাও যোগ করব।
সাহিত্যচর্চা এবং ভাষাচর্চা প্রায় কাছাকাছি এবং প্রায় একইরকম কাজ হলেও, তার মধ্যে ইচ্ছে করলে একটু অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাপারটা দেখা যায়। সত্যি বলতে কি, সাহিত্যচর্চা বিষয়টা খুবই বড় এবং সীমাহীন এবং তারমধ্যে মানুষ, সভ্যতা, সমাজ সংস্কৃতি… সবকিছুর পৃথিবীব্যাপী সামগ্রিকতা মিশে রয়েছে।
কিন্তু ভাষাচর্চা বিষয়টিকে ইচ্ছে করলে আমরা একটু সীমাবদ্ধ করেও ভাবতে পারি… যেহেতু আমাদের চর্চার মাধ্যম হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমার নিবন্ধ রচনার আগ্রহ এবং রাজী হওয়ার অনেকটা কারণ কিন্তু ওই বাংলাভাষার কারণেও… অর্থাৎ কিনা সাধারণভাবে আলোচনাসূত্রে নানান কথার অবতারণা হলেও, বর্তমান নিবন্ধে কিন্তু আমরা বাংলাভাষা, সাহিত্য ও তার চর্চা নিয়েও কথা বলব। আর এই সত্যটাও বোঝার কোনো অসুবিধা নেই যে, ******* সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার বদলে যখনই আমরা শুধু বাংলা সাহিত্য আলোচনার দিকে মুখ ফেরাব, স্বাভাবিকভাবেই তখন ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও কিছুটা সংকুচিত হয়ে আসবে।
বিশেষ করে বাংলাভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে কথা বলা, আলোচনার আগ্রহ কেন, সেই বিষয়েও আলোকপাত করব।
প্রথমকথা তো অবশ্যই বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং যে কোনো ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারেই আমরা সর্বাপেক্ষা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করব, তাই নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। তবে বাঙালি মাত্রই তাদের মাতৃভাষা বাংলা হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং তাদের প্রকাশ মাধ্যম-ই বা কী হবে, আমরা জানি না। কিন্তু বাংলাভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের আমরা অবশ্যই ‘বাঙালি’ বলব।
ভাষা এবং সাহিত্যচর্চা করতে গেলেই দুটি ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হয়। সৌন্দর্যবোধ এবং সংযম। সুতরাং চর্চা যেখানে বাংলা নিয়ে, সেখানেও প্রতিটি পদে আমাদের দেশ, বাঙালিয়ানা, প্রকৃতি, সংস্কৃতি… সবকিছুর নিরিখেই ওই দুটি ব্যাপার স্মরণ করতে হবে বারবার, কিন্তু বাঙালি হয়েও যাঁরা দেশ-ভাষা-সংস্কৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা উদাসীন, তাদের বাঙালি তক্মা যদি থেকেও থাকে, তা সত্ত্বেও অন্তত সাহিত্য বিষয়টা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য, কেননা ভাষাগত সৌন্দর্য এবং ভাষাগত সংযমের বিষয়টা কিছুতেই তাঁদের মাথায় ঢুকবে না। ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের হয়তো সাহিত্যে ওই দুটি শর্তের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো সম্ভব হবে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে তাদের ভূমিকা কী এবং কতখানি, তা তারা ধরতে পারবে না। এবং এই কথাটা বিশেষভাবে মনে আসার কারণ, আমরা প্রবাসী বাঙালি এবং সাহিত্যচর্চা, ভাষাচর্চা করে থাকি নিয়মিত সেইজন্যই। প্রসঙ্গটির সামান্য আর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
এটা বিশেষ করে আমাদের বঙ্গসন্তানদের এক অনিবার্য প্রবণতা যে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর বসবাস অর্থাৎ ভূগোল-কে ছড়িয়ে দেওয়া। একদিকে আমরা বলি, পৃথিবী এখন কত ছোট হয়ে গেছে। আর একদিকে, লেখক যদি ইংল্যান্ড আমেরিকায় থাকেন, তাঁকে বলা হয় – প্রবাসী লেখক। শুধু তাই বা কেন! একটা সময় এমনকী বিহার-এর ভাগলপুর, মুঙ্গের, ছোটনাগপুরের বাসিন্দা হিসাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-কেও বলা হতো প্রবাসী বাঙালি লেখক। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড আমেরিকা সত্যি তো প্রবাস-ই বটে!
কথা হচ্ছে এই তক্মাটা কারা দেয় এবং কেন? সচেতনভাবেই কি, নাকি অবচেতন মনের হীনমন্যতার কারণে!
নাহ্ একটা সময়ে লেখক নামের পূর্বে এই অতিরিক্ত বিশেষণ বসানোর জন্য বাঙালির অন্তত কোনো হীনমন্যতা ছিল না। বরং প্রবাসী বিশেষণে কৃতী বঙ্গসন্তানকে একটু বেশি শ্রদ্ধেয় আসনে বসাবারই উদ্যোগ টের পাওয়া যেত। এবং সেটা দিতেন তৎকালীন পত্র-পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক থেকে শুরু করে সাধারণ পাঠকপাঠিকারাও। এই দেওয়ার পেছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল, তা হচ্ছে, নিজের দেশ (বাংলা), জাতি ও ভাষার জন্য অনিবার্য দুর্বলতা। সেখানে এমনকী ধর্মেরও কোনো পৃথক ভূমিকা ছিল না। আর একটা কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে, সারস্বতচর্চা করা সম্মানীয়জনকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাবার মতো মানসিক উদারতা। লেখালিখি, সাহিত্যচর্চা করা, শিল্পসংস্কৃতির চর্চা যে এলেবেলে, আটপৌরে, কাঠখোট্টা, হাটুরে-ফড়ে-ফেরেব্বাজ-চোরজোচ্চোরদের কাজ নয়, তারজন্য শিক্ষা-রুচি-বোধ-দর্শন-ভাবনার দরকার… মানুষ হিসেবে তাদের একটু অন্যরকম হতে হয়, এই ব্যাপারটা সাধারণ লোকজন বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই তাঁদের অন্য চোখে দেখতেন।
এমনকী প্রবাসী লেখক-সাহিত্যিকদের প্রতি দেশের মানুষের একটা কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল।
পাঠকপাঠিকা, সম্পাদকমণ্ডলী ভাবতেন, মানুষটা নিজের কাছে, প্রয়োজনে, ব্যবসায় বা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রবাসে থাকলেও নিজের ভাষার প্রতি দুর্বলতা এবং শ্রদ্ধা ত্যাগ করেননি, যে কারণে লেখালিখি করেন মাতৃভাষায়। এছাড়াও বাঙালি পাঠক ভাবতেন, লেখক প্রবাসে আছেন বলেই, তাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা দূরদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে এং সেখানকার মানুষ-জীবনযাপন-প্রকৃতি-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে জীবন ও সমাজের আয়না। সেই আয়নায়, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, প্রতিফলনের মাধ্যমে পাঠকরা অনেক কিছু দেখতে পান, জানতে পারেন।
সাম্প্রতিক কালে, আর্থসামাজিক বিবর্তনের ফলে মানুষের মানসিকতা বদলে গেছে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে… এমনকী মূল্যবোধও। বিশেষ করে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে একটা সবজান্তা ভাব এসেছে, সেটা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়। আমার তো মনে হয় আমরা দীর্ঘকাল বিদেশবিভূঁইয়ে জীবনযাপন করছি বলেই, যেন বেশ দূর থেকে, পাখির চোখে দেখার মতো, নিজের দেশ ও জাতিটাকে আরও ভালভাবে দেখার সুযোগ পাই। আর টের পাই, বাঙালির পরিবর্তনগুলো কেমন হয়েছে। খুব সত্যি কথা বললে, বলতে হয় – পরিবর্তনের ইতি থেকে নেতিবাচক দিকগুলোই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকট হয়েছে।
ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালিদের একটা “কলার ওল্টানো”র মতো আচার আচরণ টের পাওয়া যেত। এমন একটা ভাব ছিল বাঙালির, যে আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরাই পণ্ডিত, আমরাই জ্ঞানী-গুণী-বোদ্ধা। আমরা বিহারীদের মেড়ো ও খোট্টা, ওড়িয়াদের উড়ে, দক্ষিণীদের তেঁতুল, গুজরাটিদের গুজু, তামিলদের রাবণ… ইত্যাদি বলে উপহাস করতাম। উনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিংশশতাব্দীর কয়েকটি দশক পর্যন্ত সত্যি সত্যিই উন্নতজাতি হিসেবে বাঙালির তো একটা গরিমা এবং পরিচিতি ছিলই। কিন্তু তারপর? সেই অতীত পরিচয় ভাঙ্গিয়েই, এবং প্রত্যক্ষভাবে নিজেরা পলিটিকস্ ছাড়া অন্যকিছু না করে, চায়ের কাপে তুফান তুলে, অন্যের সমালোচনা করে, ফাঁকি মেরে, টুকলি করে, পরিশ্রম না করে… নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করেছে। এবং সর্বাঙ্গীণ সর্বনাশের সূচনা হয়েছে তখন থেকে।
একটু একটু করে বোঝা গেছে, দেশের মধ্যেই ক্রমশ রাজ্য এবং জাতি হিসেবে ধারাবাহিক অবনতি হয়ে চলেছে বাংলা ও বাঙালির। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃতি- ব্যবসা-যানবাহন-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক- উন্নয়ন-সামাজিকতা- রাস্তাঘাট- জলসম্পদ-সবুজায়ন-উড়ান-চিকিৎসা- দেশের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ… প্রত্যেকটি শাখায় বাঙালিরা একমাত্র ‘মুখে মারিতং জগত’ ছাড়া, কোনো দিকেই উন্নতি করতে পারে নি। বরং আগের দিনে যে গরিমা ছিল, ক্রমশ তা-ও অপহৃত হয়ে চলল। যুক্তফ্রন্ট সরকার কম্প্যুটার ঢুকতে দেয় নি সময়মতো এবং প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইংরিজি সরিয়ে দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। তখন থেকে ছাত্ররা অন্যরাজ্যে পড়তে এবং চাকরি করতে গেছে। আর অসুস্থ মানুষ চিকিৎসার জন্য ছুটল চেন্নাই-ভেলোর-মুম্বাই… সেই ধারাবাহিকতা আজও চলছে।
মস্তান- রংবাজ- তোলাবাজ-ঘুষখোরদের আবাসভূমি হতে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ। তারমধ্যে জন্ম নিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। বাঙালি আবেগে ভাসল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, সমগ্র বাঙালিজাতির চেতনা এবং বঙ্গসংস্কৃতি সেই ঘটনায় কতটা প্রভাবিত আর উপকৃত হয়েছিল বা হয়েছে, ভাবতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকের ধ্বস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থার মধ্যে নতুন শতাব্দীর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন যে কোনো শুভ বার্তা বহন করে নিয়ে আসেনি। বিগত একটি দশকেই তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে গেলছে। ঘুষ-দুর্নীতি-চোরাকারবার-মিথ্যাচার- সত্যের কণ্ঠরোধ-কৃতীজনকে অস্বীকার অপমান এবং চাটুকারদের স্বীকৃতি, রাজনীতিকে ধনী এবং ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার… এসবই পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙালির বৈশিষ্ট্য আর পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আর এইসব পরিবর্তন ও মানসিকতার প্রবল প্রভাব পড়েছে আমাদের তথাকথিত কালচার ও সাহিত্যের ওপরে। পড়াটাই স্বাভাবিক। কেননা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক পরিবর্তন, মূল্যবোধ যেদিকে যাবে, মানুষের প্রতিক্রিয়া ও প্রকাশও সেইদিকে যাবে। একটু আগে সাহিত্যকে সমাজের আয়না বলেছি। সুতরাং এখনকার যে বাংলা সাহিত্য, তারমধ্যে পরিষ্কারভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে বিস্মৃত, বিপন্ন, বিধ্বস্ত, মূল্যবোধহীন, গভীরতাহীন, লম্পট মানসিকতা। নেহাৎ দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতিত, যারা এই চর্চা এবং ব্যবসায় আছে, তারাও তো এই সমাজ ও পরিস্থিতির প্রোডাক্ট্।
যাই হোক, বাঙালি লেখকদের প্রবাসী বিশেষণে চিহ্নিতকরণের প্রসঙ্গেই আরও কিছু কথা এসে পড়ল… সম্ভবত যেসব কথা থেকে বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সম্পর্কিত সাম্প্রতিক অবক্ষয়েরও একটা ধারণা পাওয়া যাবে। প্রবাসী ছাপ্পা দিয়ে অনেক উৎকৃষ্ট রচনা এবং কৃতী লেখককে বাংলা সাহিত্য জগত ইদানীং দূরে সরিয়ে রাখার উদ্যোগ নেয়। তাঁদের লেখায় দেশের জীবনযাপনও মানসিকতা সম্পর্কে সমালোচনা, স্পষ্টোচ্চারণ দেশের সাহিত্য মাফিয়ারা সহ্য করতে পারে না। কথায় কথায় বলে ফেলেন, ওঁরা তো প্রবাসী… দেশের সম্যক অবস্থা জানবেন কোত্থেকে!
তখন কিন্তু দেশের সাহিত্য কারবারিরা মনে রাখেন না – পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে! যাক সে কথা।
সাহিত্যে অবক্ষয়ের ধারাবাহিকতা আরও বেশি দেখি ফেসবুক বা ফেবু সাহিত্য নামে গজিয়ে ওঠা নতুন মাধ্যমের প্রকাশে। শুধু ফেবু লেখার মধ্যেই না, অতঃপর তার মন্তব্যধারার মধ্যেও। প্রথমত খুব বিরল ব্যাতিক্রম ছাড়া, ফেবু-সাহিত্য যে নেহাতই হালকা, তাৎক্ষণিক, অগভীর, শস্তা, বানানো এবং দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যম ও উদ্যোগ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিষ্কার বোঝাই যায়, পত্রপত্রিকায় জায়গা ও সুযোগ না পেয়ে, নাম কেনার জন্য কিছু অযোগ্য লোক, নারীপুরুষ নির্বিশেষে, এই মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছে। এই মাধ্যমে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, বিচার বিবেচনা নেই। সুতরাং হাবিজাবি, এলোমেলো কিছু কথা… কিছু আবেগ, কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাদিকে গল্প-কবিতা-নিবন্ধ… যা ইচ্ছে বলে তুলে দেওয়া হয়।
তারপর এসব লেখক-লেখিকার মূল্যায়ন হয় লাইক-কমেন্ট-এর মাধ্যমে।
সেও এক বিচিত্র আয়োজন। বোঝা যায়, কিছু কিছু লোকের পেটোয়া অর্থাৎ ফিট করা মন্তব্যকারী বা মন্তব্যকারিণী থাকে, যারা অক্লেশে ওই ফেবু রচনার প্রবল প্রশংসা করে যায়। দারুণ, অসাধারণ, অসাম, সুপার্ব, অপূর্ব… ইত্যাদি কতরকম বিশেষণে যে বিশেষ কিছু কিছু রচয়িতার লেখার জন্য মন্তব্য বর্ষিত হয়, দেখে অবাক হতে হয়। কিন্তু ওই … সব ব্যাপারটাই মাত্র কিছুক্ষণের। তারপরেই শেষ। ভুঁইফোড় লেখক, ভুঁইপটকার মতো তার স্থায়িত্ব।
আর এক শ্রেণির লেখকও ইদানীং চিহ্নিত হচ্ছে বাংলাসাহিত্যে। এরা হচ্ছে টুকলিবাজ। ইংরিজিতে যাকে প্লাগিয়ারিজম বা বাংলায় আত্মসাৎ করা বলে, এরা হচ্ছে তাই। অন্যের লেখা থেকে টুকে বা চুরি করে এরা নিজের নামে চালায়। এই মূহুর্তে এরকম কিছু লেখক-লেখিকা যে বাংলা বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা এমনকি আমার মত প্রবাসীও জানে। এই বিষয়ে দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা বেশ একটা কঠোর এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যখনই কোনো টুকলি করা গল্প, রচনা ধরা পড়েছে, তখনই ওই পত্রিকা দপ্তর থেকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই সব লেখক-লেখিকার কোনো রচনা আর কোনোদিনই ওই হাউজের কোনো কাগজে ছাপা হবে না। কিন্তু অনেক টুকলি তো ধরাও পড়ে না। আসল কথা হচ্ছে, মানসিকতার অবনমন। যে নিজে যা নয়, সে নিজেকে তার থেকে বেশি করে দেখাতে চাইছে। দেখাতে গিয়ে ধরাও পড়ছে, কিন্তু তার তো লাজলজ্জা নেই। কথা আছে, ‘দুর্জনের নাহি লাজ, নাহি অপমান / সুজনকে এক কথা মরণ সমান’ কিন্তু সুজনের বড় অভাব।
আর কৃতী হতে চাওয়া এজাতীয় লোভী, মূর্খ, যশোপ্রার্থীদের মানসিকতায় সুযোগ নিতে বাংলাবাজারে নেমে পড়েছে একদল ধূর্ত ব্যবসায়ী, তারা কখনও আবার নিজেদের সম্পাদক – প্রকাশক বলেও পরিচয় দেয়… অনেকক্ষেত্রে তাদের একটি পত্রিকা এবং প্রকাশন সংস্থাও থাকে। এরা রীতিমত ভাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে, ওইসব যশোপ্রার্থীদের লেখা এবং বই ছাপিয়ে দেয় তাদের সংস্থা থেকে। একটা চুক্তি থাকে – কতটাকায় কত বই তারা ছাপিয়ে দেবে… এবং লেখক নিজেই তা বিক্রির দায়িত্ব নেয়… যদিও আসলে তা শেষপর্যন্ত জঞ্জালের মতো বিলি করতে হয় অনিচ্ছুক পাঠকদের কাছে। শস্তায় লেখক-সাহিত্যিক হতে চাওয়ার এহেন উদাহরণ বাঙালি ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে কজন আছে জানি না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বাজারে এখন ভুরি ভুরি – একথা আর চেপে রাখা যাচ্ছে না।
মুশকিল হচ্ছে অশিক্ষিত, অসাধু সাহিত্য ব্যবসায়ী এবং যশোপ্রার্থী, দুর্নীতিগ্রস্ত, লোভী লেখকদের দাপটে, প্রকৃত সাহিত্যবোধসম্পন্ন, মননশীল, চিন্তাশীল, শান্ত-ভাবুক-সচেতন লেখকরা হয়ে পড়ছেন প্রান্তবাসী। মাত্র দেড়শ বছর আগেও আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের এমনই একটা দশা ছিল, যে মানুষের বিশ্বাস ছিল না বাংলাভাষা কোনোদিন আন্তর্জাতিক স্তরে, শ্রদ্দেয় ভূমিকায় উঠে আসতে পারে। রাজা রামমোহন রায় প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত দিক থেকে বঙ্গদেশকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যাকে এখনও আমরা বলি বাংলার নবজাগরণ বা বেঙ্গল রেনেসাঁস। সমাজনীতি – সাহিত্য – রাজনীতি – ভাষা … বাংলাদেশের আধুনিকতা নির্মাণে এমন কোনো দিক নেই যার সূত্রপাত রামমোহন করেন নি। অতঃপর হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কৃতী ও খ্যাতিমান, বিবেকসম্পন্ন বঙ্গসন্তানরা বাংলা গড়ার জন্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন।
তার মধ্যে বিশেষভাবে ভাষা ও সাহিত্য (বাংলা)কে উপযুক্ত মর্যাদায়, গৌরবশালিনী করে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর প্রবল প্রতিভা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে। তারপরে পুরোধা হিসাবে এলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। অবশ্যই আরও অনেকে ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কল্লোলযুগের লেখক কবিবৃন্দ – সহ নজরুল-জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-প্রবোধকুমার… প্রমুখ ছিলেন। তারপরেই প্রায় কাছাকাছি সময়ে এলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর। তাঁদের ধারাপ্রবাহ অস্তমিত হতে হতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ধ্বজা উড়িয়ে আবির্ভূত হলেন প্রবল প্রতিভাবান সমরেশ-কালকূট। হ্যাঁ আরও ছিলেন তো বটেই… নরেন্দ্র – রমাপদ – সন্তোষ – বিমল – জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ। কিন্তু মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন স্বনাম ও ছদ্মনামে সমরেশ-কালকূট যিনি উভয়নামেই যতটা কৃতী ততটাই খ্যাতিমান। কিন্তু তারপর?
কোথায় যেন বাংলাসাহিত্য একটু থমকে যাওয়ার মতো অবস্থায় কাল গুনছে। সুনীল প্রয়াত হয়েছেন দশবছর আগে। শ্যামল চলে গেছে আরও আগে, তাঁদের সময়ের কেউ কেউ অস্তমিত হয়েও এখনও রয়েছেন। তাঁদের পরের দশকের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের লেখক সাহিত্যিক তো প্রায় নেই বললেই চলে। যা দু-তিনজন আছেন, তাঁদের মধ্যে বাণী বসুকে সম্ভবত সঠিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানই ব্যবহার করে নি। অবশ্য বাংলা সাহিত্যজগতে আনন্দবাজার ছাড়া আর সেরকম প্রতিষ্ঠানই বা কে! তাদের সম্পর্কে যা-ই বলা হোক, এখনও তারাই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেউ কেউ তাঁদের সম্পর্কে বাজারি পত্রিকা ইত্যাদি তক্মা দিলেও, বাস্তবতা এই যে, ওই হাউজের পত্রপত্রিকায় লেখার জন্য নির্বাচিত লেখক-লেখিকার পরিচিতি অন্তত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর কে টিকে থাকবেন বা থাকবেন না, সেটা নির্ভর করবে তাদের রচনার ওপর। এমন বেশ কয়েকজন লেখক আছেন, যাঁরা দেশ-আনন্দবাজার পত্রিকায় অনেক সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু কৃতী সাহিত্যিকের ভূমিকায় নিজেকে সম্মানীয় চিহ্নিত করে নিতে পারেন নি। কিন্তু অনেকেই পেরেছেন।
বাংলা সাহিত্যে (পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই। বাংলাদেশের সাহিত্যজগতের কথা এখানে আনছি না।) এরপরেই এসে পড়েছিলেন। সত্তর দশকের একগুচ্ছ লেখক, যাঁরা এখনও সৃষ্টিশীল… দুএকজন চলেও গেছেন। এঁদের মধ্যে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর, ভগীরথ মিশ্র, নবকুমার, ঝড়েশ্বর, স্বপ্নময়, (প্রয়াত সুচিত্রা) কিন্নর রায়, নলিনী… নিয়মিত লেখেন। এঁদেরও বয়েস বসে নেই। সুতরাং স্থায়িত্বের দৌড়ে শেষপর্যন্ত কতজন টিকে থাকবেন সময় বলবে। একজন, দুজন জায়গা করে নিচ্ছেন তারপরেও। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় হয় নি। তাছাড়া প্রচুর বেনোজল মিশে গেছে… এইসব আশি নব্বই দশকের লেখকদের মধ্যে। ঝাড়াই বাছাই হতে সময় লাগবে।
তবে একটা কথা ঠিক। সাহিত্যজগত কখনই বদ্ধ জলাশয় হয়ে থাকতে পারে না। হয় জোয়ার, নয়তো ভাঁটা কোনো একটা দিকে তাকে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যজগত যে সমরেশ-কালকূট এ এসে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলা যায় না, হয়তো আপাত নিস্তরঙ্গতার তলদেশে কোনো অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু তা অগ্র নাকি পশ্চাতে, বোঝা যাচ্ছে না এখনও। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। কিন্তু সেটা যে সামাজিক মাধ্যমে ঢাক পিটিয়ে আর আত্মপ্রচার করে হবে না, তা নিয়ে কোনোও সন্দেহ নেই। বরং কিছু পরিচিত লেখকের এই অসম্ভব বোকা বোকা, শস্তা আত্মপ্রচার তাদের ক্ষতি করে বলেই মনে হয়। অথচ এই প্রবণতা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এক গভীর অসুখ মনে হচ্ছে – নিজেই নিজের লেখা সম্বন্ধে বলে বেড়াচ্ছে – দারুণ, ফাটাফাটি! দেখে শুনে মনে হয়, এরা সাহিত্যচর্চা না করে ঝালমুড়ি, চানাচুর বিক্রি করেন না কেন!
আসলে সাহিত্যের বিচারশক্তি জন্মাতে সময় লাগে। তার বিকাশও হয় দেরিতে। তাড়াহুড়ো করে এবং অতি প্রগলভ্ হয়ে নিজেকে প্রকাশ ও খ্যাতিমান করতে গিয়ে অনেকেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। সাহিত্যের মধ্যে মিতাচারণ, শৃঙ্খলা আর প্রাজ্ঞতা না থাকলে কখনই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। মত্ততা যেমন আনন্দ নয়, তেমন সংযমই সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করে এবং সাহিত্যিককে সতত এসব কথা স্মরণ রাখতেই হবে।
আজ জনসংখ্যার নিরিখে আমাদের বাংলাভাষা পঞ্চম আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু সত্যোচ্চারণ করলে আমরা কি বুকে হাত রেখে বলতে পারি, ওই স্বীকৃতি প্রকৃত অর্থে কতখানি সম্মানিত করেছে আমাদের পৃথিবীর কাছে! কতটা গৃহীত হয় আমাদের সাহিত্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে? সামান্য… অতি সামান্য। কখনও যদি পরিচিতি স্বীকৃতির জন্য দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবে, তাহলে সেই সাহিত্য বা রচনাকে অন্তত ইংরিজিতে অনুবাদ করার দরকার হয়। কিন্তু কে করবে সে অনুবাদ? তেমন অনুবাদক কোথায় যিনি, বাংলা ছাড়াও ইংরিজি, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ বা জার্মান ভাষা জানেন! তাহলে আমাদের সাহিত্যের স্বীকৃতি-ই বা হবে কি করে?
মাঝখান থেকে অতি শস্তা, ফালতু, নেহাৎ এলেবেলে দুএকটা প্রান্তিক স্বীকৃতি যদি একটা দুটো গল্প বা রচনা অনুবাদের মাধ্যমে জুটে যায়, আমাদের আটপৌরে বাংলা সাহিত্যজগত তাই নিয়েই লম্ফঝম্ফ শুরু করে দেয়। কিছু কুয়োর ব্যাঙ সমালোচক তাই নিয়ে ফেবুতে লিখতে শুরু করে দেয় – আসল ব্যাপারটা না জেনেই। অনেক সময়, প্রতিযোগিতা বা স্বীকৃতি বা পুরস্কৃত হওয়া নয়, অনুদিত রচনার জন্য সৌজন্য প্রকাশকেই কেউ কেউ পুরষ্কার প্রাপ্তি বা বিরাট স্বীকৃতি বলে প্রচার শুরু করে দেয়। বহু অজ্ঞ বাঙালি পাঠক তাইতে হুজুগে মাতেন। কিছু বলার নেই নেহাৎ সহ্য করা ছাড়া। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগেই বলেছিলেন, “… বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মানলাভের ভাষা নহে, অর্থোপার্জনের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা…”। আজ পঞ্চম আন্তর্জাতিক ভাষার সম্মানিত স্বীকৃতির পরেও, আমরা মাতৃভাষার আবেগ ছাড়া আর কী সম্মান, স্বীকৃতি পেয়েছি? এই প্রশ্নের সামনে স্তব্ধ ও মূক হয়ে আরও কতদিন আমাদের বসে থাকতে হবে, সে উত্তর জানা নেই।
এই পৃষ্ঠাটি লাইক এবং শেয়ার করতে নিচে ক্লিক করুন


অতুলনীয়
Probonhyo ti puro porecho ami. Olpo porisore khub guchiye likecho. Sob je sohomot ta noy tobe nobbui vag sohomot. Lekhok der samne je voyonkor bipod seta thik bolecho. Ashakori valo acho. Sutapan chattopadhyay